মত দ্বিমত
বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে দায়, দুর্নীতি ও আত্মসমালোচনার অনুপস্থিতি
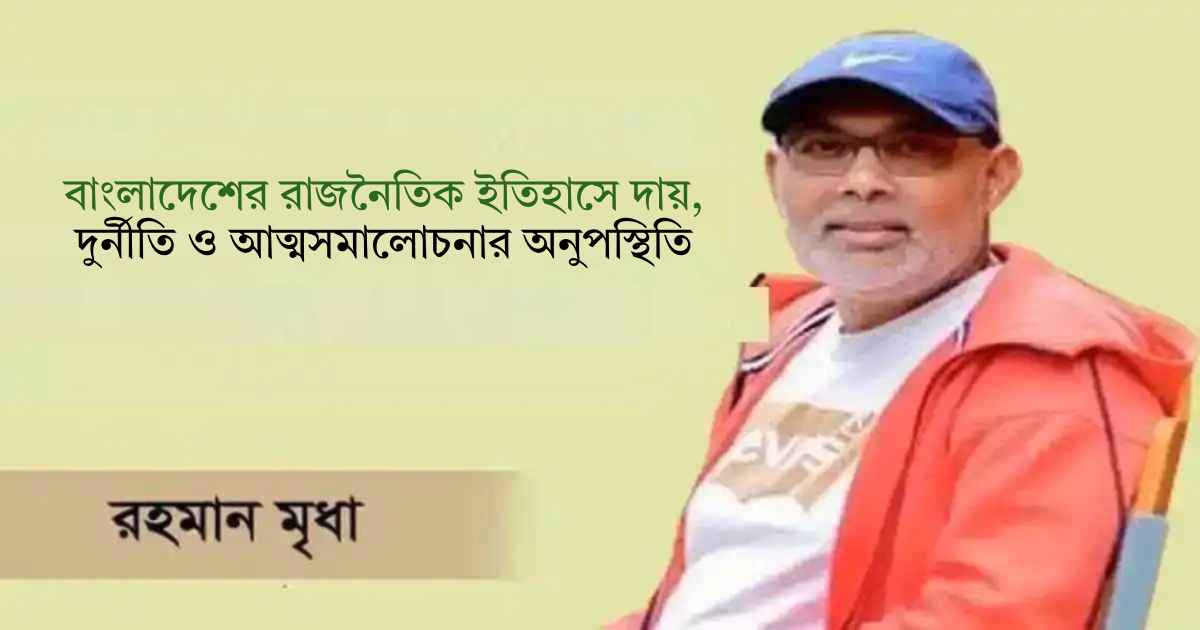
বাংলাদেশের রাজনীতিতে এখন এক অদ্ভুত রীতি গড়ে উঠেছে— দেশের যেকোনো ব্যর্থতা, দুর্নীতি বা অন্যায়ের দায় যেন সবসময় এক দলের ঘাড়েই পড়ে। যেন এ দেশের অন্য কারও কোনো পাপ নেই, কোনো অপরাধ নেই, কোনো দায় নেই। দেশে একটা প্রচলিত প্রবাদ আছে— “সব মাছে গু খায়, ঘাউরা মাছের দোষ হয়।” এই প্রবাদটাই যেন বাংলাদেশের রাজনৈতিক বাস্তবতার খোলামেলা প্রতিচ্ছবি।
গত পাঁচ দশকের ইতিহাস ঘাটলে দেখা যায়, ক্ষমতার মসনদে বসা প্রতিটি নেতা— শেখ মুজিব থেকে শুরু করে জিয়াউর রহমান, এরশাদ, খালেদা জিয়া কিংবা শেখ হাসিনা— সবাই কখনও না কখনও ক্ষমতার অপব্যবহার, দুর্নীতি, অন্যায় আর মানবাধিকার লঙ্ঘনের সঙ্গে জড়িত থেকেছেন। তবু আজ যখন ইতিহাসের বোঝা তোলা হয়, তখন সেই সব দোষের ভার যেন একচেটিয়াভাবে চাপিয়ে দেওয়া হয় আওয়ামী লীগের ঘাড়ে।
কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে— সব অপরাধ কি এক দলের?
দেশে যে রাজনৈতিক দুর্নীতি, নৈতিক অবক্ষয়, প্রশাসনিক অনাচার আর জনগণের প্রতি অবিচার চলেছে, তার মূল শেকড় তো বহু গভীরে — সব দলের শাসনকালেই এর জন্ম, বিকাশ, আর প্রাতিষ্ঠানিক রূপ। তাহলে কেন আজও এই জাতি সেই একই “ঘাউরা মাছের দোষ” সংস্কৃতির শিকার? বাংলাদেশের রাজনীতি যেন এক রসাতলে নেমে গেছে, যেখানে ক্ষমতার লোভ, দুর্নীতির প্রলোভন, এবং রাজনৈতিক প্রতিহিংসা মিলেমিশে তৈরি করেছে এক অদৃশ্য কিন্তু প্রাণঘাতী চক্র। আর সেই চক্রের ভেতরে থেকে সব দলই যেমন অপরাধে জড়িত, তেমনি নিজেদের দায় এড়াতে অন্যের ঘাড়ে দোষ চাপাতে ব্যস্ত।
আসুন, একটু জানি দেশের প্রেসিডেন্ট/প্রধানমন্ত্রীদের কুকর্ম ও তার ফলাফল সম্পর্কে
শেখ মুজিবুর রহমান (১৯৭২–১৯৭৫)
কুকর্ম: একদলীয় শাসনব্যবস্থা (BAKSAL) প্রতিষ্ঠা, রাজনৈতিক বিরোধীদের দমন, ১৯৭৪ সালের দুর্ভিক্ষে প্রশাসনিক ব্যর্থতা, জাতীয় রক্ষী বাহিনীর (Jatiya Rakkhi Bahini) মাধ্যমে গ্রেপ্তার, নির্যাতন ও বিচারবহির্ভূত হত্যা। তিনি এক নায়কতন্ত্র শাসন কায়েম করেন — শতভাগ ক্ষমতার অপব্যবহার ও দুর্নীতিগ্রস্ত পরিবারতন্ত্রের রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করেন।
ফলাফল: ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট সেনাবাহিনীর একদল অফিসারের হাতে নিহত হন।
জিয়াউর রহমান (১৯৭৭–১৯৮১)
কুকর্ম: সেনা অভ্যুত্থানের মাধ্যমে ক্ষমতা দখল, সরকারি তহবিলের অপব্যবহার, রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড ও ক্ষমতার অপব্যবহার। দলীয় স্বার্থে সামরিক প্রশাসনকে ব্যবহার করে গণতন্ত্রকে প্রহসনে পরিণত করেন।
ফলাফল: ১৯৮১ সালের ৩০ মে সেনা অভ্যুত্থানে নিহত হন।
হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদ (১৯৮২–১৯৯০)
কুকর্ম: সেনা অভ্যুত্থানের মাধ্যমে ক্ষমতা দখল, সংবিধান স্থগিত, নির্বাচনী প্রহসন, বিরোধী আন্দোলন দমন, ব্যাপক দুর্নীতি ও প্রশাসনিক অবক্ষয়। জনগণের কণ্ঠরোধ করে নিজের ক্ষমতা দীর্ঘায়িত করেন।
ফলাফল: তীব্র গণআন্দোলনের চাপে ক্ষমতা হারান; মৃত্যুর আগ পর্যন্ত দুর্নীতি ও রাজনৈতিক সমালোচনার মুখোমুখি থাকেন।
খালেদা জিয়া (১৯৯১–১৯৯৬, ২০০১–২০০৬)
কুকর্ম: দুর্নীতি মামলা (জিয়া অরফানেজ ট্রাস্ট, গ্যাটকো), রাজনৈতিক সহিংসতা, ২১ আগস্ট গ্রেনেড হামলার নেপথ্য অভিযোগ, মানবাধিকার লঙ্ঘন, প্রশাসনিক দুর্নীতি ও দলীয় সন্ত্রাস।
ফলাফল: দেশে ব্যাপক অস্থিরতা বৃদ্ধি; সেনা হস্তক্ষেপের পর ক্ষমতা হারান ও দীর্ঘদিন রাজনৈতিকভাবে অচল অবস্থায় থাকেন।
উৎস: আমার নিজের দেখা।
শেখ হাসিনা (২০০৯ – ২০২৪)
কুকর্ম: ছাত্র আন্দোলন দমন (১৪০০+ নিহত), গুম, নির্যাতন ও রাজনৈতিক প্রতিশোধমূলক মামলা, দুর্নীতি (পদ্মা সেতু, মেঘনা–গোমতি সেতু, পূর্বাচল প্লট বরাদ্দসহ), সংবাদমাধ্যম ও বিচার বিভাগের উপর দমননীতি। তিনি একদলীয় কর্তৃত্ববাদী শাসনের প্রতীক হয়ে ওঠেন— যেখানে দেশ, দল ও পরিবার একাকার হয়ে গেছে।
ফলাফল: আইনি অভিযোগ ও আন্তর্জাতিক সমালোচনার মুখেও ক্ষমতা ত্যাগ করেননি; শেষপর্যন্ত ‘সেফ একজিট’ চুক্তিতে ভারতে আশ্রয় নেন।
বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে এই নেতাদের কুকর্মের প্রতিফলন আজও সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রতিটি স্তরে রক্তক্ষরণের মতো দৃশ্যমান। কেউ ক্ষমতার নেশায় মানুষ হত্যা করেছে, কেউ জাতির সম্পদ লুটেছে, কেউ স্বাধীনতার নামে স্বাধীনতাকে বন্দি করেছে। অনেকে তাদের অপরাধের ফল ভোগ করেছে—কেউ গুলিতে নিহত, কেউ জনগণের রোষে অপদস্থ, কেউ দেশ ছেড়ে পালিয়ে বিদেশে নির্বাসিত জীবন কাটাচ্ছে। কিন্তু বিস্ময়কর সত্য হলো—একজনও স্বেচ্ছায় ক্ষমতা ত্যাগ করেননি। যেন ক্ষমতা তাদের কাছে এক ঈশ্বরত্ব, যার জন্য জীবন, নীতি, এমনকি দেশকেও উৎসর্গ করা যায়।
বাংলাদেশের রাজনৈতিক নেতা ও দলগুলোর আচরণে তাই এক ধরনের বেহায়া নির্লজ্জতা ও নৈতিক দেউলিয়াত্ব স্পষ্ট। জনগণের প্রতি দায়িত্ববোধ নেই, লজ্জা নেই, আত্মসমালোচনার ক্ষমতাও নেই। রাজনীতি এখন আর সেবা নয়, এক নির্মম প্রতিযোগিতা— কে বেশি দুর্নীতিগ্রস্ত, কে বেশি নিষ্ঠুর, কে ক্ষমতার চাবিকাঠি বেশি শক্ত করে ধরে রাখতে পারে। এই সংস্কৃতি রাজনৈতিক সহিংসতা, দুর্নীতি, এবং প্রশাসনিক অপব্যবহারের এক অন্ধকার যুগ সৃষ্টি করেছে, যেখানে রাষ্ট্রের শান্তি, ন্যায় ও স্থিতিশীলতা চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে গেছে।
উপরে তো কেবল সংক্ষিপ্তভাবে উল্লেখ করা হয়েছে টপ লেভেলের কিছু নেতার নাম, কিন্তু ভাবুন—যে অসংখ্য নেতা ও কর্মীর বিরুদ্ধে ভয়ঙ্কর অপরাধ, দুর্নীতি, হত্যা, মানবাধিকার লঙ্ঘন ও অর্থপাচারের অভিযোগ রয়েছে, তারা দিব্যি বিদেশে বিলাসবহুল জীবন কাটাচ্ছে। কেউ লন্ডনে, কেউ দুবাইয়ে, কেউ কানাডায়—সবাই নিরাপদ, অথচ দেশের আইন তাদের নাগাল পায় না।
প্রশ্ন জাগে—বিশ্বজুড়ে যখন আইনের এক জাল আছে, ইন্টারপোল নামের শক্তিশালী আন্তর্জাতিক সংস্থা রয়েছে, তখন গত ৫৪ বছরে তারা কি একজনকেও বাংলাদেশে ফেরত পাঠিয়েছে? না, একটিও না। কেন? কারণ, বাংলাদেশের আইন ও বিচারব্যবস্থা এতটাই দুর্বল, দলনির্ভর ও দুর্নীতিগ্রস্ত যে বিশ্বের কোনো দেশই আজ বাংলাদেশের ন্যায়বিচার ব্যবস্থার ওপর আস্থা রাখতে চায় না।
যখনই কোনো সরকার ক্ষমতা হারায়, তখনই হাজারো মিথ্যা মামলা, রাজনৈতিক প্রতিহিংসা ও প্রশাসনিক নিপীড়নের শিকার হয় পরাজিত পক্ষ। ফলে সত্য-মিথ্যা, অপরাধ-অভিযোগ— সবই মিশে গেছে এক অনিশ্চিত ধোঁয়াশায়। এই বাস্তবতাই প্রমাণ করে—আমরা জাতি হিসেবে কতটা দুরবস্থার শিকার, আর আন্তর্জাতিক অঙ্গনে আমাদের গ্রহণযোগ্যতা কতটা ক্ষয়প্রাপ্ত হয়েছে।
আমরা এখন এমন এক রাষ্ট্রব্যবস্থার বন্দি, যেখানে অপরাধীরা পালিয়ে যায়, কিন্তু ন্যায়বিচার পালানোর পথ খুঁজে পায় না। এখন যেমন সব দোষ শুধু আওয়ামী লীগের ওপর চাপানো হচ্ছে, তার কারণ যেমন;
১. দীর্ঘকাল ক্ষমতাসীন থাকা: দীর্ঘ সময় ক্ষমতায় থাকলে জনগণের প্রত্যাশা বাড়ে, হতাশাও বাড়ে। তাই সরকারের প্রতিটি ব্যর্থতা, প্রতিটি ক্ষোভ সরাসরি ক্ষমতাসীন দলের দিকেই ধাবিত হয়।
২. মিডিয়া ও রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা:বাংলাদেশের সংবাদমাধ্যম ও বিরোধী দলগুলোর একাংশ রাজনৈতিক হিসাবেই সব দোষ একপাক্ষিকভাবে প্রচার করে। তথ্যের চেয়ে আবেগ, যুক্তির চেয়ে প্রতিশোধ প্রবল।
৩. জনমতের মনস্তত্ত্ব: জনগণ প্রায়ই ব্যক্তিকে বিচ্ছিন্নভাবে বিচার করতে চায় না; বরং বৃহত্তম ও দৃশ্যমান শক্তিকে দোষারোপ করাই সহজ। আওয়ামী লীগ সেই দৃশ্যমান শক্তি—তাই দোষারোপের ভার তার ঘাড়েই পড়ে।
৪. প্রবাদের বাস্তব প্রতিফলন: বাংলাদেশ আজ সেই প্রবাদটির এক জীবন্ত প্রতিচ্ছবি— “সব মাছে গু খায়, ঘাউরা মাছের দোষ হয়।” সবাই অপরাধ করেছে, সবাই কুকর্মে জড়িত, কিন্তু দৃশ্যমান ও ক্ষমতাধর ঘাউরা মাছের ঘাড়েই এখন দোষের সমস্ত ভার চাপানো হচ্ছে।
বাংলাদেশে দুর্নীতি কোনো একক ব্যক্তি বা দলের সমস্যা নয়—এটি পুরো রাজনৈতিক সংস্কৃতির মজ্জাগত রোগে পরিণত হয়েছে। ক্ষমতা, সুবিধা, আর ব্যক্তিগত স্বার্থের অন্ধ নেশায় আজ রাজনীতি নীতিহীন, প্রশাসন জবাবদিহিহীন, আর জনগণ নিরুপায়।
•রাজনৈতিক স্বার্থ: ক্ষমতাসীন দল থেকে শুরু করে বিরোধী দল—সকলেই নিজেদের সুবিধার জন্য দুর্নীতি, ক্ষমতার অপব্যবহার এবং প্রশাসনিক জালিয়াতিতে জড়িয়ে পড়েছে। একে অপরকে দোষারোপ করলেও বাস্তবে তারা একই মুদ্রার এপিঠ-ওপিঠ।
•আইনি দুর্বলতা: বিচারব্যবস্থা পক্ষপাতদুষ্ট, তদন্ত সংস্থা ভীত, আর আইনের প্রয়োগ বেছে বেছে করা হয়। ফলে দুর্নীতি, মানবাধিকার লঙ্ঘন বা রাষ্ট্রদুর্বৃত্তি—সবই পার পেয়ে যায় ক্ষমতার ছায়াতলে।
•ভয় ও রাজনৈতিক চাপ: ক্ষমতাধর নেতাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিলে সেটি “রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র” বলে আখ্যা দেওয়া হয়, আর সেই অজুহাতে আইনি নীরবতা জারি থাকে। ফল—ন্যায়বিচারের বদলে ভয়ই হয়ে ওঠে রাষ্ট্রের নীতি।
•ফলাফল: শেখ হাসিনার শাসনকাল এই সংস্কৃতির চূড়ান্ত প্রতিচ্ছবি। দুর্নীতিগ্রস্ত প্রশাসন ও তোষণনীতি তাকে ক্ষমতায় টিকিয়ে রেখেছে, কিন্তু সেই সুরক্ষাই দেশকে আজ দুর্নীতির এক অশেষ চক্রে বন্দি করে ফেলেছে। তবে শ্রীলঙ্কা প্রমাণ করেছে—জনগণ যদি জাগে, দুর্নীতিগ্রস্ত শাসক টিকতে পারে না। সেখানে মানুষ রাস্তায় নেমে একসময় সর্বশক্তিমান রাজাপাক্ষেকে ক্ষমতা থেকে সরিয়ে দিয়েছে। তাদের এই গণঅভ্যুত্থান ছিল দুর্নীতির বিরুদ্ধে এক জাগ্রত জাতির গর্জন।
বাংলাদেশও ইতিহাসে এমন গণজোয়ার দেখেছে—স্বৈরাচারের পতন ঘটেছে, কিন্তু দুর্নীতির শিকড় রয়ে গেছে অটুট। কারণ, আমরা শাসক বদলেছি, কিন্তু রাজনৈতিক সংস্কৃতি বদলাতে পারিনি। যতদিন পর্যন্ত জনগণ সত্যিকার অর্থে নৈতিকভাবে সজাগ, ঐক্যবদ্ধ ও দৃঢ় হবে না—ততদিন দুর্নীতি, ক্ষমতার অপব্যবহার ও সহিংসতা বাংলাদেশের ভবিষ্যৎকে বন্দি রাখবে।
এখন কী করা উচিত?
১. দুর্নীতি ও সন্ত্রাসমুক্ত রাজনৈতিক সংস্কার: রাজনীতি হতে হবে সেবা, ক্ষমতা নয়। দলের আগে দেশ, আর দেশের আগে ন্যায়বোধ।
২. সততা ও স্বচ্ছতা: প্রশাসন ও দলীয় কাঠামোতে স্বচ্ছতা নিশ্চিত না হলে, কোনো সংস্কারই টেকসই নয়।
৩. আইন ও বিচারব্যবস্থার স্বাধীনতা: বিচারব্যবস্থাকে সম্পূর্ণ রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত করতে হবে—ন্যায়বিচার যেন কোনো দলের নয়, জনগণের অধিকার হয়।
৪. নাগরিক সচেতনতা: জনগণকে বুঝতে হবে, নীরবতা মানেই অপরাধের পক্ষে থাকা। প্রতিটি নাগরিককে দুর্নীতি ও অপব্যবহারের বিরুদ্ধে নিজের অবস্থান নিতে হবে।
৫. জনগণের অংশগ্রহণ: শুধু নির্বাচনে নয়—রাষ্ট্র পরিচালনার প্রতিটি পর্যায়ে জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে।
গণতন্ত্রকে টিকিয়ে রাখতে হলে গণচাপই হতে হবে দুর্নীতিবিরোধী অস্ত্র।
বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাস আজ এক নির্মম সত্যের সামনে দাঁড়িয়ে— ক্ষমতা কখনও কাউকে ন্যায়বান করেনি, বরং দুর্নীতিগ্রস্ত করেছে। এই দেশে অনেক নেতা নিহত হয়েছেন, কেউ স্বৈরাচারের পতনে অপমানিত, কেউ বিদেশে নির্বাসিত, কেউ আজও গোপনে অপরাধের দায় বহন করছে। কিন্তু একটিও ব্যতিক্রম নেই—কেউ স্বেচ্ছায় ক্ষমতা ত্যাগ করেননি।
ফ্রান্সের প্রধানমন্ত্রী রাজনৈতিক ব্যর্থতার দায় নিয়ে পদত্যাগ করেন, কিন্তু বাংলাদেশে নেতারা ব্যর্থতাকেও সাফল্য হিসেবে ঘোষণা করেন। এ যেন এক বেহায়া রাজনৈতিক সংস্কৃতি, যেখানে লজ্জা নেই, নীতি নেই, কেবল ক্ষমতার প্রতি অন্ধ আসক্তি। শেখ মুজিব থেকে শুরু করে জিয়াউর রহমান, এরশাদ, খালেদা জিয়া, শেখ হাসিনা— সবাই ক্ষমতার মোহে একই অপরাধ করেছেন, ভিন্ন সময়ে, ভিন্ন নাম নিয়ে। এ যেন এক দীর্ঘ শৃঙ্খল—একটি জাতির নৈতিক পতনের জীবন্ত ইতিহাস।
পাঁচ দশকের বাংলাদেশের রাজনীতি আমাদের এক কঠিন সত্যের মুখোমুখি দাঁড় করিয়েছে— আমাদের নেতাদের রাজনীতি এখন নীতিহীনতা, ক্ষমতার লালসা ও জনগণের আস্থা হারানোর প্রতীক। ভোট চুরি, দুর্নীতি, রাজনৈতিক হত্যা, গণহত্যা—এসব কেবল অতীতের কাহিনি নয়; আজও এগুলো দেশের শ্বাসরুদ্ধকর বাস্তবতা। যারা একসময় ক্ষমতার কেন্দ্রে ছিল, তাদের কুকর্মের ফলেই জন্ম নিয়েছে দীর্ঘ রাজনৈতিক অস্থিরতা, সমাজে বিভাজন, আর ন্যায়বিচারের প্রতি মানুষের আস্থা হারিয়ে গেছে। কিন্তু এই অন্ধকারের মাঝেও এখনো একটি আশার আলো জ্বলছে।
বাংলাদেশ এখনো পথ হারায়নি—যদি আমরা চাই, আমরা পারি একটি নতুন রাজনৈতিক সংস্কৃতি গড়ে তুলতে। যা এখন করা জরুরি
১. গণতান্ত্রিক সংস্কার বাস্তবায়ন: দুর্নীতি ও ক্ষমতার অপব্যবহার রোধে প্রতিটি নেতা ও দলকে জবাবদিহির আওতায় আনতে হবে।
কেউই আইনের ঊর্ধ্বে নয়—প্রত্যেক শাসককে তার কর্মের দায় নিতে হবে।
২. আইনের শাসন ও বিচারব্যবস্থার স্বাধীনতা: বিচার যেন আর কোনো দলের বা ক্ষমতার নয়, কেবল সত্য ও জনগণের হয়। দোষী নেতা, যে দলেরই হোক, আইনের সামনে সমানভাবে দাঁড়াবে—এই বিশ্বাস ফিরিয়ে আনতে হবে।
৩. সচেতন ও সক্রিয় জনগণ: জনগণই রাষ্ট্রের মালিক—এই চেতনা ফিরিয়ে আনতে হবে। শ্রীলঙ্কার মতো গণঅভ্যুত্থান প্রমাণ করেছে, যখন জনগণ জাগে, দুর্নীতি পালায়। বাংলাদেশেও সেই শক্তি আছে, শুধু ঐক্য আর সাহসের প্রয়োজন।
৪. দুর্নীতিমুক্ত রাজনৈতিক সংস্কৃতি: রাজনীতিকে পুনরায় নৈতিকতা ও দায়িত্ববোধে ফিরিয়ে আনতে হবে। সাংবাদিক, প্রশাসক, শিক্ষক, ব্যবসায়ী—প্রত্যেকে নিজের জায়গা থেকে সৎ থাকতে হবে। কারণ দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াই কেবল সরকারের নয়, সমগ্র জাতির।
বাংলাদেশের পাঁচ দশকের ইতিহাস আমাদের শেখায়— ক্ষমতার মোহ শেষ পর্যন্ত কাউকে রক্ষা করেনি। শেখ মুজিব থেকে শেখ হাসিনা পর্যন্ত সকল শাসকের কুকর্মের ফলাফল এক— মৃত্যু, নির্বাসন, অস্থিরতা ও জনগণের বিশ্বাস হারানো। কিন্তু প্রশ্ন হলো—আমরা কি কিছুই শিখিনি? দেশকে শান্তির পথে ফেরাতে এখনই প্রয়োজন সততা, নৈতিকতা, দায়িত্ববোধ এবং জনগণের একাগ্রতা। আমাদের ভোট, আমাদের প্রতিবাদ, আমাদের সাহস— এই তিনই পারে বাংলাদেশকে দুর্নীতি, লোভ আর স্বৈরাচারের অন্ধকার থেকে উদ্ধার করতে। কোনো অপরাধই গ্রহণযোগ্য নয়। আমাদের লক্ষ্য হতে হবে একটি দুর্নীতিমুক্ত, ন্যায়ভিত্তিক ও শান্তিপূর্ণ বাংলাদেশ। শ্রীলঙ্কার উদাহরণ দেখিয়েছে, জনগণ চাইলে ক্ষমতার অপব্যবহার থামানো যায়।
তাহলে প্রশ্ন জাগে— আজকের বাংলাদেশে কত শতাংশ মানুষ সত্যিই দুর্নীতিমুক্ত? আমরা কি নিজেরাই দুর্নীতির অংশ হয়ে যাচ্ছি না অজান্তেই? যে জাতি নিজের নৈতিকতার কাছে সৎ, সেই জাতির পথ কেউ রোধ করতে পারে না। বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ এখন আমাদের হাতে—সৎ, সাহসী এবং ঐক্যবদ্ধ নাগরিকদের হাতে।
রহমান মৃধা, গবেষক ও লেখক, সাবেক পরিচালক, ফাইজার, সুইডেন। Rahman.Mridha@gmail.com
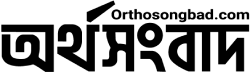
মত দ্বিমত
দুর্নীতিমুক্ত সংসদ ছাড়া ন্যায়বিচার অসম্ভব
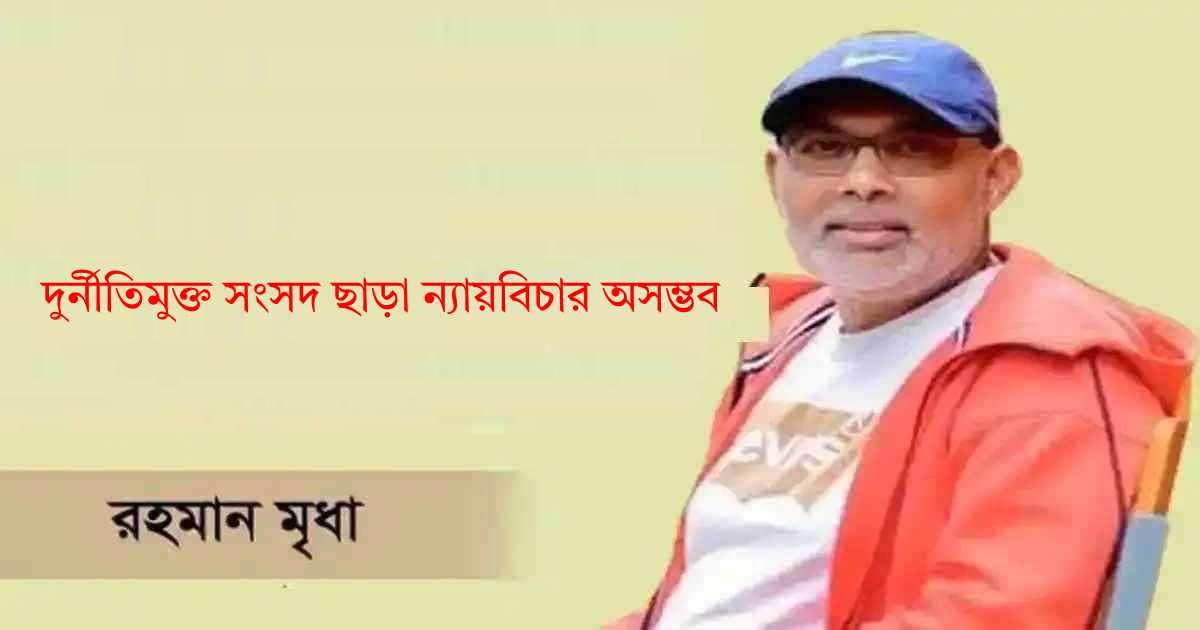
“যতদিন সংসদে দুর্নীতিমুক্ত ও ঋণখেলাপিমুক্ত সংসদ সদস্য না যাবে, ততদিন বাংলাদেশে সংবিধান থেকে জাতি ন্যায়বিচার পাবে না। কারণ, অপরাধী রাজনীতিবিদরা যখন আইন তৈরি করবে, তখন আপনি কখনই ন্যায়বিচার পাবেন না।”
এটি কেবল একটি বাক্য নয়, এটি রাষ্ট্রের ভেতরের অমীমাংসিত সংকটের সংক্ষিত সারাংশ। এখানে প্রশ্ন ব্যক্তির নয়, কাঠামোর। প্রশ্ন দলীয় নয়, নৈতিকতার।
সংবিধান বনাম বাস্তবতা
সংবিধান একটি জাতির সর্বোচ্চ নীতিপত্র, যেখানে ন্যায়, সমতা, মানবাধিকার ও জবাবদিহির অঙ্গীকার লেখা থাকে। কিন্তু সেই সংবিধান বাস্তবায়নের দায়িত্ব যাদের হাতে, তারাই যদি দুর্নীতি, ঋণখেলাপি, লুটপাট, ক্ষমতার অপব্যবহার, চাঁদাবাজি ও ভোট জালিয়াতির অভিযোগে অভিযুক্ত হন, তবে সংবিধানের ভাষা কাগজেই সীমাবদ্ধ থাকে। ন্যায়বিচার তখন নথিতে থাকে, বাস্তবে নয়।
বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে দীর্ঘদিন ধরে একটি বিপজ্জনক প্রবণতা তৈরি হয়েছে। নির্বাচনী প্রতিযোগিতা এখন নীতির লড়াই নয়, বরং প্রভাবের লড়াই হয়ে দাঁড়িয়েছে। ঋণখেলাপিরা ব্যাংকিং ব্যবস্থাকে দুর্বল করেছে, অথচ সাধারণ আমানতকারীরা অনিশ্চয়তায় ভুগেছে। বড় প্রকল্পে অনিয়ম আর জবাবদিহির অভাব সাধারণ মানুষের আস্থায় চিড় ধরিয়েছে। তরুণ প্রজন্মের মধ্যে এই ধারণা জন্মেছে যে—যোগ্যতা নয়, রাজনৈতিক সংযোগই সাফল্যের একমাত্র পথ। এই মানসিকতা রাষ্ট্রের জন্য এক গভীর বিপদের সংকেত।
সবচেয়ে উদ্বেগজনক বিষয় হলো ভোটের প্রতি আস্থার সংকট। যদি নাগরিক বিশ্বাস করতে না পারেন যে তাদের ভোটই প্রতিনিধিত্ব নির্ধারণ করে, তবে গণতন্ত্র কেবল আনুষ্ঠানিকতায় পরিণত হয়। গণতন্ত্রের প্রাণ হলো আস্থা। সেই আস্থা ক্ষয় হলে সংবিধানের প্রতিশ্রুতি দুর্বল হয়ে পড়ে।
এই বাস্তবতায় মূল প্রশ্নটি স্পষ্ট। আইন প্রণেতারা যদি নৈতিকভাবে প্রশ্নবিদ্ধ হন, তবে আইন কি ন্যায় প্রতিষ্ঠা করতে পারে? যখন অপরাধের অভিযোগে অভিযুক্ত বা আর্থিক অনিয়মে জড়িত ব্যক্তিরা আইন প্রণয়ন করেন, তখন আইনের প্রতি জনগণের শ্রদ্ধা কমে যায়। আইনের শাসন তখন ব্যক্তির শাসনে রূপ নিতে শুরু করে।
সমাধান কোনো ব্যক্তিবিশেষের বিরোধিতায় নয়, বরং কাঠামোগত শুদ্ধিতে। রাজনৈতিক দলগুলোর প্রার্থী মনোনয়নে নৈতিক মানদণ্ড কঠোর করা, ঋণখেলাপি ও দুর্নীতির অভিযোগে অভিযুক্তদের সংসদে প্রবেশ চিরতরে বন্ধ করা, নির্বাচনী প্রক্রিয়ার পূর্ণ স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা এবং বিচার বিভাগের স্বাধীনতাকে বাস্তব অর্থে শক্তিশালী করা জরুরি।
রাষ্ট্রকে বাঁচাতে হলে প্রথমে সংসদকে শুদ্ধ করতে হবে। কারণ সংসদই আইন তৈরি করে, আর আইনই রাষ্ট্রের চরিত্র নির্ধারণ করে। আইন যদি নৈতিকতার উপর দাঁড়ায়, রাষ্ট্র টিকে থাকে। আইন যদি স্বার্থের উপর দাঁড়ায়, রাষ্ট্র ভেঙে পড়ে।
অতএব এই বাক্যটি কেবল প্রতিবাদ নয়, একটি সতর্কবার্তা। ন্যায়বিচার কাগজে লেখা থাকে না, তা মানুষের হাতে গড়ে ওঠে। আর সেই হাত যদি কলুষিত হয়, তবে সংবিধানও ন্যায় দিতে পারে না।
প্রশ্নটি এড়ানো যায় না। রাষ্ট্রের জনগণ যেমন, তার নেতৃত্বও সাধারণত তেমনি হয়। বাংলাদেশের জন্য কি এই কথাটি প্রযোজ্য?
নেতৃত্ব আকাশ থেকে পড়ে না; তারা সমাজের ভেতর থেকেই উঠে আসে। সমাজ যদি দুর্নীতিকে সহনীয় মনে করে কিংবা ঋণখেলাপিকে কৌশলী ব্যবসায়ী হিসেবে বাহবা দেয়,ভোট জালিয়াতিকে রাজনৈতিক কৌশল হিসেবে মেনে নেয় এবং চাঁদাবাজিকে প্রভাবের অংশ মনে করে, তবে সেই মানসিকতার প্রতিফলনই একদিন সংসদে বসে। তখন আমরা কেবল নেতৃত্বকে দোষ দিই, কিন্তু আয়নায় নিজেদের দেখি না।
তবে এর অর্থ এই নয় যে জনগণই দায়ী বলেই রাষ্ট্র দায়ী। বরং পরিবর্তনের শক্তিও জনগণের হাতেই। সমাজ যদি নৈতিক মানদণ্ড উঁচু করে, ভোটাররা যদি প্রশ্ন করতে শেখেন এবং দলীয় অন্ধত্বের বদলে নৈতিকতার ভিত্তিতে প্রতিনিধি বাছেন, তবেই সংসদ বদলাবে। রাষ্ট্রকে বাঁচাতে হলে সংসদকে শুদ্ধ করতে হবে। কারণ সংসদই আইন তৈরি করে, আর আইনই রাষ্ট্রের চরিত্র নির্ধারণ করে।
বাংলাদেশের জন্য প্রশ্নটি তাই দ্বিমুখী। নেতৃত্ব কি জনগণের প্রতিচ্ছবি, নাকি জনগণকে এমন কাঠামোর মধ্যে রাখা হয়েছে যেখানে বিকল্পই সংকুচিত? যদি দ্বিতীয়টি সত্য হয়, তবে কাঠামো ভাঙতে হবে। যদি প্রথমটি আংশিক সত্য হয়, তবে মানসিকতা বদলাতে হবে।
অতএব, যতদিন সংসদে দুর্নীতিমুক্ত ও ঋণখেলাপিমুক্ত প্রতিনিধি না যাবে, ততদিন সংবিধানের প্রতিশ্রুতি পূর্ণ হবে না। পরিবর্তনের চাবিকাঠি কিন্তু সাধারণ মানুষের হাতেই।
পরিশেষে, আমরা কি কেবল অভিযোগ করে যাব, নাকি নিজেদের রাজনৈতিক নৈতিকতাকেও পুনর্গঠন করব?
এমএন/ রহমান মৃধা, গবেষক ও লেখক, প্রাক্তন পরিচালক, ফাইজার, সুইডেন
মত দ্বিমত
নাসিরউদ্দিন পাটোয়ারী: স্পষ্টভাষিতা বিতর্ক এবং নতুন রাজনীতির রূপরেখা
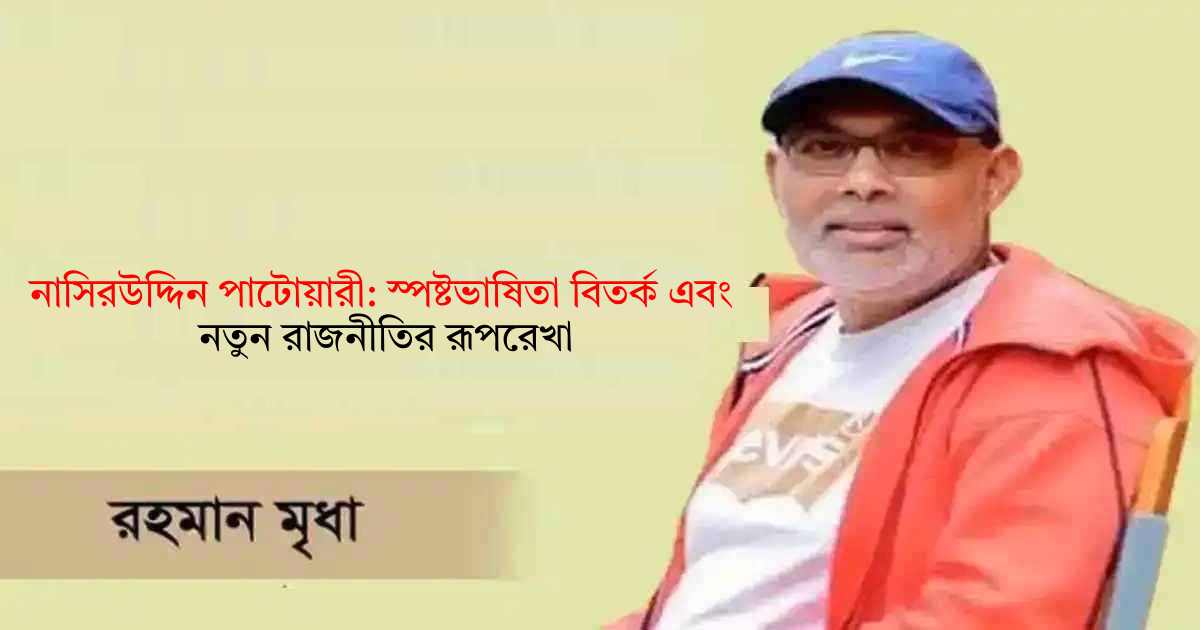
আমি দূর প্রবাসে থাকলেও তাকে আমি চিনি, যদিও কখনও চোখে দেখিনি। জুলাইয়ের গণঅভ্যুত্থানে আমার লেখালিখির সক্রিয় অংশগ্রহণের সময় আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত যারা ছিল তাদের মধ্যেই নাসিরউদ্দিন পাটোয়ারী আমার নজর আলাদাভাবে কেড়েছিল। তার অদম্য সাহস, দৃঢ় সংকল্প এবং মানুষের কল্যাণের প্রতি আন্তরিক দৃষ্টিভঙ্গি তখনই স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। সেই দিনের মুহূর্ত থেকে সে আমার চোখে শুধুই একজন রাজনৈতিক নেতা নয়; সে এক অনন্য চরিত্র, যার প্রভাব কেবল আমার ব্যক্তিগত উপলব্ধিতে সীমাবদ্ধ নয়, বরং দেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে সময়ের সঙ্গে প্রতিফলিত হয়েছে।
বাংলাদেশের রাজনীতিতে স্পষ্টভাষী নেতা বিরল। নাসিরউদ্দিন পাটোয়ারী সেই অদ্বিতীয় কণ্ঠ, যে সরাসরি দৃঢ় এবং প্রায়শই বিতর্কিত বক্তব্য দেয়। তার ভাষা সমালোচনার জন্ম দেয়, সমর্থনও জন্মায়। কিন্তু সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো, এটি বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতির ঘাটতি ও সম্ভাবনার উভয়ই প্রতিফলন। এই প্রতিবেদনে আমি বিশ্লেষণ করেছি সে কীভাবে রাজনৈতিক অঙ্গনে প্রভাব ফেলছে, নতুন প্রজন্ম তাকে কীভাবে দেখছে এবং তার নেতৃত্ব কীভাবে নতুন মানদণ্ড স্থাপন করতে পারে।
বাংলাদেশের সমসাময়িক রাজনৈতিক অঙ্গনে নাসিরউদ্দিন পাটোয়ারী একটি আলোচিত নাম। তাকে কেউ দেখে দুর্নীতিবিরোধী আপসহীন কণ্ঠ হিসেবে, কেউ দেখে বিতর্কপ্রবণ রাজনীতিক হিসেবে। কিন্তু তাকে ঘিরে যে আলোচনা, তা কেবল ব্যক্তিকে নিয়ে নয়। এটি বাংলাদেশের রাজনৈতিক ভাষা, সংস্কৃতি ও কাঠামোগত সীমাবদ্ধতার গভীর প্রশ্নকে সামনে আনে।
নাসিরউদ্দিন পাটোয়ারীর বিরুদ্ধে বিভিন্ন সময়ে অশ্লীলতার অভিযোগ উঠেছে। সমালোচকদের বক্তব্য, তার ভাষা প্রায়ই তীব্র। সমর্থকদের দাবি, সে কেবল অপ্রিয় সত্য উচ্চারণ করে। এখানে একটি মৌলিক প্রশ্ন সামনে আসে। কঠোর ভাষা ও অশ্লীলতার কি একই বিষয়? নাকি আমরা এমন এক রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে অভ্যস্ত, যেখানে তোষামোদ স্বাভাবিক এবং সরাসরি সমালোচনা অস্বস্তিকর?
বাংলাদেশের রাজনৈতিক বাস্তবতায় ব্যক্তিকেন্দ্রিক আনুগত্য প্রায়ই নীতিগত বিতর্ককে ছাপিয়ে যায়। ফলে শক্ত সমালোচনা সহজেই ব্যক্তিগত আক্রমণ হিসেবে ব্যাখ্যা পায়। এই প্রেক্ষাপটে পাটোয়ারীর ভাষা বিতর্ক সৃষ্টি করলেও তা রাজনৈতিক সংস্কৃতির অন্তর্নিহিত সংকটকেই উন্মোচন করে।
নতুন প্রজন্মের চাওয়া
নতুন প্রজন্মের এক অংশ তাঁর এই আপসহীনতাকে সততার প্রতীক মনে করলেও, অন্য অংশ তাঁর বক্তব্যের চেয়ে সুস্পষ্ট কর্মপরিকল্পনা ও ফলাফল দেখতে আগ্রহী। আজকের তরুণ সমাজ শুধু স্লোগান চায় না, তারা চায় রাষ্ট্র সংস্কারের বাস্তব রূপরেখা। এই প্রেক্ষাপটে পাটোয়ারীর সামনে বড় চ্যালেঞ্জ হলো তাঁর এই সাহসকে কৌশলী নীতিতে রূপান্তর করা।
পাটোয়ারীর স্পষ্টভাষিতা তার শক্তি, আবার ঝুঁকিও
ইতিবাচক দিক হলো, সে আলাদা রাজনৈতিক পরিচিতি গড়ে তুলেছে। দুর্নীতিবিরোধী অবস্থান তাকে দৃশ্যমান করেছে। তরুণদের একটি অংশ তার মধ্যে প্রতিবাদী নয়, সম্ভাব্য সংস্কারকের প্রতিচ্ছবি দেখে।
নেতিবাচক দিক হলো, যদি ভাষাই আলোচনার কেন্দ্রে থাকে তবে নীতিগত গভীরতা আড়ালে পড়তে পারে। জোটভিত্তিক রাজনীতিতে সমঝোতার প্রয়োজন থাকে। অতিরিক্ত তীব্রতা রাজনৈতিক সমীকরণকে কঠিন করে তুলতে পারে। আইনি ও প্রশাসনিক চাপের ঝুঁকিও থেকে যায়।
কাঠামোগত সংস্কারের প্রয়োজন
১: রাজনৈতিক আচরণবিধির স্পষ্ট সংজ্ঞা প্রয়োজন, যাতে কঠোর সমালোচনা ও ব্যক্তিগত অশালীনতার পার্থক্য নির্ধারিত হয়।
২: প্রমাণভিত্তিক বক্তব্যের সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠা জরুরি। অভিযোগের সঙ্গে দলিল যুক্ত হলে ভাষা নয়, তথ্য আলোচনার কেন্দ্রে আসে।
৩: স্বাধীন তথ্য যাচাই কাঠামো শক্তিশালী করা দরকার, যাতে গুজব ও বিকৃত বক্তব্য দ্রুত সংশোধিত হয়।
৪: নির্বাচিত প্রতিনিধিদের জন্য রাজনৈতিক যোগাযোগ ও নৈতিক ভাষা ব্যবহারের প্রশিক্ষণ প্রয়োজন।
৫: সমালোচনার পাশাপাশি লিখিত নীতিপত্র ও বাস্তবায়ন রূপরেখা প্রকাশ করতে হবে।
সংসদে নতুন মানদণ্ডের প্রত্যাশা
জাতীয় সংসদে নীতিগত আলোচনার যে ঘাটতি প্রায়ই দেখা যায়, সেখানে নাসিরউদ্দিন পাটোয়ারীর মতো নেতার উপস্থিতি তাৎপর্যপূর্ণ হতে পারে। তবে সংসদীয় রাজনীতিতে কার্যকর হতে হলে তিনটি বিষয় নিশ্চিত করা জরুরি:
- জবাবদিহিমূলক বিতর্কের সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠা।
- আইন প্রণয়নের পাশাপাশি বাস্তবায়ন কাঠামো নিয়ে সুস্পষ্ট আলোচনা।
- তরুণ প্রজন্মকে দেখানো যে রাজনীতি সৃজনশীল, নীতিনির্ভর এবং মানুষের কল্যাণমুখী হতে পারে।
তার বক্তব্যে যে বার্তাগুলো ধারাবাহিকভাবে উঠে আসে তা হলো তোষামোদ নয়, জবাবদিহি; আইন প্রয়োগই রাষ্ট্রের শক্তি; দুর্নীতির বিরুদ্ধে আপসহীনতা; নাগরিক সাহসের চর্চা। এই বার্তা যদি কেবল বক্তৃতায় সীমাবদ্ধ না থেকে প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোয় রূপ পায়, তবে তা রাজনৈতিক সংস্কৃতির পরিবর্তনে ভূমিকা রাখতে পারে।
নাসিরউদ্দিন পাটোয়ারীকে ঘিরে বিতর্ক আসলে বাংলাদেশের রাজনৈতিক পরিপক্বতার পরীক্ষা। সে একই সঙ্গে আশার প্রতীক, বিতর্কের কেন্দ্র এবং সম্ভাব্য সংস্কারক। তার সামনে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হলো সাহসকে কৌশলে রূপান্তর করা, ভাষাকে নীতিতে রূপান্তর করা এবং আবেগকে প্রাতিষ্ঠানিক পরিবর্তনে রূপান্তর করা।
আজ বাংলাদেশের রাজনীতি একটি সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে। জনগণ ক্লান্ত প্রতিশ্রুতির পুনরাবৃত্তিতে, ক্লান্ত তোষামোদে, ক্লান্ত গুজবনির্ভর চরিত্রহননে। তারা এমন রাজনীতি দেখতে চায় যেখানে যোগ্যতা সম্মান পায়, সৃজনশীলতা মূল্য পায় এবং জবাবদিহি বাধ্যতামূলক হয়।
বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে আমরা প্রায়ই দেখেছি যোগ্য নেতৃত্বের অভাবে রাজনীতি আমলাতন্ত্রের কাছে হার মেনেছে। যোগ্য, ত্যাগী ও দূরদর্শী নেতৃত্বের অভাব দেশের নীতিনির্ধারণকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। আসন্ন নির্বাচনের পর একটি শক্তিশালী বিরোধী দল এবং একটি ‘ছায়া মন্ত্রিসভা’ গঠন করা গেলে জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা সম্ভব হবে। নাসিরউদ্দিন পাটোয়ারীর সাম্প্রতিক নির্বাচনী প্রচারণায় যে দায়িত্বশীল রাজনৈতিক চর্চার আভাস মিলেছে, তা প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পাওয়া এখন সময়ের দাবি।
নাসিরউদ্দিন পাটোয়ারীকে ঘিরে বিতর্ক আসলে বাংলাদেশের রাজনৈতিক পরিপক্বতারই পরীক্ষা। তিনি কেবল একজন ব্যক্তি নন, বরং এক নতুন রাজনৈতিক মানদণ্ডের সম্ভাবনা। যদি তাঁর স্পষ্টভাষিতা ও সাহসের সাথে প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কারের সংমিশ্রণ ঘটে, তবে তা নতুন প্রজন্মের কাছে এই বার্তাই দেবে যে—রাজনীতি মানে ক্ষমতা নয়, বরং মানুষের কল্যাণে নিবেদিত একটি মহান দায়িত্ব।
লেখক: রহমান মৃধা
গবেষক ও লেখক, প্রাক্তন পরিচালক, ফাইজার, সুইডেন
মত দ্বিমত
গণতন্ত্র নিষ্ঠুর, কিন্তু অন্ধ নয়
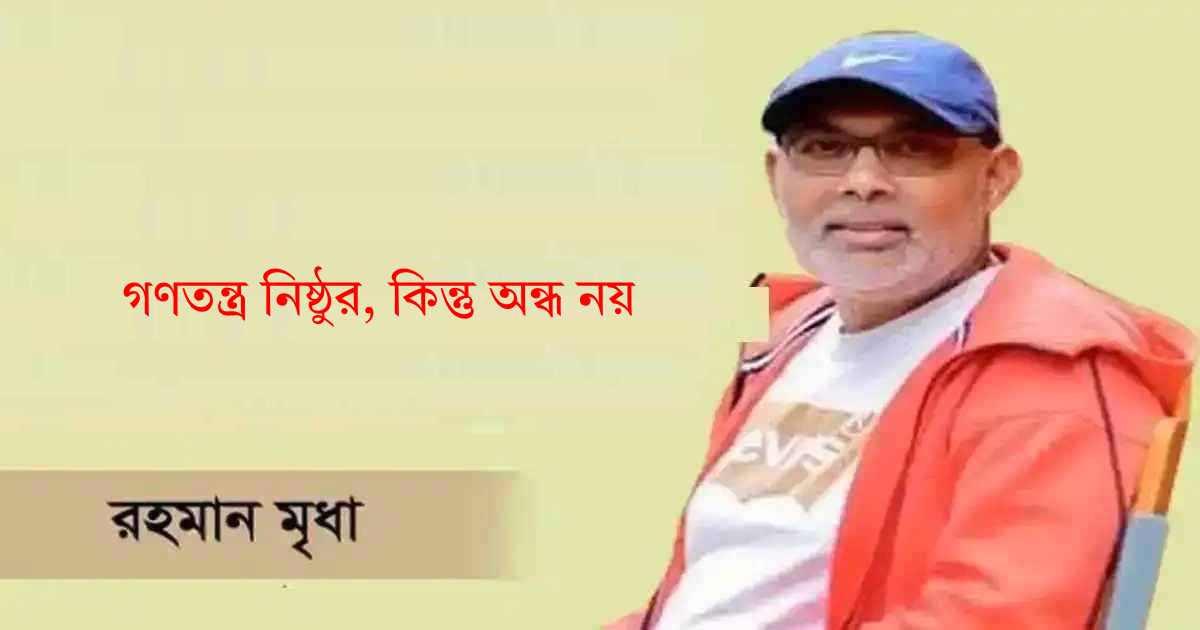
বাংলাদেশের ১৮ কোটি মানুষের যেন ১৮ কোটি মতামত, যা গণমাধ্যমে প্রতিনিয়ত উচ্চারিত হচ্ছে। তারপরও বাংলাদেশের নবনির্বাচিত ও মনোনীত প্রার্থীদের মধ্যে বিএনপির গণজোয়ার যেন একটি স্পষ্ট বার্তা দিচ্ছে, জনমতকে চিরদিন উপেক্ষা করা যায় না। এবার আর বলার সুযোগ নেই যে দিনের ভোট রাতে হয়েছে বা জনগণ নিজের ভোট নিজে দিতে পারেনি। অজুহাতের রাজনীতি থেকে বেরিয়ে এসে বাস্তবতাকে গ্রহণ করার সময় এখন, যার যার মুল্লুক তার শক্তি। তবে এই বাক্যটির আরেকটি গভীর পাঠ আছে। ক্ষমতা কখনো শূন্য থেকে জন্মায় না, এটি শেষ পর্যন্ত সমাজের ভেতর থেকেই উঠে আসে। একটি জাতি শেষ পর্যন্ত তার মনের মতো নেতৃত্বই খুঁজে পায়। যেমন জাতি তেমন নেতা, কারণ আম গাছের তলায় আমই পড়ে। তাই প্রশ্নটা শুধু কে ক্ষমতায় গেল তা নয়, আমরা কেমন সমাজ তৈরি করেছি, কেমন রাজনীতি সহ্য করেছি, আর কেমন নেতৃত্বকে নীরবে অনুমোদন দিয়েছি। নেতৃত্ব আসলে জাতিরই আয়না, সেখানে প্রতিফলিত হয় আমাদের সাহস, আমাদের ভয়, আমাদের নৈতিকতা এবং আমাদের সীমাবদ্ধতা।
প্রকৃতপক্ষে গণতন্ত্রের মতো নিষ্ঠুর আচরণ আর কোনো ব্যবস্থায় নেই। কারণ কি জানেন? ইতিহাস বারবার দেখিয়েছে, মাত্র একটি ভোটের ব্যবধানে কেউ হেরে গেছে, কেউ জিতে গেছে। সেই একটি ভোটই কখনো একটি দেশের ভবিষ্যৎ বদলে দিয়েছে, কখনো একটি প্রজন্মের স্বপ্নকে নতুন দিক দেখিয়েছে। অনেকেই তাই বলেন, এটিই গণতন্ত্রের সৌন্দর্য। কিন্তু এই সৌন্দর্যের ভেতরেই লুকিয়ে আছে কঠোর জবাবদিহি, নির্মম বাস্তবতা এবং জনগণের নীরব অথচ চূড়ান্ত ক্ষমতা।
আজ এই ক্ষণে আমার ছোটবেলার একটি গল্প খুব মনে পড়ছে। গ্রামে বিষাক্ত সর্প দংশনে একজন প্রতিবেশী মৃত্যুবরণ করেছিলেন। চারদিকে কান্নার রোল উঠেছিল। পাড়া প্রতিবেশীরা এসে সান্ত্বনা দিচ্ছিলেন, নানা জন নানা ভাবে স্মৃতিচারণ করছিলেন। হঠাৎ এক বয়স্ক মহিলা এসে লক্ষ করলেন, সাপে কামড় দিয়েছে চোখের একটু উপরে। গভীর দুঃখ প্রকাশ করে তাকে বলতে শুনেছিলাম, “ইশ, একটুর জন্য চোখটা বেঁচে গেছে।”
সেদিন প্রথম বুঝেছিলাম, মানুষ কখনো কখনো সবচেয়ে বড় ক্ষতির মাঝেও অদ্ভুত এক সান্ত্বনা খোঁজে। কিন্তু প্রশ্ন হলো, আমরা কি বারবার একইভাবে নিজেদের সান্ত্বনা দিয়ে যাব, নাকি সত্যের মুখোমুখি দাঁড়াব?
সদ্য বাংলাদেশের নির্বাচন শেষ হয়েছে। বিজয়ের ঘণ্টা বেজেছে, সেই সাথে পরাজয়েরও। তারপরও জল্পনা কল্পনা চলছে, চলবেই। কী করণীয় ছিল, কী করা উচিত ছিল না, এই আলোচনা গণতন্ত্রেরই অংশ। জয় পরাজয় থাকবেই, অতীতেও ছিল, ভবিষ্যতেও থাকবে। কিন্তু যে শিক্ষা সবচেয়ে জরুরি, সেটি হলো অজুহাত নয়, সমাধান খুঁজুন।
রাজনীতি কেন করবেন? উদ্দেশ্য কি? সেবা দেবেন, নাকি সেবা নেবেন? শাসন করবেন, নাকি শোষণ করবেন? স্বৈরাচারী হবেন, নাকি কর্মচারীর মতো জনগণের পাশে দাঁড়াবেন? একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করবেন, নাকি গণতন্ত্রকে শক্ত ভিত্তির ওপর দাঁড় করাবেন? দেশ গড়বেন, নাকি শুধু নিজেকে গড়বেন?
এই প্রশ্নগুলো শুধু রাজনীতিবিদদের জন্য নয়, একটি জাতির আত্মপরিচয়ের প্রশ্ন। কারণ রাজনীতি শেষ পর্যন্ত ক্ষমতার খেলা নয়, এটি আস্থার সম্পর্ক।
এ ধরনের চিন্তা ভাবনাকে ব্রেনস্টর্মিং করতে হবে। একটি টু ডু লিস্ট তৈরি করতে হবে। তারপর নিজেকেই প্রশ্ন করতে হবে, গো অর নট গো। কারণ নেতৃত্ব মানে শুধু সামনে দাঁড়ানো নয়, সঠিক সময়ে সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার সাহস।
ধরুন, আপনি মনেপ্রাণে বিশ্বাস করেন দুর্নীতিমুক্ত বাংলাদেশ গড়া সম্ভব। কীভাবে সম্ভব, সেটাও আপনি জানেন। কিন্তু আপনার কোনো ক্ষমতা নেই, জনগণ আপনার পাশে নেই, তাহলে? ইতিহাস বলে, পরিবর্তন কখনো ক্ষমতা দিয়ে শুরু হয় না, শুরু হয় বিশ্বাস দিয়ে। তারপর সেই বিশ্বাসই একসময় জনশক্তিতে রূপ নেয়।
আমি আজ একটি ক্ষেত্রেই দেশের অগ্রগতি নিঃসন্দেহে দৃশ্যমান, সেটি দুর্নীতি। কথাটি হতাশার শোনালেও এর ভেতরে লুকিয়ে আছে একটি সতর্কবার্তা। কারণ শক্তি নিজে কখনো ভালো বা মন্দ নয়, আমরা তাকে কোন পথে ব্যবহার করছি সেটিই আসল প্রশ্ন।
আলফ্রেড নোবেল ডিনামাইট আবিষ্কার করেছিলেন ধ্বংসের জন্য নয়। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল সুইডেনের দুর্গম পাহাড় কেটে রাস্তা নির্মাণ করা, নর্ডিক দেশগুলোর যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত করা এবং বহির্বিশ্বের সঙ্গে ব্যবসা বাণিজ্যের নতুন দুয়ার খুলে দেওয়া। সেই স্বপ্ন বাস্তব হয়েছিল, যার সুফল আজও চোখে পড়ে। কিন্তু সময়ের পরিক্রমায় একই ডিনামাইট যুদ্ধক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়ে লাখো মানুষের মৃত্যুর কারণ হয়েছে। যে শক্তি উন্নয়নের প্রতীক ছিল, সেটিই পরিণত হয়েছে ধ্বংসের অস্ত্রে।
প্রযুক্তির ক্ষেত্রেও আমরা যেন একই দ্বিধাবিভক্ত পথের সামনে দাঁড়িয়ে আছি। অভূতপূর্ব প্রযুক্তিগত অগ্রগতি সত্ত্বেও আমরা তাকে সুশাসনের হাতিয়ার হিসেবে গড়ে তুলতে পারিনি। অথচ চাইলে শতভাগ প্রযুক্তিনির্ভর প্রশাসন, নগদবিহীন লেনদেন, স্বচ্ছ নির্বাচন ব্যবস্থা এবং দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণ আজ আর কল্পনা নয়, বাস্তব সম্ভাবনা। প্রশ্ন একটাই, আমরা কি প্রযুক্তিকে অগ্রগতির সিঁড়ি বানাব, নাকি নিজেদের সীমাবদ্ধতার কারণে তাকে ধ্বংসের আরেকটি উপকরণে পরিণত করব?
জুলাই গণঅভ্যুত্থানে আমরা দেখেছি, কত ভালো মানুষের হাত পা কাটা গেল, কত তরুণ তরুণী জীবন দিল, দুর্নীতির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ালো। তাদের আত্মত্যাগ আমাদের একটি কঠিন প্রশ্নের সামনে দাঁড় করায়, আমরা কি সত্যিই ন্যায়বিচার চাই, নাকি শুধু ক্ষণিকের প্রতিশোধ? যারা দুর্নীতি করল বা এত মানুষকে হত্যা করল, সবাই জানে তারা কারা। তারপরও কি সেই দুর্নীতিবাজদের শাস্তি হিসেবে হুট করে হাত পা কাটা যাবে? না। কারণ আইনের ঊর্ধ্বে উঠে বিচার করা মানে আবারও অন্যায়কে জন্ম দেওয়া। এখানেই বিবেকের দ্বন্দ্ব।
এই দ্বন্দ্বের মোকাবিলা করা যেমন কঠিন, তেমনি কঠিন পরাজয়কে মেনে নেওয়া। পরাজয় মানুষকে ভেঙেও দেয়, আবার গড়েও তোলে। আমি বহু বছর ধরে খেলাধুলার জগতের সাথে জড়িত। আমার ছেলে মেয়েরা তাদের শৈশব, কৈশোর এবং যৌবনের একটি বড় সময় পার করছে জয় পরাজয়ের মধ্য দিয়ে। জয়ের উল্লাস যেমন মানুষকে আত্মবিশ্বাসী করে, তেমনি পরাজয়ের গ্লানি মানুষকে গভীরভাবে আত্মসমালোচনা করতে শেখায়। চলার পথে আমরা প্রতিনিয়ত এগিয়ে চলেছি। তারপরও আমরা থেমে নেই। কারণ সেই একই প্রশ্ন আমাদের সামনে থাকে, কী, কেন এবং কীভাবে।
স্বাভাবিকভাবেই জয়ের মধ্যে সময় কাটানোর উপলব্ধি আর পরাজয়ের মধ্যে সময় কাটানোর অনুভূতি এক নয়। তবুও মেনে নেওয়া শিখতে হবে। কারণ যে জাতি হার স্বীকার করতে জানে না, সে কখনো জয়ের মর্যাদাও বুঝতে পারে না।
আমাদের সুইডেনের একজন প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী প্রায় বলতেন, “jag låter min fru alltid vinna, på så sätt är det jag som bestämmer att hon vinner।” এর বাংলা অর্থ, “আমি সবসময় আমার স্ত্রীকে জিততে দিই, আর এভাবেই আমিই ঠিক করি যে সে জিতবে।” কথাটি রসিকতা মনে হলেও এর ভেতরে লুকিয়ে আছে এক গভীর সত্য, কখনো কখনো ছেড়ে দেওয়াও প্রজ্ঞার পরিচয়, আর সম্মান দিয়েই টেকসই সম্পর্ক তৈরি হয়।
গণতন্ত্রের মূল মন্ত্র হলো agree to disagree, অর্থাৎ দ্বিমত থাকা সত্ত্বেও সহাবস্থান করা। মতের ভিন্নতা কোনো দুর্বলতা নয়, বরং একটি পরিণত সমাজের শক্তি। দুর্ভাগ্যজনকভাবে এই চর্চাটির ভীষণ অভাব বাংলাদেশে। আমরা ভিন্ন মতকে প্রতিপক্ষ ভাবতে শিখেছি, সহযাত্রী হিসেবে দেখতে শিখিনি।
খুব ইচ্ছে জাগে, যদি আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় ন্যূনতম পরিবর্তন এনে মত ও দ্বিমত পোষণের প্রক্রিয়াটিকে শেখানো যেত। কারণ গণতন্ত্র কেবল ব্যালট বাক্সে জন্মায় না, এটি জন্মায় শ্রেণিকক্ষে, পরিবারে, আলোচনায়, এবং পারস্পরিক শ্রদ্ধার সংস্কৃতিতে।
শেষ পর্যন্ত একটি সত্য অস্বীকার করার উপায় নেই, গণতন্ত্র কোনো আরামদায়ক যাত্রা নয়। এটি প্রশ্ন করে, চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দেয়, কখনো আঘাত করে, আবার নতুন করে পথও দেখায়। তাই অজুহাত নয়, আত্মসমালোচনা দরকার। প্রতিশোধ নয়, ন্যায়বিচার দরকার। বিভাজন নয়, পরিণত সহাবস্থান দরকার।
কারণ একটি জাতির ভবিষ্যৎ নির্ধারিত হয় শুধু কে জিতল বা হারল তা দিয়ে নয়, বরং আমরা হার থেকে কী শিখলাম এবং জয়কে কতটা দায়িত্বে রূপান্তর করতে পারলাম তা দিয়ে। গণতন্ত্র নিষ্ঠুর হতে পারে, কিন্তু অন্ধ নয়। অন্ধ হলে আমরা।
রহমান মৃধা, গবেষক ও লেখক, প্রাক্তন পরিচালক, ফাইজার, সুইডেন
rahman.mridha@gmail.com
মত দ্বিমত
গরীব দেশে অথচ দুর্নীতিবাজ কোটিপতিদের সংখ্যা বেশি, ঘটনা কী
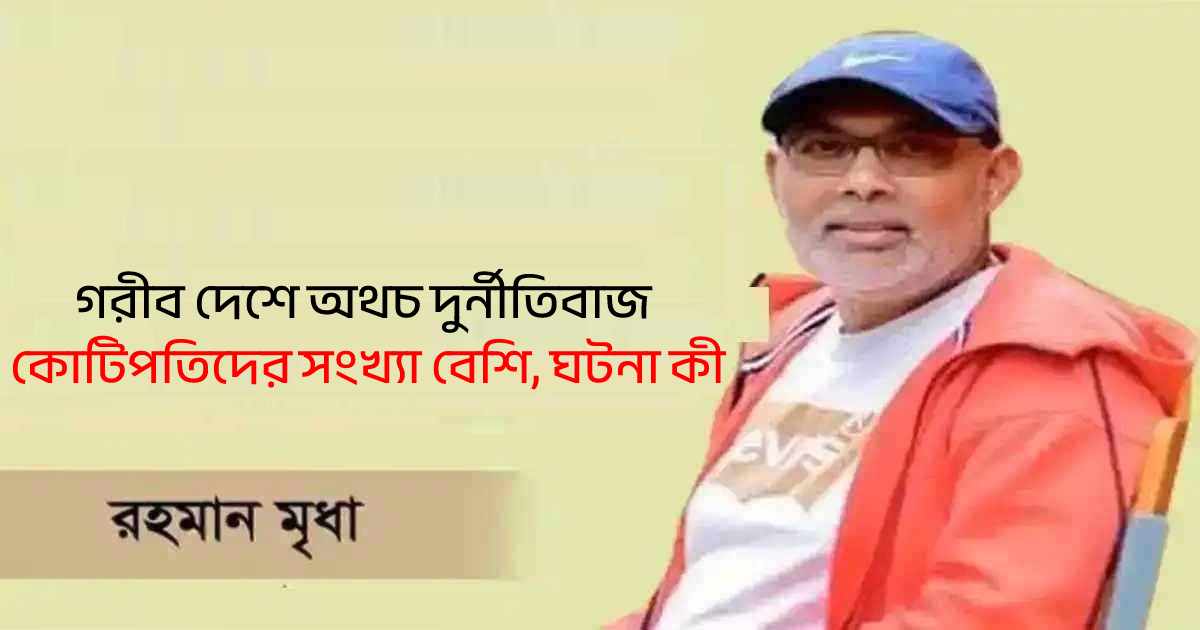
বাংলাদেশ এখন এক অদ্ভুত বৈপরীত্যের দেশ। একদিকে উন্নয়নের পরিসংখ্যান, অবকাঠামোর দৃশ্যমান অগ্রগতি, ডিজিটাল রূপান্তরের প্রচার; অন্যদিকে দ্রুত বাড়ছে অস্বচ্ছ সম্পদের মালিক কোটিপতিদের সংখ্যা। প্রশ্নটি তাই ক্রমেই জোরালো হচ্ছে: একটি দেশ যেখানে এখনও নুন আনতে তেল ফুরোয়, বিপুল দরিদ্র জনগোষ্ঠী জীবনযুদ্ধেই ব্যস্ত, সেখানে এত সম্পদ জমছে দুর্নীতিবাজ রাজনীতিবিদদের হাতে, কীভাবে?
কীভাবে এই সম্পদ তৈরি হচ্ছে
অর্থনীতির স্বাভাবিক নিয়ম হলো উৎপাদন, উদ্ভাবন এবং প্রতিযোগিতার মাধ্যমে সম্পদ সৃষ্টি। কিন্তু যখন সম্পদের বড় অংশ আসে ব্যাংক ঋণ খেলাপি, প্রকল্প ব্যয়ের অস্বাভাবিক বৃদ্ধি, সরকারি ক্রয়ে অনিয়ম, টেন্ডার কারসাজি এবং রাজনৈতিক প্রভাবের মাধ্যমে, তখন তা আর অর্থনৈতিক সাফল্য নয়; বরং প্রাতিষ্ঠানিক দুর্বলতার লক্ষণ। অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায়, লোকসান শেষ পর্যন্ত রাষ্ট্র বহন করে, আর মুনাফা ব্যক্তির হাতে যায়। ফলে সম্পদ সৃষ্টি হয়, কিন্তু তা জাতীয় সমৃদ্ধিতে রূপ নেয় না।
কেন এমন হচ্ছে
এর পেছনে সবচেয়ে বড় কারণ হলো দুর্বল জবাবদিহি। যখন আইনের প্রয়োগ নির্বাচিতভাবে হয়, তদন্ত ধীরগতির হয়, আর শাস্তির নজির কম থাকে, তখন দুর্নীতি ঝুঁকিপূর্ণ নয়, বরং লাভজনক হয়ে ওঠে। আরও একটি কারণ হলো ক্ষমতা ও অর্থের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। রাজনৈতিক সুরক্ষা অর্থনৈতিক সুযোগ তৈরি করে, আর অর্থ আবার রাজনৈতিক প্রভাব বাড়ায়। এই চক্র ভাঙা কঠিন হয়ে পড়ে।
জনগণের ভূমিকা কী
দুর্নীতির দায় শুধু ক্ষমতাবানদের নয়; সমাজও অনেক সময় নীরব সমর্থক হয়ে ওঠে। দ্রুত সুবিধা পাওয়ার সংস্কৃতি, “সবাই তো করছে” ধরনের মানসিকতা, এবং শক্তিশালী নাগরিক চাপের অভাব পরিস্থিতিকে আরও জটিল করে। যেখানে ভোটাররা নীতির চেয়ে তাৎক্ষণিক সুবিধাকে অগ্রাধিকার দেয়, সেখানে দীর্ঘমেয়াদি সুশাসনের দাবি দুর্বল হয়ে যায়।
বিশ্ব কীভাবে দেখছে
আন্তর্জাতিক সূচকগুলো প্রায়ই দেখায়, বিনিয়োগকারীরা স্থিতিশীলতা চান, কিন্তু একই সঙ্গে চান স্বচ্ছতা এবং আইনের নিশ্চয়তা। যখন দুর্নীতির ধারণা প্রবল হয়, তখন বিদেশি বিনিয়োগ সতর্ক হয়ে পড়ে, আর দেশের ভাবমূর্তি প্রশ্নের মুখে পড়ে। বাংলাদেশের সম্ভাবনা নিয়ে বিশ্ব আশাবাদী, কিন্তু সেই আশার সঙ্গে একটি সতর্কবার্তাও থাকে: টেকসই উন্নয়ন সম্ভব নয় যদি প্রাতিষ্ঠানিক স্বচ্ছতা নিশ্চিত না হয়।
ডিজিটাল বাংলাদেশ
কিন্তু অর্থনৈতিক প্রভাব কোথায়, ডিজিটালাইজেশন শুধু সেবা দ্রুত করার জন্য নয়; এটি দুর্নীতি কমানোরও শক্তিশালী হাতিয়ার হতে পারত। ই-গভর্ন্যান্স, স্বচ্ছ ডেটা, অনলাইন টেন্ডার, ট্র্যাকযোগ্য লেনদেন বাস্তবায়িত হলে অনিয়ম কমার কথা। কিন্তু প্রযুক্তি তখনই কার্যকর হয়, যখন সেটি ব্যবহারের রাজনৈতিক সদিচ্ছা থাকে। অন্যথায় ডিজিটাল কাঠামোও কেবল নতুন আকারে পুরোনো সমস্যাকে বহন করে।
জবাবদিহির অনুপস্থিতি
যে রাষ্ট্রে প্রশ্ন করা কঠিন, তথ্য পাওয়া সীমিত, এবং দায় নির্ধারণ বিরল, সেখানে দুর্নীতি ব্যতিক্রম নয়, বরং কাঠামোগত বাস্তবতা হয়ে দাঁড়ায়। জবাবদিহি শুধু আইনি প্রক্রিয়া নয়; এটি একটি সাংস্কৃতিক চর্চা, যা প্রতিষ্ঠান, গণমাধ্যম এবং নাগরিক সমাজ মিলেই তৈরি করে।
দুর্নীতি, সন্ত্রাস এবং চাঁদাবাজি: রন্ধ্রে রন্ধ্রে বিস্তার
যখন অর্থনৈতিক অপরাধ শাস্তিহীন থাকে, তখন তা সামাজিক অপরাধকেও উৎসাহ দেয়। চাঁদাবাজি ব্যবসার খরচ বাড়ায়, সন্ত্রাস বিনিয়োগ নিরুৎসাহিত করে, আর সাধারণ মানুষ নিরাপত্তাহীনতায় ভোগে। শেষ পর্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হয় পুরো অর্থনীতি।
মূল কাঠামোগত কারণগুলো-
১. রাষ্ট্রীয় কাঠামোর ভেতরেই দুর্নীতির আশ্রয়
Transparency International বলছে, অব্যাহত দুর্নীতি, রাষ্ট্রীয় সুরক্ষা, দুর্বল আইন প্রয়োগ এবং প্রাতিষ্ঠানিক দুর্বলতা বাংলাদেশের অবস্থার অবনতির বড় কারণ। ক্ষমতার অপব্যবহারের সুযোগ থাকলে এবং জবাবদিহিমূলক প্রতিষ্ঠানগুলো রাজনৈতিক হয়ে পড়লে দুর্নীতি “ফ্লরিশ” করবেই। অর্থাৎ সমস্যা ব্যক্তি নয়, সিস্টেম।
২. সম্পদের ভয়াবহ অসম বণ্টন
এক গবেষণায় দেখা গেছে, জাতীয় আয়ের ৪৪% মাত্র ১০% মানুষের হাতে, আর নিচের ৫০% পেয়েছে মাত্র ১৭.১%। এমনকি ১% মানুষই ১৬% আয়ের মালিক। এটি দেখায়, সম্পদ তৈরি হচ্ছে, কিন্তু তা অর্থনীতির ভেতর ছড়িয়ে পড়ছে না।
৩. গ্লোবাল করাপশন ইকোনমি
প্রতি বছর বিশ্বজুড়ে প্রায় ১ ট্রিলিয়ন ডলার চুরি হয়, যার বড় অংশ উন্নয়নশীল দেশ থেকে পাচার হয়ে যায়। এই অর্থ যদি চুরি না হতো, তাহলে GDP বাড়ত এবং বৈষম্য কমত। অর্থাৎ দুর্নীতি শুধু নৈতিক সমস্যা নয়, এটি সরাসরি উন্নয়নকে ধ্বংস করে।
৪. অলিগার্কি ও অর্থনীতি লুটের অভিযোগ
এক রিপোর্টে বলা হয়েছে, প্রায় ২৩৪ বিলিয়ন ডলার সরকারি তহবিল ১৫ বছরে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে, এবং প্রবৃদ্ধির একটি অংশ “কৃত্রিম” ছিল বলে অভিযোগ উঠেছে। আরেক তদন্তে দেখা যায়, এক রাজনীতিকের বিদেশে ৪৮২টি সম্পত্তি ছিল, যা জটিল অর্থপাচারের মাধ্যমে গড়ে ওঠার সন্দেহ। এটি আর বিচ্ছিন্ন দুর্নীতি নয়; এটি সংগঠিত সম্পদ স্থানান্তর।
৫. ব্যাংক ও আর্থিক ব্যবস্থার দখল
কিছু ক্ষেত্রে নিরাপত্তা কাঠামোর সহায়তায় ব্যাংকের নিয়ন্ত্রণ নেওয়া এবং বিপুল অর্থ সরিয়ে নেওয়ার অভিযোগ উঠেছে; ফলে খেলাপি ঋণ ৩২% পর্যন্ত পৌঁছেছে। যখন ব্যাংক দুর্বল হয়, তখন পুরো অর্থনীতি ঝুঁকিতে পড়ে।
৬. বৈশ্বিক সূচকে সতর্কবার্তা
২০২৫ সালে বাংলাদেশ ১০০ এর মধ্যে মাত্র ২৪ স্কোর পেয়েছে এবং “serious corruption problem” হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। এটি বিনিয়োগ, আস্থা এবং আন্তর্জাতিক ভাবমূর্তির ওপর সরাসরি প্রভাব ফেলে।
গভীরতর বাস্তবতা: কেন দরিদ্র দেশে দ্রুত ধনী তৈরি হয়?
• আইন দুর্বল, ঝুঁকি কম
• ক্ষমতার ঘনত্ব, সুযোগ বেশি
• বৈষম্য বেশি, প্রতিরোধ কম
• রাজনৈতিক সুরক্ষা, শাস্তি কম
এই চারটি একসঙ্গে হলে “দ্রুত সম্পদ” তৈরি হয়, কিন্তু “টেকসই অর্থনীতি” তৈরি হয় না।
কঠিন শেষ স্টেটমেন্ট
বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় সংকট দারিদ্র্য নয়। সবচেয়ে বড় সংকট হলো অন্যায্য সম্পদ সৃষ্টি স্বাভাবিক হয়ে যাওয়া। যে দেশে ধনী হওয়া যদি উৎপাদনের চেয়ে ক্ষমতার কাছাকাছি থাকার ওপর নির্ভর করে, তাহলে সেখানে উন্নয়ন কাগজে বাড়ে, বাস্তবে নয়। রাষ্ট্র তখন আর সুযোগের ক্ষেত্র থাকে না; হয়ে ওঠে সম্পদ স্থানান্তরের যন্ত্র।
ইতিহাস একটি নির্মম সত্য শেখায়:
অসমতা সহ্য করতে পারে সমাজ, কিন্তু অন্যায্য সম্পদকে দীর্ঘদিন মেনে নেয় না। যেদিন সাধারণ মানুষ বিশ্বাস হারায় যে পরিশ্রম নয়, প্রভাবই সফলতার পথ, সেদিন থেকেই অর্থনৈতিক সংকট নয়, রাষ্ট্রীয় আস্থার পতন শুরু হয়।
লেখক: রহমান মৃধা, গবেষক ও লেখক, প্রাক্তন পরিচালক, ফাইজার, সুইডেন
rahman.mridha@gmail.com
মত দ্বিমত
জুলাই বিপ্লবের প্রজন্ম: পরিবর্তনের অগ্নিশিখা না নতুন রাষ্ট্রচিন্তার সূচনা?
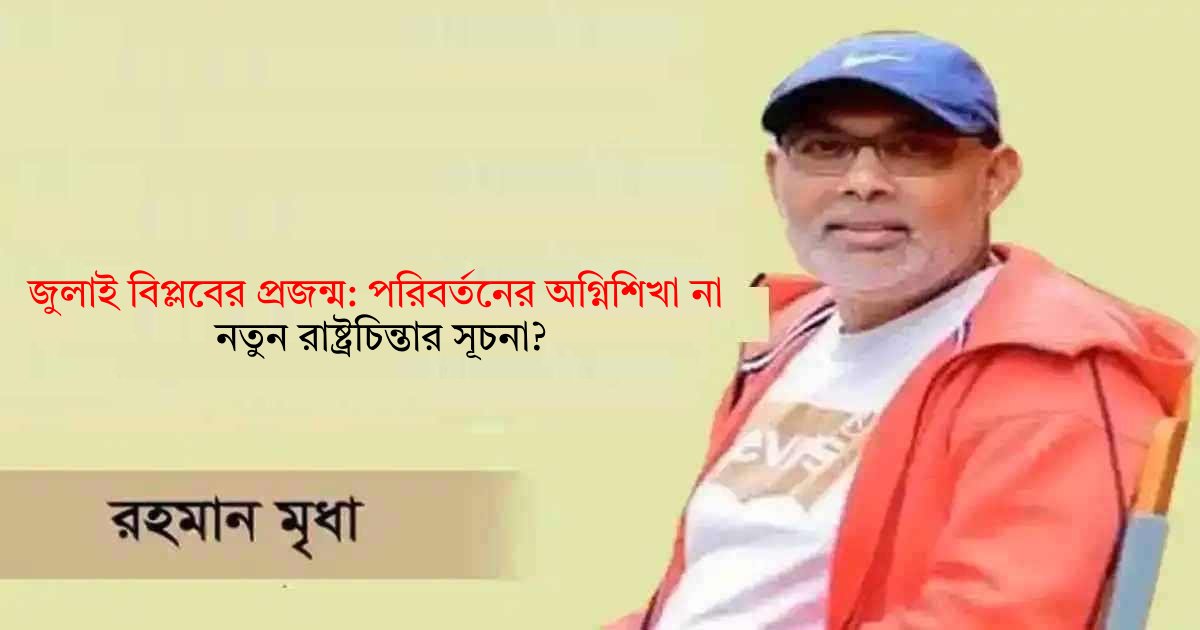
ছাত্রনেতৃত্বে এক অভ্যুত্থান শুধু সরকার পরিবর্তন করেনি, বরং প্রশ্ন তুলেছে ক্ষমতা, গণতন্ত্র এবং ভবিষ্যৎ রাষ্ট্রব্যবস্থা নিয়ে।ইতিহাসের কিছু মুহূর্ত থাকে যা কেবল একটি রাজনৈতিক ঘটনা নয়, বরং একটি জাতির মানসিক রূপান্তরের সূচনা। বাংলাদেশের জুলাই বিপ্লব তেমনই একটি মুহূর্ত। ছাত্রদের নেতৃত্বে শুরু হওয়া এই আন্দোলন শেষ পর্যন্ত এমন এক গণঅভ্যুত্থানে রূপ নেয়, যার ফলে দীর্ঘদিনের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পদত্যাগ করতে বাধ্য হন।
এই আন্দোলনের শুরু ছিল সরকারি চাকরির কোটা ব্যবস্থার বিরুদ্ধে ছাত্রদের প্রতিবাদ থেকে, কিন্তু দ্রুত তা জাতীয় বিদ্রোহে পরিণত হয়। এখানেই নতুন প্রজন্মের চরিত্র স্পষ্ট হয়: তারা কেবল একটি নীতির পরিবর্তন চায়নি, তারা রাষ্ট্রের কাঠামো নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে। কিন্তু এই প্রজন্ম কি সত্যিই অতীত থেকে আলাদা?
হ্যাঁ, একটি বড় অর্থে আলাদা। তারা ক্ষমতার উত্তরাধিকারকে স্বাভাবিক ধরে নেয় না। তারা বৈষম্যহীন সমাজের স্বপ্নে সংগঠিত হয়েছে, যেমন ‘বৈষম্যের বিরুদ্ধে শিক্ষার্থীরা’ প্ল্যাটফর্মটি দেখায়, যা আন্দোলনের মাধ্যমে রাজনৈতিক পরিসর গড়ে তুলতে কাজ করেছে। এই তরুণ নেতৃত্বের মধ্যেই উঠে এসেছে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ নাম।
নাহিদ ইসলাম, যিনি ছাত্র আন্দোলনের কেন্দ্রীয় সমন্বয়ক ছিলেন, এক পর্যায়ে প্রধানমন্ত্রী পদত্যাগের এক দফা দাবি ঘোষণা করে বিপ্লবের সবচেয়ে পরিচিত মুখ হয়ে ওঠেন। পরে তিনি অন্তর্বর্তী সরকারেও দায়িত্ব পালন করেন। অন্যদিকে, নাসিরউদ্দিন পাটোয়ারী জাতীয় নাগরিক কমিটির আহ্বায়ক হিসেবে একটি বৈষম্যহীন ও অন্তর্ভুক্তিমূলক গণতন্ত্র গঠনের লক্ষ্যে প্ল্যাটফর্ম তৈরি করেছেন।
ঢাকা-৮ আসনের মতো রাজনৈতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ এক মঞ্চে নাসিরউদ্দিন পাটোয়ারীর প্রার্থিতা শুধু একটি নির্বাচন নয়, বরং নতুন ধারার রাজনীতির এক প্রতীকী পরীক্ষা। জাতীয় নাগরিক পার্টি তাঁকে এই আসনে প্রার্থী করেছে, যা তরুণ নেতৃত্বের সামনে আসার একটি স্পষ্ট ইঙ্গিত বহন করে। কিন্তু তাঁর পথ মোটেই মসৃণ নয়। প্রচারণার সময় তাঁকে লক্ষ্য করে ডিম নিক্ষেপ ও হয়রানির ঘটনা ঘটেছে, যা রাজনৈতিক মতভেদের প্রতি অসহিষ্ণুতার প্রশ্ন তুলে দিয়েছে এবং তদন্তের নির্দেশও দেওয়া হয়েছে।
তবু এখানেই এই গল্পের মোড়। প্রতিকূলতার মুখে দাঁড়িয়েও তাঁর অংশগ্রহণ দেখায় যে রাজনীতি কেবল ক্ষমতার প্রতিযোগিতা নয়, বরং ধারণা, সাহস এবং সামাজিক চিন্তারও প্রতিযোগিতা। ঢাকা-৮-এর লড়াই তাই একটি আসনের সীমা ছাড়িয়ে ভিন্ন মতের সহাবস্থান, অংশগ্রহণমূলক রাজনৈতিক সংস্কৃতি এবং নতুন প্রজন্মের আত্মপ্রকাশের প্রতীক হয়ে উঠছে। যখন একটি প্ল্যাটফর্ম সমাজকে শুধু বিনোদনের আলোচনায় আটকে না রেখে চিন্তার পরিসরকে বিস্তৃত করতে চায়। তখন সেই রাজনীতি ধীরে ধীরে বিশ্বদরবারে নিজের ভাষা তৈরি করে। আর সেই ভাষার কেন্দ্রে থাকে একটি বার্তা: ভয় নয়, ভবিষ্যৎই শেষ পর্যন্ত ইতিহাস লিখে। এটি শুধু নেতৃত্ব নয়, একটি দৃষ্টিভঙ্গির ইঙ্গিত। পরিবর্তনের দর্শন: পরিষ্কার না হলেও শক্তিশালী।
সমালোচকেরা বলেন, নতুন প্রজন্মের পরিকল্পনা সবসময় স্পষ্ট নয়। সত্যি বলতে, বিপ্লবের ভাষা প্রায়ই অসম্পূর্ণ হয়। কিন্তু অসম্পূর্ণতা মানেই দুর্বলতা নয়। জুলাই ঘোষণাপত্রে রাজনৈতিক ও সাংবিধানিক সংস্কার, গণতান্ত্রিক পুনর্গঠন এবং বিশ্বাসযোগ্য নির্বাচনের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে।
অর্থাৎ, এই আন্দোলনের কেন্দ্রবিন্দুতে ছিল একটি বড় প্রশ্ন: রাষ্ট্র কাদের জন্য? ত্যাগের মূল্য এই বিপ্লব ছিল রক্তহীন নয়। সহিংসতার সময় এক হাজারেরও বেশি মানুষ নিহত হন, যা দেশের স্বাধীনতার পর সবচেয়ে প্রাণঘাতী সময়গুলোর একটি হিসেবে বিবেচিত। এটি মনে করিয়ে দেয়, পরিবর্তন কখনোই বিনামূল্যে আসে না। ভুল, বিভ্রান্তি এবং বাস্তবতা যে কোনো গণআন্দোলনের মতো এখানেও বিতর্ক আছে। কেউ কেউ অভিযোগ তুলেছেন যে বিপ্লবের স্মৃতি রাজনৈতিকভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে, যার বিরুদ্ধে নাগরিক নেতারা সতর্ক করেছেন। এই সতর্কবার্তা গুরুত্বপূর্ণ।
কারণ একটি বিপ্লব তখনই সফল হয়, যখন তা ক্ষমতার নতুন কেন্দ্রে পরিণত না হয়ে প্রতিষ্ঠান তৈরি করে। নতুন পৃথিবীর ইঙ্গিত আজকের বিশ্বে তরুণরা আর কেবল দর্শক নয়। তারা রাষ্ট্রের অংশীদার হতে চায়। বাংলাদেশের ঘটনাপ্রবাহ দেখায়, ঐক্য এমন এক শক্তি যা কেনা যায় না।
এই প্রজন্ম হয়তো সব প্রশ্নের উত্তর জানে না। কিন্তু তারা একটি প্রশ্ন করতে শিখেছে: কেন নয় এবং ইতিহাসে প্রায় সব বড় পরিবর্তন শুরু হয়েছে এই প্রশ্ন থেকেই। সবচেয়ে বড় পরীক্ষা এখন স্বৈরাচারী পরিবার ও সরকারের পতন বিপ্লবের শেষ নয়, বরং শুরু।
নতুন নেতৃত্ব কি প্রতিষ্ঠান গড়তে পারবে? তারা কি ব্যক্তিনির্ভর রাজনীতি ভেঙে নীতিনির্ভর রাষ্ট্র তৈরি করবে? তারা কি আবেগকে নীতিতে রূপ দিতে পারবে? যদি পারে, তবে জুলাই শুধু একটি মাসের নাম থাকবে না। এটি হয়ে উঠবে একটি রাজনৈতিক পুনর্জন্মের প্রতীক।
পরিশেষে একটি আহ্বান বাংলাদেশ আজ এক সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে। তরুণরা দেখিয়ে দিয়েছে সাহস কাকে বলে। এখন তাদের প্রমাণ করতে হবে প্রজ্ঞা কাকে বলে। কারণ বিপ্লবের সবচেয়ে কঠিন কাজ হলো ক্ষমতা দখল নয়,ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা। জাগো বাংলাদেশ জাগো কিন্তু এবার শুধু প্রতিবাদে নয়, রাষ্ট্রগঠনে।
রহমান মৃধা, গবেষক ও লেখক, সাবেক পরিচালক, ফাইজার, সুইডেন
rahman.mridha@gmail.com

























