মত দ্বিমত
দুর্নীতির গহ্বর থেকে রাষ্ট্রের পুনর্জন্ম, সময়ের দাবি
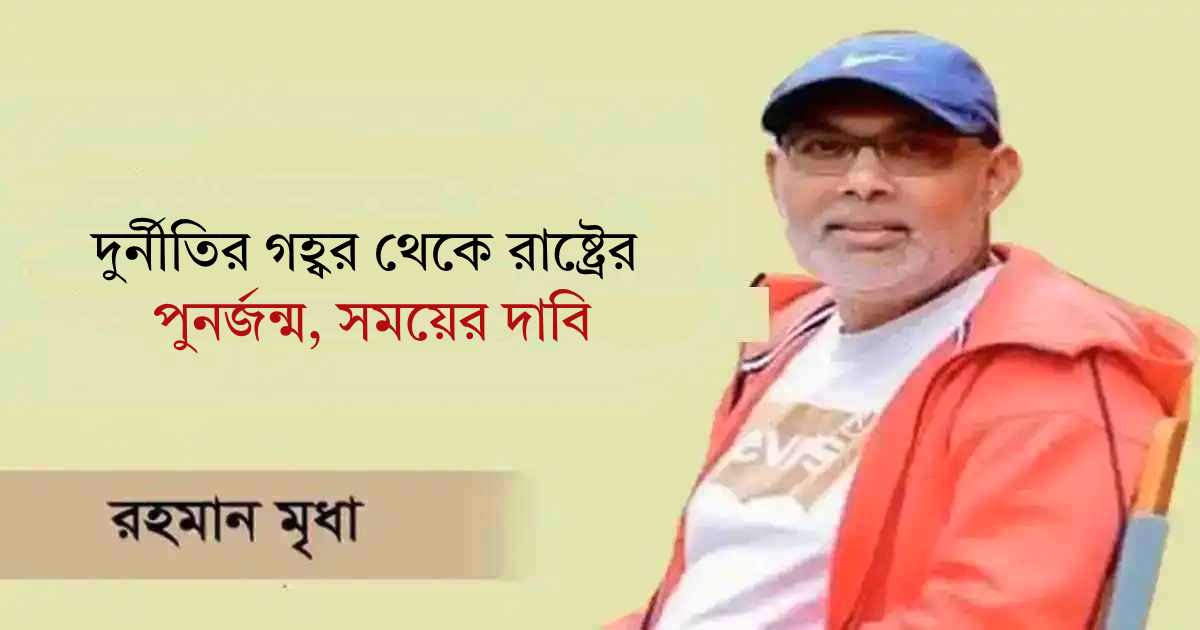
যাদের কাছে দেশ পরিচালনার জন্য কিছুই নেই, শুধু দুর্নীতি ছাড়া, তারা কিভাবে দেশ পরিচালনা করবে? হ্যাঁ, বলছি বাংলাদেশের দুর্নীতিগ্রস্ত রাজনীতিবিদদের কথা। স্বৈরশাসনের পতনের পর দীর্ঘ চৌদ্দ মাস কেটে গেল, অথচ দেশের স্থিতিশীলতা আজও ফেরেনি। কারণ একটাই: দুর্নীতিবিরোধী স্লোগানের আড়ালে লুকিয়ে থাকা দুর্নীতিবাজদের আসল মুখ।
যাদের নেই সৃজনশীল শিক্ষা, নেই সামাজিক দায়িত্ব, নেই কোনো দেশগঠনের দৃষ্টি—তাদের হাতে শুধু ধান্দাবাজি, চাঁদাবাজি, দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি, হানাহানি ও সন্ত্রাস। এই মানুষগুলোই এখন রাষ্ট্র চালায়! তারা যদি সত্যিই দেশ পরিচালনা করতে পারতো, তাহলে শেখ হাসিনা ষোল বছর ক্ষমতায় থাকতে পারতো না।
যদি ছাত্রসমাজ ও সাধারণ মানুষ স্বৈরাচারীর বিরুদ্ধে না দাঁড়াতো, তাহলে কি সম্ভব হতো এই দুর্নীতিবাহিনীকে ক্ষমতা থেকে উৎখাত করা? একটি দরিদ্র দেশের মানুষ যখন তেল আনতে নুনের খরচ যোগাতে পারে না, তখন সেই দেশের শাসকশ্রেণি যদি বিলাসিতা, ঘুষ ও অরাজকতায় মত্ত থাকে—এটা কেবল রাষ্ট্রীয় ব্যর্থতা নয়, এটি জাতির আত্মহনন।
আমরা আসলে কী করছি? আমাদের রাজনীতি আজ আত্মবিনাশের পথে, এবং রাষ্ট্রের প্রতিটি স্তরে সেই পচনের দুর্গন্ধ ছড়িয়ে পড়েছে। এখন রন্ধ্রে রন্ধ্রে বুঝতে পারছি কেন ভারত আমাদের বারোটা বাজাচ্ছে! এটা ভারতের দোষ নয়—আমরাই সুযোগ তৈরি করছি, আর তারা তা দক্ষতার সাথে কাজে লাগাচ্ছে। ভারত আমাদের প্রতিপক্ষ নয়, আমাদের দুর্বলতার দর্পণ। যে জাতি নিজস্ব নীতি ও মর্যাদায় টিকে থাকতে পারে না, তাকে অন্য কেউ কখনো সম্মান করবে না।
যে সকল দুর্নীতিবাজ রাজনীতিবিদরা বলে তারা বাংলাদেশের ভাগ্য বদলাবে, তারা আসলে নিজেদের ভাগ্য মজবুত করার খেলায় ব্যস্ত। কারণ না আছে তাদের আন্তর্জাতিক গ্রহণযোগ্যতা, না আছে নীতিনিষ্ঠ পরিকল্পনা, না আছে শক্তিশালী অর্থনৈতিক রিজার্ভ। তাহলে এইসব দুর্নীতিবাজদের পিছনে সময় নষ্ট করে কোনো সমাধান আসবে? কী মনে হয়?
জাতিসংঘ ইতিমধ্যেই বাংলাদেশি শান্তিরক্ষীদের অংশগ্রহণ নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে। রেমিটেন্স যোদ্ধারা বিদেশে প্রতিনিয়ত সমস্যার মুখে পড়ছে। আগামী দিনে যদি শ্রমবাজার বন্ধ হয়ে যায়, রেমিটেন্স কমে যায়—তখন কী হবে এই দুর্নীতিগ্রস্ত রাষ্ট্রব্যবস্থার? একটি জাতির জন্য এটি কেবল অর্থনৈতিক বিপর্যয় নয়, এটি আন্তর্জাতিক পরিসরে এক প্রকার নির্বাসন।
গণতন্ত্রের ভণ্ডামি ও বাস্তবতার প্রশ্ন
বাংলাদেশের বর্তমান গণতন্ত্র এক প্রহসন ছাড়া আর কিছু নয়। এখানে নির্বাচন মানে টাকা, অস্ত্র, আর ভয় দেখানোর প্রতিযোগিতা। রাজনীতি মানে পরিবারতন্ত্র, যেখানে জনগণ কেবল দর্শক আর ভোট কেবল একদিনের মঞ্চনাটক।
এই ভণ্ড গণতন্ত্রের কারণে প্রশাসন ভেঙে পড়েছে, ন্যায়বিচার বিক্রি হয়েছে, এবং সমাজে নৈতিকতার জায়গা দখল করেছে ধান্দাবাজি ও ভয়। গণতন্ত্র তখনই অর্থবহ, যখন নেতৃত্ব জবাবদিহি করে; যখন রাষ্ট্রের প্রতিটি স্তরে দক্ষতা, সততা ও দূরদৃষ্টি থাকে। বাংলাদেশে আজ সেই তিনটি জিনিসই অনুপস্থিত।
তাই গণতন্ত্র নয়—এই দেশের দরকার শৃঙ্খলা, কঠোরতা, এবং বাস্তব উন্নয়নবাদী রাষ্ট্রনীতি। বাংলাদেশের আজকের বাস্তবতা এমন এক পর্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছে যেখানে পশ্চিমা ধাঁচের গণতন্ত্র একেবারেই অচল। যে দেশে নির্বাচন মানে অর্থ আর অস্ত্রের প্রতিযোগিতা, যেখানে রাজনীতি মানে পরিবারতন্ত্র আর দুর্নীতির সমীকরণ, সেখানে গণতন্ত্র নামের নাটক কেবল লুটপাটের বৈধ লাইসেন্স ছাড়া আর কিছু নয়। পশ্চিমা মডেল আমাদের জন্য নয়—আমাদের প্রয়োজন শৃঙ্খলা, দায়িত্ববোধ ও কঠোর রাষ্ট্রচিন্তা। আর এখানেই চীনের পথ বাংলাদেশের জন্য আশার আলো।
চীন কোনো দিবাস্বপ্নের দেশ নয়—চীন হলো প্রমাণ, যে সুশাসন মানে বক্তৃতা নয়, কাজ। সেখানে দুর্নীতি করলে মৃত্যুদণ্ড হয়, ক্ষমতার অপব্যবহার করলে নিজ দলের মধ্যেই বিচার হয়, এবং রাষ্ট্রের নীতি নির্ধারণ হয় দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনার মাধ্যমে, নির্বাচন কমিশনের নাটক বা তোষণ দিয়ে নয়। বাংলাদেশে এই দৃঢ়তা নেই, কারণ এখানে সবাই দায় এড়িয়ে বাঁচতে চায়। এখানে কেউ চায় না জবাবদিহিতা, কারণ জবাবদিহি মানেই দুর্নীতির পর্দা উন্মোচন।
চীন তার জনগণকে দিয়েছে বাস্তব উন্নয়ন—বিদ্যুৎ, শিল্প, প্রযুক্তি, কর্মসংস্থান। ওরা সময় নষ্ট করেনি স্লোগানে, তারা সময় দিয়েছে পরিকল্পনায়। বাংলাদেশকে এখন সেই পথেই যেতে হবে। যেখানে দুর্নীতি হবে রাষ্ট্রদ্রোহ, যেখানে নেতার কাজ হবে সেবা, লুট নয়। চীনের সাথে কৌশলগত সম্পর্ক মানে শুধু বিনিয়োগ নয়, মানে একটি শৃঙ্খলিত প্রশাসনিক কাঠামো শেখা।
আমাদের দরকার developmental authoritarianism—একটি এমন প্রশাসনিক কাঠামো, যা দুর্নীতির নরম সুরে নয়, কঠোর বাস্তবতায় কাজ করে। চীনের শৃঙ্খলা বাংলাদেশের জন্য ওষুধের মতো। আজ যে রাষ্ট্রে স্কুলে ঘুষ, হাসপাতালে দালালি, আদালতে কেনাবেচা, সেখানকার রোগ একটাই—দুর্নীতি। এই রোগে ওষুধ লাগবে; আর এই ওষুধের নাম ‘state discipline’। পশ্চিমা গণতন্ত্র বলবে, “মানবাধিকার।” কিন্তু যে দেশে মানুষ নিজের অধিকারই জানে না, সেখানে মানবাধিকার শুধু মশকরা। প্রথমে দরকার রাষ্ট্রের শৃঙ্খলা, পরে আসবে মানবাধিকার।
চীনের মডেল বাংলাদেশে আনতে হবে তিন ধাপে –
প্রথম, প্রশাসনে শূন্য সহনশীলতা নীতি; দ্বিতীয়, দলীয় রাজনীতি থেকে আমলাতন্ত্র ও বিচার বিভাগকে সম্পূর্ণ আলাদা করা; তৃতীয়, পরিকল্পিত শিল্পায়ন ও স্থানীয় উৎপাদনমুখী রাষ্ট্রনীতি।
চীন এগুলো করেছে বলেই তাদের গ্রামের মানুষ আজও উন্নয়নের সুফল পায়। বাংলাদেশের মানুষ পায় না, কারণ উন্নয়ন মানে এখানে দলীয় ঠিকাদারি আর মিডিয়ার প্রচার। এখন সময় এসেছে—পশ্চিমা অনুকরণ বন্ধ করে এশীয় বাস্তবতার পথে হাঁটার। যদি সত্যিই বাংলাদেশকে আমরা বাঁচাতে চাই, তাহলে চীনের থেকে শিখতে হবে কীভাবে দুর্নীতিকে কবর দিতে হয়, কীভাবে রাষ্ট্রের প্রতিটি স্তরে কঠোর শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করতে হয়। এই দেশের মাটিতে এখন আর স্লোগান নয়—প্রয়োজন লোহার শাসন, কাঠামোগত সংস্কার এবং নতুন রাষ্ট্রদৃষ্টি।
রহমান মৃধা
গবেষক ও লেখক
সাবেক পরিচালক, ফাইজার, সুইডেন
Rahman.Mridha@gmail.com
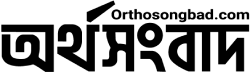
মত দ্বিমত
ধর্ম, ভূরাজনীতি এবং মানবজাতির অস্তিত্ব

মধ্যপ্রাচ্য যখন ইরানের অভ্যন্তরীণ অস্থিরতা, ক্ষমতার দ্বন্দ্ব এবং জনঅসন্তোষের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে, ঠিক সেই সময়ে যুক্তরাষ্ট্রের রাজনীতিতে ডোনাল্ড ট্রাম্পকে ঘিরে এক নতুন ধর্মীয় বয়ান তৈরি হচ্ছে। প্রশ্ন উঠছে, এই দুই প্রান্তের অস্থিরতার মধ্যে কি কোনো অদৃশ্য কৌশলগত সংযোগ আছে?
ইরানের ভেতরে দীর্ঘদিন ধরে অর্থনৈতিক চাপ, সামাজিক নিয়ন্ত্রণ এবং রাজনৈতিক অসন্তোষ জমে আছে। অন্যদিকে ইসরায়েল তার নিরাপত্তা কৌশলকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকারে রেখেছে। এমন বাস্তবতায় একটি প্রশ্ন স্বাভাবিকভাবে উঠে আসে: আঞ্চলিক শক্তিগুলো কি অভ্যন্তরীণ সংকটকে বহির্মুখী সংঘাতে রূপান্তরিত করার চেষ্টা করছে?
ডোনাল্ড ট্রাম্পের ওপর হত্যাচেষ্টা এবং তার পরবর্তী সময়ে তাকে “ঐশ্বরিকভাবে রক্ষিত নেতা” হিসেবে উপস্থাপন করার রাজনৈতিক প্রচার কি কেবল অভ্যন্তরীণ মার্কিন রাজনীতির অংশ, নাকি এটি বৃহত্তর ভূরাজনৈতিক কৌশলের উপাদান?
ইসরায়েল কি তার নিরাপত্তা নীতিকে শক্তিশালী করতে মার্কিন অভ্যন্তরীণ রাজনীতির নির্দিষ্ট ধারাকে প্রভাবিত করছে?
ইরানের অভ্যন্তরীণ ক্ষোভ কি আঞ্চলিক উত্তেজনাকে আরও উসকে দিচ্ছে?
নাকি আমরা কেবল সমান্তরাল সংকটকে একটি বৃহৎ কাহিনিতে জোড়া লাগানোর চেষ্টা করছি?
এই প্রশ্নগুলোই আমাদের বর্তমান বৈশ্বিক বাস্তবতা বোঝার সূচনা বিন্দু।
বর্তমান বিশ্ব এমন এক পর্যায়ে দাঁড়িয়ে আছে যেখানে ধর্মীয় ভাষা, রাজনৈতিক কৌশল এবং ভূরাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা এক জটিল বিন্যাস তৈরি করেছে। বিশেষ করে যুক্তরাষ্ট্রের সাম্প্রতিক রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহ, মধ্যপ্রাচ্যের উত্তেজনা এবং “শেষ সময়ের যুদ্ধ” ধরনের ভাষার পুনরুত্থান আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে নতুন বিতর্ক সৃষ্টি করেছে। এই প্রতিবেদনটি ঘটনাগুলো ধারাবাহিকভাবে বিশ্লেষণ করছে।
১. ট্রাম্পকে ঘিরে “ঐশ্বরিক রক্ষা” ধারণা: ২০২৪ সালের নির্বাচনী প্রচারের সময় ডোনাল্ড ট্রাম্পের ওপর হত্যাচেষ্টা এবং তার বেঁচে যাওয়া মার্কিন রাজনীতিতে গভীর প্রতীকী প্রভাব ফেলে। তার কিছু সমর্থকের মধ্যে ধারণা জোরদার হয় যে তিনি ঈশ্বরের দ্বারা রক্ষিত অথবা ঈশ্বরের পরিকল্পনার অংশ।
এই বিশ্বাসের পেছনে কয়েকটি ধর্মীয় ব্যাখ্যা কাজ করে। মার্কিন ইভানজেলিক্যাল খ্রিস্টানদের একটি অংশ মনে করে ঈশ্বর ইতিহাসে রাজনৈতিক নেতাদের ব্যবহার করেন। বাইবেলের পুরনো নিয়মে এমন উদাহরণ রয়েছে যেখানে নৈতিকভাবে নিখুঁত নন এমন রাজাকেও ঐশ্বরিক পরিকল্পনায় ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। ফলে ট্রাম্পকে কেউ কেউ নৈতিক আদর্শ নয়, বরং ঐশ্বরিকভাবে ব্যবহৃত নেতা হিসেবে উপস্থাপন করেন।
তবে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, এটি সব রিপাবলিকান বা সব খ্রিস্টানের বিশ্বাস নয়। রিপাবলিকান পার্টির কোনো আনুষ্ঠানিক ধর্মীয় মতবাদ নেই। এটি একটি গোষ্ঠীগত ধর্মীয় ব্যাখ্যা, রাজনৈতিক বাস্তবতার আনুষ্ঠানিক কাঠামো নয়।
২. ইরানকে “অশুভ শক্তি” হিসেবে চিত্রায়ন: যুক্তরাষ্ট্র ও ইরানের সম্পর্ক দীর্ঘদিন ধরে উত্তেজনাপূর্ণ। পারমাণবিক কর্মসূচি, আঞ্চলিক প্রভাব বিস্তার এবং ইসরায়েল প্রশ্ন এই উত্তেজনার কেন্দ্রে রয়েছে। মার্কিন রক্ষণশীল রাজনীতির একটি অংশ ইরানকে কৌশলগত প্রতিপক্ষ হিসেবে তুলে ধরে।
কিছু ইভানজেলিক্যাল গোষ্ঠী বাইবেলের ভবিষ্যদ্বাণীকে আধুনিক ভূরাজনীতির সঙ্গে যুক্ত করার চেষ্টা করে। তাদের মতে মধ্যপ্রাচ্যের সংঘাত “শেষ সময়ের” পূর্বাভাস হতে পারে, ইসরায়েল রক্ষা করা ঈশ্বরের পরিকল্পনার অংশ, এবং ইরান সম্ভাব্য প্রতিপক্ষ শক্তি। তবে এটি মূলধারার খ্রিস্টীয় মতবাদ নয়, বরং নির্দিষ্ট রাজনৈতিক ধর্মীয় ব্যাখ্যা।
৩. ইহুদি ধর্মে “শেষ সংঘাত” ধারণা: ইহুদি ধর্মে মেসিয়ানিক যুগের ধারণা রয়েছে, যেখানে ভবিষ্যতে শান্তি ও ন্যায় প্রতিষ্ঠিত হবে। কিছু ঐতিহ্যিক গ্রন্থে “গগ ও মাগগ” নামে একটি চূড়ান্ত সংঘাতের উল্লেখ আছে। কিন্তু এখানে একটি মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। ইহুদিরা যিশুকে মেসিয়া হিসেবে মানে না এবং যিশুর পুনরাগমনে বিশ্বাস করে না। তাদের মতে ভবিষ্যৎ মেসিয়া এখনো আগমন করেননি। ফলে “শেষ যুদ্ধের পর যিশু ফিরে আসবেন” এই ধারণা ইহুদি বিশ্বাস নয়, বরং খ্রিস্টীয় ধর্মতত্ত্বের অংশ।
৪. খ্রিস্টধর্মে পুনরাগমন ও চূড়ান্ত বিচার: খ্রিস্টধর্মে বিশেষ করে উপেনবারেলসেবোকেনে একটি চূড়ান্ত আধ্যাত্মিক সংগ্রামের বর্ণনা রয়েছে। সেখানে যিশুর পুনরাগমন, ভালো ও মন্দের চূড়ান্ত বিচার এবং নতুন আকাশ ও নতুন পৃথিবীর ধারণা উল্লেখ আছে। এই পাঠে মুসলমানদের কোনো উল্লেখ নেই, কারণ ইসলাম খ্রিস্টধর্মের কয়েক শতাব্দী পরে আবির্ভূত হয়েছে। এখানে সংঘাতটি ধর্মতাত্ত্বিক অর্থে ঈশ্বর ও অশুভ শক্তির মধ্যে, আধুনিক কোনো জাতি বা জনগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে নয়। অধিকাংশ খ্রিস্টান এই বর্ণনাকে প্রতীকী বা আধ্যাত্মিক সংগ্রাম হিসেবে দেখেন।
৫. “মুসলমানদের বিরুদ্ধে শেষ যুদ্ধ” ধারণার বিশ্লেষণ: মুসলমানদের বিরুদ্ধে অ্যাপোক্যালিপ্টিক যুদ্ধ সাধারণত এমন একটি ধর্মীয় রঙযুক্ত ধারণাকে বোঝায় যেখানে পৃথিবীর শেষ সময়ে ভালো ও মন্দের মধ্যে একটি চূড়ান্ত যুদ্ধ হবে, এবং সেখানে মুসলমানদেরকে প্রতিপক্ষ হিসেবে কল্পনা করা হয়। গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, এই ধারণা মূলধারার কোনো ধর্মীয় শিক্ষার প্রতিনিধিত্ব করে না। এটি নির্দিষ্ট কিছু উগ্র বা চরমপন্থী ব্যাখ্যার ফল। তাই বিষয়টি বোঝার জন্য আমাদের প্রথমেই দুটি জিনিস আলাদা করতে হবে। ধর্মতাত্ত্বিক বিশ্বাস এবং রাজনৈতিক বা উগ্র ব্যাখ্যা।
ইসলাম ধর্মে শেষ সময়ের ধারণা, ইসলামে “আখেরাত” ও “কিয়ামত” সংক্রান্ত একটি পূর্ণাঙ্গ তত্ত্ব আছে, যাকে এস্ক্যাটোলজি বলা হয়। কিছু হাদিসে বড় ফিতনা, আল মাহদীর আবির্ভাব এবং ঈসা আলাইহিস সালামের পুনরাগমনের কথা উল্লেখ আছে। কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়:
- এসব বর্ণনার ব্যাখ্যা বিভিন্ন আলেম বিভিন্নভাবে করেছেন।
- অধিকাংশ মুসলমান এগুলোকে প্রতীকী বা আল্লাহর জ্ঞানের অন্তর্গত বিষয় হিসেবে দেখেন।
- ইসলামের মূলধারার শিক্ষা দৈনন্দিন জীবনে ন্যায়, দায়িত্ব, শান্তি ও সহাবস্থানের উপর জোর দেয়।
অর্থাৎ ইসলাম কোনো জাতি বা নির্দিষ্ট ধর্মের বিরুদ্ধে চূড়ান্ত যুদ্ধের আনুষ্ঠানিক আহ্বান দেয় না। কিছু উগ্র গোষ্ঠী এসব বর্ণনাকে ব্যবহার করে রাজনৈতিক সহিংসতাকে বৈধতা দেওয়ার চেষ্টা করেছে, কিন্তু তা মূলধারার ইসলাম নয়।
খ্রিস্টধর্মে শেষ সময়ের ধারণা, খ্রিস্টধর্মেও শেষ সময় বা পৃথিবীর অন্তিম অধ্যায় নিয়ে বর্ণনা আছে। বিশেষ করে নতুন নিয়মের উপেনবারেলসেবোকেনে ভালো ও মন্দের এক চূড়ান্ত সংঘাতের কথা বলা হয়েছে, যাকে অনেক সময় হারমাগেডন বলা হয়।
- সেখানে মুসলমানদের কোনো উল্লেখ নেই, কারণ ইসলাম খ্রিস্টধর্মের কয়েক শতাব্দী পরে আবির্ভূত হয়েছে।
- যুদ্ধটি ধর্মতাত্ত্বিক অর্থে ঈশ্বর ও অশুভ শক্তির মধ্যে, আধুনিক কোনো নির্দিষ্ট জাতি বা জনগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে নয়।
- অধিকাংশ খ্রিস্টান এই বর্ণনাকে প্রতীকী বা আধ্যাত্মিক সংগ্রাম হিসেবে ব্যাখ্যা করেন।
কিছু চরমপন্থী গোষ্ঠী এসব পাঠকে আক্ষরিক অর্থে নিয়ে বর্তমান ভূরাজনীতির সাথে যুক্ত করার চেষ্টা করে। পার্থক্য মূলত তিনটি ক্ষেত্রে:
- ইতিহাসের শেষ অধ্যায় কিভাবে বর্ণনা করা হয়েছে
- কোন কোন ধর্মীয় চরিত্র গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন
- পাঠগুলোকে আক্ষরিক না প্রতীকীভাবে ব্যাখ্যা করা হয়
দুই ধর্মের দৈনন্দিন জীবনের মূল বার্তা হলো নৈতিকতা, দায়িত্ব, শান্তি এবং ঈশ্বরের সাথে সম্পর্ক। মুসলমানদের বিরুদ্ধে অ্যাপোক্যালিপ্টিক যুদ্ধ ধরনের ভাষা সাধারণত রাজনৈতিক প্রচারণা, চরমপন্থী মতাদর্শ, সভ্যতার সংঘাত তত্ত্ব এবং ধর্মীয় পাঠের অপব্যবহারের প্রেক্ষাপটে ব্যবহৃত হয়। এটি মূলধারার খ্রিস্টান বা মুসলমানদের বিশ্বাসকে প্রতিনিধিত্ব করে না।
৬. ইসরায়েল প্রশ্ন ও নিরাপত্তা রাজনীতি: ইসরায়েল বর্তমানে নিরাপত্তাকে রাষ্ট্রনীতির কেন্দ্রে রেখেছে। হামাস, হিজবুল্লাহ ও ইরানপন্থী গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে শক্ত অবস্থান তাদের কৌশলগত নীতির অংশ। প্রতিরোধ ক্ষমতা বজায় রাখা, শত্রুকে নিরস্ত করা এবং প্রযুক্তিগত সামরিক শ্রেষ্ঠত্ব ধরে রাখা তাদের অগ্রাধিকার। তবে আন্তর্জাতিক মহলে সামরিক পদক্ষেপের মানবিক মূল্য, দীর্ঘমেয়াদি রাজনৈতিক সমাধানের অভাব এবং ফিলিস্তিন প্রশ্নের অনিরসন নিয়ে তীব্র বিতর্ক রয়েছে। নিরাপত্তা ও মানবিকতার দ্বৈত বাস্তবতা এখানেই স্পষ্ট।
৭. ট্রাম্প প্রশাসন বিশ্ব রাজনীতিতে কয়েকটি শিক্ষা দিয়েছে:
- জাতীয়তাবাদ বহুপাক্ষিকতার ওপর প্রাধান্য পেতে পারে।
- ব্যক্তিকেন্দ্রিক কূটনীতি প্রথাগত কাঠামোকে চ্যালেঞ্জ করতে পারে।
- ধর্মীয় ভোটব্যাংক নীতিনির্ধারণে প্রভাব ফেলতে পারে।
- অভ্যন্তরীণ মেরুকরণ আন্তর্জাতিক অবস্থানকেও প্রভাবিত করতে পারে।
৮. ভবিষ্যৎ প্রবণতা: বিশ্ব এখন মূলত কৌশলগত প্রতিদ্বন্দ্বিতার যুগে প্রবেশ করেছে। যুক্তরাষ্ট্র, চীন এবং রাশিয়ার মধ্যে প্রতিযোগিতা বাড়ছে। মধ্যপ্রাচ্যে প্রক্সি সংঘাত অব্যাহত থাকার সম্ভাবনা রয়েছে। প্রযুক্তি, সাইবার যুদ্ধ এবং অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা সামরিক সংঘাতের বিকল্প হাতিয়ার হয়ে উঠছে।
বিশ্ব কি ধর্মীয় শেষ যুদ্ধের দিকে এগোচ্ছে? বাস্তব বিশ্লেষণ বলছে, না। ধর্মীয় ভাষা ব্যবহৃত হচ্ছে, কিন্তু সিদ্ধান্তগুলো মূলত নিরাপত্তা, ক্ষমতার ভারসাম্য এবং অর্থনৈতিক কৌশলের ভিত্তিতে নেওয়া হচ্ছে। ধর্মতত্ত্ব, পরিচয় রাজনীতি এবং ক্ষমতার ভাষার এই মিশ্র বাস্তবতা বোঝা আজ অত্যন্ত জরুরি। আবেগ নয়, বিশ্লেষণই হতে পারে দায়িত্বশীল গণমাধ্যমের পথ।
রহমান মৃধা, গবেষক ও লেখক, সাবেক পরিচালক, ফাইজার, সুইডেন
মত দ্বিমত
বিংশ শতাব্দীর কাঠামো না কি একবিংশ শতাব্দীর প্রযুক্তিনির্ভর: কোন পথে বাংলাদেশের প্রতিরক্ষা?

যুদ্ধের চরিত্র বদলে গেছে। একসময় যুদ্ধ মানেই ছিল সীমান্তে সৈন্য সমাবেশ, রাইফেল, কামান, ট্যাংক এবং সম্মুখসমরের সংঘর্ষ। রাষ্ট্রের শক্তি মাপা হতো সৈন্যসংখ্যা দিয়ে। বড় বাহিনী মানেই বড় শক্তি। সেই ধারণা বিংশ শতাব্দীর বাস্তবতায় কার্যকর ছিল।
কিন্তু একবিংশ শতাব্দীতে যুদ্ধের কেন্দ্র সরে গেছে। আজ যুদ্ধ শুধু সীমান্তে নয়, সার্ভার রুমে, স্যাটেলাইট কক্ষপথে, ডেটা সেন্টারে এবং কন্ট্রোল রুমে। ড্রোন আকাশে উড়ছে, সমুদ্রে স্বয়ংক্রিয় নজরদারি ব্যবস্থা কাজ করছে, সাইবার আক্রমণ বিদ্যুৎ গ্রিড অচল করতে পারে, ব্যাংকিং ব্যবস্থা অস্থিতিশীল করতে পারে, এমনকি একটি দেশের প্রশাসনিক কাঠামোকে পক্ষাঘাতগ্রস্ত করে দিতে পারে।
বিশ্বের বড় শক্তিগুলো তাদের প্রতিরক্ষা কৌশলে প্রযুক্তিকে অগ্রাধিকার দিচ্ছে। সাইবার স্পেস এখন স্বীকৃত যুদ্ধক্ষেত্র। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, ডেটা অ্যানালিটিক্স, স্বয়ংক্রিয় অস্ত্রব্যবস্থা এবং স্যাটেলাইট নজরদারি আধুনিক সামরিক শক্তির মূল উপাদান। সৈন্য আছে, কিন্তু সিদ্ধান্ত নিয়ন্ত্রণ করছে প্রযুক্তি।
এই বাস্তবতায় প্রশ্ন উঠছে, কেবল শারীরিক প্রশিক্ষণ, কুচকাওয়াজ এবং বৃহৎ জনবল দিয়ে কি আধুনিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করা সম্ভব? সাইবার আক্রমণ রুখতে রাইফেল লাগে না। ড্রোন প্রতিরোধে প্যারেড গ্রাউন্ডের অনুশীলন যথেষ্ট নয়। স্যাটেলাইট নজরদারি মোকাবিলায় প্রয়োজন ইলেকট্রনিক দক্ষতা।
জাতীয় নিরাপত্তা এখন সীমান্তের চেয়ে বেশি নির্ভর করছে প্রযুক্তিগত সক্ষমতার ওপর।
এবার বাংলাদেশের দিকে তাকাই। আমাদের প্রতিরক্ষা কাঠামো ঐতিহ্যগতভাবে জনবলনির্ভর। বৃহৎ সৈন্যসংখ্যা, বিস্তৃত প্রশাসনিক পরিকাঠামো এবং স্থায়ী ব্যয়ের কাঠামো রাষ্ট্রীয় বাজেটের বড় অংশ দখল করে আছে। প্রশ্ন হলো, এই বিপুল জনশক্তি কি পর্যাপ্ত প্রযুক্তিগত দক্ষতায় রূপান্তরিত হচ্ছে? নাকি আমরা এখনো সংখ্যাকে শক্তি মনে করে আত্মতুষ্ট?
শুধু বড় বাহিনী থাকলেই শক্তিশালী হওয়া যায় না। দক্ষতায় বড় হওয়াই আজকের শক্তি।
এখানেই একটি বিকল্প চিন্তার দরজা খুলে যায়। যদি সামরিক জনবলের একটি অংশকে পরিকল্পিতভাবে পুনঃপ্রশিক্ষণ দেওয়া হয় সাইবার ডিফেন্স, ডেটা অ্যানালিটিক্স, ড্রোন প্রযুক্তি, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা এবং প্রতিরক্ষা গবেষণায়, তাহলে একই মানবসম্পদ দ্বৈত ভূমিকা পালন করতে পারে। একদিকে জাতীয় নিরাপত্তা, অন্যদিকে প্রযুক্তিভিত্তিক অর্থনীতিতে অবদান।
প্রতিরক্ষা খাতকে কেবল ব্যয়ের খাত হিসেবে দেখা হবে, নাকি মানবসম্পদ উন্নয়নের কৌশলগত প্ল্যাটফর্ম হিসেবে গড়ে তোলা হবে, সেটিই এখন মূল প্রশ্ন।
বাংলাদেশের সামনে চারটি স্পষ্ট দিকনির্দেশনা থাকতে পারে।
প্রথমত, ডিমান্ড বেজড প্রযুক্তিগত শিক্ষা। বিশ্ববাজারে কোন দক্ষতার চাহিদা বাড়ছে তা বিশ্লেষণ করে প্রশিক্ষণ কাঠামো তৈরি করতে হবে। সাইবার নিরাপত্তা, অটোমেশন, ডেটা ব্যবস্থাপনা এবং উন্নত প্রযুক্তি দক্ষতা ছাড়া ভবিষ্যৎ অর্থনীতিতে টিকে থাকা সম্ভব নয়।
দ্বিতীয়ত, সামরিক পুনর্গঠন। ঐতিহ্যগত জনবল কাঠামোকে ধীরে ধীরে দক্ষতানির্ভর কাঠামোয় রূপান্তর করতে হবে। উচ্চ প্রযুক্তি ইউনিট গঠন এবং গবেষণা ও উন্নয়ন সক্ষমতা বৃদ্ধি অপরিহার্য।
তৃতীয়ত, সমন্বিত সাইবার ও ডিজিটাল প্রতিরক্ষা কমান্ড গঠন, যা বেসামরিক ও সামরিক উভয় অবকাঠামোকে সুরক্ষা দেবে।
চতুর্থত, দ্বৈত ব্যবহারযোগ্য প্রযুক্তিতে বিনিয়োগ। যে প্রযুক্তি সামরিক ও বেসামরিক উভয় ক্ষেত্রে প্রয়োগযোগ্য, সেখানে বিনিয়োগ করলে প্রতিরক্ষা ব্যয় উৎপাদনশীল বিনিয়োগে রূপান্তরিত হতে পারে।
কিন্তু এই চারটি সিদ্ধান্ত কেবল নীতিগত ঘোষণা হয়ে থাকলে চলবে না। এর পরেই প্রয়োজন একটি কাঠামোগত রূপান্তর পরিকল্পনা। মূল প্রশ্ন হলো, বর্তমানে সমগ্র প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় যে বিপুল জনশক্তি রয়েছে, তাদের ভবিষ্যৎ ভূমিকা কী হবে?
এই জনশক্তিকে কেবল নিরাপত্তা কাঠামোর স্থায়ী উপাদান হিসেবে না দেখে, জাতীয় উন্নয়নের কৌশলগত সম্পদ হিসেবে বিবেচনা করতে হবে।
রাষ্ট্রকে একটি দীর্ঘমেয়াদি রূপান্তর রোডম্যাপ তৈরি করতে হবে, যেখানে প্রতিরক্ষা খাতে কর্মরত জনবলকে ধাপে ধাপে নতুন প্রযুক্তি দক্ষতা, ডিজিটাল সক্ষমতা এবং সমাজকল্যাণমূলক উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের আওতায় আনা হবে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, সাইবার নিরাপত্তা, ডেটা ব্যবস্থাপনা, ড্রোন প্রযুক্তি, অবকাঠামো প্রযুক্তি এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় প্রশিক্ষণের মাধ্যমে এই জনশক্তি দ্বৈত সক্ষমতায় রূপ নিতে পারে।
এখানে আরেকটি কৌশলগত মাত্রা যুক্ত করা জরুরি। বিশ্বের বহু দেশে দক্ষ প্রযুক্তিগত ও শৃঙ্খলাবদ্ধ কর্মশক্তির ঘাটতি রয়েছে। পরিকল্পিত ও মানসম্মত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে প্রতিরক্ষা পটভূমির মানবসম্পদকে আন্তর্জাতিক শ্রমবাজারের উপযোগী করে তোলা গেলে তা বৈদেশিক আয়ের একটি নতুন দ্বার খুলতে পারে। রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে সমন্বিত চুক্তি, দক্ষতা সনদায়ন এবং পুনর্বাসন কাঠামোর মাধ্যমে এই প্রক্রিয়াকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়া সম্ভব।
অর্থাৎ প্রতিরক্ষা জনবলকে ধীরে ধীরে এমন এক মানবসম্পদ শক্তিতে রূপান্তর করা, যারা একদিকে জাতীয় নিরাপত্তায় অবদান রাখবে, অন্যদিকে অর্থনৈতিক উৎপাদনশীলতায় যুক্ত হবে, এবং প্রয়োজন হলে আন্তর্জাতিক বাজারেও অংশ নিতে পারবে।
এটি কেবল সামরিক সংস্কার নয়। এটি নতুন মানবিক উন্নয়নের রূপরেখা। একটি কাঠামো ফর বিল্ডিং ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট অব বাংলাদেশ, যেখানে প্রতিরক্ষা ব্যয়কে ব্যয় হিসেবে নয়, মানবসম্পদে বিনিয়োগ হিসেবে পুনঃসংজ্ঞায়িত করা হবে।
রাষ্ট্র যদি চায়, তবে বৃহৎ জনবলকে স্থায়ী ব্যয়ের বোঝা হিসেবে না দেখে উৎপাদনশীল শক্তিতে রূপান্তর করা সম্ভব। এটি হবে কৌশলগত মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনা, যেখানে প্রতিরক্ষা খাতের কর্মীরা একই সঙ্গে জাতীয় নিরাপত্তা রক্ষা করবে এবং দেশের প্রযুক্তিনির্ভর অর্থনীতিতে অবদান রাখবে।
এটি কোনো আবেগ বা সাধারণ মতামতের প্রশ্ন নয়। এটি রাষ্ট্রের দীর্ঘমেয়াদি কৌশলগত অবস্থানের প্রশ্ন। এটি আমাদের জাতীয় ভবিষ্যৎ, আমাদের অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা, এবং আগামী প্রজন্মের প্রতি দায়বদ্ধতার প্রশ্ন।
বাংলাদেশ কি বড় জনবল ধরে রেখে বিংশ শতাব্দীর শক্তির ধারণায় স্থির থাকবে, নাকি সাহসী সিদ্ধান্ত নিয়ে একবিংশ শতাব্দীর প্রযুক্তিনির্ভর প্রতিরক্ষা রাষ্ট্র গড়ে তুলবে?
রাষ্ট্রের শক্তি আর কেবল বন্দুকের নলে সীমাবদ্ধ নয়। আজ রাষ্ট্রের শক্তি নিহিত জ্ঞান, প্রযুক্তি এবং দক্ষ মানবসম্পদে। সিদ্ধান্তটি সরল—কিন্তু তার প্রভাব হবে ঐতিহাসিক।
রহমান মৃধা, গবেষক ও লেখক, সাবেক পরিচালক, ফাইজার, সুইডেন
মত দ্বিমত
দুর্নীতিমুক্ত সংসদ ছাড়া ন্যায়বিচার অসম্ভব
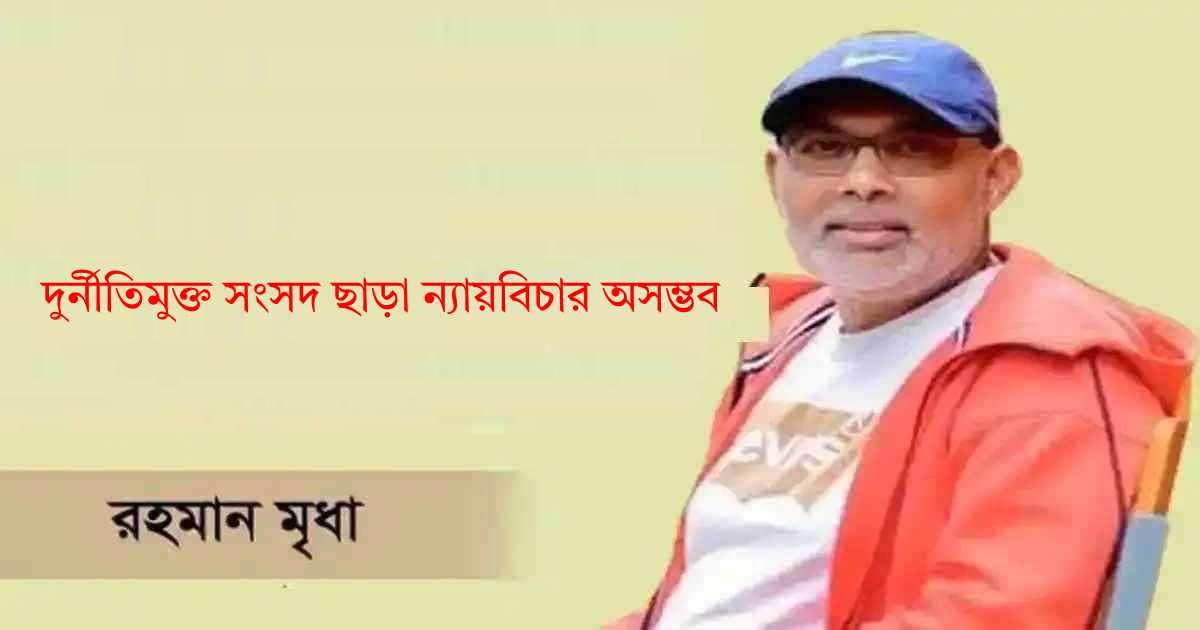
“যতদিন সংসদে দুর্নীতিমুক্ত ও ঋণখেলাপিমুক্ত সংসদ সদস্য না যাবে, ততদিন বাংলাদেশে সংবিধান থেকে জাতি ন্যায়বিচার পাবে না। কারণ, অপরাধী রাজনীতিবিদরা যখন আইন তৈরি করবে, তখন আপনি কখনই ন্যায়বিচার পাবেন না।”
এটি কেবল একটি বাক্য নয়, এটি রাষ্ট্রের ভেতরের অমীমাংসিত সংকটের সংক্ষিত সারাংশ। এখানে প্রশ্ন ব্যক্তির নয়, কাঠামোর। প্রশ্ন দলীয় নয়, নৈতিকতার।
সংবিধান বনাম বাস্তবতা
সংবিধান একটি জাতির সর্বোচ্চ নীতিপত্র, যেখানে ন্যায়, সমতা, মানবাধিকার ও জবাবদিহির অঙ্গীকার লেখা থাকে। কিন্তু সেই সংবিধান বাস্তবায়নের দায়িত্ব যাদের হাতে, তারাই যদি দুর্নীতি, ঋণখেলাপি, লুটপাট, ক্ষমতার অপব্যবহার, চাঁদাবাজি ও ভোট জালিয়াতির অভিযোগে অভিযুক্ত হন, তবে সংবিধানের ভাষা কাগজেই সীমাবদ্ধ থাকে। ন্যায়বিচার তখন নথিতে থাকে, বাস্তবে নয়।
বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে দীর্ঘদিন ধরে একটি বিপজ্জনক প্রবণতা তৈরি হয়েছে। নির্বাচনী প্রতিযোগিতা এখন নীতির লড়াই নয়, বরং প্রভাবের লড়াই হয়ে দাঁড়িয়েছে। ঋণখেলাপিরা ব্যাংকিং ব্যবস্থাকে দুর্বল করেছে, অথচ সাধারণ আমানতকারীরা অনিশ্চয়তায় ভুগেছে। বড় প্রকল্পে অনিয়ম আর জবাবদিহির অভাব সাধারণ মানুষের আস্থায় চিড় ধরিয়েছে। তরুণ প্রজন্মের মধ্যে এই ধারণা জন্মেছে যে—যোগ্যতা নয়, রাজনৈতিক সংযোগই সাফল্যের একমাত্র পথ। এই মানসিকতা রাষ্ট্রের জন্য এক গভীর বিপদের সংকেত।
সবচেয়ে উদ্বেগজনক বিষয় হলো ভোটের প্রতি আস্থার সংকট। যদি নাগরিক বিশ্বাস করতে না পারেন যে তাদের ভোটই প্রতিনিধিত্ব নির্ধারণ করে, তবে গণতন্ত্র কেবল আনুষ্ঠানিকতায় পরিণত হয়। গণতন্ত্রের প্রাণ হলো আস্থা। সেই আস্থা ক্ষয় হলে সংবিধানের প্রতিশ্রুতি দুর্বল হয়ে পড়ে।
এই বাস্তবতায় মূল প্রশ্নটি স্পষ্ট। আইন প্রণেতারা যদি নৈতিকভাবে প্রশ্নবিদ্ধ হন, তবে আইন কি ন্যায় প্রতিষ্ঠা করতে পারে? যখন অপরাধের অভিযোগে অভিযুক্ত বা আর্থিক অনিয়মে জড়িত ব্যক্তিরা আইন প্রণয়ন করেন, তখন আইনের প্রতি জনগণের শ্রদ্ধা কমে যায়। আইনের শাসন তখন ব্যক্তির শাসনে রূপ নিতে শুরু করে।
সমাধান কোনো ব্যক্তিবিশেষের বিরোধিতায় নয়, বরং কাঠামোগত শুদ্ধিতে। রাজনৈতিক দলগুলোর প্রার্থী মনোনয়নে নৈতিক মানদণ্ড কঠোর করা, ঋণখেলাপি ও দুর্নীতির অভিযোগে অভিযুক্তদের সংসদে প্রবেশ চিরতরে বন্ধ করা, নির্বাচনী প্রক্রিয়ার পূর্ণ স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা এবং বিচার বিভাগের স্বাধীনতাকে বাস্তব অর্থে শক্তিশালী করা জরুরি।
রাষ্ট্রকে বাঁচাতে হলে প্রথমে সংসদকে শুদ্ধ করতে হবে। কারণ সংসদই আইন তৈরি করে, আর আইনই রাষ্ট্রের চরিত্র নির্ধারণ করে। আইন যদি নৈতিকতার উপর দাঁড়ায়, রাষ্ট্র টিকে থাকে। আইন যদি স্বার্থের উপর দাঁড়ায়, রাষ্ট্র ভেঙে পড়ে।
অতএব এই বাক্যটি কেবল প্রতিবাদ নয়, একটি সতর্কবার্তা। ন্যায়বিচার কাগজে লেখা থাকে না, তা মানুষের হাতে গড়ে ওঠে। আর সেই হাত যদি কলুষিত হয়, তবে সংবিধানও ন্যায় দিতে পারে না।
প্রশ্নটি এড়ানো যায় না। রাষ্ট্রের জনগণ যেমন, তার নেতৃত্বও সাধারণত তেমনি হয়। বাংলাদেশের জন্য কি এই কথাটি প্রযোজ্য?
নেতৃত্ব আকাশ থেকে পড়ে না; তারা সমাজের ভেতর থেকেই উঠে আসে। সমাজ যদি দুর্নীতিকে সহনীয় মনে করে কিংবা ঋণখেলাপিকে কৌশলী ব্যবসায়ী হিসেবে বাহবা দেয়,ভোট জালিয়াতিকে রাজনৈতিক কৌশল হিসেবে মেনে নেয় এবং চাঁদাবাজিকে প্রভাবের অংশ মনে করে, তবে সেই মানসিকতার প্রতিফলনই একদিন সংসদে বসে। তখন আমরা কেবল নেতৃত্বকে দোষ দিই, কিন্তু আয়নায় নিজেদের দেখি না।
তবে এর অর্থ এই নয় যে জনগণই দায়ী বলেই রাষ্ট্র দায়ী। বরং পরিবর্তনের শক্তিও জনগণের হাতেই। সমাজ যদি নৈতিক মানদণ্ড উঁচু করে, ভোটাররা যদি প্রশ্ন করতে শেখেন এবং দলীয় অন্ধত্বের বদলে নৈতিকতার ভিত্তিতে প্রতিনিধি বাছেন, তবেই সংসদ বদলাবে। রাষ্ট্রকে বাঁচাতে হলে সংসদকে শুদ্ধ করতে হবে। কারণ সংসদই আইন তৈরি করে, আর আইনই রাষ্ট্রের চরিত্র নির্ধারণ করে।
বাংলাদেশের জন্য প্রশ্নটি তাই দ্বিমুখী। নেতৃত্ব কি জনগণের প্রতিচ্ছবি, নাকি জনগণকে এমন কাঠামোর মধ্যে রাখা হয়েছে যেখানে বিকল্পই সংকুচিত? যদি দ্বিতীয়টি সত্য হয়, তবে কাঠামো ভাঙতে হবে। যদি প্রথমটি আংশিক সত্য হয়, তবে মানসিকতা বদলাতে হবে।
অতএব, যতদিন সংসদে দুর্নীতিমুক্ত ও ঋণখেলাপিমুক্ত প্রতিনিধি না যাবে, ততদিন সংবিধানের প্রতিশ্রুতি পূর্ণ হবে না। পরিবর্তনের চাবিকাঠি কিন্তু সাধারণ মানুষের হাতেই।
পরিশেষে, আমরা কি কেবল অভিযোগ করে যাব, নাকি নিজেদের রাজনৈতিক নৈতিকতাকেও পুনর্গঠন করব?
এমএন/ রহমান মৃধা, গবেষক ও লেখক, প্রাক্তন পরিচালক, ফাইজার, সুইডেন
মত দ্বিমত
নাসিরউদ্দিন পাটোয়ারী: স্পষ্টভাষিতা বিতর্ক এবং নতুন রাজনীতির রূপরেখা
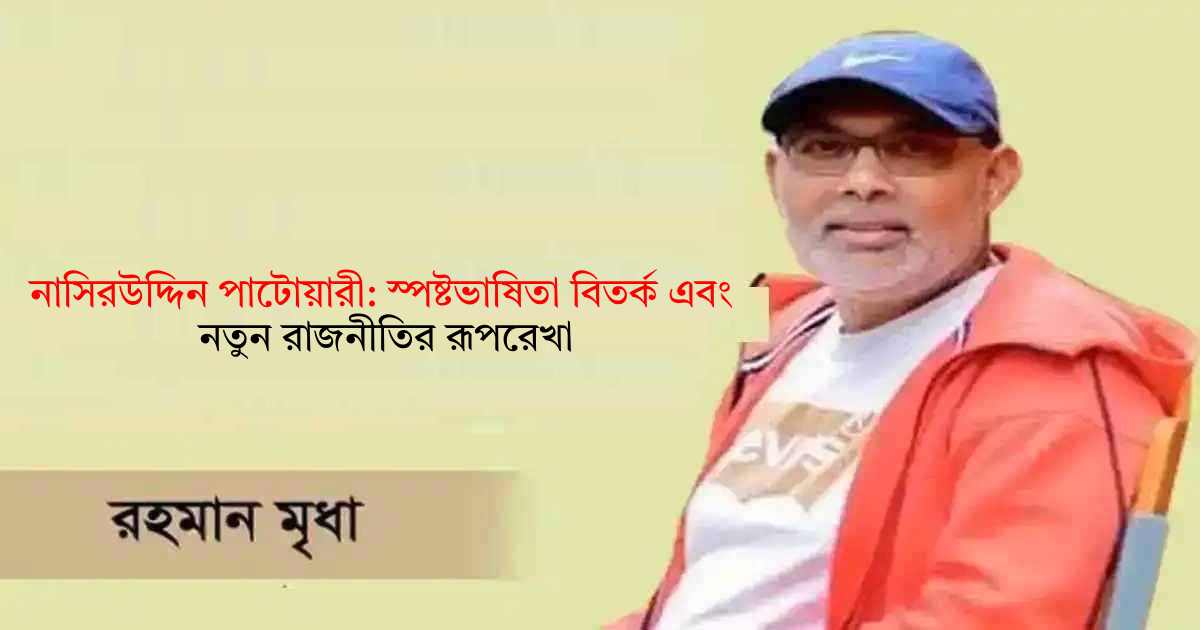
আমি দূর প্রবাসে থাকলেও তাকে আমি চিনি, যদিও কখনও চোখে দেখিনি। জুলাইয়ের গণঅভ্যুত্থানে আমার লেখালিখির সক্রিয় অংশগ্রহণের সময় আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত যারা ছিল তাদের মধ্যেই নাসিরউদ্দিন পাটোয়ারী আমার নজর আলাদাভাবে কেড়েছিল। তার অদম্য সাহস, দৃঢ় সংকল্প এবং মানুষের কল্যাণের প্রতি আন্তরিক দৃষ্টিভঙ্গি তখনই স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। সেই দিনের মুহূর্ত থেকে সে আমার চোখে শুধুই একজন রাজনৈতিক নেতা নয়; সে এক অনন্য চরিত্র, যার প্রভাব কেবল আমার ব্যক্তিগত উপলব্ধিতে সীমাবদ্ধ নয়, বরং দেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে সময়ের সঙ্গে প্রতিফলিত হয়েছে।
বাংলাদেশের রাজনীতিতে স্পষ্টভাষী নেতা বিরল। নাসিরউদ্দিন পাটোয়ারী সেই অদ্বিতীয় কণ্ঠ, যে সরাসরি দৃঢ় এবং প্রায়শই বিতর্কিত বক্তব্য দেয়। তার ভাষা সমালোচনার জন্ম দেয়, সমর্থনও জন্মায়। কিন্তু সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো, এটি বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতির ঘাটতি ও সম্ভাবনার উভয়ই প্রতিফলন। এই প্রতিবেদনে আমি বিশ্লেষণ করেছি সে কীভাবে রাজনৈতিক অঙ্গনে প্রভাব ফেলছে, নতুন প্রজন্ম তাকে কীভাবে দেখছে এবং তার নেতৃত্ব কীভাবে নতুন মানদণ্ড স্থাপন করতে পারে।
বাংলাদেশের সমসাময়িক রাজনৈতিক অঙ্গনে নাসিরউদ্দিন পাটোয়ারী একটি আলোচিত নাম। তাকে কেউ দেখে দুর্নীতিবিরোধী আপসহীন কণ্ঠ হিসেবে, কেউ দেখে বিতর্কপ্রবণ রাজনীতিক হিসেবে। কিন্তু তাকে ঘিরে যে আলোচনা, তা কেবল ব্যক্তিকে নিয়ে নয়। এটি বাংলাদেশের রাজনৈতিক ভাষা, সংস্কৃতি ও কাঠামোগত সীমাবদ্ধতার গভীর প্রশ্নকে সামনে আনে।
নাসিরউদ্দিন পাটোয়ারীর বিরুদ্ধে বিভিন্ন সময়ে অশ্লীলতার অভিযোগ উঠেছে। সমালোচকদের বক্তব্য, তার ভাষা প্রায়ই তীব্র। সমর্থকদের দাবি, সে কেবল অপ্রিয় সত্য উচ্চারণ করে। এখানে একটি মৌলিক প্রশ্ন সামনে আসে। কঠোর ভাষা ও অশ্লীলতার কি একই বিষয়? নাকি আমরা এমন এক রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে অভ্যস্ত, যেখানে তোষামোদ স্বাভাবিক এবং সরাসরি সমালোচনা অস্বস্তিকর?
বাংলাদেশের রাজনৈতিক বাস্তবতায় ব্যক্তিকেন্দ্রিক আনুগত্য প্রায়ই নীতিগত বিতর্ককে ছাপিয়ে যায়। ফলে শক্ত সমালোচনা সহজেই ব্যক্তিগত আক্রমণ হিসেবে ব্যাখ্যা পায়। এই প্রেক্ষাপটে পাটোয়ারীর ভাষা বিতর্ক সৃষ্টি করলেও তা রাজনৈতিক সংস্কৃতির অন্তর্নিহিত সংকটকেই উন্মোচন করে।
নতুন প্রজন্মের চাওয়া
নতুন প্রজন্মের এক অংশ তাঁর এই আপসহীনতাকে সততার প্রতীক মনে করলেও, অন্য অংশ তাঁর বক্তব্যের চেয়ে সুস্পষ্ট কর্মপরিকল্পনা ও ফলাফল দেখতে আগ্রহী। আজকের তরুণ সমাজ শুধু স্লোগান চায় না, তারা চায় রাষ্ট্র সংস্কারের বাস্তব রূপরেখা। এই প্রেক্ষাপটে পাটোয়ারীর সামনে বড় চ্যালেঞ্জ হলো তাঁর এই সাহসকে কৌশলী নীতিতে রূপান্তর করা।
পাটোয়ারীর স্পষ্টভাষিতা তার শক্তি, আবার ঝুঁকিও
ইতিবাচক দিক হলো, সে আলাদা রাজনৈতিক পরিচিতি গড়ে তুলেছে। দুর্নীতিবিরোধী অবস্থান তাকে দৃশ্যমান করেছে। তরুণদের একটি অংশ তার মধ্যে প্রতিবাদী নয়, সম্ভাব্য সংস্কারকের প্রতিচ্ছবি দেখে।
নেতিবাচক দিক হলো, যদি ভাষাই আলোচনার কেন্দ্রে থাকে তবে নীতিগত গভীরতা আড়ালে পড়তে পারে। জোটভিত্তিক রাজনীতিতে সমঝোতার প্রয়োজন থাকে। অতিরিক্ত তীব্রতা রাজনৈতিক সমীকরণকে কঠিন করে তুলতে পারে। আইনি ও প্রশাসনিক চাপের ঝুঁকিও থেকে যায়।
কাঠামোগত সংস্কারের প্রয়োজন
১: রাজনৈতিক আচরণবিধির স্পষ্ট সংজ্ঞা প্রয়োজন, যাতে কঠোর সমালোচনা ও ব্যক্তিগত অশালীনতার পার্থক্য নির্ধারিত হয়।
২: প্রমাণভিত্তিক বক্তব্যের সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠা জরুরি। অভিযোগের সঙ্গে দলিল যুক্ত হলে ভাষা নয়, তথ্য আলোচনার কেন্দ্রে আসে।
৩: স্বাধীন তথ্য যাচাই কাঠামো শক্তিশালী করা দরকার, যাতে গুজব ও বিকৃত বক্তব্য দ্রুত সংশোধিত হয়।
৪: নির্বাচিত প্রতিনিধিদের জন্য রাজনৈতিক যোগাযোগ ও নৈতিক ভাষা ব্যবহারের প্রশিক্ষণ প্রয়োজন।
৫: সমালোচনার পাশাপাশি লিখিত নীতিপত্র ও বাস্তবায়ন রূপরেখা প্রকাশ করতে হবে।
সংসদে নতুন মানদণ্ডের প্রত্যাশা
জাতীয় সংসদে নীতিগত আলোচনার যে ঘাটতি প্রায়ই দেখা যায়, সেখানে নাসিরউদ্দিন পাটোয়ারীর মতো নেতার উপস্থিতি তাৎপর্যপূর্ণ হতে পারে। তবে সংসদীয় রাজনীতিতে কার্যকর হতে হলে তিনটি বিষয় নিশ্চিত করা জরুরি:
- জবাবদিহিমূলক বিতর্কের সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠা।
- আইন প্রণয়নের পাশাপাশি বাস্তবায়ন কাঠামো নিয়ে সুস্পষ্ট আলোচনা।
- তরুণ প্রজন্মকে দেখানো যে রাজনীতি সৃজনশীল, নীতিনির্ভর এবং মানুষের কল্যাণমুখী হতে পারে।
তার বক্তব্যে যে বার্তাগুলো ধারাবাহিকভাবে উঠে আসে তা হলো তোষামোদ নয়, জবাবদিহি; আইন প্রয়োগই রাষ্ট্রের শক্তি; দুর্নীতির বিরুদ্ধে আপসহীনতা; নাগরিক সাহসের চর্চা। এই বার্তা যদি কেবল বক্তৃতায় সীমাবদ্ধ না থেকে প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোয় রূপ পায়, তবে তা রাজনৈতিক সংস্কৃতির পরিবর্তনে ভূমিকা রাখতে পারে।
নাসিরউদ্দিন পাটোয়ারীকে ঘিরে বিতর্ক আসলে বাংলাদেশের রাজনৈতিক পরিপক্বতার পরীক্ষা। সে একই সঙ্গে আশার প্রতীক, বিতর্কের কেন্দ্র এবং সম্ভাব্য সংস্কারক। তার সামনে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হলো সাহসকে কৌশলে রূপান্তর করা, ভাষাকে নীতিতে রূপান্তর করা এবং আবেগকে প্রাতিষ্ঠানিক পরিবর্তনে রূপান্তর করা।
আজ বাংলাদেশের রাজনীতি একটি সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে। জনগণ ক্লান্ত প্রতিশ্রুতির পুনরাবৃত্তিতে, ক্লান্ত তোষামোদে, ক্লান্ত গুজবনির্ভর চরিত্রহননে। তারা এমন রাজনীতি দেখতে চায় যেখানে যোগ্যতা সম্মান পায়, সৃজনশীলতা মূল্য পায় এবং জবাবদিহি বাধ্যতামূলক হয়।
বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে আমরা প্রায়ই দেখেছি যোগ্য নেতৃত্বের অভাবে রাজনীতি আমলাতন্ত্রের কাছে হার মেনেছে। যোগ্য, ত্যাগী ও দূরদর্শী নেতৃত্বের অভাব দেশের নীতিনির্ধারণকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। আসন্ন নির্বাচনের পর একটি শক্তিশালী বিরোধী দল এবং একটি ‘ছায়া মন্ত্রিসভা’ গঠন করা গেলে জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা সম্ভব হবে। নাসিরউদ্দিন পাটোয়ারীর সাম্প্রতিক নির্বাচনী প্রচারণায় যে দায়িত্বশীল রাজনৈতিক চর্চার আভাস মিলেছে, তা প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পাওয়া এখন সময়ের দাবি।
নাসিরউদ্দিন পাটোয়ারীকে ঘিরে বিতর্ক আসলে বাংলাদেশের রাজনৈতিক পরিপক্বতারই পরীক্ষা। তিনি কেবল একজন ব্যক্তি নন, বরং এক নতুন রাজনৈতিক মানদণ্ডের সম্ভাবনা। যদি তাঁর স্পষ্টভাষিতা ও সাহসের সাথে প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কারের সংমিশ্রণ ঘটে, তবে তা নতুন প্রজন্মের কাছে এই বার্তাই দেবে যে—রাজনীতি মানে ক্ষমতা নয়, বরং মানুষের কল্যাণে নিবেদিত একটি মহান দায়িত্ব।
লেখক: রহমান মৃধা
গবেষক ও লেখক, প্রাক্তন পরিচালক, ফাইজার, সুইডেন
মত দ্বিমত
গণতন্ত্র নিষ্ঠুর, কিন্তু অন্ধ নয়
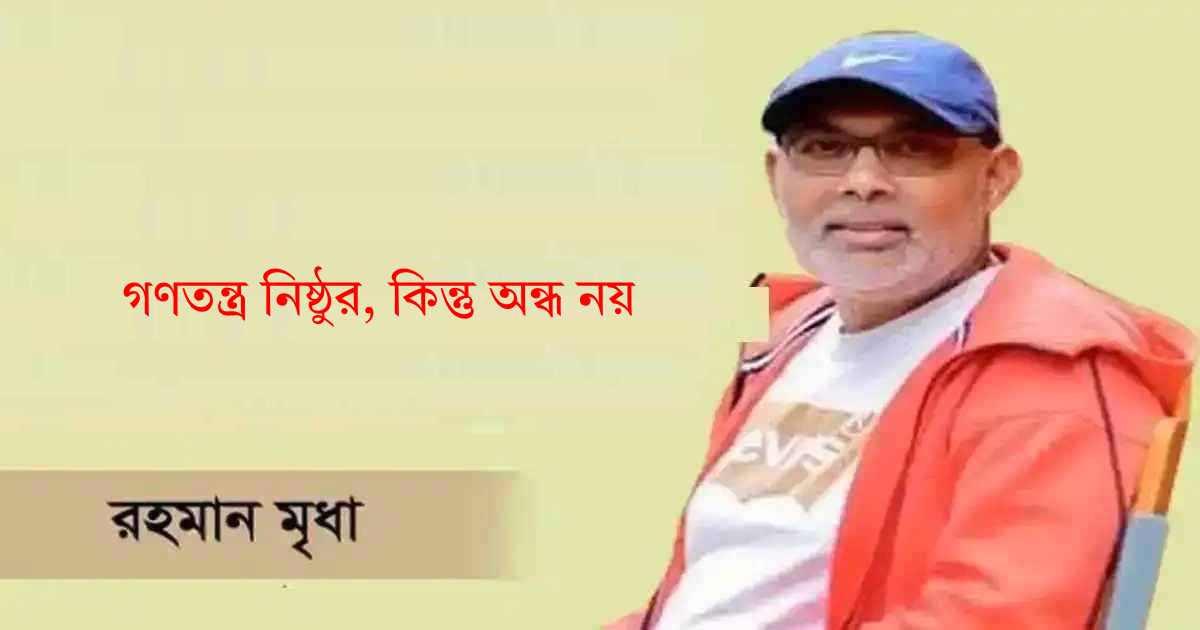
বাংলাদেশের ১৮ কোটি মানুষের যেন ১৮ কোটি মতামত, যা গণমাধ্যমে প্রতিনিয়ত উচ্চারিত হচ্ছে। তারপরও বাংলাদেশের নবনির্বাচিত ও মনোনীত প্রার্থীদের মধ্যে বিএনপির গণজোয়ার যেন একটি স্পষ্ট বার্তা দিচ্ছে, জনমতকে চিরদিন উপেক্ষা করা যায় না। এবার আর বলার সুযোগ নেই যে দিনের ভোট রাতে হয়েছে বা জনগণ নিজের ভোট নিজে দিতে পারেনি। অজুহাতের রাজনীতি থেকে বেরিয়ে এসে বাস্তবতাকে গ্রহণ করার সময় এখন, যার যার মুল্লুক তার শক্তি। তবে এই বাক্যটির আরেকটি গভীর পাঠ আছে। ক্ষমতা কখনো শূন্য থেকে জন্মায় না, এটি শেষ পর্যন্ত সমাজের ভেতর থেকেই উঠে আসে। একটি জাতি শেষ পর্যন্ত তার মনের মতো নেতৃত্বই খুঁজে পায়। যেমন জাতি তেমন নেতা, কারণ আম গাছের তলায় আমই পড়ে। তাই প্রশ্নটা শুধু কে ক্ষমতায় গেল তা নয়, আমরা কেমন সমাজ তৈরি করেছি, কেমন রাজনীতি সহ্য করেছি, আর কেমন নেতৃত্বকে নীরবে অনুমোদন দিয়েছি। নেতৃত্ব আসলে জাতিরই আয়না, সেখানে প্রতিফলিত হয় আমাদের সাহস, আমাদের ভয়, আমাদের নৈতিকতা এবং আমাদের সীমাবদ্ধতা।
প্রকৃতপক্ষে গণতন্ত্রের মতো নিষ্ঠুর আচরণ আর কোনো ব্যবস্থায় নেই। কারণ কি জানেন? ইতিহাস বারবার দেখিয়েছে, মাত্র একটি ভোটের ব্যবধানে কেউ হেরে গেছে, কেউ জিতে গেছে। সেই একটি ভোটই কখনো একটি দেশের ভবিষ্যৎ বদলে দিয়েছে, কখনো একটি প্রজন্মের স্বপ্নকে নতুন দিক দেখিয়েছে। অনেকেই তাই বলেন, এটিই গণতন্ত্রের সৌন্দর্য। কিন্তু এই সৌন্দর্যের ভেতরেই লুকিয়ে আছে কঠোর জবাবদিহি, নির্মম বাস্তবতা এবং জনগণের নীরব অথচ চূড়ান্ত ক্ষমতা।
আজ এই ক্ষণে আমার ছোটবেলার একটি গল্প খুব মনে পড়ছে। গ্রামে বিষাক্ত সর্প দংশনে একজন প্রতিবেশী মৃত্যুবরণ করেছিলেন। চারদিকে কান্নার রোল উঠেছিল। পাড়া প্রতিবেশীরা এসে সান্ত্বনা দিচ্ছিলেন, নানা জন নানা ভাবে স্মৃতিচারণ করছিলেন। হঠাৎ এক বয়স্ক মহিলা এসে লক্ষ করলেন, সাপে কামড় দিয়েছে চোখের একটু উপরে। গভীর দুঃখ প্রকাশ করে তাকে বলতে শুনেছিলাম, “ইশ, একটুর জন্য চোখটা বেঁচে গেছে।”
সেদিন প্রথম বুঝেছিলাম, মানুষ কখনো কখনো সবচেয়ে বড় ক্ষতির মাঝেও অদ্ভুত এক সান্ত্বনা খোঁজে। কিন্তু প্রশ্ন হলো, আমরা কি বারবার একইভাবে নিজেদের সান্ত্বনা দিয়ে যাব, নাকি সত্যের মুখোমুখি দাঁড়াব?
সদ্য বাংলাদেশের নির্বাচন শেষ হয়েছে। বিজয়ের ঘণ্টা বেজেছে, সেই সাথে পরাজয়েরও। তারপরও জল্পনা কল্পনা চলছে, চলবেই। কী করণীয় ছিল, কী করা উচিত ছিল না, এই আলোচনা গণতন্ত্রেরই অংশ। জয় পরাজয় থাকবেই, অতীতেও ছিল, ভবিষ্যতেও থাকবে। কিন্তু যে শিক্ষা সবচেয়ে জরুরি, সেটি হলো অজুহাত নয়, সমাধান খুঁজুন।
রাজনীতি কেন করবেন? উদ্দেশ্য কি? সেবা দেবেন, নাকি সেবা নেবেন? শাসন করবেন, নাকি শোষণ করবেন? স্বৈরাচারী হবেন, নাকি কর্মচারীর মতো জনগণের পাশে দাঁড়াবেন? একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করবেন, নাকি গণতন্ত্রকে শক্ত ভিত্তির ওপর দাঁড় করাবেন? দেশ গড়বেন, নাকি শুধু নিজেকে গড়বেন?
এই প্রশ্নগুলো শুধু রাজনীতিবিদদের জন্য নয়, একটি জাতির আত্মপরিচয়ের প্রশ্ন। কারণ রাজনীতি শেষ পর্যন্ত ক্ষমতার খেলা নয়, এটি আস্থার সম্পর্ক।
এ ধরনের চিন্তা ভাবনাকে ব্রেনস্টর্মিং করতে হবে। একটি টু ডু লিস্ট তৈরি করতে হবে। তারপর নিজেকেই প্রশ্ন করতে হবে, গো অর নট গো। কারণ নেতৃত্ব মানে শুধু সামনে দাঁড়ানো নয়, সঠিক সময়ে সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার সাহস।
ধরুন, আপনি মনেপ্রাণে বিশ্বাস করেন দুর্নীতিমুক্ত বাংলাদেশ গড়া সম্ভব। কীভাবে সম্ভব, সেটাও আপনি জানেন। কিন্তু আপনার কোনো ক্ষমতা নেই, জনগণ আপনার পাশে নেই, তাহলে? ইতিহাস বলে, পরিবর্তন কখনো ক্ষমতা দিয়ে শুরু হয় না, শুরু হয় বিশ্বাস দিয়ে। তারপর সেই বিশ্বাসই একসময় জনশক্তিতে রূপ নেয়।
আমি আজ একটি ক্ষেত্রেই দেশের অগ্রগতি নিঃসন্দেহে দৃশ্যমান, সেটি দুর্নীতি। কথাটি হতাশার শোনালেও এর ভেতরে লুকিয়ে আছে একটি সতর্কবার্তা। কারণ শক্তি নিজে কখনো ভালো বা মন্দ নয়, আমরা তাকে কোন পথে ব্যবহার করছি সেটিই আসল প্রশ্ন।
আলফ্রেড নোবেল ডিনামাইট আবিষ্কার করেছিলেন ধ্বংসের জন্য নয়। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল সুইডেনের দুর্গম পাহাড় কেটে রাস্তা নির্মাণ করা, নর্ডিক দেশগুলোর যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত করা এবং বহির্বিশ্বের সঙ্গে ব্যবসা বাণিজ্যের নতুন দুয়ার খুলে দেওয়া। সেই স্বপ্ন বাস্তব হয়েছিল, যার সুফল আজও চোখে পড়ে। কিন্তু সময়ের পরিক্রমায় একই ডিনামাইট যুদ্ধক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়ে লাখো মানুষের মৃত্যুর কারণ হয়েছে। যে শক্তি উন্নয়নের প্রতীক ছিল, সেটিই পরিণত হয়েছে ধ্বংসের অস্ত্রে।
প্রযুক্তির ক্ষেত্রেও আমরা যেন একই দ্বিধাবিভক্ত পথের সামনে দাঁড়িয়ে আছি। অভূতপূর্ব প্রযুক্তিগত অগ্রগতি সত্ত্বেও আমরা তাকে সুশাসনের হাতিয়ার হিসেবে গড়ে তুলতে পারিনি। অথচ চাইলে শতভাগ প্রযুক্তিনির্ভর প্রশাসন, নগদবিহীন লেনদেন, স্বচ্ছ নির্বাচন ব্যবস্থা এবং দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণ আজ আর কল্পনা নয়, বাস্তব সম্ভাবনা। প্রশ্ন একটাই, আমরা কি প্রযুক্তিকে অগ্রগতির সিঁড়ি বানাব, নাকি নিজেদের সীমাবদ্ধতার কারণে তাকে ধ্বংসের আরেকটি উপকরণে পরিণত করব?
জুলাই গণঅভ্যুত্থানে আমরা দেখেছি, কত ভালো মানুষের হাত পা কাটা গেল, কত তরুণ তরুণী জীবন দিল, দুর্নীতির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ালো। তাদের আত্মত্যাগ আমাদের একটি কঠিন প্রশ্নের সামনে দাঁড় করায়, আমরা কি সত্যিই ন্যায়বিচার চাই, নাকি শুধু ক্ষণিকের প্রতিশোধ? যারা দুর্নীতি করল বা এত মানুষকে হত্যা করল, সবাই জানে তারা কারা। তারপরও কি সেই দুর্নীতিবাজদের শাস্তি হিসেবে হুট করে হাত পা কাটা যাবে? না। কারণ আইনের ঊর্ধ্বে উঠে বিচার করা মানে আবারও অন্যায়কে জন্ম দেওয়া। এখানেই বিবেকের দ্বন্দ্ব।
এই দ্বন্দ্বের মোকাবিলা করা যেমন কঠিন, তেমনি কঠিন পরাজয়কে মেনে নেওয়া। পরাজয় মানুষকে ভেঙেও দেয়, আবার গড়েও তোলে। আমি বহু বছর ধরে খেলাধুলার জগতের সাথে জড়িত। আমার ছেলে মেয়েরা তাদের শৈশব, কৈশোর এবং যৌবনের একটি বড় সময় পার করছে জয় পরাজয়ের মধ্য দিয়ে। জয়ের উল্লাস যেমন মানুষকে আত্মবিশ্বাসী করে, তেমনি পরাজয়ের গ্লানি মানুষকে গভীরভাবে আত্মসমালোচনা করতে শেখায়। চলার পথে আমরা প্রতিনিয়ত এগিয়ে চলেছি। তারপরও আমরা থেমে নেই। কারণ সেই একই প্রশ্ন আমাদের সামনে থাকে, কী, কেন এবং কীভাবে।
স্বাভাবিকভাবেই জয়ের মধ্যে সময় কাটানোর উপলব্ধি আর পরাজয়ের মধ্যে সময় কাটানোর অনুভূতি এক নয়। তবুও মেনে নেওয়া শিখতে হবে। কারণ যে জাতি হার স্বীকার করতে জানে না, সে কখনো জয়ের মর্যাদাও বুঝতে পারে না।
আমাদের সুইডেনের একজন প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী প্রায় বলতেন, “jag låter min fru alltid vinna, på så sätt är det jag som bestämmer att hon vinner।” এর বাংলা অর্থ, “আমি সবসময় আমার স্ত্রীকে জিততে দিই, আর এভাবেই আমিই ঠিক করি যে সে জিতবে।” কথাটি রসিকতা মনে হলেও এর ভেতরে লুকিয়ে আছে এক গভীর সত্য, কখনো কখনো ছেড়ে দেওয়াও প্রজ্ঞার পরিচয়, আর সম্মান দিয়েই টেকসই সম্পর্ক তৈরি হয়।
গণতন্ত্রের মূল মন্ত্র হলো agree to disagree, অর্থাৎ দ্বিমত থাকা সত্ত্বেও সহাবস্থান করা। মতের ভিন্নতা কোনো দুর্বলতা নয়, বরং একটি পরিণত সমাজের শক্তি। দুর্ভাগ্যজনকভাবে এই চর্চাটির ভীষণ অভাব বাংলাদেশে। আমরা ভিন্ন মতকে প্রতিপক্ষ ভাবতে শিখেছি, সহযাত্রী হিসেবে দেখতে শিখিনি।
খুব ইচ্ছে জাগে, যদি আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় ন্যূনতম পরিবর্তন এনে মত ও দ্বিমত পোষণের প্রক্রিয়াটিকে শেখানো যেত। কারণ গণতন্ত্র কেবল ব্যালট বাক্সে জন্মায় না, এটি জন্মায় শ্রেণিকক্ষে, পরিবারে, আলোচনায়, এবং পারস্পরিক শ্রদ্ধার সংস্কৃতিতে।
শেষ পর্যন্ত একটি সত্য অস্বীকার করার উপায় নেই, গণতন্ত্র কোনো আরামদায়ক যাত্রা নয়। এটি প্রশ্ন করে, চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দেয়, কখনো আঘাত করে, আবার নতুন করে পথও দেখায়। তাই অজুহাত নয়, আত্মসমালোচনা দরকার। প্রতিশোধ নয়, ন্যায়বিচার দরকার। বিভাজন নয়, পরিণত সহাবস্থান দরকার।
কারণ একটি জাতির ভবিষ্যৎ নির্ধারিত হয় শুধু কে জিতল বা হারল তা দিয়ে নয়, বরং আমরা হার থেকে কী শিখলাম এবং জয়কে কতটা দায়িত্বে রূপান্তর করতে পারলাম তা দিয়ে। গণতন্ত্র নিষ্ঠুর হতে পারে, কিন্তু অন্ধ নয়। অন্ধ হলে আমরা।
রহমান মৃধা, গবেষক ও লেখক, প্রাক্তন পরিচালক, ফাইজার, সুইডেন
rahman.mridha@gmail.com


























