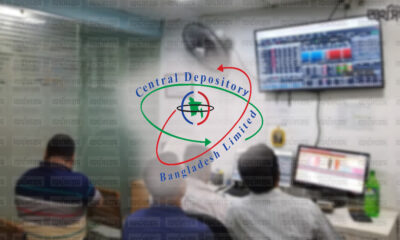মত দ্বিমত
বাংলাদেশ জন্মেছে জনগণের স্বপ্নে, কোনো পরিবারের জন্য নয়।
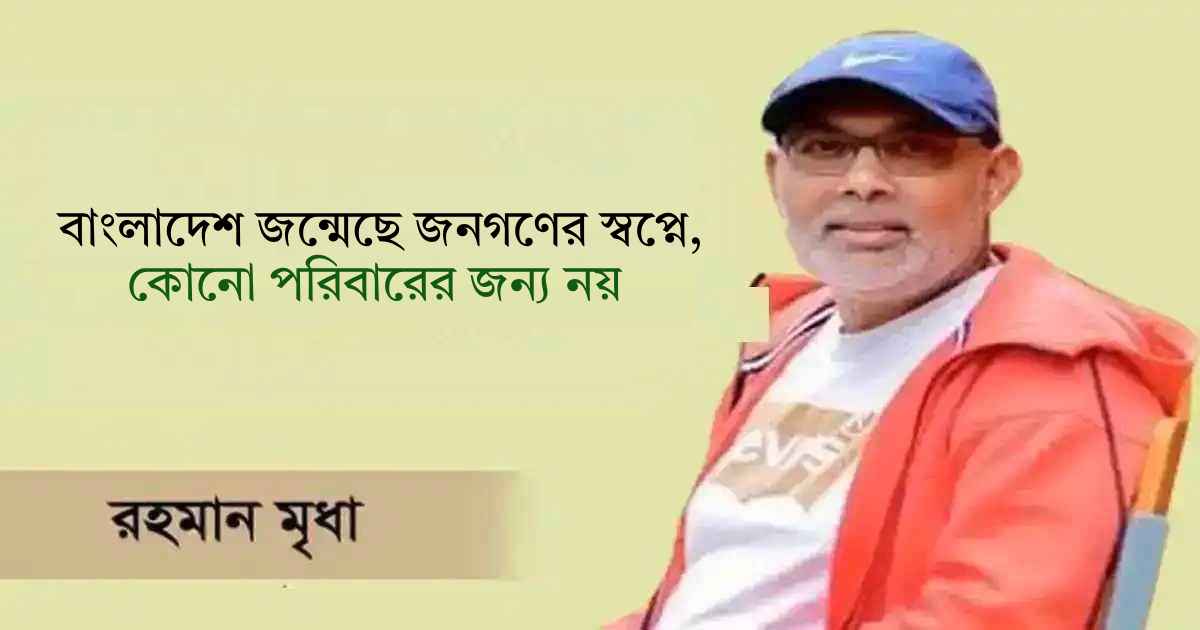
রাজতন্ত্রের পতনের পর সারা বিশ্বে গণতন্ত্র এসেছে মুক্তির আশায়। তবে ভারতীয় উপমহাদেশে গণতন্ত্রের স্বপ্ন বারবার পরিবারতন্ত্রের শিকলে ভেঙে গেছে। পাকিস্তানে ভুট্টো ও শরীফ পরিবার, ভারতে নেহরু–গান্ধী পরিবার, শ্রীলঙ্কায় বান্দারনায়েক ও রাজাপাকসে পরিবার—সব জায়গায় পরিবারতন্ত্র গণতন্ত্রকে দুর্বল করেছে। বাংলাদেশও এর ব্যতিক্রম নয়। শেখ মুজিবুর রহমান থেকে শেখ হাসিনা, এবং এখন জিয়া পরিবার থেকে তারেক রহমান—বারবার একই ভুলের পুনরাবৃত্তি।
বারবার বলা হচ্ছে—পরিবার নয়, জনগণই গণতন্ত্রের প্রকৃত ভিত্তি। অথচ আমরা সে পথে না গিয়ে বারবার পথভ্রষ্ট হচ্ছি। পরিবারতন্ত্র মানে হলো ক্ষমতা উত্তরাধিকার সূত্রে হস্তান্তর, যেখানে জনগণের ইচ্ছা নয়, বংশপরিচয় নেতৃত্ব নির্ধারণ করে। এর ক্ষতিকর প্রভাব স্পষ্ট: যোগ্যতার পরিবর্তে আনুগত্য রাজনীতিতে প্রাধান্য পায়, প্রতিষ্ঠানগুলো ভেঙে পড়ে, আইনশৃঙ্খলা দুর্বল হয়। দুর্নীতি ও দলীয়করণ সমাজে ছড়িয়ে পড়ে। জনগণ গণতন্ত্র থেকে বিমুখ হয়ে যায়। যখন রাজনীতি পরিবারকেন্দ্রিক হয়, তখন গণতন্ত্র রাজতন্ত্রের ছদ্মবেশে পরিণত হয়।
শেখ হাসিনা উন্নয়নের নামে কিছু প্রকল্প দেখালেও তাঁর শাসনের চিহ্ন হিসেবে দেখা যায় বিরোধী দমন, ভোটাধিকার হরণ, প্রশাসন ও বিচারব্যবস্থার দলীয়করণ এবং দুর্নীতি ও ভয়ের সংস্কৃতি। একজন বাবা হারা শেখ হাসিনা শেষ পর্যন্ত দেশ হারা হলেন—এটাই পরিবারতন্ত্রের নির্মম পরিণতি। তার পতন প্রমাণ করে, পরিবারতন্ত্র যতই শক্তিশালী মনে হোক, একদিন তা ধসে পড়বেই।
শেখ হাসিনার ব্যর্থতা কি বিএনপিকে নতুন দিশা দিয়েছে? দুঃখজনকভাবে না। বিএনপির ইতিহাসে জিয়া পরিবারকেন্দ্রিকতা বরাবরই প্রবল। খালেদা জিয়ার পর এখন তারেক রহমানকে ক্ষমতায় বসানোর চেষ্টা চলছে। তিনি জনগণের আস্থা বা রাজনৈতিক যোগ্যতায় নয়, বরং বংশপরিচয়ের কারণে এগিয়ে আসছেন। শেখ হাসিনাকে পরিবারতন্ত্রের দায়ে দেশ ছাড়তে হয়েছে, সমালোচনা চলছে, কিন্তু বিএনপি যদি একই ফাঁদে পা দেয়, তাদের বৈধতা কোথায় দাঁড়াবে—ভাবা দরকার।
বিশ্ব ইতিহাস সাক্ষী। পাকিস্তানে ভুট্টো পরিবার সামরিক অভ্যুত্থানে ছিন্নভিন্ন হয়েছে। শ্রীলঙ্কায় রাজাপাকসে পরিবার পতনের পর দেশ দেউলিয়া হয়েছে। ভারতে গান্ধী পরিবারের প্রভাব কমে আঞ্চলিক নেতৃত্ব শক্তিশালী হয়েছে। গবেষণাও বলছে, ডাইনাস্টিক রাজনীতি অর্থনৈতিক উন্নয়ন বাধাগ্রস্ত করে, দুর্নীতি বাড়ায়, জনগণের আস্থা কমায়। এক ব্যর্থতা থেকে যদি শিক্ষা না নেওয়া হয়, তবে সেই ব্যর্থতাই নতুন ব্যর্থতার জন্ম দেয়। বাংলাদেশ আজ সেই দুষ্টচক্রেই বন্দি।
বিএনপির অতীত শাসনকাল দেশের রাজনীতি ও প্রশাসনে মারাত্মক প্রভাব ফেলেছে। সরকারি তহবিল ও প্রকল্প বরাদ্দে অসদাচরণ এবং অনিয়ম বেড়েছে। বিরোধী দলের ওপর গুম, খুন এবং নিপীড়নের ঘটনা ঘটেছে। স্বাধীন সংবাদমাধ্যম দমন করা হয়েছে। পুলিশ ও সরকারি কর্মকর্তাদের দলীয় কাজে ব্যবহার হয়েছে। শেখ হাসিনার আমলে যে গুম-খুন ও গণতান্ত্রিক অধিকার হরণ ঘটেছে, এর মাত্রা আসলেই কমেছে কি না—সেটা বলা কঠিন।
শেখ হাসিনার পতনের পর গত ১৪ মাসে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের তথ্যবাঁধনের সুযোগে বিএনপি দেশের রাজনীতি ও প্রশাসনে শুধু চাঁদাবাজি ও ধান্দাবাজিই বৃদ্ধি করেনি, বরং জনগণের আস্থা ও ন্যায়বিচারের ভিত্তিক কাঠামোকে লক্ষ্য করে নানা ধরনের অপকর্ম চালিয়েছে। অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের শাসনামলেও সরকারি তহবিল ও প্রকল্প বরাদ্দে অসদাচরণ এবং অনিয়ম বেড়েছে। ব্যবসায়ী ও সাধারণ নাগরিকদের ওপর রাজনৈতিক চাপ, হয়রানি এবং ভয় পরিস্থিতি আরও জোরদার হয়েছে।
এই দুষ্টচক্র ভাঙার জন্য এখনই কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া জরুরি। দলীয় অভ্যন্তরীণ গণতন্ত্র নিশ্চিত করতে হবে—নেতৃত্ব নির্বাচন হোক ভোট ও মেধার ভিত্তিতে, বংশের নয়। মনোনয়ন প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা আনতে হবে—প্রার্থীর যোগ্যতা, আর্থিক অবস্থা ও অতীত প্রকাশ্যে ঘোষণা করা হোক। ক্যাম্পেইন অর্থায়ন সংস্কার করতে হবে—রাজনৈতিক তহবিলের উৎস প্রকাশ করা হোক। নেপোটিজম বিরোধী আইন কার্যকর করতে হবে—প্রশাসনে স্বজনপ্রীতির সুযোগ বন্ধ করতে হবে। স্বাধীন নির্বাচন কমিশন ও বিচারব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে। তরুণ নেতৃত্বের বিকাশ করতে হবে—পরিবার ছাড়া সমাজের নানা স্তর থেকে নতুন নেতৃত্ব গড়ে তুলতে হবে। গণমাধ্যম ও নাগরিক সমাজের স্বাধীনতা রক্ষা করতে হবে—তাহলেই নাগরিকদের কণ্ঠস্বর নিশ্চিহ্ন হবে না।
বাংলাদেশের জনগণের সামনে আজ মূল প্রশ্ন হলো, আমরা কি আবারও পরিবার বনাম পরিবার খেলায় বন্দি থাকব, নাকি জনগণকেন্দ্রিক রাজনীতি গড়ে তুলব? শেখ হাসিনা পরিবারতন্ত্রের কারণে দেশ হারালেন। বিএনপি যদি একই পথে হাঁটে, তার ফলাফলও ভিন্ন হবে না। এখন সময়—নতুন শিক্ষা নেওয়ার। পরিবার নয়, জনগণ; বংশ নয়, যোগ্যতা। অন্যথায় ইতিহাস বারবার আমাদের শিখিয়ে দেবে, কিন্তু আমরা বারবার একই ভুলে পতিত হব।
শেষে বলা যায়, একটি গণতান্ত্রিক জাতির স্থায়িত্ব নিশ্চিত করার জন্য কিছু ওয়ার্ল্ড ক্লাস নীতি অপরিহার্য: নেতৃত্ব নির্বাচন হোক যোগ্যতা, নৈতিকতা ও জনমতের ভিত্তিতে। শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান তৈরি করতে হবে, যাতে কোনো ব্যক্তি বা পরিবার রাজনীতি ও প্রশাসনে আধিপত্য বিস্তার করতে না পারে। স্বচ্ছ ও দায়িত্বশীল আর্থিক ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করতে হবে। গণমাধ্যম ও নাগরিক সমাজের স্বাধীনতা সর্বোচ্চ রক্ষা করতে হবে। যুব ও নতুন নেতৃত্বের বিকাশে বিনিয়োগ করতে হবে, যাতে পরবর্তী প্রজন্ম গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ ধরে রাখতে পারে।
মনে রাখতে হবে যে সত্যিকারের গৌরব আসে না স্লোগান বা বংশীয় ক্ষমতা থেকে। গৌরব আসে সততা, ন্যায়বিচার এবং জনগণের সেবার মধ্য দিয়ে। দুই দুর্নীতিগ্রস্ত শক্তির ছায়ায় জাতি বারবার ব্যর্থ হয়েছে। এই সত্য মেনে, নতুন পথ খুঁজে বের করাই আমাদের একমাত্র মুক্তি।
আজ সময় এসেছে—সৎ, সাহসী এবং দূরদর্শী নেতৃত্বের। যারা বংশ বা দলের নয়, দেশের মানুষকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেবে। আগামী প্রজন্মের অধিকার একটি মর্যাদাশালী বাংলাদেশ—গড়ে উঠবে নৈতিকতা, সততা ও উদ্যোগের ভিত্তিতে, রাজবংশীয় অহংকারে নয়। আসুন, অতীতের অন্ধকার ভেঙে নতুন নেতৃত্বের পথ খুলে দিই—যারা আমাদের জাতিকে আশা, মর্যাদা এবং অগ্রগতির দিকে এগিয়ে নেবে। কারণ দুটি অবিচ্ছিন্ন পরিবারতান্ত্রিক রাজনীতির জন্য আমরা বারবার রক্তক্ষরণ করতে জন্মায়নি—আমরা জন্মেছি স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়তে।
রহমান মৃধা, সাবেক পরিচালক, ফাইজার, সুইডেন। Rahman.Mridha@gmail.com
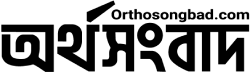
মত দ্বিমত
ভারত–লন্ডন নেতৃত্বের দ্বন্দ্ব ও জনগণের অনুপস্থিতি
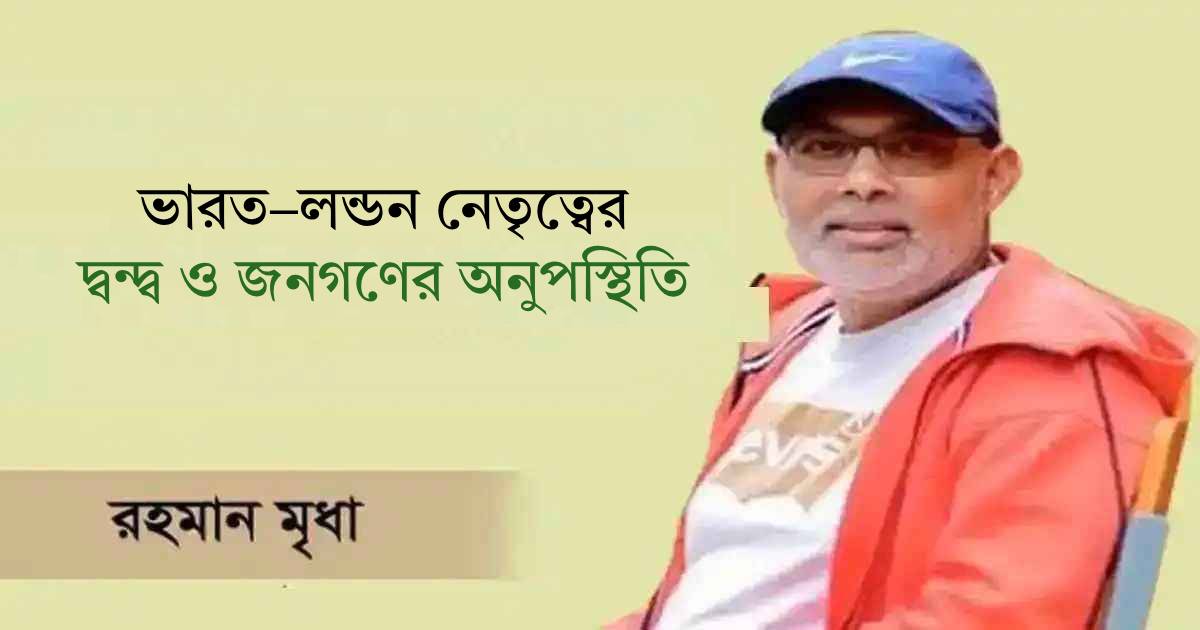
৫ আগস্ট ২০২৪—অনেকেই এই দিনটিকে ভেবেছিলেন বাংলাদেশের রাজনৈতিক সঙ্কট থেকে উত্তরণের দিন হিসেবে। প্রত্যাশা ছিল, এই দিনে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার দায়িত্ব নিয়ে শাসনতন্ত্রের স্থিতিশীলতা ফিরিয়ে আনবে। কিন্তু বাস্তবে হলো উল্টো। দেশ স্বাধীন হলো না, বরং রাষ্ট্রকে দুই টুকরো করা হলো। শেখ হাসিনাকে ক্ষমতা থেকে সরানো হলো বটে, কিন্তু তাঁকে ভারত পাঠানো হলো। ফলাফল? একদিকে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার, অন্যদিকে শেখ হাসিনা—ভারত থেকে এখনো তাঁর দল ও সমর্থকদের নিয়ন্ত্রণ করছেন।
এই সিদ্ধান্ত ছিল ভয়াবহ ভুল। তাঁকে সরানো হলো, কিন্তু সমাধান করা হলো না। দল ও প্রশাসনের অনেকেই এখনো তাঁকেই নেত্রী মনে করছে, তাঁকেই অনুসরণ করছে। ফলে দেশের শাসনতন্ত্র কার্যত বিভক্ত হয়ে গেছে—অর্ধেক চলছে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের নির্দেশনায়, অর্ধেক চলছে শেখ হাসিনার প্রভাবমুক্ত নয় এমন প্রশাসনের অধীনে। এই দ্বৈত নেতৃত্ব রাষ্ট্রযন্ত্রকে অচল করে দিয়েছে।
আরেকদিকে বিএনপির নেতৃত্ব দিচ্ছেন লন্ডন থেকে তারেক রহমান। ভারত থেকে শেখ হাসিনা, লন্ডন থেকে তারেক রহমান—“ডিজিটাল বাংলাদেশ” যেন দুই প্রবাসী কেন্দ্র থেকে চালিত হচ্ছে। অথচ দেশের ভেতরে কার্যকর নেতৃত্ব নেই। বাইরে থেকে নির্দেশনা আসছে, কিন্তু ভেতরে সমস্যার সমাধান করার মতো উপস্থিত নেতৃত্ব নেই। এই কারণেই বলা যায়—দেশের বারোটা বেজে গেছে।
জনগণ কে?
আমরা সবসময় বলি—জনগণ এটা চায় না, জনগণ এটা মেনে নেবে না। কিন্তু প্রশ্ন হলো—জনগণ কে?
•বিএনপি কি জনগণের দল নয়?
•জামায়াত, আওয়ামী লীগ বা অন্য সব দল কি জনগণের অংশ নয়?
•তাহলে দলগুলো বাদ দিয়ে আর কে আছে, যে বুকে হাত দিয়ে বলতে পারবে—“আমি জনগণ”?
বাস্তবে সত্যিকারের জনগণের ভূমিকায় যারা আছে, তাদের সংখ্যা খুবই কম। তারা আছে, কিন্তু বিচ্ছিন্ন, সংগঠিত নয়। ফলাফল হলো—জনগণের নাম ব্যবহার করা হচ্ছে, কিন্তু জনগণের জন্য কাজ করা হচ্ছে না। অতীতে হয়নি, ভবিষ্যতেও হবে না—যদি না আমরা ডেসপারেটলি চেষ্টা করি।
দুর্নীতি, অনীতি ও বিভক্ত প্রশাসন
আজ দেশের বৃহত্তম রাজনৈতিক দল দুর্নীতি, অনীতি, লুটপাট, চাঁদাবাজিতে নিমগ্ন। প্রশাসন বিভক্ত—কেউ অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের পক্ষে, কেউ শেখ হাসিনার প্রতি অনুগত। এক্ষেত্রে “হাড়ি ভেঙে দই পড়েছে, বিড়ালের হইছে বাহার”—এই প্রবাদটাই সঠিক। সবাই নিজের সুবিধা নেওয়ার প্রতিযোগিতায় নেমেছে, কিন্তু সাধারণ মানুষের ভাগ্যে কিছুই জোটেনি।
ভুলটা কোথায় হলো?
•শেখ হাসিনাকে ক্ষমতা থেকে সরানো হলো, কিন্তু রাজনৈতিকভাবে সমাধান করা হলো না।
•তাঁকে ভারত পাঠানো মানে তাঁর প্রভাবকে সরানো নয়—বরং বাইরে বসে তাঁকে আরও রহস্যময় ও শক্তিশালী করা হলো।
•তারেক রহমানও একইভাবে লন্ডন থেকে দল পরিচালনা করছেন—যা দেশের ভেতরে নেতৃত্বশূন্যতার জন্ম দিয়েছে।
•দুই প্রবাসী নেতা ডিজিটালি দল চালাচ্ছেন, আর দেশে সাধারণ মানুষ পড়েছে নেতৃত্বশূন্য ও বিশৃঙ্খল পরিস্থিতিতে।
দেশকে জনগণের করতে কী চেষ্টা দরকার?
১. জনগণের সক্রিয় উপস্থিতি তৈরি করা: দল নয়, নাগরিক প্ল্যাটফর্মকে শক্তিশালী করতে হবে। স্থানীয় পর্যায়ে টাউন-হল, নাগরিক কমিটি, নিরপেক্ষ জনমত সংগ্রহ শুরু করতে হবে।
২. দুর্নীতির বিরুদ্ধে দৃশ্যমান পদক্ষেপ: দুর্নীতি, লুটপাট ও ক্ষমতার অপব্যবহারের ঘটনা নথিভুক্ত ও প্রকাশ করতে হবে। ন্যায়বিচারের জন্য আইনি ও সামাজিক চাপ তৈরি করতে হবে।
৩. ছোট সেবা দিয়ে আস্থা ফেরানো: পানি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য—এই খাতে স্থানীয় উদ্যোগ দেখাতে হবে। এতে জনগণ বুঝবে—কেউ তাদের জন্য কাজ করছে।
৪. স্বচ্ছ নেতৃত্ব ও জবাবদিহি: জনগণের নামে রাজনীতি নয়, জনগণের কাজে রাজনীতি। স্বচ্ছতা ছাড়া আস্থা আসবে না।
৫. বহির্বর্তী প্রভাব থেকে বের হওয়া: ভারত ও লন্ডন থেকে ভার্চুয়াল নেতৃত্বের পরিবর্তে স্থানীয়, জনগণকেন্দ্রিক নেতৃত্ব তৈরি করতে হবে। দেশের ভিতরে সমাধান তৈরি করতে হবে, বাইরে নয়।
আজকের বাংলাদেশে ত্রৈমুখী নেতৃত্ব, বিভক্ত প্রশাসন, দুর্নীতিগ্রস্ত দল এবং “জনগণ” নামের এক অদৃশ্য সত্তা—সব মিলিয়ে রাষ্ট্র অচলাবস্থায়। শেখ হাসিনা ভারতে বসে প্রভাব চালাচ্ছেন, তারেক রহমান লন্ডন থেকে নির্দেশ দিচ্ছেন, আর দেশে আন্দোলন করছে ছোট দলগুলো। ফলে রাষ্ট্রযন্ত্র এক ভয়ঙ্কর অস্থিরতায় আছড়ে পড়েছে। যে দেশে সবাই কোনো না কোনো দলের সমর্থক, যে দেশে কেউ ভুল স্বীকার করে না, অন্যায়ের পর অনুশোচনা নেই, শুধু জনগণের নামে দায় চাপানো হয়—সেই দেশ কিভাবে জনগণের হতে পারে?
পরিবর্তন একদিনে হবে না। তবে ছোট ছোট নাগরিক উদ্যোগ, স্থানীয় স্বচ্ছ নেতৃত্ব, দুর্নীতির বিরুদ্ধে দাঁড়ানো এবং জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণ ছাড়া কোনো পথ নেই। যদি আমরা চেষ্টা না করি, তাহলে জনগণ সবসময় কেবল শ্লোগানেই থেকে যাবে—কাজে নয়।
অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের মূল দায়িত্ব ও অঙ্গীকার ছিল নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে রাজনৈতিক সঙ্কট সমাধান করা, শাসনতন্ত্রে জনগণের আস্থা ফিরিয়ে আনা এবং অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন আয়োজন করা। কিন্তু বাস্তবে সেই প্রতিশ্রুতি পূরণ হয়নি। জবাবদিহিতার অভাব, সিদ্ধান্তহীনতা এবং ক্ষমতার ভারসাম্যহীনতা পরিস্থিতিকে আরও জটিল করে তুলেছে। শেখ হাসিনার মনোনীত প্রেসিডেন্ট আজও অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের শীর্ষ অবস্থানে রয়েছেন—ফলে সরকারের বৈধতা ও নিরপেক্ষতা প্রশ্নবিদ্ধ হয়েছে। এ অবস্থায় সশস্ত্র বাহিনীর দায়িত্ব ছিল রাষ্ট্রকে রক্ষা করা, আইন-শৃঙ্খলা বজায় রাখা এবং নিরপেক্ষতা নিশ্চিত করা; কিন্তু তারা যদি সত্যিকারের নিয়ন্ত্রণ ও নিরপেক্ষতা প্রতিষ্ঠা করতে না পারে, তাহলে রাষ্ট্রব্যবস্থা ভেঙে পড়ার ঝুঁকি থেকেই যায়।
এই প্রেক্ষাপটে ড. মুহাম্মদ ইউনূসের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল। তিনি অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান হিসেবে সঙ্কট সমাধানের কার্যকর নেতৃত্ব নিতে পারতেন, কিন্তু তাঁর পদক্ষেপ সীমিত থাকায় প্রত্যাশিত পরিবর্তন ঘটেনি। তাই এখন জরুরি একটি ন্যায্য রূপান্তর—যেখানে রাজনৈতিক দলগুলো টিকে থাকবে, কিন্তু তাদের ভেতরে থাকা দুর্নীতি, লুটপাট, মানবাধিকার লঙ্ঘন বা অন্য অপরাধে দণ্ডিত নেতৃত্বকে কঠোরভাবে বাদ দিতে হবে। দল হচ্ছে জনগণের সংগঠিত অভিব্যক্তি; তাদের সম্পূর্ণ অস্বীকার করা গণতন্ত্রকেই অস্বীকার করা।
অতএব, প্রয়োজন এমন একটি অন্তর্বর্তীকালীন সরকার, যেখানে থাকবে সৎ ও যোগ্য নেতৃত্ব, নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিত্ব, নিরপেক্ষ প্রশাসন, বিশেষজ্ঞ পেশাজীবী এবং তরুণ প্রজন্মের সক্রিয় অংশগ্রহণ। এই সরকারকে কঠোর জবাবদিহিতার আওতায় থাকতে হবে, যেন প্রতিটি সিদ্ধান্ত স্বচ্ছ, যাচাইযোগ্য এবং জনগণের কাছে ব্যাখ্যা-সাপেক্ষ হয়। কেবল এভাবেই দলীয় অস্তিত্ব রক্ষা করে অপরাধী নেতৃত্বকে ছাঁটাই করা সম্ভব, এবং গড়ে তোলা সম্ভব একটি নতুন শাসনব্যবস্থার ভিত্তি—যেখানে জনগণের আস্থা ফিরবে, রাষ্ট্রে স্থিতিশীলতা আসবে এবং ভবিষ্যতের নির্বাচন হবে সত্যিকারের গণতান্ত্রিক। এর পরেই জাতীয় নির্বাচনের মাধ্যমে জনগণকে তাদের প্রকৃত সিদ্ধান্তের অধিকার ফিরিয়ে দেওয়া ছাড়া দেশের ভবিষ্যৎ নিরাপদ নয়।
রহমান মৃধা, সাবেক পরিচালক, ফাইজার, সুইডেন। Rahman.Mridha@gmail.com
মত দ্বিমত
যেখানে প্রতিভা নষ্ট হয়, সেখানে জাতি হারে
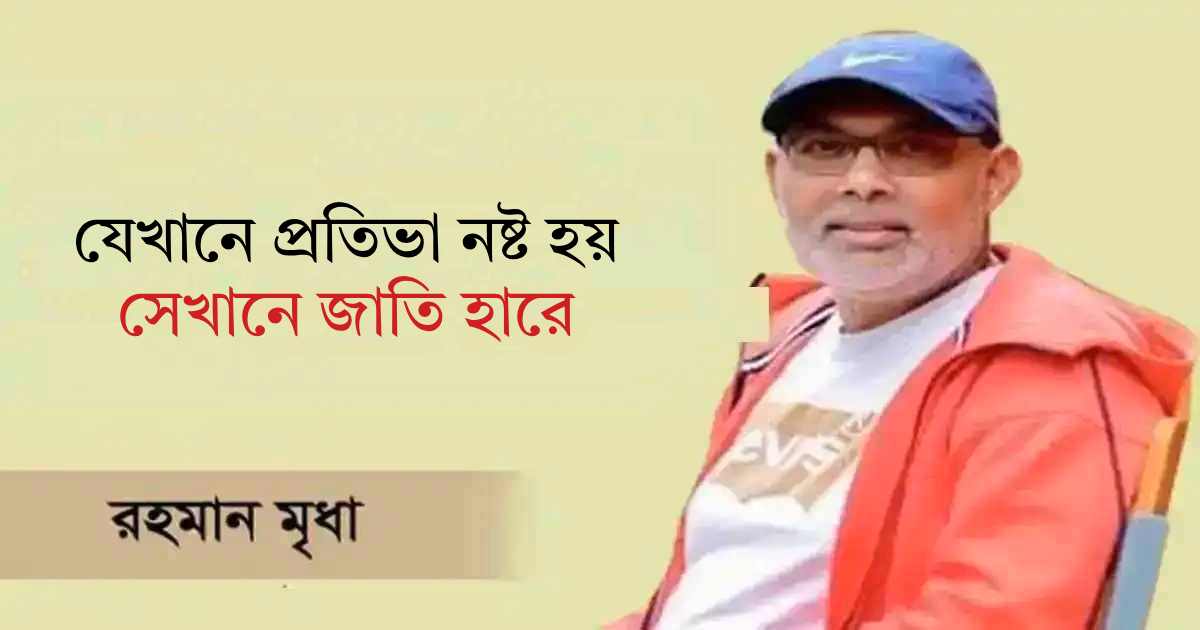
আমি ফেসবুকের তর্ক-বিতর্কে সচরাচর অংশ নিই না, তবে নানা পোস্ট চোখে পড়ে। কিছু পড়ি, কিছু মনে দাগ কেটে যায়, আবার কিছু নিজের পেজে রেখে দিই শিক্ষণীয় বিষয় বা চিন্তার খোরাক হিসেবে। সম্প্রতি এমনই একটি পোস্ট আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে:
“আমার বাবা বলতেন, ভাতে গরীব হলে সমস্যা নেই। কিন্তু জাতে গরীব হলে সমস্যা। জাতে গরীব মানুষগুলো ভয়ঙ্কর হয়।
বাবা আরও বলেছেন, ফকিরকে ভিক্ষা দেওয়ার সময় তোমাকেও ফকিরের সমান দাঁড়াতে হবে। এদের ক্ষেত্রে মানবতা দেখালে, ফকির তোমাকে বন্ধু ভেবে বসবে এবং সুযোগ বুঝে তোমাকেই ধ্বংস করবে।”
এই লেখার শেষে আরও বলা হয়েছে:
“চব্বিশের পাঁচ আগস্ট বাঙালি জাতি নতুন শিক্ষা পেয়েছে। যে সাকিব আল হাসানের জুতা টানার যোগ্য নয়, সে যদি দখলকৃত ক্ষমতার অধিকারী হয়, তবে সে সাকিবকে দমিয়ে রাখতে চাইবে। এ ধরনের জাতের ফকিরদের স্থান ইতিহাসের ডাস্টবিন।”
এটা পড়ে মনে হলো—এটা আসলে গভীর কোনো বিশ্লেষণ নয়, বরং তীব্র রাগের বহিঃপ্রকাশ।
সাকিব ও আসিফ : দুই ভিন্ন প্রতীক
সাম্প্রতিক সময়ে দেখছি, সাকিব আল হাসান এবং আসিফ মাহমুদ ভুঁইয়াকে ঘিরে উত্তেজনা তুঙ্গে। এদের নিয়ে যেমন নিজেরা পরস্পরের সাথে ঠেলাঠেলি করছে, তার চেয়েও বেশি করছে গণমাধ্যম ও সামাজিক মাধ্যম।
সাকিব এবং আসিফ—দুজনেই সাধারণ পরিবার থেকে উঠে আসা মানুষ। একজন খেলাধুলার জগতে অসাধারণ মেধা ও পরিশ্রমে পৌঁছেছেন শিখরে; অন্যজন বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস থেকে নেতৃত্ব দিয়েছেন মুক্তির আন্দোলনে, নিজের জীবন ঝুঁকিতে ফেলে গোটা জাতির ভাগ্য পরিবর্তনের সংগ্রামে নেমেছেন।
আমরা ভুলে যাই—একজন ক্রিকেটার একদিনে তৈরি হয় না। সাকিবের সাধনা, দক্ষতা, পারফরম্যান্স তাকে কোটি মানুষের হৃদয়ে পৌঁছে দিয়েছে। আবার ভুলে যাই—আসিফ মাহমুদের মতো তরুণরা প্রশাসনের ব্যর্থতার জায়গায় দাঁড়িয়ে জাতিকে স্বৈরাচারী দাসত্ব থেকে মুক্ত করেছে। এ কাজ তুচ্ছ নয়, বরং ঐতিহাসিক।
জাতির সংস্কৃতি ও অবক্ষয়
বাংলাদেশের সংস্কৃতিতে একটি দুঃখজনক প্রবণতা আছে:
কাউকে অপছন্দ হলেই গালিগালাজ, কুরুচিপূর্ণ পোস্ট আর অবমাননাই হয়ে ওঠে প্রতিক্রিয়ার ভাষা। সমালোচনা থাকে, কিন্তু তা হয় না সৃজনশীল। ফলে ব্যক্তি নয়, জাতির সম্পদই ক্ষতিগ্রস্ত হয়।
সাকিবকে রাজনীতির খেলায় টেনে আনা হলো—এটা কেন হলো, কার দায় ছিল, তার উত্তর সময়ই দেবে। কিন্তু একজন জাতীয় সম্পদকে এভাবে ব্যবহৃত হতে দেখা বেদনাদায়ক। একইভাবে আসিফ মাহমুদদের মতো ত্যাগী তরুণদের অবমূল্যায়ন মানে জাতির আত্মত্যাগকে অস্বীকার করা।
পাকা আমের রূপক
একটি আম যখন ধীরে ধীরে পাকে, তখন সেটি জাতিকে পুষ্টি দিতে পারে। কিন্তু যদি তার সঠিক ব্যবহার না হয়, তবে সেটি পচে যায়, নষ্ট হয়, পোকামাকড় খেয়ে ফেলে।
আমরা জাতি হিসেবে সেই পাকা আমগুলোকেই কাজে লাগাতে পারছি না। প্রতিভা, মেধা ও সাহস—সবই আছে আমাদের। কিন্তু সঠিক ব্যবহারের অভাবে সেগুলো নষ্ট হচ্ছে আমাদের চোখের সামনেই।
ড. ইউনূস একজন বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব এবং মুরব্বি, ভেবেছিলাম তিনি পারবেন পাকা আমগুলোকে কাজে লাগাতে। যখন তিনি বলেছিলেন—“একটি পচা বাংলাদেশকে আমরা নতুন করে গড়ে তুলব”—আমি মুরব্বির কথা বিশ্বাস করেছিলাম। বিশ্বাসে মিলায় বস্তু, তর্কে বহুদুর!
রহমান মৃধা
গবেষক ও লেখক
সাবেক পরিচালক, ফাইজার, সুইডেন
Rahman.Mridha@gmail.com
মত দ্বিমত
দীর্ঘমেয়াদি অর্থায়নের সংকটে দেশ: বন্ড মার্কেট বিকাশের প্রয়োজনীয়তা ও দিকনির্দেশনা

বাংলাদেশের অর্থনীতি গত দুই দশকে ধারাবাহিক প্রবৃদ্ধি অর্জন করেছে। তবে আর্থিক কাঠামো এখনো ব্যাংক-নির্ভর, যেখানে কর্পোরেট বন্ড মার্কেট কার্যত অনুপস্থিত। দীর্ঘমেয়াদি অর্থায়নের জন্য শক্তিশালী বন্ড বাজার অপরিহার্য হলেও বাংলাদেশের বিকাশ নানা কারণে বাধাগ্রস্ত। এই প্রেক্ষাপটে বন্ড মার্কেটের গুরুত্ব, বাংলাদেশের বর্তমান অবস্থা, প্রধান প্রতিবন্ধকতা, সাম্প্রতিক নীতি উদ্যোগ ও আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতা বিশ্লেষণ এবং করণীয় নীতিগত সংস্কার ও ভবিষ্যৎ দিক নির্দেশনার বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে।
বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ার দ্রুততম বিকাশমান অর্থনীতির একটি। ধারাবাহিক প্রবৃদ্ধি, রপ্তানি বৃদ্ধি, প্রবাসী আয় এবং অবকাঠামো উন্নয়নের মাধ্যমে দেশ ইতিমধ্যে একটি মধ্যম আয়ের অর্থনীতিতে পরিণত হয়েছে। তবে দেশের আর্থিক কাঠামোতে বড় একটি দুর্বলতা রয়ে গেছে-একটি কার্যকর ও শক্তিশালী বন্ড মার্কেটের অনুপস্থিতি।
যেখানে যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপ, জাপান, চীন কিংবা ভারত তাদের প্রবৃদ্ধি টিকিয়ে রাখতে বন্ড মার্কেটকে অর্থনৈতিক কাঠামোর অন্যতম মূল স্তম্ভে রূপান্তর করেছে, সেখানে বাংলাদেশ প্রায় সম্পূর্ণভাবে ব্যাংক ঋণের উপর নির্ভরশীল। এর ফলে –
•ব্যাংকিং খাতের উপর অতিরিক্ত চাপ তৈরি হচ্ছে,
•দীর্ঘমেয়াদি অর্থায়ন সীমিত হয়ে যাচ্ছে,
•আর্থিক খাতে বৈচিত্র্যের অভাব দেখা দিচ্ছে।
বন্ড মার্কেটকে সাধারণত দীর্ঘমেয়াদি অর্থায়নের সবচেয়ে কার্যকর উৎস হিসেবে বিবেচনা করা হয়। আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতা বলছে-
•যুক্তরাষ্ট্র: বিশ্বের বৃহত্তম বন্ড মার্কেট, প্রায় ৫০ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলার আকারের (SIFMA, ২০২৩)।
•ভারত: কর্পোরেট বন্ড বাজার GDP-র ১৭% (RBI, ২০২২); গত দশকে বাজার প্রায় তিনগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে।
•মালয়েশিয়া: ইসলামিক সুকুক বাজারে বিশ্বসেরা; দেশটির মোট বন্ড মার্কেটের ৬০% সুকুকভিত্তিক।
•ভিয়েতনাম: সাম্প্রতিক কর প্রণোদনা ও নিয়ন্ত্রক সংস্কারের ফলে কর্পোরেট বন্ড বাজার জিডিপির ১৫% এ উন্নীত হয়েছে।
অন্যদিকে, বাংলাদেশে কর্পোরেট বন্ড বাজার জিডিপির ১% এরও কম (বিএসইসি, ২০২৪) । এই ব্যবধান দেশের আর্থিক কাঠামোর দুর্বলতাকে স্পষ্টভাবে প্রকাশ করে।
বাংলাদেশের বন্ড মার্কেটের বর্তমান প্রেক্ষাপট
বাংলাদেশের বন্ড মার্কেটকে মূলত দুটি অংশে ভাগ করা যায়-সরকারি বন্ড বাজার এবং কর্পোরেট বন্ড বাজার। দেশের দীর্ঘমেয়াদি অর্থায়নের ক্ষেত্রে এই দুটি বাজার গুরুত্বপূর্ণ হলেও বাস্তবে উভয় ক্ষেত্রেই সীমিত কার্যক্রম এবং নানা প্রতিবন্ধকতা দেখা দেয়।
সরকারি বন্ড বাজার
সরকারি বন্ড বাজার বাংলাদেশের আর্থিক খাতের সবচেয়ে স্থিতিশীল অংশ। বাংলাদেশ ব্যাংক বাজেট ঘাটতি পূরণ এবং অর্থনীতিতে স্থিতিশীলতা বজায় রাখার জন্য নিয়মিতভাবে ট্রেজারি বিল (T-Bill) এবং ট্রেজারি বন্ড (T-Bond) ইস্যু করে।
•T-Bill সাধারণত ৩, ৬ এবং ১২ মাসের জন্য ইস্যু হয়, আর T-Bond দীর্ঘমেয়াদি (২ থেকে ২০ বছর) প্রকল্প অর্থায়নের জন্য ব্যবহৃত হয়।
•সরকারি বন্ড প্রধানত ব্যাংক, বীমা কোম্পানি, পেনশন ফান্ড এবং অন্যান্য প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারীরা ক্রয় করে থাকে।
•যদিও সরকারি বন্ড ইস্যু হয়, তবুও সেকেন্ডারি মার্কেট খুব সীমিত, ফলে বিনিয়োগকারীরা সহজে বন্ড বিক্রি বা ক্রয় করতে পারেন না।
•সুদের হার বাংলাদেশ ব্যাংক এবং বাজারের চাহিদা অনুযায়ী নির্ধারিত হয়। সরকারি বন্ড সাধারণত নিরাপদ বিনিয়োগ হিসেবে বিবেচিত হয়, তাই প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারীদের মধ্যে গ্রহণযোগ্যতা বেশি।
কর্পোরেট বন্ড বাজার
বাংলাদেশে কর্পোরেট বন্ড বাজার কার্যত অনুপস্থিত। ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্ত কর্পোরেট বন্ডের সংখ্যা হাতে গোনা। উল্লেখযোগ্য উদাহরণ হলো বেক্সিমকো গ্রীণ সুকক (২০২১), যা দেশের প্রথম গ্রিন সুকুক। তবে এ ধরনের উদ্যোগ এখনও ব্যতিক্রমী এবং ধারাবাহিক নয়।
•বড় কর্পোরেট সংস্থা সাধারণত ব্যাংক ঋণকে প্রাধান্য দেয়, কারণ এটি সহজলভ্য এবং ঝুঁকিমুক্ত।
•নিয়ন্ত্রক জটিলতা, কর কাঠামো, এবং সেকেন্ডারি মার্কেটের অভাব কর্পোরেট বন্ডের বিকাশে বাধা সৃষ্টি করে।
•ফলশ্রুতিতে, দীর্ঘমেয়াদি অর্থায়নের জন্য বেসরকারি খাত এখনও প্রধানত ব্যাংক ঋণের উপর নির্ভরশীল, যা ব্যাংক খাতের ওপর অতিরিক্ত চাপ তৈরি করছে।
সরকারি বন্ড বাজার প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারীদের জন্য স্থিতিশীল এবং নিরাপদ হলেও, খুচরা বিনিয়োগকারীর জন্য প্রায় অপ্রাপ্য। কর্পোরেট বন্ড বাজার প্রায় অনুপস্থিত, ফলে দেশের অর্থনৈতিক খাতে বিনিয়োগের বিকল্প সীমিত। শক্তিশালী নীতি সংস্কার, কর প্রণোদনা এবং সেকেন্ডারি মার্কেট উন্নয়ন ছাড়া কার্যকর বন্ড মার্কেট গড়ে তোলা সম্ভব নয়।
বাংলাদেশের বন্ড মার্কেট বিকাশে চ্যালেঞ্জ
১. ব্যাংক-নির্ভর আর্থিক কাঠামো -ব্যাংকগুলো কর্পোরেটদের সহজে ঋণ দিয়ে থাকে, ফলে তারা বন্ড ইস্যুর পথে আগ্রহী নয়।
২. সেকেন্ডারি মার্কেটের অভাব – সক্রিয় মার্কেট মেকার না থাকায় বন্ড সহজে ক্রয়-বিক্রয় করা যায় না।
৩. তথ্য স্বচ্ছতার ঘাটতি- অনেক কর্পোরেট নির্ভরযোগ্য আর্থিক বিবরণী প্রকাশ করে না। ক্রেডিট রেটিং কার্যকর হলে ও সবসময় আস্থা তৈরি করে না।
৪. নিয়ন্ত্রক জটিলতা বিএইসির অনুমোদন প্রক্রিয়া সময়সাপেক্ষ ও ব্যয়বহুল।
৫. বিনিয়োগকারীর মানসিকতা -দ্রুত মুনাফার জন্য বিনিয়োগকারীরা শেয়ার বাজারকে অগ্রাধিকার দেয়, বন্ডে আগ্রহ সীমিত।
৬. কর কাঠামো – উৎসে কর, স্ট্যাম্প ডিউটি ও অন্যান্য চার্জ বন্ড বিনিয়োগকে নিরুৎসাহিত করে ।
৭. ডেরিভেটিভ মার্কেটের অনুপস্থিতি – ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার জন্য হেজিং টুলস না থাকায় বিনিয়োগকারীদের আস্থা বাড়ছে না।
৮. কুপন রেট এ যুক্তি নির্ভর পার্থক্য বাংলাদেশে কর্পোরেট বন্ডে বিনিয়োগে উদ্বৃত্ত করার জন্য, কর্পোরেট বন্ড (ঝুকি নির্ভর) এবং এড়াঃ. ট্রেজারী বন্ড (ঝুকি মুক্ত) এ-ইন্টারেস্ট রেট অথবা কুপন রেট এ যুক্তি নির্ভর পার্থক্য থাকা উচিত।
-৯. ক্রেডিট রেটিং এজেন্সীর উপর নির্ভরতা বিশাসযোগ্য এবং গ্রহনেযোগ্য লোকাল ক্রেডিট রেটিং এজেন্সীগুলোর উপর নির্ভরযোগ্যতা বাড়াতে হবে।
১০. High Risk ওয়েটেড এসেট বন্ডে বিনিয়োগে High Risk ওয়েটেড এসেট- যেটি কিনা ১২৫% থেকে কমিয়ে আনতে হবে।
সাম্প্রতিক নীতি উদ্যোগ
বাংলাদেশ সরকার এবং নিয়ন্ত্রক সংস্থাগুলো সাম্প্রতিক বছরগুলোতে দেশের বন্ড মার্কেটকে শক্তিশালী এবং টেকসই করার জন্য কিছু গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। এই পদক্ষেপগুলো এখনও প্রাথমিক পর্যায়ে থাকলেও, বাজারের কাঠামো ও প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারীর আস্থা বৃদ্ধিতে ইতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে।
•বাংলাদেশ ব্যাংক ও বিএসইসির যৌথ টাস্কফোর্স গঠন।
•গ্রিন বন্ড ও ইসলামিক সুকুক ইস্যুর উদ্যোগ।
•ইলেকট্রনিক বন্ড ট্রেডিং প্ল্যাটফর্ম চালুর প্রক্রিয়া, এটি প্রাতিষ্ঠানিক এবং খুচরা বিনিয়োগকারীদের জন্য বন্ড ক্রয় ও বিক্রয় সহজ করবে।
•অবকাঠামো বন্ডের পাইলট প্রকল্প।
সাম্প্রতিক নীতি উদ্যোগগুলো বাংলাদেশের বন্ড মার্কেটকে সক্রিয় করার দিক দিয়ে একটি ইতিবাচক সূচনা। তবে কার্যকর এবং ব্যাপক প্রভাবের জন্য আরও নীতি সংস্কার, কর প্রণোদনা এবং প্রাতিষ্ঠানিক ও খুচরা বিনিয়োগকারীর অংশগ্রহণ বাড়ানো প্রয়োজন।
আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা
•ভারত: কর্পোরেট বন্ডে কর ছাড়, বাধ্যতামূলক রেটিং এবং সহজ ট্রেডিং প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বাজারকে তিনগুণ বাড়িয়েছে।
•মালয়েশিয়া: ইসলামিক সুকুক বাজারকে দীর্ঘমেয়াদি অর্থায়নের প্রধান উৎসে পরিণত করেছে।
•ভিয়েতনাম: কর প্রণোদনা ও বিশেষ নিয়ন্ত্রক কাঠামোর মাধ্যমে জিডিপির ১৫% পর্যন্ত কর্পোরেট বন্ড বাজার তৈরি করেছে।
•চীন: সরকারি উদ্যোগে বন্ড মার্কেট দ্রুত প্রসারিত হয়েছে; পেনশন ফান্ড ও বীমা খাতকে বন্ডে বিনিয়োগে উৎসাহিত করা হয়েছে।
বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতা এবং অন্যান্য দেশের প্রমাণিত নীতি থেকে প্রাপ্ত অন্তর্দৃষ্টি ব্যবহার করে, নিজস্ব প্রেক্ষাপটে প্রযোজ্য নীতি ও নিয়ন্ত্রক কাঠামো উন্নয়ন এবং সংস্কার কার্যকরভাবে বাস্তবায়ন করতে পারে। বাংলাদেশে কর্পোরেটরা সহজ সমাধান হিসেবে ব্যাংক ঋণের উপর নির্ভর করছে। কিন্তু এর ফলে-
•ব্যাংকের উপর ঋণের চাপ বাড়ছে,
•দীর্ঘমেয়াদি প্রকল্প অর্থায়ন সীমিত হচ্ছে,
•বিনিয়োগকারীদের বিকল্প বিনিয়োগের সুযোগ সংকুচিত হচ্ছে।
আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতা এবং নীতিগত সুপারিশ
আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতা প্রমাণ করে যে, একটি শক্তিশালী ও টেকসই বন্ড মার্কেট গড়ে তুলতে তিনটি মূল উপাদান অপরিহার্য:
১.নীতি ও নিয়ন্ত্রক সংস্কার
২.কর প্রণোদনা
৩.সেকেন্ডারি মার্কেটের সক্রিয়তা
উপরোক্ত অন্তর্দৃষ্টি বিবেচনা করে, বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে নিম্নলিখিত নীতিগত সুপারিশ প্রাসঙ্গিক ও প্রযোজ্য:
১.নীতিগত সংস্কার: বন্ড ইস্যু সংক্রান্ত নিয়ম ও প্রক্রিয়াগুলোকে সহজ, দ্রুত এবং স্বচ্ছ করা।
২.কর প্রণোদনা: উৎসে কর এবং স্ট্যাম্প ডিউটি হ্রাসের মাধ্যমে বন্ড ইস্যুকে আরও আকর্ষণীয় করে তোলা।
৩.সেকেন্ডারি মার্কেট উন্নয়ন: কার্যকর মার্কেট মেকার তৈরি এবং ইলেকট্রনিক ট্রেডিং প্ল্যাটফর্ম চালু করা।
৪.স্বচ্ছতা বৃদ্ধি: কর্পোরেট ও সরকারি প্রতিষ্ঠানের আর্থিক বিবরণী প্রকাশ এবং ক্রেডিট রেটিংকে বাধ্যতামূলক করা।
৫.প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগ উৎসাহিত করা: পেনশন ফান্ড, বীমা কোম্পানি ও মিউচুয়াল ফান্ডকে বন্ডে বিনিয়োগে নীতিগত প্রণোদনা প্রদান।
৬.খাতভিত্তিক বন্ড ইস্যু: গ্রিন বন্ড, ইসলামিক সুকুক এবং অবকাঠামো বন্ডকে অগ্রাধিকার দিয়ে বিশেষ প্রকল্পের জন্য তহবিল নিশ্চিত করা।
৭.বিনিয়োগকারী শিক্ষা ও সচেতনতা: খুচরা বিনিয়োগকারীদের জন্য প্রশিক্ষণ ও সচেতনতা কর্মসূচি বাস্তবায়ন।
এই সুপারিশগুলো বাস্তবায়িত হলে, বাংলাদেশের বন্ড মার্কেট আরও স্থিতিশীল, স্বচ্ছ ও টেকসই হয়ে উঠতে পারবে এবং দীর্ঘমেয়াদি অর্থায়নের বিকল্প পথ সৃষ্টি হবে।
বাংলাদেশের বন্ড মার্কেট এখনও প্রাথমিক পর্যায়ে রয়েছে এবং ব্যাংককেন্দ্রিক আর্থিক কাঠামো কর্পোরেট বন্ড বাজারের সম্প্রসারণকে সীমিত করছে। দীর্ঘমেয়াদি অর্থায়ন, অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা এবং বিনিয়োগের বৈচিত্র্যময় বিকল্প সৃষ্টির জন্য একটি সক্রিয়, স্বচ্ছ ও টেকসই বন্ড মার্কেট অপরিহার্য।
একটি শক্তিশালী বন্ড মার্কেট গড়ে তুলতে সরকার, নিয়ন্ত্রক সংস্থা, ব্যাংক, কর্পোরেট সেক্টর এবং প্রাতিষ্ঠানিক ও খুচরা বিনিয়োগকারীদের সমন্বিত প্রচেষ্টা প্রয়োজন। যথাযথ নীতি সংস্কার, কর প্রণোদনা, সেকেন্ডারি মার্কেট উন্নয়ন এবং বিনিয়োগকারীর সচেতনতা বৃদ্ধি নিশ্চিত করার মাধ্যমে বাংলাদেশ আগামী দশকে একটি স্থায়ী, কার্যকর এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক বন্ড মার্কেট গড়ে তুলতে সক্ষম হবে।
এ ধরনের উন্নয়ন শুধুমাত্র দীর্ঘমেয়াদি প্রকল্পের জন্য তহবিল নিশ্চিত করবে না, বরং দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে আরও টেকসই করবে, বিনিয়োগের বিকল্প পথ সম্প্রসারিত করবে এবং সমৃদ্ধি অর্জনের জন্য একটি দৃঢ় আর্থিক কাঠামো স্থাপন করবে । সুসংগত নীতি প্রয়োগ ও বাজার প্রণোদনার মাধ্যমে, বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক স্তরের বন্ড মার্কেটের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে সক্ষম হবে এবং ভবিষ্যতের আর্থিক চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় প্রস্তুত থাকবে।
মোহাম্মদ ওবায়দুর রহমান, পরিচালক, এএএ ফাইন্যান্স অ্যান্ড ইনভেস্টমেন্ট লিমিটেড। ই-মেইল: obayad77@gmail.com
মত দ্বিমত
দেশের চিকিৎসা ব্যবস্থার সমাধান- পরকালে, নাকি বিবেকের ময়দানে?
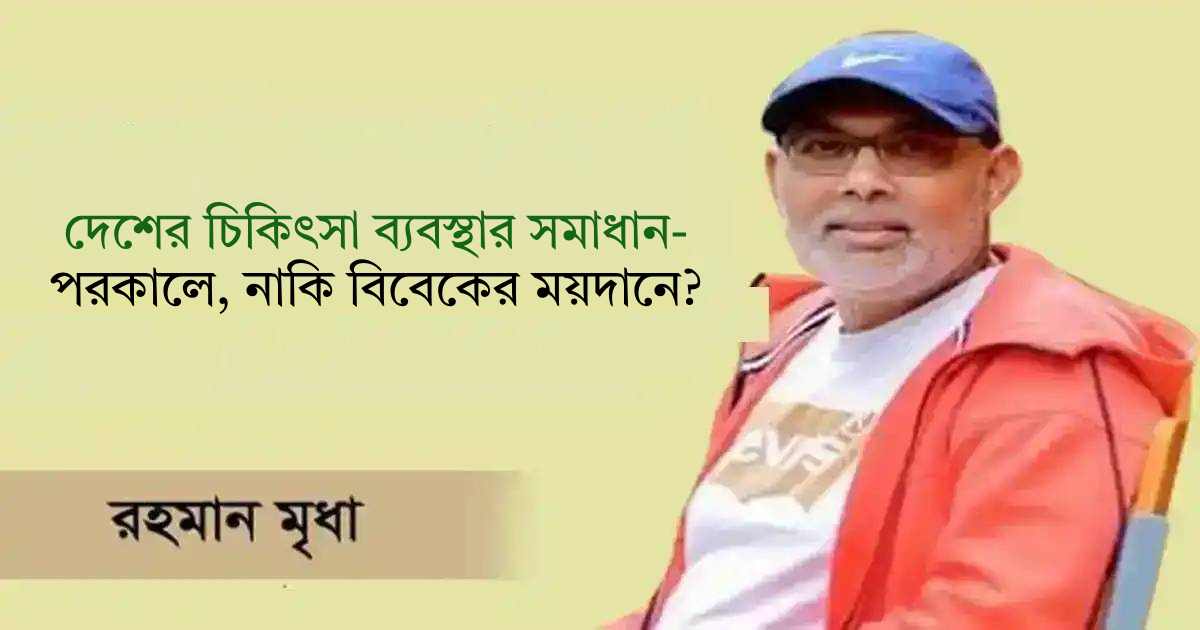
সকল ধর্মবিশ্বাসী মানুষের মুখে প্রায়ই শোনা যায় একটি কথা—‘ডেস্টিনি’। ধারণা করা হয়, অপরাধ করলে তার বিচার কেবল পরকালে হবে। কিন্তু প্রশ্ন হলো—তাহলে কি দুনিয়ায় কোনো শাস্তি নেই? যদি আজ কেউ অন্যায় করে, মানুষের ক্ষতি সাধন করে, তবে তার পরিণতি কি আমরা এই জীবনেই দেখতে পাই না?
এই প্রসঙ্গে আলোচনা শুরু হলেই তর্ক-বিতর্ক তৈরি হয়। অনেকে প্রশ্ন তোলেন—এর প্রমাণ কোথায়? তখনই বিশ্বাস আর অবিশ্বাসের দ্বন্দ্ব সামনে আসে। আমি সেই বিতর্কে ঢুকতে চাই না। বরং যেসব বিষয়ে আমরা শতভাগ নিশ্চিত, সেগুলো নিয়েই কথা বলতে চাই। কারণ নিশ্চিত সত্যকে কেন্দ্র করেই সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছানো যায়। দ্বিমত থাকলেও অন্তত সত্য আর মিথ্যার সীমারেখা স্পষ্ট হয়ে ওঠে।
আমাদের বিবেক সক্রিয় থাকলে আমরা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই একমত হতে পারি। তাই এখন চলুন এমন একটি বিষয়ে মনোযোগ দিই, যা কেবল বিশ্বাস নয়, বাস্তব অভিজ্ঞতার ভেতরেও প্রতিদিন স্পষ্ট হয়ে ধরা দেয়।
আমি দীর্ঘদিন ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানিতে কাজ করেছি। ওষুধ তৈরির সঙ্গে সরাসরি যুক্ত থাকার ফলে উৎপাদন প্রক্রিয়া, গুণগত মান নিশ্চিতকরণ এবং নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার খুঁটিনাটি বিষয়ে হাতে-কলমে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছি। একই সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের FDA, জাপান এবং ইউরোপীয় ইউনিয়নসহ বিশ্বের নানা দেশের স্বাস্থ্য সংস্থার সঙ্গেও কাজ করার সুযোগ হয়েছে। সেই অভিজ্ঞতা থেকে বুঝেছি—স্বাস্থ্যখাতের সমস্যা কেবল তাত্ত্বিক নয়, বরং মানুষের জীবন-মরণের সঙ্গে গভীরভাবে জড়িত।
নকল ও ভেজাল ওষুধ: বৈশ্বিক প্রেক্ষাপট
যেমন খাবারে ভেজাল হয়, ঠিক তেমনি ওষুধেও ভেজাল ঢুকে গেছে। নিয়মিত মনিটরিং ও কঠোর আইন থাকলেও বাজারে নকল ও নিম্নমানের ওষুধের উপস্থিতি এখনো ভয়াবহ বাস্তবতা। বিস্ময়কর হলেও সত্য—এই প্রক্রিয়ায় অনেক সময় শিক্ষিত সমাজের অংশ, যেমন ডাক্তার, ব্যবসায়ী কিংবা উৎপাদকও জড়িত থাকে। কঠোর আইন থাকার পরও নকল ওষুধের প্রবাহ রোধ করা যাচ্ছে না; বাংলাদেশও এ সংকট থেকে মুক্ত নয়।
বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO)-র হিসাব অনুযায়ী, প্রতি বছর প্রায় ৭ লক্ষ মানুষ নিম্নমানের বা নকল ওষুধের কারণে প্রাণ হারান। দক্ষিণ এশিয়া ও আফ্রিকা সবচেয়ে বেশি ঝুঁকিপূর্ণ অঞ্চল। অর্থাৎ এটি কোনো একটি দেশের সমস্যা নয়, বরং বৈশ্বিক সংকট।
উদাহরণ
ভাবুন তো—আপনার রক্তে খারাপ কোলেস্টেরল বেড়ে গেছে। যদি উপযুক্ত ওষুধ না মেলে, তাহলে স্ট্রোকের ঝুঁকি তীব্র হয়ে উঠবে। ডাক্তার প্রেসক্রিপশন দেবেন, কিন্তু একই নাম বা উপাদানের ওষুধ তৈরি করছে অনেক কোম্পানি। এর মধ্যে যদি নিম্নমান বা নকল ওষুধ পৌঁছে যায়, তখন রোগীর জীবনের ওপর নেমে আসে ভয়াবহ বিপদ। ভুল বা নকল ওষুধের কারণে শরীরের অবনতি যেমন দ্রুত ঘটে, তেমনি অকাল মৃত্যুও ডেকে আনে। আর এই মৃত্যুর দায়ভার তখন কার ওপর বর্তায়—রোগী, ডাক্তার, নাকি সেই ভেজাল ব্যবসার সঙ্গে জড়িত অদৃশ্য কারবারিদের ওপর?
ডাক্তারের দায়িত্ব ও নৈতিকতা
সকল দায় এককভাবে কোম্পানির ওপর চাপানো যায় না। একজন ডাক্তার যখন রোগীকে দেখেন, তখন তাঁর হাতে থাকে মানুষের জীবন। অধিকাংশ ডাক্তারই আন্তরিকভাবে রোগীর সুস্থতা কামনা করেন এবং তাঁদের নৈতিক দায়িত্ব পালনে সচেষ্ট থাকেন। কিন্তু বাস্তবতা হলো—চিকিৎসা ব্যবস্থার কাঠামোতে নানা ফাঁক-ফোঁকর রয়ে গেছে, যেখানে সৎ ডাক্তারও সীমাবদ্ধতার মধ্যে কাজ করেন।
ডাক্তারকে ওষুধ লিখতে হয় বাজারে বিদ্যমান কোম্পানির প্রোডাক্ট থেকে। অথচ সব কোম্পানির ওষুধ সমান মানসম্পন্ন হয় না। এখানে দায়িত্বের প্রশ্ন আসে—ডাক্তার কি রোগীর জন্য সবচেয়ে ভালো ওষুধটি বেছে নেবেন, নাকি প্রচলিত প্রথা বা প্রভাবিত ব্যবস্থার কাছে নতি স্বীকার করবেন?
এখানেই নৈতিকতার গুরুত্ব। ডাক্তার যদি মনে করেন—“এই প্রেসক্রিপশনের পেছনে একটি জীবন দাঁড়িয়ে আছে”—তাহলে তাঁর কলমের প্রতিটি দাগই হয়ে উঠতে পারে জীবনরক্ষাকারী অস্ত্র। বিপরীতে, সামান্য অবহেলা বা স্বার্থপর সিদ্ধান্ত রোগীর জন্য হতে পারে মৃত্যুদণ্ড। তবে এটাও সত্য, সব দোষ ডাক্তারের নয়। সিস্টেমে যদি স্বচ্ছতা ও কঠোর নিয়ন্ত্রণ না থাকে, তাহলে চিকিৎসা প্রক্রিয়া সঠিকভাবে চলতে পারে না। তাই ডাক্তারদের ব্যক্তিগত সততার পাশাপাশি প্রয়োজন একটি শক্তিশালী ও সৎ স্বাস্থ্যব্যবস্থা, যেখানে দুর্নীতির জায়গা নেই, আর রোগী নিশ্চিতভাবে বিশ্বাস করতে পারে—তার চিকিৎসা সর্বোচ্চ নিরাপদ হাতে রয়েছে।
কোম্পানি প্রতিনিধিদের সীমাবদ্ধতা
ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানির প্রতিনিধিরা মূলত ডাক্তারদের কাছে তাঁদের ওষুধের বৈশিষ্ট্য ও নতুন তথ্য উপস্থাপন করেন। তাঁদের কাজ হলো তথ্য দেওয়া, বোঝানো—জোর করা নয়। একজন ডাক্তার কোন ওষুধ প্রেসক্রাইব করবেন, সেই সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণ তাঁর নিজের। তবে বাস্তবতায় দেখা যায়, কোম্পানির সেলস টার্গেট পূরণের চাপ অনেক সময় প্রতিনিধিদের অস্বস্তিকর পরিস্থিতিতে ফেলে দেয়। কেউ কেউ উপহার বা প্রলোভনের আশ্রয় নেয়—যা পেশাদারীত্বের সীমা লঙ্ঘন করে এবং চিকিৎসক-প্রতিনিধির সম্পর্ককে স্বচ্ছতার বদলে সন্দেহের জায়গায় নিয়ে যায়।
আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো প্রেসক্রিপশন কপি সংগ্রহ। অনেক কোম্পানি প্রমাণস্বরূপ প্রেসক্রিপশন কপি চায়, যা রোগীর গোপনীয়তা লঙ্ঘনের শামিল। স্বাস্থ্যসেবা অত্যন্ত ব্যক্তিগত ক্ষেত্র; তাই এ ধরনের চর্চা কেবল অনৈতিকই নয়, আইনি দিক থেকেও প্রশ্নবিদ্ধ। প্রকৃতপক্ষে, প্রতিনিধিদের সীমাবদ্ধতা হলো—তাঁরা সিস্টেমকে পাল্টাতে পারেন না। তাঁরা শুধু বার্তা বহন করেন। রোগীর জন্য সঠিক ওষুধ নির্বাচন, মান নিয়ন্ত্রণ আর নৈতিক ব্যবহারের দায়ভার শেষ পর্যন্ত ডাক্তার, কোম্পানি ও নিয়ন্ত্রক সংস্থার উপরই বর্তায়।
রোগীর গোপনীয়তা
রোগীর প্রেসক্রিপশন শুধু একটি কাগজ নয়; এটি তাঁর ব্যক্তিগত জীবন, শারীরিক অবস্থা ও চিকিৎসার ইতিহাসের সংবেদনশীল দলিল। এই তথ্যের মধ্যে লুকিয়ে থাকে তাঁর দুর্বলতা, ভয়, এমনকি সামাজিক মর্যাদার সঙ্গে যুক্ত বিষয়গুলোও।
তাই প্রেসক্রিপশনকে সুরক্ষিত রাখা কেবল আইনি বাধ্যবাধকতা নয়, এটি চিকিৎসার নৈতিকতার অন্যতম মূলভিত্তি। বাস্তবে দেখা যায়, অনেক সময় কোম্পানির স্বার্থে বা সেলস টার্গেটের কারণে প্রেসক্রিপশন কপি সংগ্রহ করা হয়। রোগীর অজান্তে তাঁর গোপনীয়তা ভঙ্গ করা হয়—যা কেবল পেশাগত সীমালঙ্ঘন নয়, বরং মানবিক আস্থার ওপর আঘাত। রোগীর সম্মতি ছাড়া তাঁর চিকিৎসা সংক্রান্ত কোনো তথ্য ব্যবহার বা প্রকাশ করা উচিত নয়। এই সীমারেখা ডাক্তার, কোম্পানি প্রতিনিধি ও ফার্মাসিস্ট—সবারই কঠোরভাবে মেনে চলা প্রয়োজন।
বাংলাদেশ বনাম অন্যান্য দেশ
বাংলাদেশে অনুমোদিত ঔষধ কোম্পানির সংখ্যা ২৫০টিরও বেশি। ডাক্তাররা এখানে যেকোনো অনুমোদিত কোম্পানির ওষুধ প্রেসক্রাইব করতে পারেন। কিন্তু সিস্টেমিক দুর্নীতি, নিয়ন্ত্রণের ফাঁকফোকর এবং অপ্রতুল তদারকি রোগীর জন্য ঝুঁকি তৈরি করে। ফলে রোগী নিশ্চিত হতে পারেন না—হাতে পাওয়া ওষুধটি সত্যিই নিরাপদ কি না।
তুলনামূলকভাবে দেখা যায়, ভারত ও জাপানের মতো দেশে ডাক্তাররা স্বাধীনভাবে যেকোনো কোম্পানির ওষুধ প্রেসক্রাইব করতে পারেন, কিন্তু প্রতিটি ওষুধ কঠোর পরীক্ষানিরীক্ষার মধ্য দিয়ে বাজারে আসে। রোগী নিশ্চিন্ত থাকেন—প্রতিটি পণ্য নিয়ন্ত্রিত এবং নিরাপদ। অন্যদিকে, বাংলাদেশে সচেতনতা ও সঠিক তদারকি না থাকলে রোগী সহজেই ভেজাল ওষুধের শিকার হতে পারেন।
অতএব, শুধু অনুমোদনের সংখ্যা নয়, প্রয়োজন একটি শক্তিশালী, স্বচ্ছ ও জবাবদিহিমূলক স্বাস্থ্যব্যবস্থা, যেখানে প্রতিটি ওষুধ পরীক্ষা-নিরীক্ষা, তদারকি এবং রোগীর নিরাপত্তার সঙ্গে সরাসরি যুক্ত থাকে।
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও পরিশ্রম
চিকিৎসক এবং কোম্পানি প্রতিনিধিরা সহজভাবে এই পেশায় প্রবেশ করেননি। বছরের পর বছর কঠোর শিক্ষা, প্রশিক্ষণ এবং পরীক্ষার মধ্য দিয়ে তাঁরা দক্ষতা অর্জন করেন। নতুন ওষুধের বৈশিষ্ট্য বোঝানো, রোগীর সঠিক চিকিৎসা নিশ্চিত করা—এ সবই তাঁদের কঠোর পরিশ্রমের অংশ।
একজন ডাক্তার যখন রোগীর জীবন রক্ষার জন্য সঠিক ওষুধ নির্বাচন করেন, তখন সেটি শুধু পেশাগত দায়িত্ব নয়; এটি নৈতিক দায়বোধের প্রকাশ। একইভাবে, কোম্পানি প্রতিনিধিরাও প্রচলিত নিয়ম মেনে রোগীর মঙ্গলের জন্য তথ্য ভাগাভাগি করেন। তাঁদের পরিশ্রম ও সততা না থাকলে চিকিৎসা ব্যবস্থার কাঠামোই ব্যর্থ হয়ে যেত।
তাহলে শুধুমাত্র ব্যক্তির উপর দোষ চাপানো ঠিক হবে না। সঠিক চিকিৎসা নিশ্চিত করতে প্রয়োজন ব্যক্তিগত সততার সঙ্গে একটি শক্তিশালী ও স্বচ্ছ স্বাস্থ্যব্যবস্থার সমন্বয়।
ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট
ভেজাল ওষুধ বা নিম্নমানের চিকিৎসা কেবল আধুনিক সমস্যা নয়। মধ্যযুগীয় ইউরোপে খাবার ও ওষুধের ভেজালের কারণে মৃত্যুর ঘটনা থেকে “Apothecary Laws” চালু হয়েছিল। এ আইনগুলো রোগীর সুরক্ষা ও ওষুধের মান নিয়ন্ত্রণ নিশ্চিত করেছিল।
বাংলাদেশের উপনিবেশকালে নীলচাষীদের জন্যও নকল ওষুধ এবং ভেজাল খাবারের সমস্যার উল্লেখ পাওয়া যায়। অর্থাৎ, এটি মানবসভ্যতার দীর্ঘ ইতিহাসের অংশ। তবে যুগ পরিবর্তন সত্ত্বেও, সঠিক নিয়ম-নীতি ও সতর্ক নজরদারি না থাকলে সমস্যা পুনরায় ফিরে আসে। এ ইতিহাস শেখায়—সিস্টেমের দুর্বলতা ও নৈতিক দায়িত্বের অভাব কেবল ব্যক্তির নয়, বরং পুরো সমাজের জন্য বিপদ ডেকে আনে।
বিবেক ও নৈতিক প্রশ্ন
ওষুধ জীবন রক্ষাকারী। যদি ওষুধই জীবন নাশের কারণ হয়, মানুষ কাকে বিশ্বাস করবে—ডাক্তার, বিক্রেতা নাকি কোম্পানিকে? যদি দেশে রন্ধ্রে রন্ধ্রে দুর্নীতির বীজ রোপণ করা হয়, তখন ঠিক কাদের থেকে সঠিক চিকিৎসা আশা করা যাবে?
যে ব্যক্তি ভেজাল ওষুধ বিক্রি করে, তিনিও এক একজন বাবা-মা। তবে কি তিনি ভেবেছেন অন্যের পরিবারও তার মতোই স্নেহ-ভালোবাসার উপর টিকে আছে? যদি তিনি এক মুহূর্তের জন্য ভাবতেন যে তাঁর সন্তানকেও কোনোদিন এই ভেজাল ওষুধ গিলে নিতে হতে পারে, তবে কি তিনি একই পথে হাঁটতেন?
বিবেক জাগ্রত হলে বোঝা যেত—অন্যের সন্তানের কান্না আর নিজের সন্তানের হাসির মাঝে কোনো পার্থক্য নেই। আর এই উপলব্ধিই হতে পারে পরিবর্তনের প্রথম পদক্ষেপ।
দুনিয়ার বিচার
যদি আমরা জেনেশুনে এই ধরনের অপরাধের সঙ্গে যুক্ত থাকি, তাহলে কি মনে হয় সব অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডের ফলাফল শুধুই পরকালে ভোগ করতে হবে? না—ফল দুনিয়াতেই আসে। মানুষ অসুস্থ হয়, অকালে প্রাণ হারায়, পরিবার শোকে ডুবে যায়, সমাজ হারায় কর্মক্ষম মানুষ ও মানবিক মূল্যবোধ। এটাই দুনিয়ার বিচার—যেখানে অন্যের ক্ষতি আসলে আমাদের নিজেদের জীবন ও সমাজকেই ক্ষতিগ্রস্ত করে।
সমাধানের আহ্বান
কষ্ট আমরা করি নিজের পরিবারের জন্য। অন্যেরাও তাদের পরিবারের জন্য একইভাবে কষ্ট করে। কষ্টই যখন করি, তখন হালাল উপায়ে উপার্জন করব না কেন? এই প্রশ্নের উত্তরই দিতে পারে সমাধান।
ব্যক্তিগত বিবেক সচেতন হলে, ওষুধ ও খাদ্যে ভেজাল রোধে বড় পরিবর্তন আনা সম্ভব। আমাদের নীতিনির্ধারক, নিয়ন্ত্রক এবং পেশাজীবীদের মিলিত প্রচেষ্টা দরকার—এবং প্রতিটি নাগরিককেও সতর্ক ও দায়বদ্ধ হতে হবে।
শেষ বার্তা
পরকালের বিচার নিশ্চিত, কিন্তু দুনিয়ার বিচারও অস্বীকারযোগ্য নয়। ভেজাল খাবার বা নকল ওষুধের কারণে যদি আজই একটি প্রাণ ঝরে যায়, সেটি কি কেবল পরকালের সাজা? না, এটি বর্তমানের কঠিন বাস্তবতা।
তাই “সব সাজাই কি মৃত্যুর পরে হবে” ভাবনা আমাদের নীরবে বসিয়ে দেয়। সত্য হলো—আজই যদি আমরা বিবেকবান ও দায়িত্বশীল হই, তাহলে কালকের প্রজন্ম একটি নিরাপদ সমাজ পাবে।
রহমান মৃধা, সাবেক পরিচালক, ফাইজার, সুইডেন। Rahman.Mridha@gmail.com
মত দ্বিমত
জাতিসংঘ: পতনের ছায়া নাকি পুনর্জাগরণের আলো?
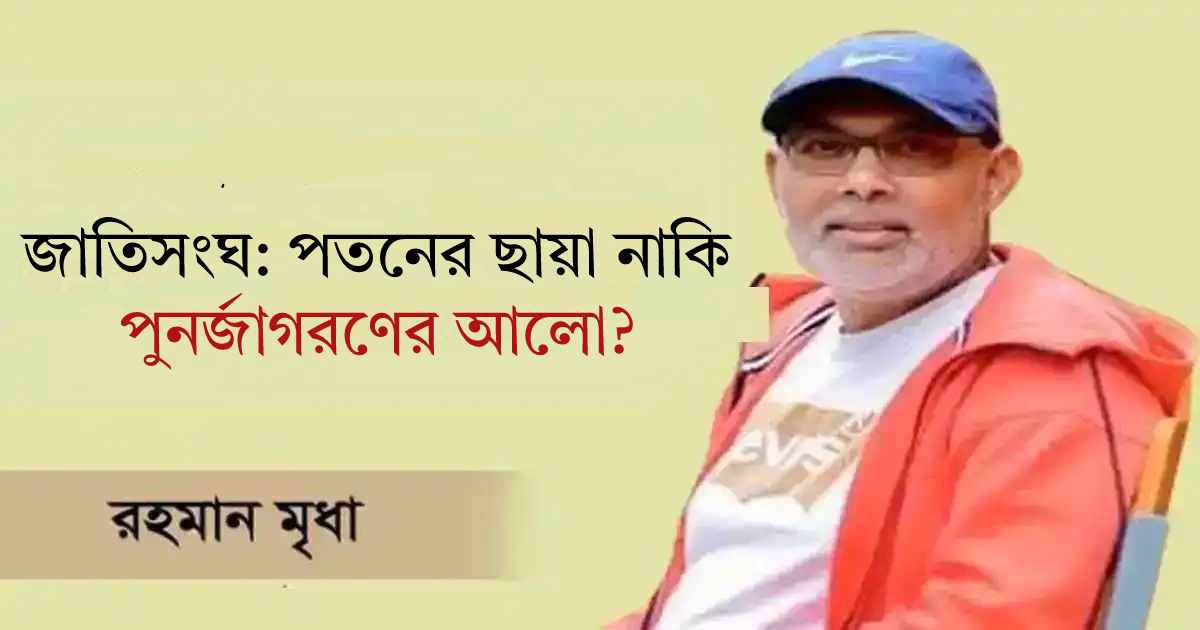
গাজায় শিশুর কান্না, ইউক্রেনে যুদ্ধবিধ্বস্ত শহর, রোহিঙ্গাদের দীর্ঘশ্বাস—তাহলে জাতিসংঘ কোথায়? দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ধ্বংসস্তূপ থেকে মানবতার শান্তি, ন্যায় ও নিরাপত্তার আশায় ১৯৪৫ সালে জাতিসংঘের জন্ম হয়েছিল। প্রতিশ্রুতি ছিল—একটি বৈশ্বিক মঞ্চ, যেখানে সব রাষ্ট্র সমানভাবে অংশ নেবে, আলোচনার মাধ্যমে বিরোধ মীমাংসা হবে, আর মানুষের জীবন, স্বাধীনতা ও মর্যাদা রক্ষা পাবে। কিন্তু প্রায় আট দশক পর প্রশ্ন উঠছে—জাতিসংঘ কি সেই স্বপ্ন পূরণ করতে পেরেছে, নাকি এটি আজ পতনের দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে আছে?
আমি ব্যক্তিগতভাবে গত কয়েক বছরে সুইডেনসহ বিশ্বের নানা দেশে এ বিষয়ে প্রতিবাদ করেছি এবং বহু নিবন্ধ লিখেছি। কারণ কথা ছিল—যুদ্ধ নয়, আলোচনার মাধ্যমে বিরোধ মীমাংসা হবে। সেই স্বপ্নের নাম ছিল জাতিসংঘ। ১৯৪৫ সালের ২৪ অক্টোবর নিউইয়র্কে প্রতিষ্ঠার সময় ৫১টি রাষ্ট্র বিশ্ব শান্তি ও মানবাধিকার রক্ষার অঙ্গীকার করেছিল। আজ সেই সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১৯৩-এ।
প্রতিষ্ঠার সময় কাঠামো ও লক্ষ্য ছিল স্পষ্ট। সাধারণ পরিষদ, নিরাপত্তা পরিষদ, আন্তর্জাতিক আদালত, অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ—এসব অঙ্গ সংস্থা রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে সমন্বয় ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার জন্য তৈরি হয়েছিল। নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্যদের জন্য ভেটো ক্ষমতা নির্ধারণ করা হয়েছিল, যা তখন মনে করা হয়েছিল বড় শক্তিগুলোর মধ্যে সংঘাত প্রতিরোধ করবে। অথচ আজ দেখা যাচ্ছে, এই ভেটোই মানবিক সংকট মোকাবিলার প্রধান অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে।
২০২৫ সালের ২৩ সেপ্টেম্বর মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে এক তীব্র সমালোচনামূলক ভাষণ দেন। তিনি সংস্থাটিকে “বিকল” এবং “অকার্যকর” বলে আখ্যা দেন, দাবি করেন এটি বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠায় ব্যর্থ। এমনকি তিনি জাতিসংঘ ভবনের একটি ভাঙা এস্কেলেটর ও টেলিপ্রম্পটারের ত্রুটি পর্যন্ত তুলে ধরেন, যদিও জাতিসংঘের মুখপাত্র পরে স্পষ্ট করেন—এগুলো যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধি দলের কারণে হয়েছিল। ট্রাম্পের বক্তৃতায় অভিবাসন, জলবায়ু পরিবর্তন, ইউক্রেন যুদ্ধ এবং ফিলিস্তিন রাষ্ট্রের স্বীকৃতির প্রসঙ্গও উঠে আসে। তিনি ইউরোপীয় ইউনিয়নের অভিবাসন নীতি ও সবুজ জ্বালানি প্রকল্পের সমালোচনা করেন, জলবায়ু পরিবর্তনকে “বিশ্বের সবচেয়ে বড় প্রতারণা” বলে উল্লেখ করেন এবং ন্যাটো দেশগুলোর রাশিয়ার জ্বালানি ক্রয়কে দ্বৈত নীতি হিসেবে আখ্যা দেন।
ট্রাম্পের এ বক্তব্য বিশ্বজুড়ে আলোচিত হয়। ফরাসি প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাক্রোঁ জাতিসংঘকে আন্তর্জাতিক সহযোগিতার প্রতীক হিসেবে তুলে ধরেন, যা ট্রাম্পের জাতীয়তাবাদী দৃষ্টিভঙ্গির বিপরীত। ব্রাজিলের প্রেসিডেন্ট লুইজ ইনাসিও লুলা দা সিলভা তাঁর একতরফা নীতির সমালোচনা করে বলেন, এটি সার্বভৌমত্বের প্রতি হুমকি। জাতিসংঘ মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেসও ট্রাম্পের মন্তব্য প্রত্যাখ্যান করে শান্তি প্রতিষ্ঠায় সংস্থাটির প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করেন এবং যুক্তরাষ্ট্রের সহযোগিতা কামনা করেন।
কিন্তু বাস্তবতায় দেখা যায়, জাতিসংঘ প্রায়ই শক্তিধর রাষ্ট্রগুলোর স্বার্থের কাছে জিম্মি হয়ে পড়ে। ২০২৪ সালের গাজা সংকট তার বড় উদাহরণ। নিরাপত্তা পরিষদে মানবিক ত্রাণ পাঠানোর প্রস্তাব ভেটোর কারণে স্থগিত হয়, ফলে হাজারো শিশু, বৃদ্ধ ও অসহায় মানুষ খাদ্য ও চিকিৎসা থেকে বঞ্চিত হয়। শুধু গাজাই নয়, ইউক্রেন, মিয়ানমার, আফগানিস্তান বা হাইতির মতো দেশগুলোতেও জাতিসংঘের সীমাবদ্ধতা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।
জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনকে তার সাফল্যের নিদর্শন হিসেবে দেখাতে চায়। বাংলাদেশ, ভারত, নেপালসহ দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলো এতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে। কিন্তু হাইতিতে শান্তিরক্ষীদের বিরুদ্ধে যৌন নির্যাতন ও শিশুশোষণের অভিযোগ আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে গভীর প্রশ্ন তুলেছে। ২০১০ সালে হাইতিতে চোলেরা মহামারির জন্যও শান্তিরক্ষা বাহিনীকে দায়ী করা হয়েছিল। এসব ব্যর্থতা জাতিসংঘের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ করেছে।
বাজেটের ক্ষেত্রেও অসমতা স্পষ্ট। যুক্তরাষ্ট্র একাই প্রায় ২২% অর্থায়ন করে, যার কারণে সিদ্ধান্ত গ্রহণে তার প্রভাব অস্বাভাবিকভাবে বেশি। ছোট দেশগুলোর কণ্ঠস্বর প্রান্তিক হয়ে পড়ে। মানবাধিকার কাউন্সিলও প্রায়শ দ্বিমুখী নীতি অনুসরণ করে—ফিলিস্তিন বা ইয়েমেনে নীরবতা, অথচ তুলনামূলক দুর্বল রাষ্ট্রগুলোর ক্ষেত্রে কঠোর অবস্থান। আন্তর্জাতিক আদালত ও অপরাধ আদালত প্রভাবশালী রাষ্ট্রগুলোর বিরুদ্ধে কার্যকর হতে ব্যর্থ, কারণ যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া ও চীন এসব আদালতের রায় মানতে অস্বীকার করে।
আজ জাতিসংঘের সামনে এক কঠিন বাস্তবতা দাঁড়িয়ে আছে। ভেটো ক্ষমতার সংস্কার, মহাসচিব নির্বাচনে স্বচ্ছতা, বাজেটে ভারসাম্য, শান্তিরক্ষা মিশনে জবাবদিহিতা, মানবাধিকার কাউন্সিলের নিরপেক্ষতা—এসব ছাড়া জাতিসংঘকে আধুনিক বিশ্বের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় কার্যকর করা সম্ভব নয়। জাতিসংঘ আধুনিক ইতিহাসে এক অমূল্য প্রতিষ্ঠান—দুর্যোগে ত্রাণ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য প্রকল্পে এর অবদান অনস্বীকার্য। তবুও কাঠামোগত সীমাবদ্ধতা ও রাজনৈতিক প্রভাবের কারণে এটি প্রায় অচল হয়ে পড়ছে।
বাংলাদেশের জন্য এই সংকট আরও গভীর। রাজনৈতিক অস্থিরতা, সীমান্ত সমস্যা, জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত, রোহিঙ্গা সংকট, দুর্যোগপূর্ণ এলাকায় শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবার সীমাবদ্ধতা—এসবই আমাদের জনগোষ্ঠীর নিরাপত্তা ও মর্যাদাকে প্রতিনিয়ত হুমকির মুখে ফেলছে। বৈশ্বিক সংহতি ও কার্যকর আন্তর্জাতিক সহযোগিতা ছাড়া এসব চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করা প্রায় অসম্ভব। একজন বাংলাদেশি হিসেবে আমি বিশ্বাস করি, জাতিসংঘের সংস্কার কেবল বৈশ্বিক শান্তির জন্য নয়, আমাদের মতো উন্নয়নশীল দেশের টিকে থাকার জন্যও অত্যাবশ্যক।
তাহলে প্রশ্ন একটাই—জাতিসংঘ কি পতনের পথে যাবে, নাকি পুনর্জাগরণের আলোয় বিশ্বকে নেতৃত্ব দেবে? আজ আমাদের দৃঢ় কণ্ঠে বলতে হবে—সংস্কারই জাতিসংঘের পুনর্জন্মের একমাত্র পথ।
রহমান মৃধা
গবেষক ও লেখক
সাবেক পরিচালক, ফাইজার, সুইডেন
Rahman.Mridha@gmail.com