মত দ্বিমত
বাজেট: বাস্তবতা, চ্যালেঞ্জ ও সম্ভাবনা
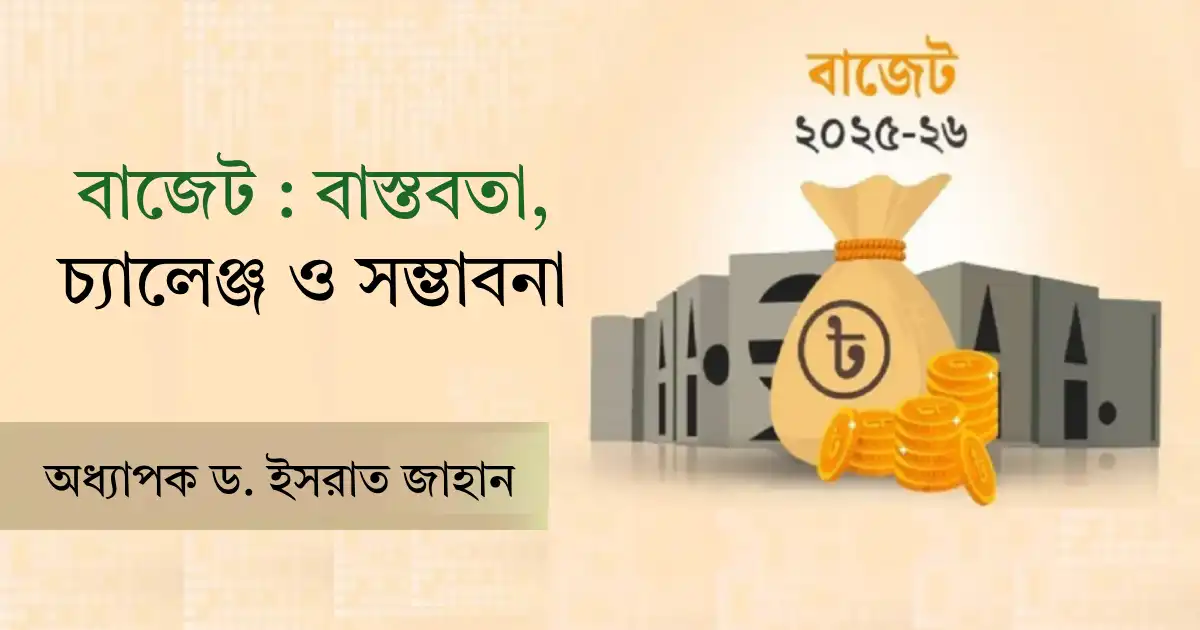
২০২৫-২০২৬ অর্থবছরের জন্য জাতীয় বাজেট প্রণয়নের প্রাথমিক কাজ প্রায় শেষ র্পযায়ে। জাতীয় বাজেট একটি সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা এবং রাষ্ট্রের আর্থিক পরিকল্পনা। সরকার কর্তৃক উপস্থাপিত বাজেট একটি রাষ্ট্রীয় দলিল। জাতীয় সংসদ কার্যকর না থাকায় জুনের প্রথম সপ্তাহে প্রস্তাবিত বাজেট অন্তর্বর্তী সরকারের উপদেষ্টা পরিষদের কাছে অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করা হবে। সাধারনত: প্রতিবছরই বাজেট জাতীয় সংসদের মাধ্যমে অনুমোদিত হয়েছে। তবে সামরিক শাসনামল এবং ২০০৭-২০০৮ ও ২০০৮-২০০৯ অর্থবছরে জাতীয় সংসদে বাজেট পেশ হয় নাই। রাজনৈতিক সরকারের বাজেট, সামরিক শাসনামলের বাজেট এবং অন্তর্বর্তী সরকার বাজেট চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে এক একটি বাজেট এক এক ধরনের।
গণঅভ্যুত্থানে পতিত সরকারের নানা ধরনের দুর্নীতি ও অনিয়মের কারণে দেশের অর্থনীতি বিপর্যয়ের মুখে রয়েছে। জুলাই-আগস্টের গণ-আন্দোলন এবং আন্দোলন-পরবর্তী সামাজিক অস্থিরতার কারণে রাজস্ব আদায় বিঘ্নিত হয়। ফলে চলতি অর্থবছরের রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হওয়ার কোনোই সম্ভাবনা নেই। ফলে বাজেট প্রণয়নের ক্ষেত্রে কিছু অসুবিধা থাকবে। তবে দলিয় সরকার না থাকায় একটি যৌক্তিক ও বাস্তবসম্মতভাবে বাজেট রূপ দেওয়ার সম্ভব। বাস্তবমূখী বাজেট এবং এই বাজেট বাস্তবায়নের একটা রূপরেখাও থাকা উচিত। আগামী ২০২৫-২০২৬ অর্থবছরের প্রস্তাবিত বাজেট উপলক্ষে কিছু সুপারিশ করা হয়েছে।
বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে দ্বিতীয় সর্বনিম্ন ট্যাক্স আদায় হয়। বর্তমানে দেশে ট্যাক্স-জিডিপি রেশিও ৭ দশমিক ৫০ শতাংশ। বাজেট অর্থায়নের জন্য স্থানীয় সূত্র থেকে অর্থ সংগ্রহের ওপর বেশি মাত্রায় নির্ভর করতে হয়। আগামী বাজেটে বিভিন্ন ক্ষেত্রে আরোপিত করের হার কমিয়ে করের পরিধি বাড়ানোর উদ্যোগ নিলে রাজস্ব আদায় বাড়ার সম্ভাবনা রয়েছে। অটোমেশন নিশ্চিত করে তথ্য প্রযুক্তির ওপরে আরও গুরুত্ব দিয়ে অনলাইনের ব্যবস্থা করলে রাজস্ব আদায় বাড়ার সম্ভাবনা রয়েছে।উচ্চ মাত্রায় কর নির্ধারণ করলে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কর ফাঁকি দেওয়ার প্রবণতা বাড়ে। অভ্যন্তরীণ সুশাসনের অভাবে রাজস্ব আদায় যেভাবে বৃদ্ধি পাওয়ার কথা তা হচ্ছে না। মফস্বলে কর দেওয়ার মতো অনেক ব্যবসায়ী আছেন। তাদের করের আওতায় আনা যায় কিনা তা ভাবা দরকার।
চলতি অর্থবছরের (২০২৪-২০২৫) মূল বাজেট বরাদ্দ ছিল ৭ লাখ ৯৭ হাজার কোটি টাকা, যা সংশোধন করে সাড়ে ৭ লাখ কোটি টাকায় সীমিত রাখা হচ্ছে। ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের মূল বাজেট বরাদ্দ ছিল ৭ লাখ ৬১ হাজার ৭৮৫ কোটি টাকা, যা পরবর্তীকালে ৭ লাখ ১৪ হাজার ৪১৮ কোটি টাকায় নামিয়ে আনা হয়েছিল। বিভিন্ন সূত্র মতে, আগামী অর্থবছরের (২০২৫-২০২৬) বাজেটের আকার হতে পারে ৮ লাখ ৪৮ হাজার কোটি টাকা।
চলতি অর্থবছরে জিডিপি প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারিত আছে ৬ দশমিক ৮ শতাংশ, যা আগামী বাজেটে ৫ দশমিক ৫ শতাংশে নামিয়ে আনা হতে পারে। চলতি অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে ব্যয় বরাদ্দ আছে ২ লাখ ৬৫ হাজার কোটি টাকা, আগামী অর্থবছরে এটা সামান্য বৃদ্ধি পেয়ে ২ লাখ ৭০ হাজার কোটি টাকায় উন্নীত হতে পারে। বেতন-ভাতা বাবদ বর্তমান বছরের বাজেটে বরাদ্দ আছে ৮২ হাজার কোটি টাকা, যা আগামী বছর ৯০ হাজার কোটি টাকায় উন্নীত করা হতে পারে। বৈদেশিক ঋণের সুদ বাবদ চলতি অর্থবছরে পরিশোধের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারিত আছে ১ লাখ ১৩ হাজার কোটি টাকা। আগামী অর্থবছরের জন্য এ খাতে ১ লাখ ২০ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হতে পারে। মূল্যস্ফীতির হার চলতি অর্থবছরের জন্য ৬ দশমিক ৫ শতাংশ নির্ধারিত ছিল। আগামী অর্থবছরের জন্য এটা ৭ শতাংশ নির্ধারণ করা হতে পারে।
রাজনৈতিক সরকারের আমলে দলীয় বিবেচনায় অপ্রয়োজনীয় প্রকল্প গ্রহণ করা হতো। বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকারের আমলে রাজনৈতিক বিবেচনার পরিবর্তে বাস্তবতার নিরিখে প্রকল্প গ্রহণ করা হবে বলে আশা করা হচ্ছে। প্রতিবছর দেখা যায়, বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় যেসব প্রকল্প গ্রহণ করা হয় তার বাস্তবায়ন বিলম্বিত হয় এবং ব্যয় বৃদ্ধি পায়। এ প্রবণতা রোধ করা দরকার। কোনো ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান যদি নির্দিষ্ট সময়ে প্রাক্কলিত ব্যয়ে প্রকল্প বাস্তবায়ন করতে ব্যর্থ হয়, তাহলে তার দায়ভার সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানকেই বহন করতে হবে। জনগণ কেন তার দায়ভার বহন করবে? প্রকল্প বিলম্বিত হওয়া এবং ব্যয়বৃদ্ধির বিষয়টি সংশ্লিষ্ট ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে জরিমানা আকারে আদায় করা যেতে পারে।
আগামী অর্থবছর জিডিপির প্রবৃদ্ধি বাড়ানোর দিকে মনোযোগ না দিয়ে অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করতে অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত । ব্যাংকিং খাতে স্থিতিশীলতা ফেরানো, বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ স্থিতিশীল রাখা জরুরি। এ সময় অভ্যন্তরীণ অর্থনীতিতে স্থিতিশীলতা না থাকলে অর্থনীতিতে আরো নেতিবাচক প্রভাব পড়ার আশঙ্কা রয়েছে।
কর পরিশোধিত আয় থেকে একজন ব্যক্তি ব্যাংকে টাকা জমা রাখলে মুনাফার ওপর ১০-১৫ শতাংশ কর কাটা হয়। আবার ব্যাংকের জমা স্থিতির ভিত্তিতে আবগরী শুল্ক কাটা হয়। এমনিতেই মানুষের সঞ্চয় সক্ষমতা কমেছে। আবার বিভিন্ন ভীতির কারণে অনেকে ব্যাংকে টাকা রাখতে চাইছেন না। এরকম অবস্থায় ৫/১০ লাখ টাকা পর্যন্ত জমার ওপর আবগরী শুল্ক প্রত্যাহার এবং মুনাফার ওপর কর কমানো যেতে পারে। আগামী অর্থবছরের মূল্যস্ফীতি কমানোর দিকে সর্বোচ্চ মনোযোগ দেওয়া প্রয়োজন । উচ্চ মূল্যস্ফীতির হার বিবেচনায় নিয়ে করমুক্ত আয়সীমা অন্তত ৫ লাখ টাকা নির্ধারণ করা। যেখানে ভারতে ১২ লাখ টাকা পর্যন্ত আয়ে কোনও কর দিতে হয় না।
শিক্ষা হচ্ছে একটি জাতির সবচেয়ে মূল্যবান ভবিষ্যৎ বিনিয়োগ। শিক্ষা খাতের ওপর যথাযথ গুরুত্ব দিয়ে অধীত শিক্ষার মানোন্নয়ন ঘটানো না গেলে কোনোদিনই টেকসই উন্নয়ন অর্জন করা সম্ভব হবে না। বাংলাদেশে শিক্ষা খাতে সরকারি বরাদ্দ (জিডিপির অনুপাতে) গত ২০ বছর ধরে দক্ষিণ এশিয়ার মধ্য সর্বনিম্ন। আগামী অর্থবছরের প্রস্তাবিত বাজেটে শিক্ষা খাতের ওপর সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিতে হবে। প্রতিবছরই বাজেটে শিক্ষা খাতে সর্বোচ্চ বরাদ্দ দেখানো হয়। কিন্তু সেখানে শুভংকরের ফাঁকি রয়েছে। শিক্ষা খাতের সঙ্গে আরও দু-একটি খাতকে অন্তর্ভুক্ত করে ব্যয় বরাদ্দ দেওয়া হয়। শিক্ষা খাতে বাজেটের বড় অংশই অবকাঠামোগত উন্নয়নে ব্যয়িত হয়। ফলে শিক্ষা গবেষণা খাতের জন্য অর্থ সংকুলান করা কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। ইউনেস্কোর মতে, একটি দেশের মোট জিডিপির অন্তত ৬ শতাংশ শিক্ষা খাতে বরাদ্দ থাকা প্রয়োজন। কিন্তু আমাদের দেশে প্রতিবছর বাজেটে শিক্ষা খাতে যে বরাদ্দ দেওয়া হয়, তার পরিমাণ জিডিপির ২ শতাংশের কম। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোয় যাতে গবেষণা কাজে বেশি অর্থ বরাদ্দ করা হয় তার ব্যবস্থা করতে হবে। বিশেষায়িত অনেক বিশ্ববিদ্যালয় আছে, যেখানে সাধারণ বিষয়ও পড়ানো হচ্ছে। এতে শিক্ষার মানের অবনতি ঘটছে। দেশে বর্তমানে ৫৫টি সরকারি এবং ১১৫টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে। স্বাধীনতার পর থেকেই আমাদের শিক্ষার মানের অবনতি ঘটতে শুরু করে। এখন তা চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। বিগত সরকারের আমলে শিক্ষার মানোন্নয়নের চেয়ে শিক্ষিতের হার বেশি দেখানোর প্রবণতা লক্ষ করা গেছে। অনেকের ধারণা, বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থাকে পরিকল্পিতভাবে ধ্বংস করার জন্য শিক্ষার মানের অবনতি ঘটানো হচ্ছে। বর্তমানে যারা উচ্চশিক্ষা অর্জন করছেন, তারা কর্মক্ষেত্রে প্রবেশের ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতায় টিকতে পারছে না। প্রাথমিক পর্যায় থেকে শুরু করে শিক্ষাব্যবস্থার প্রতিটি স্তরে গুণগত মান নিশ্চিত করার উদ্যোগ নিতে হবে। শিক্ষা খাতে প্রতিবছর যে বাজেট বরাদ্দ, এর কত অংশ গবেষণা খাতে ব্যয় করতে হবে, এটা নির্দিষ্ট করে দেওয়া যেতে পারে।
বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়, বেসরকারি মেডিকেল কলেজ, বেসরকারি ডেন্টাল কলেজ, বেসরকারি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ বা শুধু তথ্যপ্রযুক্তি বিষয়ে শিক্ষাদানে নিয়োজিত বেসরকারি কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের আয়ের ওপর ১৫ শতাংশ কর আরোপের প্রস্তাব করা হয়েছে। শিক্ষার ওপর কর কোনোভাবেই কাম্য নয়; বরং সংবিধান পরিপন্থি। সংবিধানের দ্বিতীয় ভাগের রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতির ১৫তম অনুচ্ছেদে মৌলিক চাহিদা হিসেবে নাগরিকের জন্য শিক্ষা নিশ্চিতের কথা বলা হয়েছে। তাছাড়া কর আরোপিত হয় বাণিজ্যিক পণ্য বা সেবার ওপর। শিক্ষা প্রথমত পণ্য নয়। দ্বিতীয়ত, বেসরকারি উদ্যোগের উচ্চশিক্ষা কোনো বাণিজ্যিক তৎপরতাও নয়। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন ২০১০ অনুযায়ী ট্রাস্টের অধীন বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো অলাভজনক প্রতিষ্ঠান হিসেবে পরিচালিত। ট্রাস্ট আইন ১৮৮২ অনুযায়ী ট্রাস্টের অধীন পরিচালিত হওয়ায় অলাভজনক প্রতিষ্ঠান করযোগ্য নয়। কোম্পানি আইন ১৯৯৪-এর আওতায় লাভজনক প্রতিষ্ঠান হিসেবে পরিচালিত মেডিকেল কলেজ ও ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের সঙ্গে ট্রাস্ট আইনে অলাভজনক হিসেবে পরিচালিত বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ওপর একই আওতায় সমভাবে আয়কর আরোপের প্রস্তাবনা আইনের পরিপন্থি এবং তা কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। আরোপিত করের বোঝার সিংহভাগই শিক্ষার্থীদের ঘাড়ে এসে পড়বে, এমনকি কর যদি সরাসরি শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে না নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কাছ থেকেও নেওয়া হয়। দেশে ১১৫টি অনুমোদিত বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রায় পাঁচ লাখ শিক্ষার্থী পড়াশোনা করছে। বাড়তি করের চাপ একদিকে যেমন শিক্ষার্থীদের পরিবারের ওপর একটা অমানবিক বোঝা হয়ে দাঁড়াবে, অন্যদিকে দেশে উচ্চশিক্ষার প্রসারকে বাধাগ্রস্ত এবং নিরুৎসাহিত করবে।
বর্তমানে যেসব বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করছে, তাদের অধিকাংশেরই অবকাঠামো, গবেষনাগার,নিজস্ব শিক্ষকের স্বল্পতা রয়েছ ।সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের খণ্ডকালীন শিক্ষক হিসাবে নিয়োগ দিয়ে থাকেন। এতে বেসরকারি ও সরকারি উভয় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্যক্রম বিঘ্নিত হচ্ছে। এ প্রবণতা থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় অনেকের মাঝেই শিক্ষা বিস্তারের চেয়ে ব্যবসায়িকভাবে লাভবান হওয়ার প্রবণতা কাজ করে, এর অন্যতম কারণ আর্থীক স্বচ্ছলতা না থাকা ফলে বিশ্ববিদ্যালয়কে সাধারণ ব্যবসার মতো বিবেচনা করে থাকেন। কেউ যাতে বিশ্ববিদ্যালয়কে সাধারণ ব্যবসার মতো মনে করতে না পারেন, সে বিষয়ে দৃষ্টি রাখতে হবে।
মানসম্পন্ন ও যুগোপযোগী কারিগরি শিক্ষাকে সহজলভ্য এবং যথাসম্ভব সাশ্রয়ী করতে হবে। দক্ষ মানবসম্পদ সৃষ্টিতে কার্যকর উদ্যোগ নিতে হবে। কারণ, প্রতি বছর বিপুল পরিমাণ বিদেশি বাংলাদেশের শ্রমবাজারে প্রবেশ করছে। অন্যদিকে, দক্ষতার অভাবে বাংলাদেশিরা চাকরি পাচ্ছে না। প্রয়োজনে পিপিপির মাধ্যমে উপযুক্ত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে বেসরকারি খাত উপযোগী জনবলকে দক্ষ করে তুলতে হবে।
অন্তর্বর্তীকালীন সরকার বিভিন্ন খাতে সংস্কারের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। কিন্তু কোন খাতে কোন ধরনের সংস্কার হবে, তার প্রভাব অর্থনীতি ও জনজীবনে কতটা পড়বে-সে সম্পর্কে কেউ ধারণা করতে পারছেন না। তাই সরকার তার মেয়াদে কোন কোন সংস্কার করতে আগ্রহী এবং তার সম্ভাব্য প্রভাব কি হবে, তা বাজেট বক্তব্যে সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করা যেতে পারে। ব্যক্তি খাতের বিনিয়োগে গতি নেই। ফলে বর্ধিত কর্মসংস্থান সৃষ্টি হচ্ছে না। বিভিন্ন শিল্প কারখানা বন্ধের কারণে লাখো শ্রমিক বেকার হয়েছে। কর্মসংস্থান ও অভ্যন্তরীণ উৎপাদন বাড়াতে বাজেটে বেসরকারি খাতের বিনিয়োগ উৎসাহিত করতে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেওয়া দরকার। কর ছাড় দেওয়ার ক্ষেত্রে সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা ও জবাবদিহি থাকতে হবে। প্রতি করছাড়ের আদেশ এর সাথে কত রাজস্ব ক্ষতি হলো তার একটা প্রাক্কলন দেওয়া।
বাজেট কাঠামো, বরাদ্দ এবং বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ অনেক দূর এগিয়েছে। বাজেটকে একটি উদ্ভাবনী এবং ব্যবসা-বান্ধব করার আকাঙ্ক্ষা সরকারের থাকলেও শেষ মুহূর্তের বিভিন্ন কারনে বিচ্যুতি ঘটে। যারফলে অনেক হতাশার সাথে, এটি কেবল সংখ্যার সমন্বয় সাধনের একটি এলোমেলো অনুশীলনে পরিণত হয়। সন্দেহ নাই আগামী ২০২৫-২০২৬ অর্থবছরের জন্য প্রস্তাবিত জাতীয় বাজেট নানা কারণেই ভিন্নতর হবে। এবার বাজেট জনবান্ধব,জাতীয় স্বার্থ সামাজিক উন্নয়ন ও মূল্যস্ফীতি প্রাধান্য পাবে, এটাই প্রত্যাশিত।
লেখক: ড. ইসরাত জাহান, অধ্যাপক এবং ডীন ব্যবসায় প্রশাসন সাউর্দান ইউনির্ভাসিটি
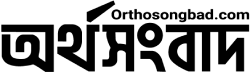
মত দ্বিমত
বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে দায়, দুর্নীতি ও আত্মসমালোচনার অনুপস্থিতি
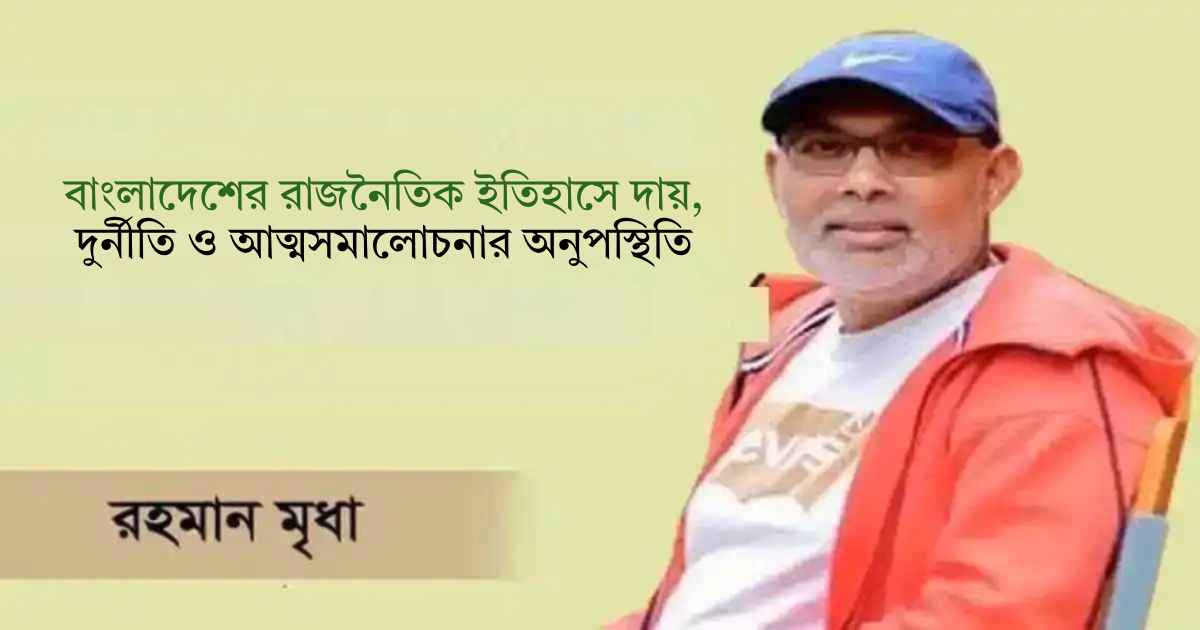
বাংলাদেশের রাজনীতিতে এখন এক অদ্ভুত রীতি গড়ে উঠেছে— দেশের যেকোনো ব্যর্থতা, দুর্নীতি বা অন্যায়ের দায় যেন সবসময় এক দলের ঘাড়েই পড়ে। যেন এ দেশের অন্য কারও কোনো পাপ নেই, কোনো অপরাধ নেই, কোনো দায় নেই। দেশে একটা প্রচলিত প্রবাদ আছে— “সব মাছে গু খায়, ঘাউরা মাছের দোষ হয়।” এই প্রবাদটাই যেন বাংলাদেশের রাজনৈতিক বাস্তবতার খোলামেলা প্রতিচ্ছবি।
গত পাঁচ দশকের ইতিহাস ঘাটলে দেখা যায়, ক্ষমতার মসনদে বসা প্রতিটি নেতা— শেখ মুজিব থেকে শুরু করে জিয়াউর রহমান, এরশাদ, খালেদা জিয়া কিংবা শেখ হাসিনা— সবাই কখনও না কখনও ক্ষমতার অপব্যবহার, দুর্নীতি, অন্যায় আর মানবাধিকার লঙ্ঘনের সঙ্গে জড়িত থেকেছেন। তবু আজ যখন ইতিহাসের বোঝা তোলা হয়, তখন সেই সব দোষের ভার যেন একচেটিয়াভাবে চাপিয়ে দেওয়া হয় আওয়ামী লীগের ঘাড়ে।
কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে— সব অপরাধ কি এক দলের?
দেশে যে রাজনৈতিক দুর্নীতি, নৈতিক অবক্ষয়, প্রশাসনিক অনাচার আর জনগণের প্রতি অবিচার চলেছে, তার মূল শেকড় তো বহু গভীরে — সব দলের শাসনকালেই এর জন্ম, বিকাশ, আর প্রাতিষ্ঠানিক রূপ। তাহলে কেন আজও এই জাতি সেই একই “ঘাউরা মাছের দোষ” সংস্কৃতির শিকার? বাংলাদেশের রাজনীতি যেন এক রসাতলে নেমে গেছে, যেখানে ক্ষমতার লোভ, দুর্নীতির প্রলোভন, এবং রাজনৈতিক প্রতিহিংসা মিলেমিশে তৈরি করেছে এক অদৃশ্য কিন্তু প্রাণঘাতী চক্র। আর সেই চক্রের ভেতরে থেকে সব দলই যেমন অপরাধে জড়িত, তেমনি নিজেদের দায় এড়াতে অন্যের ঘাড়ে দোষ চাপাতে ব্যস্ত।
আসুন, একটু জানি দেশের প্রেসিডেন্ট/প্রধানমন্ত্রীদের কুকর্ম ও তার ফলাফল সম্পর্কে
শেখ মুজিবুর রহমান (১৯৭২–১৯৭৫)
কুকর্ম: একদলীয় শাসনব্যবস্থা (BAKSAL) প্রতিষ্ঠা, রাজনৈতিক বিরোধীদের দমন, ১৯৭৪ সালের দুর্ভিক্ষে প্রশাসনিক ব্যর্থতা, জাতীয় রক্ষী বাহিনীর (Jatiya Rakkhi Bahini) মাধ্যমে গ্রেপ্তার, নির্যাতন ও বিচারবহির্ভূত হত্যা। তিনি এক নায়কতন্ত্র শাসন কায়েম করেন — শতভাগ ক্ষমতার অপব্যবহার ও দুর্নীতিগ্রস্ত পরিবারতন্ত্রের রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করেন।
ফলাফল: ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট সেনাবাহিনীর একদল অফিসারের হাতে নিহত হন।
জিয়াউর রহমান (১৯৭৭–১৯৮১)
কুকর্ম: সেনা অভ্যুত্থানের মাধ্যমে ক্ষমতা দখল, সরকারি তহবিলের অপব্যবহার, রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড ও ক্ষমতার অপব্যবহার। দলীয় স্বার্থে সামরিক প্রশাসনকে ব্যবহার করে গণতন্ত্রকে প্রহসনে পরিণত করেন।
ফলাফল: ১৯৮১ সালের ৩০ মে সেনা অভ্যুত্থানে নিহত হন।
হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদ (১৯৮২–১৯৯০)
কুকর্ম: সেনা অভ্যুত্থানের মাধ্যমে ক্ষমতা দখল, সংবিধান স্থগিত, নির্বাচনী প্রহসন, বিরোধী আন্দোলন দমন, ব্যাপক দুর্নীতি ও প্রশাসনিক অবক্ষয়। জনগণের কণ্ঠরোধ করে নিজের ক্ষমতা দীর্ঘায়িত করেন।
ফলাফল: তীব্র গণআন্দোলনের চাপে ক্ষমতা হারান; মৃত্যুর আগ পর্যন্ত দুর্নীতি ও রাজনৈতিক সমালোচনার মুখোমুখি থাকেন।
খালেদা জিয়া (১৯৯১–১৯৯৬, ২০০১–২০০৬)
কুকর্ম: দুর্নীতি মামলা (জিয়া অরফানেজ ট্রাস্ট, গ্যাটকো), রাজনৈতিক সহিংসতা, ২১ আগস্ট গ্রেনেড হামলার নেপথ্য অভিযোগ, মানবাধিকার লঙ্ঘন, প্রশাসনিক দুর্নীতি ও দলীয় সন্ত্রাস।
ফলাফল: দেশে ব্যাপক অস্থিরতা বৃদ্ধি; সেনা হস্তক্ষেপের পর ক্ষমতা হারান ও দীর্ঘদিন রাজনৈতিকভাবে অচল অবস্থায় থাকেন।
উৎস: আমার নিজের দেখা।
শেখ হাসিনা (২০০৯ – ২০২৪)
কুকর্ম: ছাত্র আন্দোলন দমন (১৪০০+ নিহত), গুম, নির্যাতন ও রাজনৈতিক প্রতিশোধমূলক মামলা, দুর্নীতি (পদ্মা সেতু, মেঘনা–গোমতি সেতু, পূর্বাচল প্লট বরাদ্দসহ), সংবাদমাধ্যম ও বিচার বিভাগের উপর দমননীতি। তিনি একদলীয় কর্তৃত্ববাদী শাসনের প্রতীক হয়ে ওঠেন— যেখানে দেশ, দল ও পরিবার একাকার হয়ে গেছে।
ফলাফল: আইনি অভিযোগ ও আন্তর্জাতিক সমালোচনার মুখেও ক্ষমতা ত্যাগ করেননি; শেষপর্যন্ত ‘সেফ একজিট’ চুক্তিতে ভারতে আশ্রয় নেন।
বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে এই নেতাদের কুকর্মের প্রতিফলন আজও সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রতিটি স্তরে রক্তক্ষরণের মতো দৃশ্যমান। কেউ ক্ষমতার নেশায় মানুষ হত্যা করেছে, কেউ জাতির সম্পদ লুটেছে, কেউ স্বাধীনতার নামে স্বাধীনতাকে বন্দি করেছে। অনেকে তাদের অপরাধের ফল ভোগ করেছে—কেউ গুলিতে নিহত, কেউ জনগণের রোষে অপদস্থ, কেউ দেশ ছেড়ে পালিয়ে বিদেশে নির্বাসিত জীবন কাটাচ্ছে। কিন্তু বিস্ময়কর সত্য হলো—একজনও স্বেচ্ছায় ক্ষমতা ত্যাগ করেননি। যেন ক্ষমতা তাদের কাছে এক ঈশ্বরত্ব, যার জন্য জীবন, নীতি, এমনকি দেশকেও উৎসর্গ করা যায়।
বাংলাদেশের রাজনৈতিক নেতা ও দলগুলোর আচরণে তাই এক ধরনের বেহায়া নির্লজ্জতা ও নৈতিক দেউলিয়াত্ব স্পষ্ট। জনগণের প্রতি দায়িত্ববোধ নেই, লজ্জা নেই, আত্মসমালোচনার ক্ষমতাও নেই। রাজনীতি এখন আর সেবা নয়, এক নির্মম প্রতিযোগিতা— কে বেশি দুর্নীতিগ্রস্ত, কে বেশি নিষ্ঠুর, কে ক্ষমতার চাবিকাঠি বেশি শক্ত করে ধরে রাখতে পারে। এই সংস্কৃতি রাজনৈতিক সহিংসতা, দুর্নীতি, এবং প্রশাসনিক অপব্যবহারের এক অন্ধকার যুগ সৃষ্টি করেছে, যেখানে রাষ্ট্রের শান্তি, ন্যায় ও স্থিতিশীলতা চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে গেছে।
উপরে তো কেবল সংক্ষিপ্তভাবে উল্লেখ করা হয়েছে টপ লেভেলের কিছু নেতার নাম, কিন্তু ভাবুন—যে অসংখ্য নেতা ও কর্মীর বিরুদ্ধে ভয়ঙ্কর অপরাধ, দুর্নীতি, হত্যা, মানবাধিকার লঙ্ঘন ও অর্থপাচারের অভিযোগ রয়েছে, তারা দিব্যি বিদেশে বিলাসবহুল জীবন কাটাচ্ছে। কেউ লন্ডনে, কেউ দুবাইয়ে, কেউ কানাডায়—সবাই নিরাপদ, অথচ দেশের আইন তাদের নাগাল পায় না।
প্রশ্ন জাগে—বিশ্বজুড়ে যখন আইনের এক জাল আছে, ইন্টারপোল নামের শক্তিশালী আন্তর্জাতিক সংস্থা রয়েছে, তখন গত ৫৪ বছরে তারা কি একজনকেও বাংলাদেশে ফেরত পাঠিয়েছে? না, একটিও না। কেন? কারণ, বাংলাদেশের আইন ও বিচারব্যবস্থা এতটাই দুর্বল, দলনির্ভর ও দুর্নীতিগ্রস্ত যে বিশ্বের কোনো দেশই আজ বাংলাদেশের ন্যায়বিচার ব্যবস্থার ওপর আস্থা রাখতে চায় না।
যখনই কোনো সরকার ক্ষমতা হারায়, তখনই হাজারো মিথ্যা মামলা, রাজনৈতিক প্রতিহিংসা ও প্রশাসনিক নিপীড়নের শিকার হয় পরাজিত পক্ষ। ফলে সত্য-মিথ্যা, অপরাধ-অভিযোগ— সবই মিশে গেছে এক অনিশ্চিত ধোঁয়াশায়। এই বাস্তবতাই প্রমাণ করে—আমরা জাতি হিসেবে কতটা দুরবস্থার শিকার, আর আন্তর্জাতিক অঙ্গনে আমাদের গ্রহণযোগ্যতা কতটা ক্ষয়প্রাপ্ত হয়েছে।
আমরা এখন এমন এক রাষ্ট্রব্যবস্থার বন্দি, যেখানে অপরাধীরা পালিয়ে যায়, কিন্তু ন্যায়বিচার পালানোর পথ খুঁজে পায় না। এখন যেমন সব দোষ শুধু আওয়ামী লীগের ওপর চাপানো হচ্ছে, তার কারণ যেমন;
১. দীর্ঘকাল ক্ষমতাসীন থাকা: দীর্ঘ সময় ক্ষমতায় থাকলে জনগণের প্রত্যাশা বাড়ে, হতাশাও বাড়ে। তাই সরকারের প্রতিটি ব্যর্থতা, প্রতিটি ক্ষোভ সরাসরি ক্ষমতাসীন দলের দিকেই ধাবিত হয়।
২. মিডিয়া ও রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা:বাংলাদেশের সংবাদমাধ্যম ও বিরোধী দলগুলোর একাংশ রাজনৈতিক হিসাবেই সব দোষ একপাক্ষিকভাবে প্রচার করে। তথ্যের চেয়ে আবেগ, যুক্তির চেয়ে প্রতিশোধ প্রবল।
৩. জনমতের মনস্তত্ত্ব: জনগণ প্রায়ই ব্যক্তিকে বিচ্ছিন্নভাবে বিচার করতে চায় না; বরং বৃহত্তম ও দৃশ্যমান শক্তিকে দোষারোপ করাই সহজ। আওয়ামী লীগ সেই দৃশ্যমান শক্তি—তাই দোষারোপের ভার তার ঘাড়েই পড়ে।
৪. প্রবাদের বাস্তব প্রতিফলন: বাংলাদেশ আজ সেই প্রবাদটির এক জীবন্ত প্রতিচ্ছবি— “সব মাছে গু খায়, ঘাউরা মাছের দোষ হয়।” সবাই অপরাধ করেছে, সবাই কুকর্মে জড়িত, কিন্তু দৃশ্যমান ও ক্ষমতাধর ঘাউরা মাছের ঘাড়েই এখন দোষের সমস্ত ভার চাপানো হচ্ছে।
বাংলাদেশে দুর্নীতি কোনো একক ব্যক্তি বা দলের সমস্যা নয়—এটি পুরো রাজনৈতিক সংস্কৃতির মজ্জাগত রোগে পরিণত হয়েছে। ক্ষমতা, সুবিধা, আর ব্যক্তিগত স্বার্থের অন্ধ নেশায় আজ রাজনীতি নীতিহীন, প্রশাসন জবাবদিহিহীন, আর জনগণ নিরুপায়।
•রাজনৈতিক স্বার্থ: ক্ষমতাসীন দল থেকে শুরু করে বিরোধী দল—সকলেই নিজেদের সুবিধার জন্য দুর্নীতি, ক্ষমতার অপব্যবহার এবং প্রশাসনিক জালিয়াতিতে জড়িয়ে পড়েছে। একে অপরকে দোষারোপ করলেও বাস্তবে তারা একই মুদ্রার এপিঠ-ওপিঠ।
•আইনি দুর্বলতা: বিচারব্যবস্থা পক্ষপাতদুষ্ট, তদন্ত সংস্থা ভীত, আর আইনের প্রয়োগ বেছে বেছে করা হয়। ফলে দুর্নীতি, মানবাধিকার লঙ্ঘন বা রাষ্ট্রদুর্বৃত্তি—সবই পার পেয়ে যায় ক্ষমতার ছায়াতলে।
•ভয় ও রাজনৈতিক চাপ: ক্ষমতাধর নেতাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিলে সেটি “রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র” বলে আখ্যা দেওয়া হয়, আর সেই অজুহাতে আইনি নীরবতা জারি থাকে। ফল—ন্যায়বিচারের বদলে ভয়ই হয়ে ওঠে রাষ্ট্রের নীতি।
•ফলাফল: শেখ হাসিনার শাসনকাল এই সংস্কৃতির চূড়ান্ত প্রতিচ্ছবি। দুর্নীতিগ্রস্ত প্রশাসন ও তোষণনীতি তাকে ক্ষমতায় টিকিয়ে রেখেছে, কিন্তু সেই সুরক্ষাই দেশকে আজ দুর্নীতির এক অশেষ চক্রে বন্দি করে ফেলেছে। তবে শ্রীলঙ্কা প্রমাণ করেছে—জনগণ যদি জাগে, দুর্নীতিগ্রস্ত শাসক টিকতে পারে না। সেখানে মানুষ রাস্তায় নেমে একসময় সর্বশক্তিমান রাজাপাক্ষেকে ক্ষমতা থেকে সরিয়ে দিয়েছে। তাদের এই গণঅভ্যুত্থান ছিল দুর্নীতির বিরুদ্ধে এক জাগ্রত জাতির গর্জন।
বাংলাদেশও ইতিহাসে এমন গণজোয়ার দেখেছে—স্বৈরাচারের পতন ঘটেছে, কিন্তু দুর্নীতির শিকড় রয়ে গেছে অটুট। কারণ, আমরা শাসক বদলেছি, কিন্তু রাজনৈতিক সংস্কৃতি বদলাতে পারিনি। যতদিন পর্যন্ত জনগণ সত্যিকার অর্থে নৈতিকভাবে সজাগ, ঐক্যবদ্ধ ও দৃঢ় হবে না—ততদিন দুর্নীতি, ক্ষমতার অপব্যবহার ও সহিংসতা বাংলাদেশের ভবিষ্যৎকে বন্দি রাখবে।
এখন কী করা উচিত?
১. দুর্নীতি ও সন্ত্রাসমুক্ত রাজনৈতিক সংস্কার: রাজনীতি হতে হবে সেবা, ক্ষমতা নয়। দলের আগে দেশ, আর দেশের আগে ন্যায়বোধ।
২. সততা ও স্বচ্ছতা: প্রশাসন ও দলীয় কাঠামোতে স্বচ্ছতা নিশ্চিত না হলে, কোনো সংস্কারই টেকসই নয়।
৩. আইন ও বিচারব্যবস্থার স্বাধীনতা: বিচারব্যবস্থাকে সম্পূর্ণ রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত করতে হবে—ন্যায়বিচার যেন কোনো দলের নয়, জনগণের অধিকার হয়।
৪. নাগরিক সচেতনতা: জনগণকে বুঝতে হবে, নীরবতা মানেই অপরাধের পক্ষে থাকা। প্রতিটি নাগরিককে দুর্নীতি ও অপব্যবহারের বিরুদ্ধে নিজের অবস্থান নিতে হবে।
৫. জনগণের অংশগ্রহণ: শুধু নির্বাচনে নয়—রাষ্ট্র পরিচালনার প্রতিটি পর্যায়ে জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে।
গণতন্ত্রকে টিকিয়ে রাখতে হলে গণচাপই হতে হবে দুর্নীতিবিরোধী অস্ত্র।
বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাস আজ এক নির্মম সত্যের সামনে দাঁড়িয়ে— ক্ষমতা কখনও কাউকে ন্যায়বান করেনি, বরং দুর্নীতিগ্রস্ত করেছে। এই দেশে অনেক নেতা নিহত হয়েছেন, কেউ স্বৈরাচারের পতনে অপমানিত, কেউ বিদেশে নির্বাসিত, কেউ আজও গোপনে অপরাধের দায় বহন করছে। কিন্তু একটিও ব্যতিক্রম নেই—কেউ স্বেচ্ছায় ক্ষমতা ত্যাগ করেননি।
ফ্রান্সের প্রধানমন্ত্রী রাজনৈতিক ব্যর্থতার দায় নিয়ে পদত্যাগ করেন, কিন্তু বাংলাদেশে নেতারা ব্যর্থতাকেও সাফল্য হিসেবে ঘোষণা করেন। এ যেন এক বেহায়া রাজনৈতিক সংস্কৃতি, যেখানে লজ্জা নেই, নীতি নেই, কেবল ক্ষমতার প্রতি অন্ধ আসক্তি। শেখ মুজিব থেকে শুরু করে জিয়াউর রহমান, এরশাদ, খালেদা জিয়া, শেখ হাসিনা— সবাই ক্ষমতার মোহে একই অপরাধ করেছেন, ভিন্ন সময়ে, ভিন্ন নাম নিয়ে। এ যেন এক দীর্ঘ শৃঙ্খল—একটি জাতির নৈতিক পতনের জীবন্ত ইতিহাস।
পাঁচ দশকের বাংলাদেশের রাজনীতি আমাদের এক কঠিন সত্যের মুখোমুখি দাঁড় করিয়েছে— আমাদের নেতাদের রাজনীতি এখন নীতিহীনতা, ক্ষমতার লালসা ও জনগণের আস্থা হারানোর প্রতীক। ভোট চুরি, দুর্নীতি, রাজনৈতিক হত্যা, গণহত্যা—এসব কেবল অতীতের কাহিনি নয়; আজও এগুলো দেশের শ্বাসরুদ্ধকর বাস্তবতা। যারা একসময় ক্ষমতার কেন্দ্রে ছিল, তাদের কুকর্মের ফলেই জন্ম নিয়েছে দীর্ঘ রাজনৈতিক অস্থিরতা, সমাজে বিভাজন, আর ন্যায়বিচারের প্রতি মানুষের আস্থা হারিয়ে গেছে। কিন্তু এই অন্ধকারের মাঝেও এখনো একটি আশার আলো জ্বলছে।
বাংলাদেশ এখনো পথ হারায়নি—যদি আমরা চাই, আমরা পারি একটি নতুন রাজনৈতিক সংস্কৃতি গড়ে তুলতে। যা এখন করা জরুরি
১. গণতান্ত্রিক সংস্কার বাস্তবায়ন: দুর্নীতি ও ক্ষমতার অপব্যবহার রোধে প্রতিটি নেতা ও দলকে জবাবদিহির আওতায় আনতে হবে।
কেউই আইনের ঊর্ধ্বে নয়—প্রত্যেক শাসককে তার কর্মের দায় নিতে হবে।
২. আইনের শাসন ও বিচারব্যবস্থার স্বাধীনতা: বিচার যেন আর কোনো দলের বা ক্ষমতার নয়, কেবল সত্য ও জনগণের হয়। দোষী নেতা, যে দলেরই হোক, আইনের সামনে সমানভাবে দাঁড়াবে—এই বিশ্বাস ফিরিয়ে আনতে হবে।
৩. সচেতন ও সক্রিয় জনগণ: জনগণই রাষ্ট্রের মালিক—এই চেতনা ফিরিয়ে আনতে হবে। শ্রীলঙ্কার মতো গণঅভ্যুত্থান প্রমাণ করেছে, যখন জনগণ জাগে, দুর্নীতি পালায়। বাংলাদেশেও সেই শক্তি আছে, শুধু ঐক্য আর সাহসের প্রয়োজন।
৪. দুর্নীতিমুক্ত রাজনৈতিক সংস্কৃতি: রাজনীতিকে পুনরায় নৈতিকতা ও দায়িত্ববোধে ফিরিয়ে আনতে হবে। সাংবাদিক, প্রশাসক, শিক্ষক, ব্যবসায়ী—প্রত্যেকে নিজের জায়গা থেকে সৎ থাকতে হবে। কারণ দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াই কেবল সরকারের নয়, সমগ্র জাতির।
বাংলাদেশের পাঁচ দশকের ইতিহাস আমাদের শেখায়— ক্ষমতার মোহ শেষ পর্যন্ত কাউকে রক্ষা করেনি। শেখ মুজিব থেকে শেখ হাসিনা পর্যন্ত সকল শাসকের কুকর্মের ফলাফল এক— মৃত্যু, নির্বাসন, অস্থিরতা ও জনগণের বিশ্বাস হারানো। কিন্তু প্রশ্ন হলো—আমরা কি কিছুই শিখিনি? দেশকে শান্তির পথে ফেরাতে এখনই প্রয়োজন সততা, নৈতিকতা, দায়িত্ববোধ এবং জনগণের একাগ্রতা। আমাদের ভোট, আমাদের প্রতিবাদ, আমাদের সাহস— এই তিনই পারে বাংলাদেশকে দুর্নীতি, লোভ আর স্বৈরাচারের অন্ধকার থেকে উদ্ধার করতে। কোনো অপরাধই গ্রহণযোগ্য নয়। আমাদের লক্ষ্য হতে হবে একটি দুর্নীতিমুক্ত, ন্যায়ভিত্তিক ও শান্তিপূর্ণ বাংলাদেশ। শ্রীলঙ্কার উদাহরণ দেখিয়েছে, জনগণ চাইলে ক্ষমতার অপব্যবহার থামানো যায়।
তাহলে প্রশ্ন জাগে— আজকের বাংলাদেশে কত শতাংশ মানুষ সত্যিই দুর্নীতিমুক্ত? আমরা কি নিজেরাই দুর্নীতির অংশ হয়ে যাচ্ছি না অজান্তেই? যে জাতি নিজের নৈতিকতার কাছে সৎ, সেই জাতির পথ কেউ রোধ করতে পারে না। বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ এখন আমাদের হাতে—সৎ, সাহসী এবং ঐক্যবদ্ধ নাগরিকদের হাতে।
রহমান মৃধা, গবেষক ও লেখক, সাবেক পরিচালক, ফাইজার, সুইডেন। Rahman.Mridha@gmail.com
মত দ্বিমত
একটি নতুন বাংলাদেশের আশা ও হতাশা: সত্যের মুখোমুখি সময়
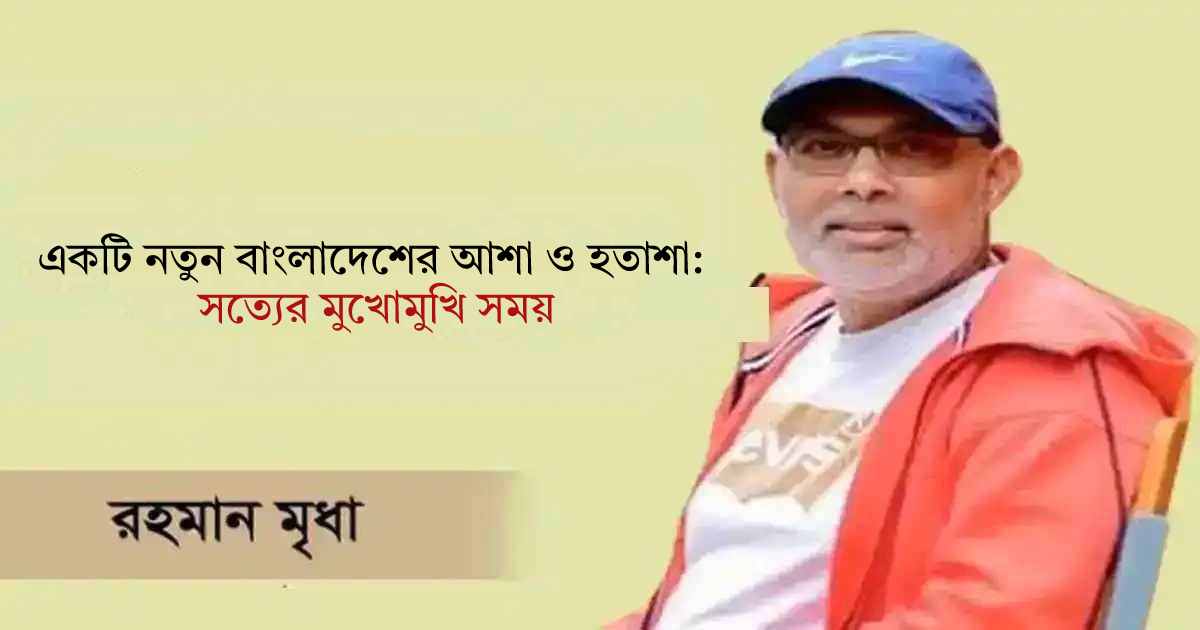
বাংলাদেশের জন্মলগ্ন ছিল একই সঙ্গে আনন্দ ও বিষাদের এক অনন্য অধ্যায়। একদিকে স্বাধীনতার আনন্দ, অন্যদিকে লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে অর্জিত এক দেশ। তখন আমাদের প্রতিজ্ঞা ছিল— “একটি সোনার বাংলাদেশ গড়ব আমরা, নতুন করে আজ শপথ নিলাম: প্রথম বাংলাদেশ আমার শেষ বাংলাদেশ, জীবন বাংলাদেশ আমার মরণ বাংলাদেশ।”
কিন্তু স্বাধীনতার সেই স্বপ্ন আজও অপূর্ণ। ২০২৪ সালের ৫ আগস্ট আবারও এক ঐতিহাসিক মুহূর্তে দেশ নতুন করে জেগে উঠেছিল— নতুন প্রজন্মের নেতৃত্বে গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের আন্দোলনে স্বৈরাচার পতনের মাধ্যমে সৃষ্টি হয়েছিল এক নতুন উদ্দীপনা, এক নতুন বাংলাদেশ।
অপ্রত্যাশিত পরিণতি ও হতাশার সূচনা
কিন্তু সেই বাংলাদেশ আজ স্বপ্নভঙ্গের পথে। আমি কষ্ট পাই কারণ ভেবেছিলাম—ড. ইউনুসের নেতৃত্বে আমরা হয়তো সত্যিকার অর্থে একটি নতুন, গণতান্ত্রিক ও মানবিক বাংলাদেশ গড়তে পারবো। কিন্তু বাস্তবতা ভিন্ন। বিচারপতি থেকে রাষ্ট্রপতি, সেনাপ্রধান থেকে পুলিশ প্রধান, প্রশাসন থেকে রাজনৈতিক দল—প্রায় সর্বত্রই দুর্নীতি, প্রভাব, আত্মস্বার্থ ও জবাবদিহির অভাব স্পষ্ট। এই অবস্থায় কীভাবে একটি স্বাধীন, সার্বভৌম ও গণতান্ত্রিক সোনার বাংলা গড়া সম্ভব?
বাস্তব প্রেক্ষাপট ও সাম্প্রতিক ইতিহাস (৫ আগস্ট ২০২৪–এর পর)
২০২৪ সালের ৫ আগস্ট, তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ব্যাপক ছাত্র-জনতার আন্দোলনের মুখে পদত্যাগ করেন এবং দেশ ত্যাগ করেন। দেশজুড়ে উত্তেজনা, বিশৃঙ্খলা ও সহিংসতার পর এক অন্তর্বর্তীকালীন প্রশাসন দায়িত্ব নেয়— নেতৃত্বে ছিলেন নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ ড. মুহাম্মদ ইউনুস।
প্রথমদিকে অনেকেই আশা করেছিলেন—এই সরকার হবে পরিবর্তনের প্রতীক, দুর্নীতি-নির্মূল ও প্রতিষ্ঠান-সংস্কারের সূচনা। কিন্তু সময়ের পরিক্রমায় দেখা গেল, প্রধান অপরাধী বা ক্ষমতার দখলদাররা এখনও অক্ষত, আর কিছু নিরীহ মানুষ হয়রানির শিকার হচ্ছে।
শেখ হাসিনা ও তাঁর ঘনিষ্ঠদের বাইরে, রাষ্ট্রের উচ্চপদস্থ অনেকেই এখনও দায়মুক্ত। রাষ্ট্রপতি, প্রধান বিচারপতি, সেনাপ্রধান, পুলিশপ্রধান—এদের ভূমিকা ও দায় নিয়ে কোনো কার্যকর তদন্ত বা বিচার হয়নি। অথচ প্রশাসনের অনেক ছোট কর্মচারী বা নিরপেক্ষ ব্যক্তিরা অভিযোগ বা হয়রানির মুখে পড়েছেন।
গভীর সংকট: কেন পরিবর্তন এলেও কাঠামো অপরিবর্তিত?
বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় কাঠামো এখনো ব্যক্তি-নির্ভর, প্রতিষ্ঠান-নির্ভর নয়। বিচারব্যবস্থা, নির্বাচন কমিশন, দুর্নীতি দমন কমিশন—সব জায়গায় রাজনৈতিক প্রভাব স্পষ্ট। প্রশাসন ও নিরাপত্তা বাহিনীর উচ্চপদস্থদের বড় অংশ অতীতে রাজনৈতিক আনুগত্যে ক্ষমতার অংশীদার হয়েছেন। ফলে নতুন সরকার গঠনের পরও একই গোষ্ঠী গুরুত্বপূর্ণ পদে থেকে গেছে। বাংলাদেশের গণমাধ্যম এখন সত্য বলতে ভয় পায়—একদিকে সেন্সরশিপ, অন্যদিকে নিরাপত্তা ঝুঁকি। ফলে রাষ্ট্রীয় অন্যায়ের বিরুদ্ধে জনমত তৈরির ক্ষেত্র সংকুচিত।
জনগণের অবস্থা: ভয়, বিভ্রান্তি ও নিরাশা
আজ বাংলাদেশের সাধারণ মানুষ দ্বিধায়, কেউ ভয় পায়, কেউ পথভ্রষ্ট। তারা জানে— সত্য কথা বলা মানে বিপদ ডেকে আনা। অথচ সত্য না বললে জাতি আরও অন্ধকারে তলিয়ে যাবে।
আমি চল্লিশ বছরের বেশি সময় ধরে দেশের জন্য লড়াই করেছি। প্রবাসে থেকে রেমিট্যান্স পাঠিয়ে দেশের মানুষের ভাগ্য উন্নয়নের চেষ্টা করেছি। আমি দুর্নীতির সঙ্গে জড়িত নই, আমি রাষ্ট্রের অন্ন ধ্বংস করিনি।
তাই আমার অধিকার আছে সত্য বলার— কারণ সত্যই একদিন জাতির মুক্তির পথ দেখাবে।
বিশ্লেষণাত্মক প্রবাহ (A–Z Analysis Flow)
A. ঘটনার সারমর্ম
– ৫ আগস্ট ২০২৪: ক্ষমতাসীন সরকারের পতন
– অন্তর্বর্তীকালীন প্রশাসনের আগমন
– বিচার ও পুনর্গঠন প্রক্রিয়ার অগ্রগতি স্থবির
B. মূল সমস্যা
– অপরাধীদের দায় নির্ধারণে অনীহা
– প্রশাসনের উচ্চস্তরের দুর্নীতি
– গণতন্ত্রে আস্থা হারানো জনগণ
C. প্রভাব
– রাষ্ট্রীয় অচলাবস্থা
– আন্তর্জাতিক আস্থাহীনতা
– অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তা ও রাজনৈতিক হতাশা
D. কারণসমূহ
– আইন-শাসনের দুর্বলতা
– রাজনৈতিক প্রভাব ও দলীয় স্বার্থ
– গণমাধ্যম ও নাগরিক সমাজের ভয়ের সংস্কৃতি
E. সম্ভাব্য সমাধান কাঠামো
1. স্বাধীন তদন্ত কমিশন
2. বিচার বিভাগীয় সংস্কার
3. স্বচ্ছ নির্বাচন প্রস্তুতি
4. গণমাধ্যম স্বাধীনতা নিশ্চিতকরণ
5. দুর্নীতি দমন ব্যবস্থার বাস্তবায়ন
গণতান্ত্রিক ও গ্রহণযোগ্য প্রস্তাবনা
১. স্বাধীন তদন্ত কমিশন — আন্তর্জাতিক মানদণ্ডে স্বচ্ছ কমিশন গঠন; আইনজীবী, নাগরিক সমাজ ও আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষক অন্তর্ভুক্তি।
২. নির্বাচন কমিশন পুনর্গঠন — সব দলের সমঝোতায় পেশাগত যোগ্যতার ভিত্তিতে নতুন কমিশন নিয়োগ ও নির্দিষ্ট সময়সূচি ঘোষণা।
৩. গণমাধ্যমের স্বাধীনতা — সাংবাদিকদের নিরাপত্তা ও মতপ্রকাশের স্বাধীনতা নিশ্চিত করা।
৪. বিচার বিভাগ ও আইন সংস্কার — আদালতের ডিজিটাল কেস-ট্র্যাকিং ও প্রকাশ্য শুনানি চালু করা।
৫. দুর্নীতি প্রতিরোধ — সরকারি কর্মচারীদের সম্পদ ঘোষণা বাধ্যতামূলক করা ও অনলাইন স্বচ্ছতা পোর্টাল চালু।
দীর্ঘমেয়াদি নীতি ও কাঠামোগত সংস্কার
১. শিক্ষায় নাগরিক চেতনা — গণতন্ত্র, মানবাধিকার ও নাগরিক দায়িত্ববোধ শিক্ষা।
২. অর্থনৈতিক ন্যায্যতা — প্রবাসী ও ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের জন্য প্রণোদনা ও স্বচ্ছ বিনিয়োগ নীতি।
৩. নাগরিক তদারকি কাঠামো — মিডিয়া, এনজিও ও নাগরিক সংগঠনের মাধ্যমে টেকসই জবাবদিহি ব্যবস্থা গঠন।
শেষ কথা: সত্যের পথে, নতুন বাংলাদেশের ডাক
বাংলাদেশ এখন এক সন্ধিক্ষণে। স্বাধীনতার সময় যেমন আমরা শপথ নিয়েছিলাম, আজ আবার সেই শপথ নিতে হবে— “আমরা দুর্নীতিমুক্ত, স্বচ্ছ ও মানবিক বাংলাদেশ গড়বো—যেখানে শাসনব্যবস্থা জনগণের সেবায় নিবেদিত থাকবে।” আমি বিশ্বাস করি, সত্য প্রকাশই জাতির পুনর্জাগরণের প্রথম ধাপ। ভয় নয়, দায়িত্বই আমাদের পথ দেখাবে।
রহমান মৃধা
গবেষক ও লেখক
সাবেক পরিচালক, ফাইজার, সুইডেন
Rahman.Mridha@gmail.com
মত দ্বিমত
ব্যক্তির আগে দল, দলের আগে দেশ
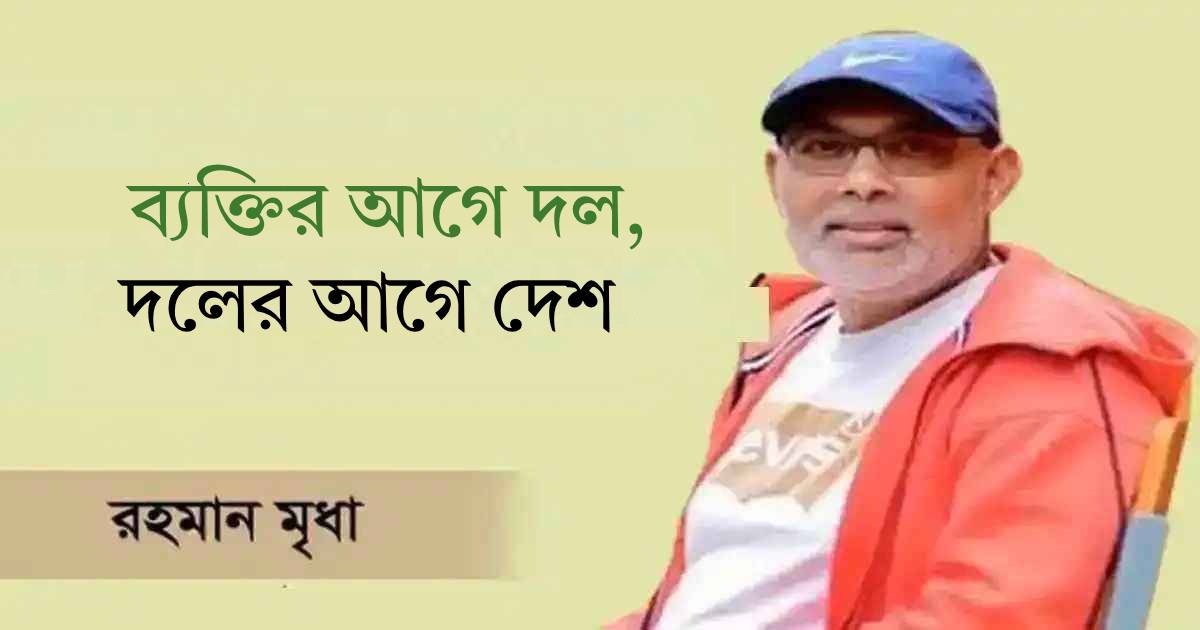
ব্যক্তির আগে দল, দলের আগে দেশ। যদি এই কথাটি সত্যিই আমাদের মনের কথা হয়, তবে এখনই সময় নিজের দিকে তাকানোর। চাঁদাবাজ, সন্ত্রাসী, দুর্নীতিবাজ, মিথ্যাবাদী এবং অশিক্ষিত ধান্দাবাজদের মনোনয়ন দিয়ে দেশকে আর বিপদের দিকে ঠেলে দেওয়া যাবে না। রাজনীতি আজ ব্যবসা হয়ে গেছে, ক্ষমতা মানে এখন লুটপাটের প্রতিযোগিতা। অথচ দেশের মানুষ আরেকটা সুযোগ চায়— এমন নেতৃত্বের, যারা দেশকে ভালোবাসে, কাজ জানে, মিথ্যা প্রতিশ্রুতি নয়, ফলাফল দিতে পারে।
আজ আমাদের প্রয়োজন দক্ষ, সুশিক্ষিত, প্রভাবশালী এবং আন্তর্জাতিক মানসচেতন কর্মী-নেতা, যারা নিজের কর্মদক্ষতা ও সততা দিয়ে সমাজের উন্নয়ন করবে, নাগরিকদের উপর বোঝা হবে না। দেশ ভালো থাকলে দলও ভালো থাকবে; আর দল ভালো থাকলে ব্যক্তিও সম্মান পাবে— এটাই রাষ্ট্রচিন্তার প্রকৃত পথ। বাংলাদেশের অর্থনীতি আজ পরিসংখ্যানের খেলা। জিডিপি-র হার, রপ্তানির অঙ্ক, রেমিট্যান্স— সবকিছু শুনতে ভালো লাগে, কিন্তু গ্রামে গিয়ে দেখা যায় বাস্তব চিত্র সম্পূর্ণ উল্টো। চাকরি নেই, দ্রব্যমূল্য বেড়েছে, ব্যাংকের খেলাপি ঋণ ভয়াবহ।
এখন দরকার দক্ষতা-ভিত্তিক অর্থনীতি। যেখানে তরুণরা হবে উৎপাদনের চালিকাশক্তি, যেখানে বিদেশে শ্রম পাঠানোর বদলে দেশেই কাজের সুযোগ সৃষ্টি হবে। সরকারি প্রকল্পে জবাবদিহি নিশ্চিত করতে হবে, ব্যাংক লুটেরাদের বিচার করতে হবে, এবং উদ্যোক্তাদের প্রকৃত উৎসাহ দিতে হবে— তবেই অর্থনীতি হবে স্থিতিশীল, আত্মনির্ভর ও টেকসই।
শিক্ষা আজ পেশা নয়, প্রতিযোগিতা। স্কুল-কলেজে মুখস্থবিদ্যা, বিশ্ববিদ্যালয়ে রাজনীতিকরণ, শিক্ষকতার পেশায় অবমূল্যায়ন— এভাবে কোনো জাতি আলোকিত হয় না। আজ আমাদের দরকার এমন শিক্ষা যা চিন্তা করতে শেখায়, প্রশ্ন করতে শেখায়, মানুষ হতে শেখায়। প্রত্যেক ছাত্রকে বাস্তবজ্ঞান ও নৈতিকতার শিক্ষা দিতে হবে। শিক্ষককে রাজনীতির চাপ থেকে মুক্ত রাখতে হবে। গবেষণা, উদ্ভাবন ও প্রযুক্তিকে জাতীয় উন্নয়নের মূল কৌশল হিসেবে ধরতে হবে। শিক্ষাকে মানবিক ও মুক্তচিন্তার চর্চার জায়গায় ফিরিয়ে আনা ছাড়া জাতির অগ্রগতি সম্ভব নয়। যে দেশ নিজের সংস্কৃতি হারায়, সে দেশ নিজের আত্মাকে হারায়।
আজকের বাংলাদেশে সংস্কৃতি রাজনীতির যন্ত্র হয়ে গেছে। সংগীত, নাটক, সাহিত্য, চলচ্চিত্র—সবখানেই বিভাজন। এই অবস্থা থেকে বেরিয়ে এসে রাষ্ট্রকে সংস্কৃতির পুনর্জাগরণের কাজ হাতে নিতে হবে। সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে রাজনীতি থেকে মুক্ত করতে হবে, শিল্পীদের মর্যাদা ফিরিয়ে দিতে হবে। কারণ সংস্কৃতি শুধু বিনোদন নয়— এটি জাতির বিবেক, সহনশীলতা ও মানবিকতার মূলভিত্তি। বাংলাদেশে এখন অসুস্থ মানুষ নয়, স্বাস্থ্যব্যবস্থাই অসুস্থ। সরকারি হাসপাতালগুলিতে ওষুধ নেই, বেসরকারি হাসপাতালে খরচ অসহনীয়। মানুষ চিকিৎসা নয়, মর্যাদা হারাচ্ছে।
এখন সময় এসেছে জনসেবা ভিত্তিক স্বাস্থ্যব্যবস্থা গড়ার— যেখানে প্রতিটি ইউনিয়নে থাকবে নার্স-নেতৃত্বাধীন ক্লিনিক, টেলেমেডিসিন, মানসিক স্বাস্থ্য সহায়তা, এবং ওষুধের দাম নিয়ন্ত্রণে সুনির্দিষ্ট নীতি। স্বাস্থ্যসেবা হবে মানবিক—এটাই নাগরিক রাষ্ট্রের পরিচয়। বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় শক্তি এখন তরুণ প্রজন্ম, আবার সবচেয়ে বড় ঝুঁকিও তারা। প্রতিদিন হাজার হাজার শিক্ষিত তরুণ কর্মহীন হয়ে পড়ছে। তারা যদি নিজের প্রতিভা ও শক্তি কাজে লাগাতে না পারে, তবে হতাশা সমাজে বিস্ফোরণ ঘটাবে। এখন সময় দক্ষতা-কেন্দ্রিক কর্মসংস্থানের। প্রতিটি জেলায় টেকনিক্যাল ট্রেনিং সেন্টার, ভোকেশনাল শিক্ষা, উদ্যোক্তা উন্নয়ন ও স্থানীয় শিল্প পুনরুজ্জীবনের কর্মসূচি নিতে হবে।
দেশে কাজের সুযোগ তৈরি করতে পারলে কেউ আর বিদেশে শ্রম বিক্রি করতে যাবে না— তখন বাংলাদেশ সত্যিকারের শক্তিশালী রাষ্ট্রে পরিণত হবে। দুর্নীতি এখন কেবল অর্থনৈতিক নয়, এটি নৈতিক মহামারী।
দুর্নীতিবাজ রাজনীতিকরা রাষ্ট্রযন্ত্র দখল করে রেখেছে, আর সাধারণ মানুষ প্রতিদিন মর্যাদাহানির শিকার হচ্ছে। এই দুষ্টচক্র ভাঙতে হলে দরকার রাজনৈতিক সদিচ্ছা ও জনগণের অংশগ্রহণ। মনোনয়ন দেওয়ার আগে শিক্ষা, সততা ও সামাজিক অবদান যাচাই বাধ্যতামূলক করতে হবে। দ্রুত বিচারব্যবস্থা চালু করতে হবে, দুর্নীতির মামলায় দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিতে হবে।
প্রতিটি সরকারি প্রকল্পের অডিট রিপোর্ট জনসমক্ষে প্রকাশ করতে হবে। জবাবদিহিতা ছাড়া উন্নয়ন কাগজে সীমাবদ্ধ থাকবে— বাস্তবে নয়। এখন সময় নতুন রাজনৈতিক চিন্তার— যেখানে ক্ষমতার কেন্দ্র মানুষ, দলের নয়; যেখানে নেতৃত্ব মানে সেবা, শাসন নয়। মনোনয়ন দিতে হবে সেইসব মানুষকে যারা রাজনীতি নয়, কর্ম দিয়ে দেশ গড়তে চায়। যাদের হাতে দেশের ভবিষ্যৎ নিরাপদ, যাদের মস্তিষ্কে পরিকল্পনা, আর হৃদয়ে দেশপ্রেম।
অ্যাওনেক্স: ব্ল্যাকবক্স মনিটরিং— দেশ ও নেতৃত্বের জবাবদিহির নতুন দিগন্ত
আজকের বিশ্বে প্রযুক্তি শুধু আমাদের জীবনকেই সহজ করেনি, রাষ্ট্র পরিচালনাকেও দিয়েছে নতুন দৃষ্টিকোণ। রাজনীতিতে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি আনতে এখন দরকার এক নতুন ধরনের নজরদারি ব্যবস্থা — যেখানে ক্ষমতা মানে দায়িত্ব, আর নেতৃত্ব মানে নাগরিক আস্থার প্রতিশ্রুতি। এই উদ্দেশ্যেই প্রস্তাব করা হচ্ছে “মেমোরিবল আর্কাইভ ও ডিজিটাল ব্ল্যাকবক্স সিস্টেম”—একটি প্রযুক্তিনির্ভর মনিটরিং ব্যবস্থা, যা প্রতিটি নির্বাচিত প্রতিনিধির কাজ, সিদ্ধান্ত ও জনসম্পৃক্ততা নথিবদ্ধ রাখবে তাদের দায়িত্বকাল জুড়ে। যেমন বিমানের ব্ল্যাকবক্স যাত্রীদের নিরাপত্তার নীরব সাক্ষী, তেমনি রাষ্ট্রের ব্ল্যাকবক্স হবে জনগণের বিশ্বাসের রক্ষক।
১. উদ্দেশ্য ও সারমর্ম
এই ব্যবস্থার মূল লক্ষ্য হলো রাজনীতিকে স্বচ্ছ ও নাগরিকমুখী করা। নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি কীভাবে কাজ করছেন, কোথায় ভুল হচ্ছে, কোথায় সাফল্য—সব কিছু নিরপেক্ষভাবে সংরক্ষিত থাকবে এই ব্ল্যাকবক্সে। এটি হবে একধরনের “নৈতিক আয়না”, যাতে জনগণ দেখতে পাবে তাদের প্রতিনিধি সত্যিই জনগণের সেবায় নিয়োজিত কি না।
২. ধাপে ধাপে বাস্তবায়ন
প্রথম পর্যায়ে কয়েকটি জেলা বেছে নিয়ে পরীক্ষামূলকভাবে শুরু করা হবে। রাজনীতিবিদ, বিশেষজ্ঞ ও সাধারণ নাগরিকদের অংশগ্রহণে এই প্রকল্পের ফলাফল দেখা হবে। এরপর ধীরে ধীরে পুরো দেশজুড়ে বিস্তৃত হবে। এটি কোনো দমননীতি নয়, বরং সহযোগিতার উদ্যোগ—যাতে ভালো রাজনীতিবিদদের মর্যাদা আরও বাড়ে, আর দুর্নীতি বা অপব্যবহার রোধ করা যায় প্রমাণসহ।
৩. প্রযুক্তি সহজভাবে
এই ব্ল্যাকবক্স একধরনের সুরক্ষিত ডিজিটাল লগবুকের মতো। রাজনীতিবিদের কাজের নথি, সরকারি প্রকল্প, অর্থনৈতিক সিদ্ধান্ত, জনসেবা কার্যক্রম ইত্যাদি এখানে সংরক্ষিত থাকবে। সব তথ্য থাকবে নিরাপদ ও পরিবর্তন-অযোগ্য। কেবল অনুমোদিত সংস্থা ও আদালত প্রয়োজনে এসব তথ্য দেখতে পারবে। জনগণের জন্য থাকবে একটি সাধারণ অনলাইন পোর্টাল—যেখানে তারা দেখতে পারবে তাদের এলাকার জনপ্রতিনিধির কার্যক্রমের সারসংক্ষেপ।
৪. তথ্যের নিরাপত্তা ও গোপনীয়তা
প্রত্যেকটি তথ্যের উৎস, সময় ও প্রেক্ষাপট সংরক্ষিত থাকবে যেন কেউ মিথ্যা তথ্য যোগ বা বাদ দিতে না পারে। তবে ব্যক্তিগত ও পারিবারিক গোপনীয়তা পুরোপুরি সুরক্ষিত থাকবে—এই প্রকল্পের উদ্দেশ্য কারও ব্যক্তিগত জীবন উন্মোচন করা নয়, বরং দায়িত্বের সীমারেখায় জবাবদিহি নিশ্চিত করা।
৫. আইন ও নীতি
এই ব্যবস্থাকে সফল করতে হবে আইনি কাঠামো ও নাগরিক অংশগ্রহণের মাধ্যমে। এজন্য একটি স্বাধীন মনিটরিং কমিশন গঠন করা হবে, যেখানে থাকবে নাগরিক প্রতিনিধি, বিচারিক সদস্য ও প্রযুক্তিবিদরা। যদি কোনো রাজনীতিবিদ দুর্নীতি বা অনৈতিক কাজের সঙ্গে যুক্ত থাকেন, প্রমাণের ভিত্তিতে তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। কিন্তু কোনো রাজনৈতিক প্রতিহিংসা এই ব্যবস্থার অংশ হবে না।
৬. মূল্যায়ন ও প্রভাব
ছয় মাসের পাইলট প্রকল্প শেষে দেখা হবে—দুর্নীতি কতটা কমেছে, কাজের গতি বেড়েছে কিনা, জনগণের আস্থা কেমন। যদি দেখা যায় সরকারি প্রকল্পে অপচয় কমে, সিদ্ধান্ত গ্রহণে গতি আসে এবং নাগরিক সন্তুষ্টি বৃদ্ধি পায়, তবে সেটিই হবে এই উদ্যোগের প্রকৃত সফলতা।
৭. মানবসম্পদ ও বাজেট
এই প্রকল্পে কাজ করবেন দেশীয় তরুণ প্রযুক্তিবিদ, তথ্য বিশ্লেষক, আইনি বিশেষজ্ঞ ও ফিল্ড অফিসাররা। এর ফলে শুধু রাজনীতির নয়, কর্মসংস্থান ও দক্ষতা উন্নয়নেও আসবে নতুন দিগন্ত।
৮. ঝুঁকি ও সমাধান
রাজনৈতিক বাধা বা প্রযুক্তিগত চ্যালেঞ্জ আসতেই পারে। তাই প্রকল্পের পরিচালনায় সব দলের প্রতিনিধিকে অন্তর্ভুক্ত করা জরুরি, যেন এটি কোনো দলের নয়—পুরো জাতির উদ্যোগ হয়ে ওঠে। নিয়মিত স্বাধীন অডিট হবে, যাতে নাগরিকের আস্থা অটুট থাকে।
৯. সাফল্যের মাপকাঠি
যদি এই ব্যবস্থার মাধ্যমে সরকারি ব্যয়ের অপচয় অন্তত ৩০% কমে, সিদ্ধান্ত গ্রহণের সময়সীমা কমে এবং নাগরিক আস্থা সূচক বাড়ে—তবে বোঝা যাবে বাংলাদেশ সত্যিই এক নতুন যুগে প্রবেশ করেছে।
১০. শেষ কথা
এই প্রকল্প শুধু প্রযুক্তি নয়—এটি একটি মানসিক বিপ্লব। যেখানে নেতৃত্ব আর ক্ষমতা নয়, দায়িত্ব। যেখানে নাগরিক কণ্ঠস্বরই রাষ্ট্রের শক্তি। একটি স্মার্ট ব্ল্যাকবক্স হয়তো রাজনীতিবিদের ভুল ঠিক করতে পারবে না, কিন্তু এটুকু নিশ্চয়তা দেবে—ভুল আর চিরদিন গোপন থাকবে না।
রহমান মৃধা, সাবেক পরিচালক, ফাইজার, সুইডেন। Rahman.Mridha@gmail.com
মত দ্বিমত
বিশ্ব শিক্ষক দিবসে এক ব্যক্তিগত স্মৃতিচারণ ও দর্শন
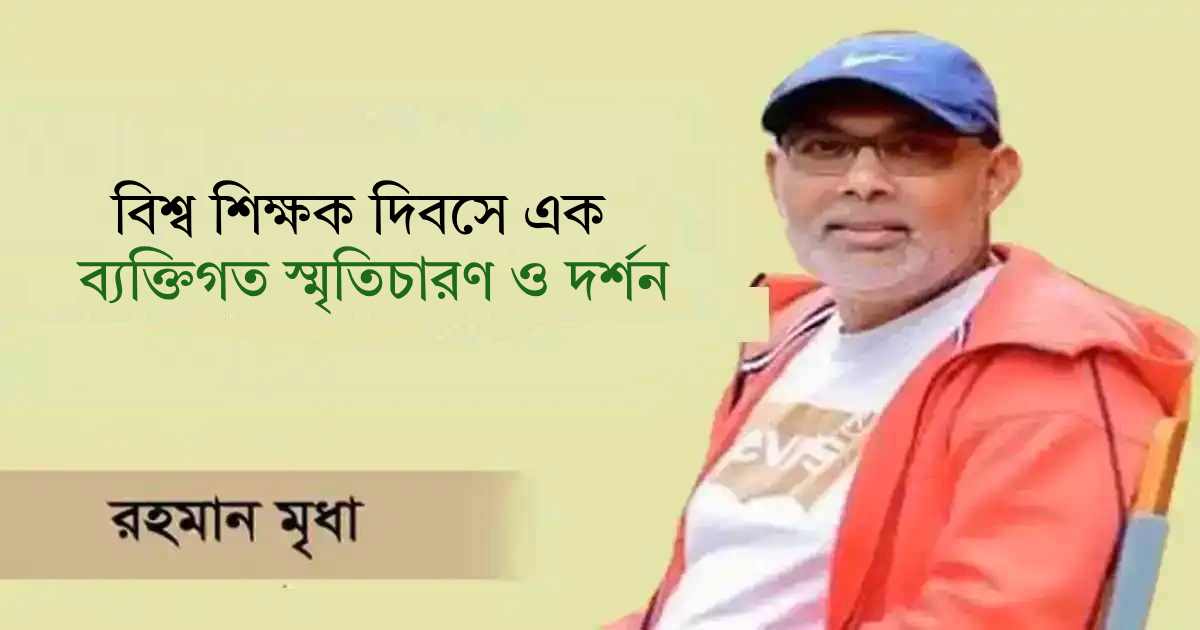
বিশ্ব শিক্ষক দিবসে সকল শিক্ষকের প্রতি সম্মান জানাতে গিয়ে আমার মন স্বভাবতই ছুটে যায় বাবা-মার কাছে। কারণ পৃথিবীর কোনো শ্রেণিকক্ষ, বিশ্ববিদ্যালয় কিংবা পাঠশালার আগে আমার শিক্ষা শুরু হয়েছিল ঘরেই—মায়ের আঁচল আর বাবার শাসনের ভেতর দিয়ে।
আমরা প্রায়শই ভুলে যাই, শিক্ষার সূচনা বই কিংবা বোর্ডে নয়—বরং ঘরের ভেতরেই। ‘প্রথম শিক্ষা মায়ের কোলেই শুরু হয়’—এই সত্য ইতিহাসের প্রতিটি সভ্যতাই স্বীকার করেছে। প্রাচীন ভারতীয় গুরুকুলে যেমন সন্তানকে প্রথম পাঠ শেখাতেন মা, তেমনি গ্রিক দার্শনিক সক্রেটিসও বলেছিলেন—“কোনো রাষ্ট্রের ভিত্তি জানতে চাইলে দেখো, সেই রাষ্ট্রের শিশুরা কেমন শিক্ষা পাচ্ছে।” আর সেই প্রথম শিক্ষালয় হলো পরিবার।
আজ ভোরে সংবাদমাধ্যমে দেখলাম, পাঁচ অক্টোবর বিশ্ব শিক্ষক দিবস আসছে। ভাবতে লাগলাম—প্রতিবছর আমরা কত শিক্ষাবিদকে স্মরণ করি, অথচ যাঁদের হাত ধরে আমাদের চরিত্র, নীতি আর মানবিকতার ভিত গড়ে ওঠে, সেই বাবা-মা সম্পর্কে কত সামান্যই বলা হয়!
আমার শৈশবের শিক্ষা ছিল ভিন্নধর্মী। মা ছিলেন স্নেহময়ী ছাত্রীসুলভ শিক্ষক। লেখাপড়ায় সাহায্য করতেন, কিন্তু খাওয়ার সময় অঙ্কে গড়মিল করতেন। আমি এক চামচ ঝোল চাইলে, তিনি ঝোলের সঙ্গে মাছের টুকরো ঢুকিয়ে দিতেন। বাবার কাছে চাইলে তিনি উল্টো বলতেন—“যতটুকু পেয়েছো, সেটা আগে শেষ করো, পরে দেখা যাবে।” মাকে রাগ করে ইংরেজিতে কিছু বললে তিনি হেসে দিতেন—মনে হতো কিছুই বোঝেননি। কিন্তু বাবা ঠিকই বুঝতেন; ভুল ইংরেজি বললে কান ধরে শাসন করতেন। মা ছিলেন বেশ মিথ্যেবাদী—না খেয়ে বলতেন খেয়েছি, খিদে নেই, তোরা খেয়ে নে। পরে বুঝেছি, খাবার কম হলে উনি আমাদের আগে খাওয়াতেন। বাবা ছিলেন কিছুটা সত্যবাদী—নিজের ক্ষুধা গোপন করে বলতেন, “তোমরা খাও, আমি পরে খাবো।” মা ছিলেন বোকা, কলুর বলদের মতো রান্নাঘরে ঢুকে আর বেরোতে পারেননি। জীবন কাটিয়েছেন কঠিন সংগ্রামের ভেতর দিয়ে। বাবা ছিলেন কঠিন, ঝড়-বৃষ্টি-রোদে সংসারের ভার কাঁধে নিয়েছেন।
বাবা-মা দুজনেই ছিলেন পাহারাদার। সন্ধ্যা হলে বাড়িতে না ফিরলে খবর ছিলো। সংসার চালিয়েছেন নীরবে, আমাদের কষ্ট বুঝতে দেননি। কখনো নির্লজ্জ, কখনো বেহায়া হয়ে আমাদের ঘরের বিছানা পর্যন্ত গুছিয়ে দিয়েছেন, খোঁজ নিয়েছেন কেমন চলছে জীবন।
মায়ের কমনসেন্স ছিল কিছুটা কম, বাবার একটু বেশি। মা প্লেট ফাঁকা দেখলেই খাবার ভরতেন, বাবা বলতেন— ‘অতিরিক্ত খেয়ো না।’ মা ছিলেন কেয়ারলেস—নিজের যন্ত্রণা ভুলে যেতেন। বাবা ছিলেন কেয়ারফুল—সংসারের ভার টেনে নিতেন চুপচাপ। মনে হতো দুজনেই ছিলেন আনস্মার্ট। মা দামী শাড়ি-গয়না পরতেন না, বাবা গাড়ি-বাড়ি-আড্ডা নিয়ে মাথা ঘামাতেন না। তবুও তাঁরা আমাদের স্বপ্ন বড় করতে শতভাগ সাহায্য করেছেন।
দুজনেই ছিলেন স্বার্থপর—নিজেদের জীবন উৎসর্গ করেছেন, নিজেদের ঘাম ঝরিয়ে পরিবারের স্বপ্ন গড়তে। তাঁরা জীবনভর আমাদের দিয়েছেন শুধু ভালোবাসা। আর আমরা সন্তানরা? কষ্ট দিয়েছি, অবহেলা করেছি, অথচ তাঁরা বদলাননি। প্রতিদিন আমাদের জন্য একই দোয়া, একই মায়া। বড় হয়েও আমরা তাঁদের উপেক্ষার বোঝা চাপিয়েছি। তবুও বাবা-মা প্রার্থনায় বসে আমাদের জন্য হাত তুলেছেন। সারা জীবন তাঁরা শুধু একটাই প্রতিদান চেয়েছেন—দিনে একবার হলেও সন্তানের মুখে শুনতে চান, ‘মা’ বা ‘বাবা।’
আমরা কতটা নির্বোধ! মা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ডাক, বাবা তাঁর সবচেয়ে বড় ছায়া। আসলে মা-বাবা কী জিনিস, সেটা সেই বোঝে যার কাছে তাঁরা নেই। বাবা-মার শাসনের ভিন্নতা আমি বড় হয়ে বুঝেছি। মানুষ হতে হলে কী শিক্ষা, কেন শিক্ষা, শিক্ষার ধরন কেমন হবে—এই প্রতিটি প্রশ্নের সঠিক উত্তর তাঁরা তাঁদের জীবন দিয়ে আমাদের শিখিয়েছেন। হয়তো সেই ভিন্নতার কারণেই আমি বাংলাদেশের পাড়াগাঁয়ের সীমা পেরিয়ে বিশ্ব নাগরিক হওয়ার পথে হাঁটতে পেরেছি।
আমার বাবা বাংলাদেশ পুলিশের একজন কর্মকর্তা ছিলেন। চাকরি শুরু করেছিলেন ব্রিটিশ আমলে, শেষ করেছিলেন স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা হাতে নিয়ে। তাঁর জীবন ছিল শৃঙ্খলা, ত্যাগ আর সংগ্রামের প্রতীক। মা সামলেছেন পুরো পরিবার, পাশাপাশি সমাজকল্যাণেও যুক্ত থেকেছেন নিঃস্বার্থভাবে।
গতকাল সহধর্মিণীর সঙ্গে বাবা-মাকে নিয়ে কথা হচ্ছিল। আলোচনার শেষে আমি বলি— ‘আমার বাবা-মা অতি সাধারণ পরিবেশে থেকেও আমাদের এতগুলো ভাই-বোনকে সৃজনশীল শিক্ষায় শিক্ষিত করতে পেরেছেন, যেন পুরো পৃথিবীর অভিজ্ঞতা ও শিক্ষা আমাদের জন্য সংগ্রহ করেছেন। তাঁরা জীবনের প্রায় শেষ বিশ বছর বাংলাদেশ এবং ইউরোপ—দুই নাগরিকত্বেই কাটিয়েছেন, যা একটি গরীব পরিবারের জন্য সত্যিই বিরল।’
আমার সহধর্মিণী মারিয়া সরাসরি উত্তর দিলেন— ‘তাঁরা ডিজার্ভ করেন। তাঁদের ত্যাগ, কঠোর পরিশ্রম এবং সংগ্রামের মধ্য দিয়ে তোমাদের বিশ্বনাগরিক বানিয়েছেন। তাঁদের জীবন ব্যতিক্রম হবে, এটাই স্বাভাবিক।’ কথাটা শোনার পরই আমার মধ্যে অজানা দায়বদ্ধতা আরও গভীর হলো। আসলে বাবা-মা শুধু অভিভাবক নন, তাঁরা জীবন্ত পাঠ্যপুস্তক। প্রতিটি ছোট কাজে লুকিয়ে থাকে বড় শিক্ষা। মায়ের নিঃশব্দ ত্যাগ আমাকে শিখিয়েছে নিঃস্বার্থ ভালোবাসা। বাবার কঠোর শাসন আমাকে শিখিয়েছে নীতি, শৃঙ্খলা ও দায়িত্ববোধ। দুজনের মিলিত শিক্ষা আমাকে শিখিয়েছে মানুষ হওয়া—শুধু ডিগ্রি পাওয়া নয়।
আজকের দিনে সন্তানরা বাবা-মাকে বোঝা ভাবে, প্রযুক্তির ভিড়ে তাঁদের শিক্ষা ভুলে যায়। কিন্তু মনে রাখতে হবে—স্কুল-কলেজের জ্ঞান হয়তো চাকরি এনে দেবে, কিন্তু বাবা-মার শিক্ষা চরিত্র গড়বে। আর চরিত্র ছাড়া জ্ঞান অন্ধ। তাই যতদিন বাবা-মা জীবিত, তাঁদের শিক্ষাকে সম্মান করতে হবে। কারণ তাঁরা আমাদের প্রথম শিক্ষক, এবং মৃত্যুর পরও তাঁদের শিক্ষা আমাদের জীবনে পথপ্রদর্শক হয়ে থাকবে।
আমি এই লেখাটি আমার বাবা-মার জন্য লিখেছি। তবে এটিকে উৎসর্গ করছি বিশ্বজুড়ে সকল বাবা-মাকে—যাঁরা আমাদের হৃদয় দিয়ে শিখিয়েছেন দৈনন্দিন শিক্ষা, মানবিক শিক্ষা, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক শিক্ষা, যোগাযোগের শিক্ষা এবং সর্বোপরি নীতি ও নৈতিকতার শিক্ষা। বাবা-মা আমাদের জন্য শুধু শিক্ষক নন; তাঁরা আমাদের জীবনের প্রথম ও চিরন্তন পথপ্রদর্শক। তাঁদের ভালোবাসা, ত্যাগ এবং শিক্ষা আমাদের প্রতিটি পদক্ষেপে ছায়ার মতো থাকে—যা আমরা হয়তো বুঝি না, কিন্তু যা আমাদের জীবনের প্রতিটি মুহূর্তে গভীরভাবে প্রভাবিত করে। আজ যাঁদের বাবা-মা নেই, তাঁদের জন্য এই স্মৃতি হোক সান্ত্বনার আলো—কারণ তাঁদের রেখে যাওয়া শিক্ষা ও দোয়া অদৃশ্য আশ্রয়ের মতো আজও আমাদের পথ দেখায়।
আর যাঁদের বাবা-মা বেঁচে আছেন, তাঁদের জন্য এই লেখা হোক এক মৃদু স্মরণ—একবার হলেও মায়ের হাত ধরে বলুন, “তুমি আমার শ্রেষ্ঠ শিক্ষক”, বাবার চোখে চোখ রেখে বলুন, “তুমি আমার জীবনের প্রথম দিশারি।” কারণ শেষ পর্যন্ত, আমরা সবাই একই সত্যে এসে দাঁড়াই— বাবা-মা চলে যান, কিন্তু তাঁদের শিক্ষা থেকে যায়; ভালোবাসা ম্লান হয় না, বরং সময়ের সাথে আরও উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।
বিশ্ব শিক্ষক দিবসে তাই আমার শ্রদ্ধা প্রথমেই বাবা-মার প্রতি, যাঁরা আমাদের শিখিয়েছেন কিভাবে গুরুজনদের সম্মান করতে হয়। এই মুহূর্তে মনে পড়ে গেল কাজী কাদের নেওয়াজের কবিতা “শিক্ষাগুরুর মর্যাদা”-এর শেষ দুটি লাইন: আজ হতে চির-উন্নত হলো শিক্ষাগুরুর শির, সত্যই তুমি মহান উদার বাদশাহ আলমগীর।
এই কবিতায় শিক্ষকের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রকাশিত হয়েছে। বাবা-মা এবং শিক্ষক —উভয়ই আমাদের জীবনের প্রথম ও চিরন্তন পথপ্রদর্শক। তাঁদের শিক্ষা ও ভালোবাসা আমাদের সঙ্গে চলমান থাকুক আজীবন।
রহমান মৃধা, সাবেক পরিচালক, ফাইজার, সুইডেন। Rahman.Mridha@gmail.com
মত দ্বিমত
ভারত–লন্ডন নেতৃত্বের দ্বন্দ্ব ও জনগণের অনুপস্থিতি
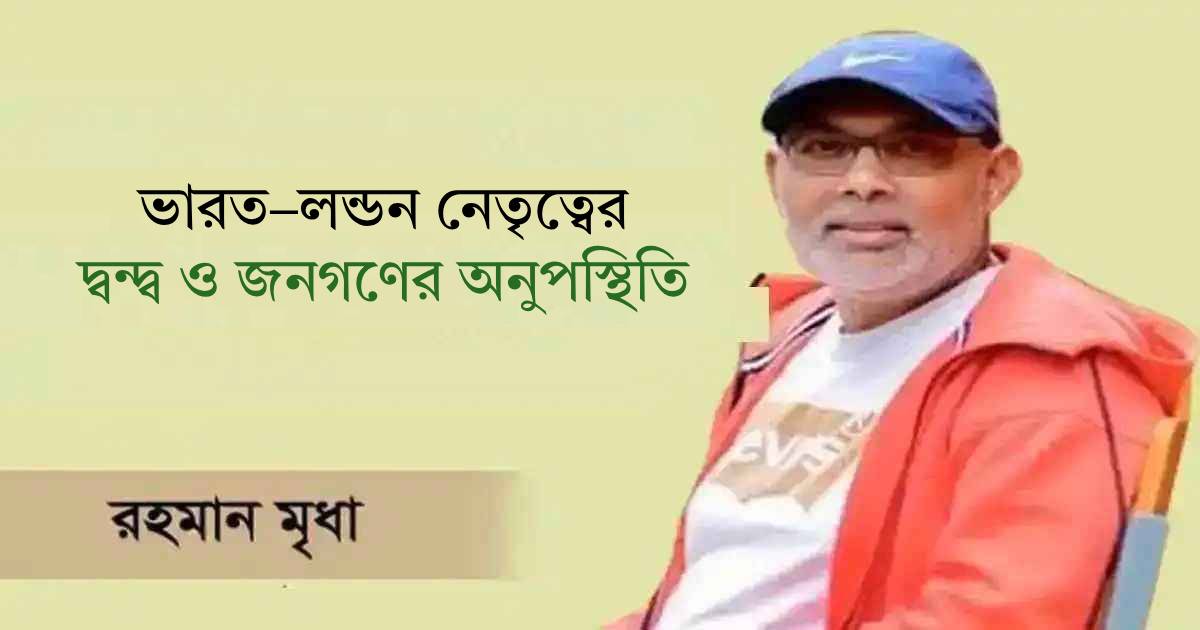
৫ আগস্ট ২০২৪—অনেকেই এই দিনটিকে ভেবেছিলেন বাংলাদেশের রাজনৈতিক সঙ্কট থেকে উত্তরণের দিন হিসেবে। প্রত্যাশা ছিল, এই দিনে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার দায়িত্ব নিয়ে শাসনতন্ত্রের স্থিতিশীলতা ফিরিয়ে আনবে। কিন্তু বাস্তবে হলো উল্টো। দেশ স্বাধীন হলো না, বরং রাষ্ট্রকে দুই টুকরো করা হলো। শেখ হাসিনাকে ক্ষমতা থেকে সরানো হলো বটে, কিন্তু তাঁকে ভারত পাঠানো হলো। ফলাফল? একদিকে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার, অন্যদিকে শেখ হাসিনা—ভারত থেকে এখনো তাঁর দল ও সমর্থকদের নিয়ন্ত্রণ করছেন।
এই সিদ্ধান্ত ছিল ভয়াবহ ভুল। তাঁকে সরানো হলো, কিন্তু সমাধান করা হলো না। দল ও প্রশাসনের অনেকেই এখনো তাঁকেই নেত্রী মনে করছে, তাঁকেই অনুসরণ করছে। ফলে দেশের শাসনতন্ত্র কার্যত বিভক্ত হয়ে গেছে—অর্ধেক চলছে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের নির্দেশনায়, অর্ধেক চলছে শেখ হাসিনার প্রভাবমুক্ত নয় এমন প্রশাসনের অধীনে। এই দ্বৈত নেতৃত্ব রাষ্ট্রযন্ত্রকে অচল করে দিয়েছে।
আরেকদিকে বিএনপির নেতৃত্ব দিচ্ছেন লন্ডন থেকে তারেক রহমান। ভারত থেকে শেখ হাসিনা, লন্ডন থেকে তারেক রহমান—“ডিজিটাল বাংলাদেশ” যেন দুই প্রবাসী কেন্দ্র থেকে চালিত হচ্ছে। অথচ দেশের ভেতরে কার্যকর নেতৃত্ব নেই। বাইরে থেকে নির্দেশনা আসছে, কিন্তু ভেতরে সমস্যার সমাধান করার মতো উপস্থিত নেতৃত্ব নেই। এই কারণেই বলা যায়—দেশের বারোটা বেজে গেছে।
জনগণ কে?
আমরা সবসময় বলি—জনগণ এটা চায় না, জনগণ এটা মেনে নেবে না। কিন্তু প্রশ্ন হলো—জনগণ কে?
•বিএনপি কি জনগণের দল নয়?
•জামায়াত, আওয়ামী লীগ বা অন্য সব দল কি জনগণের অংশ নয়?
•তাহলে দলগুলো বাদ দিয়ে আর কে আছে, যে বুকে হাত দিয়ে বলতে পারবে—“আমি জনগণ”?
বাস্তবে সত্যিকারের জনগণের ভূমিকায় যারা আছে, তাদের সংখ্যা খুবই কম। তারা আছে, কিন্তু বিচ্ছিন্ন, সংগঠিত নয়। ফলাফল হলো—জনগণের নাম ব্যবহার করা হচ্ছে, কিন্তু জনগণের জন্য কাজ করা হচ্ছে না। অতীতে হয়নি, ভবিষ্যতেও হবে না—যদি না আমরা ডেসপারেটলি চেষ্টা করি।
দুর্নীতি, অনীতি ও বিভক্ত প্রশাসন
আজ দেশের বৃহত্তম রাজনৈতিক দল দুর্নীতি, অনীতি, লুটপাট, চাঁদাবাজিতে নিমগ্ন। প্রশাসন বিভক্ত—কেউ অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের পক্ষে, কেউ শেখ হাসিনার প্রতি অনুগত। এক্ষেত্রে “হাড়ি ভেঙে দই পড়েছে, বিড়ালের হইছে বাহার”—এই প্রবাদটাই সঠিক। সবাই নিজের সুবিধা নেওয়ার প্রতিযোগিতায় নেমেছে, কিন্তু সাধারণ মানুষের ভাগ্যে কিছুই জোটেনি।
ভুলটা কোথায় হলো?
•শেখ হাসিনাকে ক্ষমতা থেকে সরানো হলো, কিন্তু রাজনৈতিকভাবে সমাধান করা হলো না।
•তাঁকে ভারত পাঠানো মানে তাঁর প্রভাবকে সরানো নয়—বরং বাইরে বসে তাঁকে আরও রহস্যময় ও শক্তিশালী করা হলো।
•তারেক রহমানও একইভাবে লন্ডন থেকে দল পরিচালনা করছেন—যা দেশের ভেতরে নেতৃত্বশূন্যতার জন্ম দিয়েছে।
•দুই প্রবাসী নেতা ডিজিটালি দল চালাচ্ছেন, আর দেশে সাধারণ মানুষ পড়েছে নেতৃত্বশূন্য ও বিশৃঙ্খল পরিস্থিতিতে।
দেশকে জনগণের করতে কী চেষ্টা দরকার?
১. জনগণের সক্রিয় উপস্থিতি তৈরি করা: দল নয়, নাগরিক প্ল্যাটফর্মকে শক্তিশালী করতে হবে। স্থানীয় পর্যায়ে টাউন-হল, নাগরিক কমিটি, নিরপেক্ষ জনমত সংগ্রহ শুরু করতে হবে।
২. দুর্নীতির বিরুদ্ধে দৃশ্যমান পদক্ষেপ: দুর্নীতি, লুটপাট ও ক্ষমতার অপব্যবহারের ঘটনা নথিভুক্ত ও প্রকাশ করতে হবে। ন্যায়বিচারের জন্য আইনি ও সামাজিক চাপ তৈরি করতে হবে।
৩. ছোট সেবা দিয়ে আস্থা ফেরানো: পানি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য—এই খাতে স্থানীয় উদ্যোগ দেখাতে হবে। এতে জনগণ বুঝবে—কেউ তাদের জন্য কাজ করছে।
৪. স্বচ্ছ নেতৃত্ব ও জবাবদিহি: জনগণের নামে রাজনীতি নয়, জনগণের কাজে রাজনীতি। স্বচ্ছতা ছাড়া আস্থা আসবে না।
৫. বহির্বর্তী প্রভাব থেকে বের হওয়া: ভারত ও লন্ডন থেকে ভার্চুয়াল নেতৃত্বের পরিবর্তে স্থানীয়, জনগণকেন্দ্রিক নেতৃত্ব তৈরি করতে হবে। দেশের ভিতরে সমাধান তৈরি করতে হবে, বাইরে নয়।
আজকের বাংলাদেশে ত্রৈমুখী নেতৃত্ব, বিভক্ত প্রশাসন, দুর্নীতিগ্রস্ত দল এবং “জনগণ” নামের এক অদৃশ্য সত্তা—সব মিলিয়ে রাষ্ট্র অচলাবস্থায়। শেখ হাসিনা ভারতে বসে প্রভাব চালাচ্ছেন, তারেক রহমান লন্ডন থেকে নির্দেশ দিচ্ছেন, আর দেশে আন্দোলন করছে ছোট দলগুলো। ফলে রাষ্ট্রযন্ত্র এক ভয়ঙ্কর অস্থিরতায় আছড়ে পড়েছে। যে দেশে সবাই কোনো না কোনো দলের সমর্থক, যে দেশে কেউ ভুল স্বীকার করে না, অন্যায়ের পর অনুশোচনা নেই, শুধু জনগণের নামে দায় চাপানো হয়—সেই দেশ কিভাবে জনগণের হতে পারে?
পরিবর্তন একদিনে হবে না। তবে ছোট ছোট নাগরিক উদ্যোগ, স্থানীয় স্বচ্ছ নেতৃত্ব, দুর্নীতির বিরুদ্ধে দাঁড়ানো এবং জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণ ছাড়া কোনো পথ নেই। যদি আমরা চেষ্টা না করি, তাহলে জনগণ সবসময় কেবল শ্লোগানেই থেকে যাবে—কাজে নয়।
অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের মূল দায়িত্ব ও অঙ্গীকার ছিল নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে রাজনৈতিক সঙ্কট সমাধান করা, শাসনতন্ত্রে জনগণের আস্থা ফিরিয়ে আনা এবং অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন আয়োজন করা। কিন্তু বাস্তবে সেই প্রতিশ্রুতি পূরণ হয়নি। জবাবদিহিতার অভাব, সিদ্ধান্তহীনতা এবং ক্ষমতার ভারসাম্যহীনতা পরিস্থিতিকে আরও জটিল করে তুলেছে। শেখ হাসিনার মনোনীত প্রেসিডেন্ট আজও অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের শীর্ষ অবস্থানে রয়েছেন—ফলে সরকারের বৈধতা ও নিরপেক্ষতা প্রশ্নবিদ্ধ হয়েছে। এ অবস্থায় সশস্ত্র বাহিনীর দায়িত্ব ছিল রাষ্ট্রকে রক্ষা করা, আইন-শৃঙ্খলা বজায় রাখা এবং নিরপেক্ষতা নিশ্চিত করা; কিন্তু তারা যদি সত্যিকারের নিয়ন্ত্রণ ও নিরপেক্ষতা প্রতিষ্ঠা করতে না পারে, তাহলে রাষ্ট্রব্যবস্থা ভেঙে পড়ার ঝুঁকি থেকেই যায়।
এই প্রেক্ষাপটে ড. মুহাম্মদ ইউনূসের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল। তিনি অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান হিসেবে সঙ্কট সমাধানের কার্যকর নেতৃত্ব নিতে পারতেন, কিন্তু তাঁর পদক্ষেপ সীমিত থাকায় প্রত্যাশিত পরিবর্তন ঘটেনি। তাই এখন জরুরি একটি ন্যায্য রূপান্তর—যেখানে রাজনৈতিক দলগুলো টিকে থাকবে, কিন্তু তাদের ভেতরে থাকা দুর্নীতি, লুটপাট, মানবাধিকার লঙ্ঘন বা অন্য অপরাধে দণ্ডিত নেতৃত্বকে কঠোরভাবে বাদ দিতে হবে। দল হচ্ছে জনগণের সংগঠিত অভিব্যক্তি; তাদের সম্পূর্ণ অস্বীকার করা গণতন্ত্রকেই অস্বীকার করা।
অতএব, প্রয়োজন এমন একটি অন্তর্বর্তীকালীন সরকার, যেখানে থাকবে সৎ ও যোগ্য নেতৃত্ব, নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিত্ব, নিরপেক্ষ প্রশাসন, বিশেষজ্ঞ পেশাজীবী এবং তরুণ প্রজন্মের সক্রিয় অংশগ্রহণ। এই সরকারকে কঠোর জবাবদিহিতার আওতায় থাকতে হবে, যেন প্রতিটি সিদ্ধান্ত স্বচ্ছ, যাচাইযোগ্য এবং জনগণের কাছে ব্যাখ্যা-সাপেক্ষ হয়। কেবল এভাবেই দলীয় অস্তিত্ব রক্ষা করে অপরাধী নেতৃত্বকে ছাঁটাই করা সম্ভব, এবং গড়ে তোলা সম্ভব একটি নতুন শাসনব্যবস্থার ভিত্তি—যেখানে জনগণের আস্থা ফিরবে, রাষ্ট্রে স্থিতিশীলতা আসবে এবং ভবিষ্যতের নির্বাচন হবে সত্যিকারের গণতান্ত্রিক। এর পরেই জাতীয় নির্বাচনের মাধ্যমে জনগণকে তাদের প্রকৃত সিদ্ধান্তের অধিকার ফিরিয়ে দেওয়া ছাড়া দেশের ভবিষ্যৎ নিরাপদ নয়।
রহমান মৃধা, সাবেক পরিচালক, ফাইজার, সুইডেন। Rahman.Mridha@gmail.com






















