মত দ্বিমত
বাংলার এই দুর্দিনে তারেক রহমান এখনো কেন লন্ডনে?
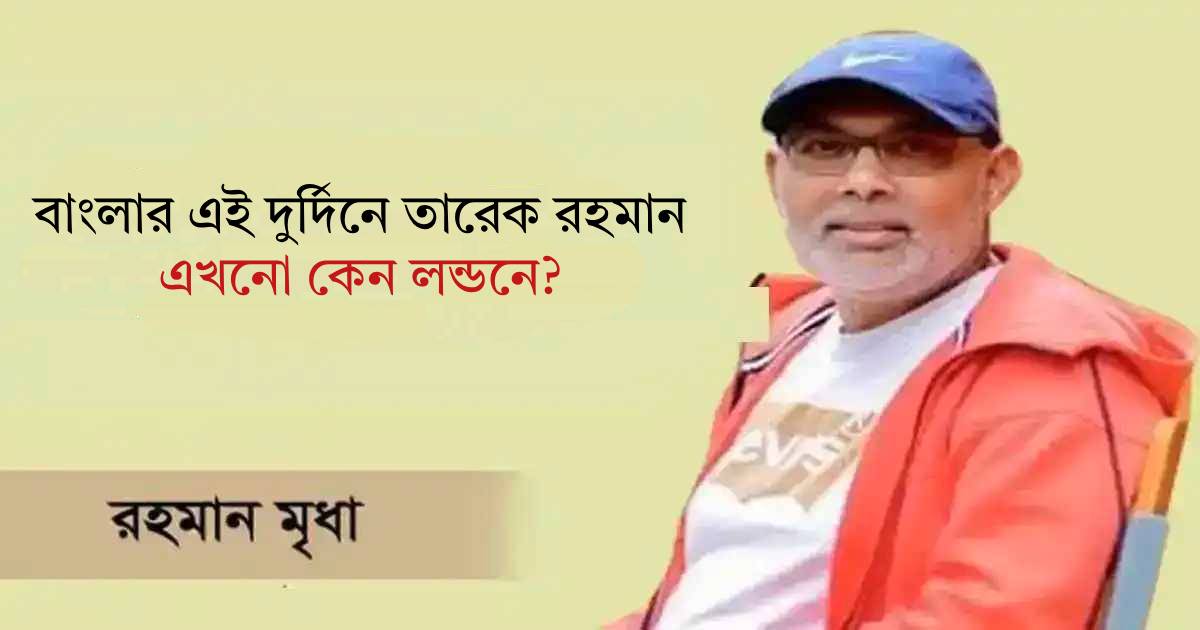
বলছি বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের কথা। আজ যখন বাংলাদেশ গভীর রাজনৈতিক, সামাজিক এবং নৈতিক সংকটে নিপতিত, তখন তিনি কোথায়? দেশের মাটিতে নন, লন্ডনের নিরাপদ আশ্রয়ে। প্রশ্ন ওঠে-এটা কি মৃত্যুভয়, নাকি মিলিটারি কিংবা সরকারের রোষানলে পড়ার আতঙ্ক? আজ দেশের জন্য প্রয়োজন সাহসী, প্রজ্ঞাসম্পন্ন ও মাঠঘাটে সরব নেতৃত্ব। অথচ, তারেক রহমান এখনো দেশের মাটিতে ফেরার সাহস দেখাতে পারছেন না।
জিয়াউর রহমান বা খালেদা জিয়া কখনো ভাড়াটে সন্ত্রাসীর ওপর নির্ভর করে নেতৃত্ব দেননি। তাঁরা রাজনীতি করেছেন মাটি ও মানুষের সঙ্গে, জীবনবাজি রেখে। তাহলে আজ বিএনপির রাজনীতিতে কেন এত সন্ত্রাসী চরিত্র, দূর-নির্দেশনা নির্ভরতা, আর মাঠের কর্মীদের আত্মবিশ্বাসহীনতা?
যদি তারেক রহমান জেল, হয়রানি, কিংবা জীবনের নিরাপত্তার আশঙ্কায় দেশে না ফেরেন, তাহলে কীভাবে তিনি একটি দেশের শাসনভার নেবেন? রাজনীতি তো শুধু বক্তব্য ও দূরবর্তী নিয়ন্ত্রণ নয়—এটি উপস্থিতি, আত্মত্যাগ, নেতৃত্ব এবং মানুষের পাশে দাঁড়ানোর সাহসের নাম।
বাংলাদেশের বাস্তবতা অত্যন্ত করুণ। মানুষ ধর্ম পালন করে—নামাজ, রোজা, হজ, ওমরাহ সবই আছে; কিন্তু সমাজে সততা, ন্যায়বোধ, জবাবদিহি নেই। চাঁদাবাজি, দুর্নীতি, রাজনৈতিক প্রতারণা—এসবই যেন এখন নিত্যনৈমিত্তিক। মানুষ ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চলে, কিন্তু সামাজিক নৈতিকতা ও দায়বদ্ধতা হারিয়ে ফেলেছে। এই চিত্রের মধ্যেই দেশের বৃহত্তম রাজনৈতিক দলগুলোর নেতৃত্ব আজ বিভ্রান্ত ও জনবিচ্ছিন্ন।
এই পরিস্থিতিতে যদি ডিসেম্বরেই জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়, তবে প্রশ্ন থেকে যায়—তারেক রহমান কি লন্ডনে বসেই বিএনপির নির্বাচন পরিচালনা করবেন? দেশ চালানোর প্রস্তুতি কি বিদেশে বসে নেয়া সম্ভব? সবকিছু তার পছন্দমতো ‘অনুকূল’ হলে দেশে ফেরার শর্ত রাজনীতিতে কতটা গ্রহণযোগ্য?
বাংলাদেশের মানুষ কি শুধুই রক্ত দেবে? কি শুধুই গুলিবিদ্ধ হবে? আর বসন্তের কোকিলেরা বছরে একবার দেশে ফিরে নেতৃত্বের দাবি করবে? এই কি সেই গণতন্ত্র, যার জন্য এদেশের মানুষ সংগ্রাম করেছে? পাকিস্তানের পতনের পর, একদলীয় শাসনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে যদি নতুন আশার জন্ম দিতে পারে, তবে আজও সেই আশা কেন মরে যাবে?
এই দেশের মানুষ প্রতারণায় ক্লান্ত, তারা দৃঢ় নেতৃত্ব চায়। সাহসী সিদ্ধান্ত চায়। তারেক রহমান, আপনি কি প্রস্তুত? যদি প্রস্তুত থাকেন, তবে আজই দেশে ফিরে আসুন, রাজপথে নামুন, মানুষের পাশে দাঁড়ান। আর যদি আপনার শর্তই হয় নিরাপত্তা ও অনুকূল পরিবেশ, তাহলে দয়া করে নেতৃত্ব দাবি করবেন না। কারণ মানুষ আর প্রতারিত হতে চায় না।
এখন সিদ্ধান্ত আপনার—আপনি কী করবেন? সাহসিকতার পথ ধরবেন, না নিরাপদ দুরপরবাসেই থাকবেন?
কারণ এই দেশ আর সময় চায় না। দেশের মানুষ দীর্ঘ ৫৪ বছর ধরে নিপীড়িত, নির্যাতিত, অনিয়ম-অবিচারে জর্জরিত। বছরের পর বছর তারা প্রতিশ্রুতির ছায়ায় বাঁচার চেষ্টা করেছে, কিন্তু প্রতিবারই হয়েছে প্রতারিত। জাতি একসময় আশাবাদী হয়েছিল অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রতি, নতুন প্রজন্মের তরুণ নেতৃত্বের প্রতি—কিন্তু তারাও জাতিকে হতাশ করেছে।
আমরা আশাবাদী হয়েছিলাম ড. মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বেও—কিন্তু তিনিও আমাদের হৃদয়ের ভাষা, ১৬ কোটি মানুষের মনের ব্যথা বুঝতে পারেননি, বা তাকে বুঝতে দেওয়া হয়নি। তিনি থেকেছেন এলিটদের ছত্রছায়ায়, দূরে সাধারণ মানুষের কণ্ঠস্বর থেকে, এবং সে কারণেই তাঁরও পথভ্রষ্ট হওয়া অনিবার্য হয়ে উঠেছে।
তবু, এখনো সময় আছে। উপায় আছে।
যদি সকল রাজনৈতিক দলের সমর্থকদের প্রতিনিধিত্বে একটি নিরপেক্ষ, গ্রহণযোগ্য অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠন করা যায়, তবে দেশকে ফেরানো সম্ভব সঠিক পথে। সেখানে আপনি, তারেক রহমান, ড. ইউনূসের মতো একজন গ্রহণযোগ্য ব্যক্তিত্বের ছায়ায় নেতৃত্ব দিতে পারেন—নিরাপত্তার পেছনে না লুকিয়ে, সাহস নিয়ে সামনে এসে।
তবে সেই মহানুভবতার পরিচয় দিতে হলে মনে রাখতে হবে জিয়াউর রহমানের সেই ঐতিহাসিক শিক্ষা:
“ব্যক্তির আগে দল, আর দলের আগে দেশ।”
পারবেন কি আপনি সেই আত্মত্যাগ করতে? পারবেন কি দলের সংকীর্ণ গণ্ডি পেরিয়ে দেশের স্বার্থে সিদ্ধান্ত নিতে?
তাহলে আসুন, একসাথে দেশ পরিচালনা করি। ভাঙা স্বপ্নগুলো জোড়া লাগাই। বাংলাদেশের ইতিহাসের নতুন পৃষ্ঠা লিখি—সাহস, ন্যায্যতা ও মানুষের ভালোবাসার কালি দিয়ে।
রহমান মৃধা
গবেষক এবং লেখক
সাবেক পরিচালক, ফাইজার, সুইডেন
Rahman.Mridha@gmail.com
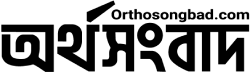
মত দ্বিমত
খাদ্য, নৈতিকতা ও নেতৃত্ব: জাতিকে আলোর পথে নিতে যাঁরা নিঃশব্দে কাজ করছেন
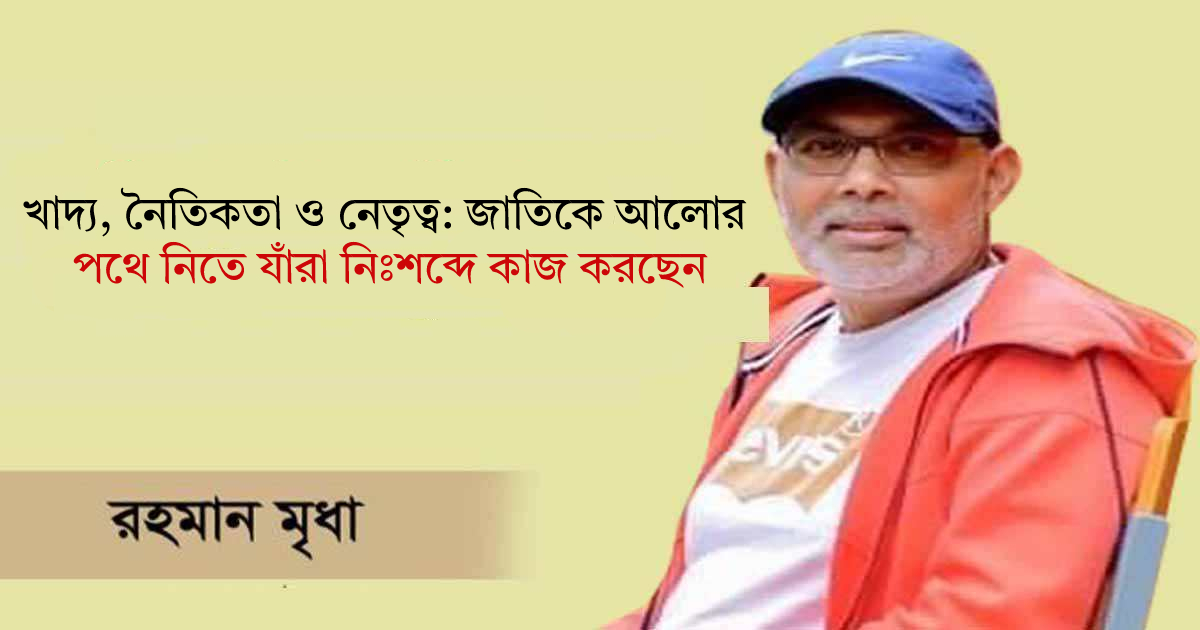
সুইডিশ ভাষায় কিছু শব্দ রয়েছে যেগুলোর মধ্যে এক ধরনের অন্তর্নিহিত শক্তি ও গভীর তাৎপর্য লুকিয়ে থাকে। এমনই একটি শব্দ ‘livsmedel’—অর্থাৎ ‘জীবনের উপকরণ’। শব্দটি শুধু খাদ্য বোঝায় না, বোঝায় এমন কিছু যা আমাদের পুষ্টি দেয়, শক্তি জোগায়, এবং মানুষ হিসেবে বেঁচে থাকার সামর্থ্য গড়ে তোলে। কিন্তু প্রশ্ন হলো, আজকের বাজারে আমরা যে খাদ্য কিনছি—তা কি সত্যিই জীবনের উপকরণ? নাকি সেগুলো এমন কিছু, যা ধীরে ধীরে আমাদের ঠেলে দিচ্ছে রোগব্যাধি, ক্লান্তি, নির্ভরশীলতা আর নিঃশব্দ বিষক্রিয়ার দিকে?
আমরা প্রায়ই বলি, সুইডেন এমন একটি দেশ যেখানে গুণমান (quality) পরিমাণের (quantity) চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। ‘লগোম’—অর্থাৎ পরিমিতিবোধ—এখানে একপ্রকার সাংস্কৃতিক বিশ্বাস। কিন্তু বাস্তবে, খাদ্যের ক্ষেত্রে আমরা এমন এক বৈশ্বিক ব্যবস্থার অংশ হয়ে পড়েছি, যেখানে ‘লগোম’-এর জায়গা দখল করে নিয়েছে—‘যত সস্তা সম্ভব’, ‘যত দীর্ঘ সময় সংরক্ষণযোগ্য’, এবং ‘শিল্পের সুবিধার জন্য যতটা সম্ভব প্রক্রিয়াজাত’ এই নীতিগুলো।
আজ আমরা সুইডেনে বিশ্বের নানা প্রান্ত থেকে যে খাবার আমদানি করছি, তা দেখতে যতই ঝকঝকে হোক না কেন, তার পুষ্টিমান প্রায়শই শূন্য। এসব খাবারে থাকে সংরক্ষণের রাসায়নিক, কৃত্রিম রং, স্বাদ বাড়ানোর উপাদান, ফিলার—আরও কত কী! এই তালিকা শুধু দীর্ঘ নয়, দিনে দিনে আরও দীর্ঘতর হচ্ছে। শিল্পোন্নত দেশ হওয়া সত্ত্বেও সুইডেন কৃষিক্ষেত্রে ব্যাপক পরিবর্তনের উদ্যোগ নিয়েছে। তারা বলছে—livsmedel, এই শব্দটির প্রকৃত মর্যাদা আমাদের ফিরিয়ে আনতেই হবে।
অথচ বাংলাদেশের মতো দেশে এখনো এমন কোনো সুদূরপ্রসারী উদ্যোগ দেখা যাচ্ছে না, যা দেশের মানুষের মৌলিক অধিকার—‘ভেজালমুক্ত ভাতে-মাছে বাঙালির বাঙালিত্ব’—পুনরুদ্ধারে কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে। আমাদের নিজেদের জিজ্ঞেস করতে হবে—আমরা কী চাই? এমন খাদ্য যা সত্যিকার অর্থে আমাদের বাঁচিয়ে রাখে, নাকি এমন কিছু, যা ধীরে ধীরে আমাদের ভেতর থেকে ভেঙে দেয়?
এখানেই আসে স্বনির্ভরতার প্রসঙ্গ। আমাদের সাহস করে বলতে হবে—নিজের খাদ্য নিজেই উৎপাদন করতে না পারলে, স্বাধীনতা অর্থহীন। মহামারির সময় আমরা এক ঝলক দেখেছিলাম—যখন বিশ্বব্যাপী সরবরাহব্যবস্থা ভেঙে পড়ে, তখন কীভাবে খাদ্যনিরাপত্তা প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে পড়ে।
আজকের পৃথিবীতে, যেখানে যুদ্ধ, জলবায়ু পরিবর্তন এবং ভূরাজনৈতিক উত্তেজনা ক্রমেই বাড়ছে, সেখানে নিজের খাদ্য নিজে উৎপাদনের সক্ষমতা শুধু যুক্তিসঙ্গত নয়—জীবনের জন্য অপরিহার্য। আমাদের দরকার এমন খাবার যা শুধু পেট ভরে না, আমাদের বিশ্বাস, স্বাস্থ্য ও মর্যাদাও রক্ষা করে। আমাদের দরকার নিরাপদ খাবার। প্রকৃত খাবার। এমন খাবার, যার উৎস আমরা জানি—আর যেটি কেবল আহার নয়, এক ধরনের আশ্বাস।
আমি সুদূর প্রবাসে বসে যখন এ রকম একজন মাটি-কেন্দ্রিক, বিজ্ঞানমনস্ক, দেশপ্রেমিক মানুষের কর্মযজ্ঞ দেখি, তখন এক প্রশ্ন আমাকে তাড়া করে ফেরে—দেশের মানুষ কেন এমন একজন সম্পদকে চিনতে ব্যর্থ হচ্ছে? কেন এমন একজন দূরদর্শী কৃষিবিজ্ঞানীর আলোর রেখা আমরা জাতীয় নীতিতে পরিণত করতে পারছি না?
খাদ্যই উন্নয়নের মূল: কৃষকের পাশে ড. আলী আফজাল এবং একটি জাতির কৃতজ্ঞতা
যেহেতু জীবন ধারণের সবকিছুই শুরু হয় খাদ্য দিয়ে। খাদ্য শুধু আমাদের শরীরের জ্বালানি নয়—এটি মনের বিকাশ, সৃজনশীলতা এবং উন্নয়নের ভিত্তি। পুষ্টিকর ও নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিত না হলে স্বাস্থ্য, শিক্ষা, কর্মক্ষমতা ও সমাজব্যবস্থার ভিত্তি ভেঙে পড়ে। একজন রাজনীতিবিদ হোন বা প্রকৌশলী, শিক্ষক হোন বা সেনা সদস্য—সবার অস্তিত্বের পেছনে নির্ভরতা এক জায়গাতেই খাদ্য।
কিন্তু যে মানুষগুলো প্রতিদিন আমাদের এই খাদ্যের নিশ্চয়তা দেন—কৃষক, খামারী, মৎস্যজীবী ও গ্রামীণ পরিশ্রমজীবী জনগোষ্ঠী—তাঁদের অবদান আজও সমাজ ও রাষ্ট্রে ন্যায্য সম্মান পায় না। বরং অবহেলা, অনিশ্চয়তা ও মধ্যস্বত্বভোগীদের চাপে তাঁরা পিছিয়ে থাকেন। এই বাস্তবতায় একজন মানুষ দীর্ঘদিন ধরে নিরবে, কিন্তু দৃঢ়তার সঙ্গে কাজ করে যাচ্ছেন। তিনি মাগুরার সন্তান, আন্তর্জাতিকভাবে প্রশংসিত কৃষিবিজ্ঞানী, সফল উদ্যোক্তা এবং দূরদর্শী সমাজগঠক—ড. মো. আলী আফজাল।
একজন কৃষকের সন্তান থেকে কৃষি-নেতা হওয়ার গল্প
১৯৬৭ সালের ২২ মার্চ মাগুরার মোহাম্মদপুর উপজেলার বালিদিয়া গ্রামে জন্ম নেওয়া ড. আফজালের শিকড় পল্লির মাটিতে। কৃষকের সন্তান হিসেবে তিনি জানতেন, কৃষির প্রকৃত সমস্যা কী, এবং সেগুলোর সমাধান কোন পথে সম্ভব। শিক্ষা ও গবেষণায় অসাধারণ কৃতিত্ব অর্জনের পর তিনি শেরে বাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচডি সম্পন্ন করেন এবং ২০ বছর ধরে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটে (BARI) কাজ করেন প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা হিসেবে। এ সময় তিনি ২২টি নতুন ফসল উদ্ভাবন করেন এবং ৮২টিরও বেশি গবেষণা প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। কিন্তু তিনি শুধু গবেষণাগারে সীমাবদ্ধ থাকেননি। গবেষণাকে মাঠে, কৃষকের হাতে, অর্থনৈতিক বাস্তবতায় রূপ দিতে চেয়েছিলেন। সেই চিন্তা থেকেই ২০০৯ সালে মাত্র ৩০ হাজার টাকা নিয়ে ৫ জন সহকর্মীকে নিয়ে প্রতিষ্ঠা করেন Krishibid Group Bangladesh (KGB)—যা আজ দেশের অন্যতম বৃহৎ কৃষি-ভিত্তিক শিল্পগোষ্ঠীতে পরিণত হয়েছে।
এক ছাতার নিচে কৃষির পূর্ণ সমাধান
বর্তমানে KGB-এর অধীনে ৩৩টি কোম্পানি রয়েছে যা মাটি ও বীজের গুণমান, সার, কীটনাশক, আধুনিক যন্ত্রপাতি, পশুখাদ্য, দুগ্ধজাত পণ্য, মাছ-মাংস উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বাজারজাতকরণের সাথে যুক্ত। কৃষকদের জন্য এটি একটি বাস্তব “ওয়ান-স্টপ সার্ভিস” ব্যবস্থা, যা তাদের শুধু প্রযুক্তিগত সহায়তা নয়—আর্থিক সুরক্ষা ও আত্মবিশ্বাসও দিচ্ছে।
KGB-তে বর্তমানে ৬৫০০ জন বিনিয়োগকারী রয়েছেন, যাঁদের অনেকেই সরাসরি কৃষক বা কৃষক পরিবারের সদস্য। গত দুই দশকে এই বিনিয়োগকারীদের গড় বার্ষিক রিটার্ন ১৯%, যেখানে মোট Tk ২৫০ কোটি বিনিয়োগের বিপরীতে Tk ৩১৫ কোটি ফেরত দেওয়া হয়েছে—এটাই প্রমাণ করে, এই উদ্যোগ শুধুমাত্র ব্যবসায়িক নয়, এটি একটি সামাজিক বিনিয়োগ ও কৃষক-ক্ষমতায়নের মডেল।
স্থানীয় উদ্যোগ, বৈশ্বিক দৃষ্টিভঙ্গি
ড. আফজাল শুধু বাংলাদেশেই নয়, আন্তর্জাতিক পর্যায়েও কৃষি গবেষণা ও উন্নয়নে কাজ করেছেন। তিনি তাইওয়ান, অস্ট্রেলিয়া ও সিরিয়া-তে কাজ করেছেন উন্নত ফসল উদ্ভাবন এবং খাদ্য নিরাপত্তা বিষয়ে, যা তাঁর দর্শনে এক বৈশ্বিক মাত্রা এনেছে। তিনি বুঝতে পেরেছেন—যে জাতি খাদ্যে স্বনির্ভর নয়, সে কখনো স্বাধীন নয়।
রাজনীতির আহ্বান: নীতির মানুষকে নেতৃত্বে চাই
যদিও ড. আলী আফজাল এখনো সরাসরি রাজনীতিতে যুক্ত হননি, কিন্তু আমাদের সমাজে আজ এমন নেতৃত্বের অভাব গভীরভাবে অনুভূত হয়—যেখানে জ্ঞান, সততা ও জনসেবার মানসিকতা একত্রে থাকে। তাঁর মতো মানুষদের রাজনীতিতে সম্পৃক্ত করা মানে হলো নীতিনির্ভর উন্নয়ন নিশ্চিত করা। আমরা চাই, আগামী দিনে তিনি বাংলাদেশের কৃষিনীতি নির্মাণ ও বাস্তবায়নে সক্রিয়ভাবে নেতৃত্ব দিন—এমনকি ভবিষ্যতের একজন যোগ্য ও জনমুখী কৃষিমন্ত্রী হিসেবেও তাঁর অংশগ্রহণ দেশ ও জাতির জন্য আশীর্বাদ হবে।
একজন মানুষের পেছনে একটি জাতির স্বপ্ন
ড. আফজাল আজ শুধুমাত্র একজন সফল ব্যক্তি নন, তিনি একটি দর্শনের প্রতীক—যে দর্শন বলে: “কৃষক যদি বাঁচে, দেশ বাঁচে। খাদ্য যদি নিরাপদ হয়, জাতি সুস্থ থাকে।” আমি সুদূর প্রবাসে বসে যখন এ রকম একজন মাটি-কেন্দ্রিক, বিজ্ঞানমনস্ক, দেশপ্রেমিক মানুষের কর্মযজ্ঞ দেখি, তখন এক প্রশ্ন আমাকে তাড়া করে ফেরে—দেশের মানুষ কেন এমন একজন সম্পদকে চিনতে ব্যর্থ হচ্ছে? কেন এমন একজন দূরদর্শী কৃষিবিজ্ঞানীর আলোর রেখা আমরা জাতীয় নীতিতে পরিণত করতে পারছি না?
আমি বহু বছর বিশ্বের অন্যতম শীর্ষস্থানীয় ওষুধ প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠানে কাজ করেছি। এখন, সুইডেনের মতো শীতল আবহাওয়ায়, কঠিন বাস্তবতার মধ্যেও কৃষিকাজে নিজেকে যুক্ত রেখেছি—শুধু একটি বার্তা ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য:
“খাদ্য কেবল পেট ভরানোর মাধ্যম নয়; এটি সভ্যতা ও নৈতিকতার বিষয়।” নিরাপদ খাদ্য মানে সুস্থ জাতি, আর ভেজাল মানে বিপর্যয়।
বাংলাদেশে ড. আলী আফজালের মতো একজন বিজ্ঞানী ও সংগঠক থাকা সত্ত্বেও, আমরা আজও কেন নিরাপদ ও ভেজালমুক্ত খাদ্যের জন্য হাহাকার করছি? কেন এখনও কৃষকের ঘাম ও পরিশ্রম যথাযথ সম্মান পাচ্ছে না? কেন জাতি তার প্রকৃত নায়ক ও পথপ্রদর্শককে চিনতে এত বিলম্ব করছে? এই প্রশ্নগুলো শুধুমাত্র প্রশ্ন নয়; এগুলো সময়ের কাছে আমাদের দায়। জবাব চাই, জাগরণ চাই। জাগো বাংলাদেশ, জাগো!
আমি ১৯৮৬ সাল থেকে আমার বড় ভাই প্রফেসর ড. মান্নান মৃধাকে দেখছি—তিনি কেবল একজন শিক্ষাবিদ নন, বরং নিবেদিত সমাজসেবক ও গবেষক, যিনি দেশের শিক্ষা ও গ্রামীণ উন্নয়নে অগ্রদূত। তিন দশকেরও বেশি সময় ধরে তিনি দেশের গ্রামীণ কৃষকদের পাশে থেকে মাঠ পর্যায়ের গবেষণামূলক কাজ করে যাচ্ছেন। তার নেতৃত্বে এলাকার প্রথম গবাদি ফার্ম গড়ে উঠেছে, মাছচাষসহ বিভিন্ন কৃষি প্রযুক্তির উন্নয়ন হয়েছে। তার গবেষণার মূল লক্ষ্য সঠিক চাষাবাদ পদ্ধতি প্রচলন ও কৃষকের জীবনমান উন্নয়ন।
তাঁর কাজের কেন্দ্রবিন্দু শুধুমাত্র কৃষি নয়; তিনি সমাজের প্রান্তিক শ্রেণীর ক্ষমতায়নে দৃঢ় বিশ্বাসী। এলাকার শিশুশিক্ষা থেকে শুরু করে সকল স্তরের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও প্রান্তিক কৃষকদের টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করতে তিনি নিরলস কাজ করে যাচ্ছেন। অসংখ্য শিক্ষার্থী ও গবেষকের তিনি পথপ্রদর্শক, যারা দেশের কৃষি ও গ্রামীণ উন্নয়নে অবদান রাখছেন।
একই লক্ষ্য নিয়ে তিনি আজও নিরলস পরিশ্রম করছেন—বাংলাদেশী মানুষের জীবনে মৌলিক পরিবর্তন আনা, তাদের ভাগ্যে নতুন আলো জ্বালানো, এবং একটি উন্নত, মানবিক ও সম্মানজনক সমাজ গড়ে তোলা, যেখানে প্রতিটি কৃষক ও গ্রামীণ জনগণ সুশিক্ষিত, স্বাবলম্বী ও মর্যাদাবান জীবন যাপন করবে।
আমরা ড. মান্নান মৃধা ও ড. আলী আফজালের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জানাই। প্রার্থনা করি তারা দীর্ঘদিন সুস্থ ও সক্রিয় থাকুন, কৃষক ও দেশের মানুষের পাশে থেকে জাতিকে আলোর পথে নিয়ে যান। যেন বাংলাদেশের প্রতিটি শিশুর মুখে নিরাপদ ও পুষ্টিকর খাদ্যের হাসি ফুটে ওঠে—এটাই আমাদের সম্মিলিত আশা ও স্বপ্ন।
রহমান মৃধা
গবেষক, লেখক ও সাবেক পরিচালক, ফাইজার সুইডেন
Rahman.Mridha@gmail.com
কাফি
মত দ্বিমত
তরুণদের আহ্বান: বৈষম্যের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রচিন্তা
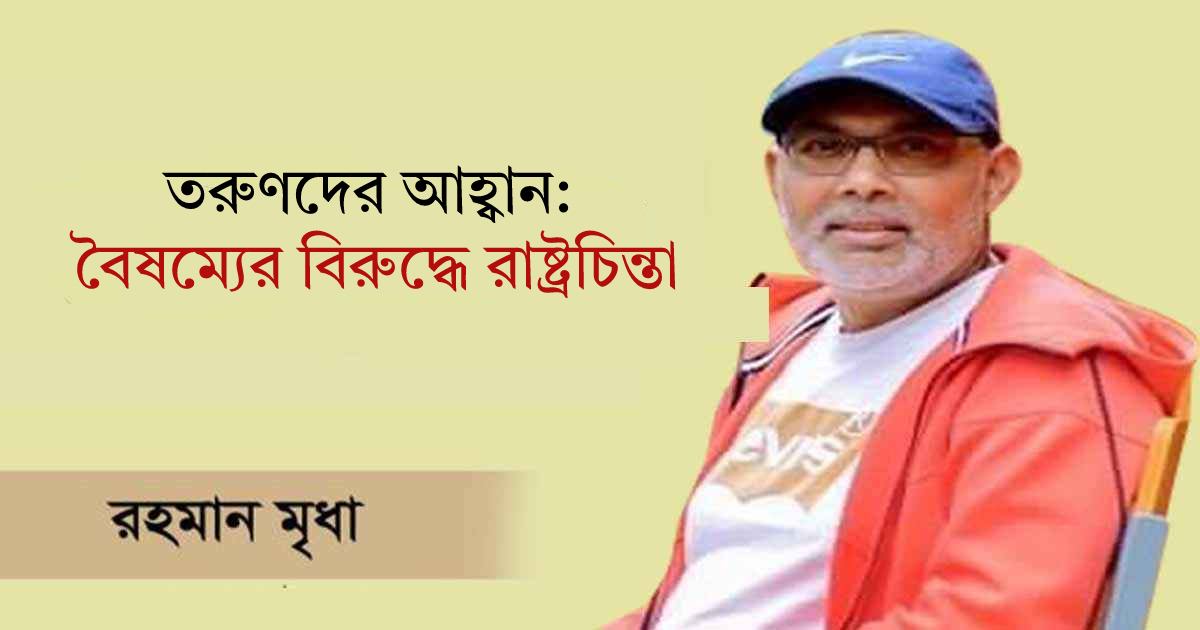
একটি নৈতিক বিপ্লব, যা শুধু সরকার নয়-সমাজের বিবেককেও প্রশ্নের মুখে ফেলেছে। বাংলাদেশের শিক্ষার্থীরা এখন আর নিছক শ্রেণিকক্ষের পাঠেই সীমাবদ্ধ নয়। তারা রাস্তায়, চত্বরে, ডিজিটাল মাধ্যমে এবং গণমাধ্যমে জোরালো কণ্ঠে বলছে এ দেশের কাঠামোগত বৈষম্য, দুর্নীতি ও সুবিধাবাদ আর চলতে পারে না। এই তরুণদের নৈতিক জাগরণ কেবল একটি সরকারের পতনের প্রতীক নয়, বরং একটি নতুন রাষ্ট্রচিন্তার সূচনা।
এটা আর শুধু প্রতিবাদ নয়—এটা এক নৈতিক অভ্যুত্থান। রাজপথে দাঁড়িয়ে থাকা শিক্ষার্থীরা কোনো দলীয় চেতনার বাহক নয়, বরং তারা এক দগ্ধ সমাজের বিবেক হয়ে উঠেছে। তাদের চোখে লজ্জা, প্রশ্ন, এবং জেগে ওঠা মূল্যবোধ—যা রাষ্ট্রের দীর্ঘকালীন বৈষম্য ও সুবিধাভোগী শ্রেণিকাঠামোর বিরুদ্ধে এক অনিবার্য প্রতিক্রিয়া। দুর্নীতির অন্ধকার গলিতে যখন ন্যায়বিচার নিঃশব্দে কাঁদে, তখন এই তরুণরাই বলে ওঠে: “আমরা চুপ থাকবো না।”
তারা আজ দাবি করছে এমন এক রাষ্ট্রব্যবস্থার, যেখানে শিক্ষক, কৃষক, গৃহকর্মী কিংবা ঝাড়ুদার—সবাই পাবেন সম্মান, নিরাপত্তা ও ন্যায্যতা। রাষ্ট্র যদি কেবল কিছু মানুষের সম্পদের পাহারাদার হয়ে থাকে, তবে সেটি আর জনতার রাষ্ট্র নয়। এই আন্দোলন সেই ব্যবধান ভাঙতে এসেছে—চেতনাকে বদলাতে, কাঠামোকে চ্যালেঞ্জ জানাতে। এটি কোনো গুজবনির্ভর আবেগ নয়—এটা এক বিবেকসচেতন, তথ্যভিত্তিক বিপ্লব।
বছরের পর বছর ধরে একটি ক্ষুদ্র, শক্তিশালী শ্রেণি সরকারি প্রশাসন, সেনাবাহিনী, পুলিশ ও অন্যান্য উচ্চপদে থেকে বিশেষ সুবিধা ভোগ করে আসছে। তাঁরা চাকরি চলাকালীন উচ্চ বেতন, নানা ভাতা এবং অবসরে প্রতীকী মূল্যে রাজধানীর অভিজাত এলাকায় প্লট পাচ্ছেন। অথচ যারা শিক্ষকতা, চিকিৎসা, প্রকৌশল, কৃষিকাজ, শ্রম কিংবা সাধারণ সরকারি চাকরিতে দেশের প্রকৃত সেবা করে যাচ্ছেন—তাঁদের জন্য নেই সম্মানজনক অবসরজীবন কিংবা ন্যূনতম সামাজিক নিরাপত্তা।
এই প্রেক্ষাপটে শিক্ষার্থীদের নেতৃত্বে যে বিষয়গুলো উঠে এসেছে, তা পাঁচটি স্পষ্ট দাবিতে সংক্ষেপ করা যায়:
১. ঢাকার চাপ কমাতে সেনানিবাস, প্রশাসনিক ভবন ও অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের পুনর্বাসন জরুরি। ঢাকা বিশ্বের অন্যতম ঘনবসতিপূর্ণ, যানজটপূর্ণ ও দূষিত শহর। অথচ এই শহরের কেন্দ্রস্থলেই অবস্থিত রয়েছে সেনানিবাস, মন্ত্রণালয়, সুপ্রিম কোর্ট, ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের মতো বহু দাপ্তরিক ও প্রশাসনিক প্রতিষ্ঠান, যা বিকল্প স্থানে সরিয়ে নেওয়া সম্ভব।
এছাড়া, হাজার হাজার অবসরপ্রাপ্ত উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা—সেনাবাহিনী, পুলিশ, প্রশাসন, বিচার বিভাগসহ—বিশেষ সুবিধাসহ রাজধানীর অভিজাত এলাকায় বসবাস করছেন। তাঁদের জন্য রাজধানীর বাইরে আধুনিক ও সম্মানজনক আবাসনের ব্যবস্থা করতে হবে, যাতে নাগরিক সুবিধা সবার জন্য উন্মুক্ত হয় এবং রাজধানীর ভারসাম্য রক্ষা পায়।
রাজধানীকে শুধু ‘ক্ষমতার কেন্দ্র’ না রেখে একটি বসবাসযোগ্য মানবিক শহর হিসেবে গড়ে তুলতে হলে, প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণ ও স্থানচ্যুতি এখন সময়ের দাবি।
২. পরিশ্রমজীবী মানুষ যেন আর বস্তিতে না বাস করেন। যারা বাস চালান, রাস্তায় ঝাড়ু দেন, বিভিন্ন সেবা দেন—তাঁরা যেন সারাজীবন কাজ করেও বস্তিতে বাস করতে বাধ্য না হন। এটি রাষ্ট্রের জন্য লজ্জাজনক। তাঁদের জন্য ন্যূনতম আবাসন, স্বাস্থ্যসেবা ও অবসরের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা রাষ্ট্রের দায়িত্ব।
৩. দুর্নীতি দমন সংস্থাগুলোকে ঘুষ ও রাজনৈতিক প্রভাবে দূষিত করে রাখা চলবে না। দুর্নীতি দমন কমিশন, আয়কর বিভাগ, ভূমি অফিসসহ সরকারি রাজস্ব ও জবাবদিহির সংস্থাগুলোর ভেতরে ঘুষ ও অবৈধ সমঝোতার চক্র গড়ে উঠেছে। এসব প্রতিষ্ঠানকে স্বাধীন, কার্যকর ও জনদায়িত্বশীল করতে না পারলে কাঙ্ক্ষিত পরিবর্তন আসবে না।
৪. নৈতিক শিক্ষা দিয়ে দুর্নীতির বিরুদ্ধে দীর্ঘমেয়াদি যুদ্ধ শুরু করতে হবে। বিচার বিভাগ, প্রশাসন, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতে অনৈতিকতা বাড়ছে। এই দুর্নীতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ কেবল আইন দিয়ে নয়—শুরু করতে হবে শিক্ষালয় থেকে। শিশুদের মধ্যে ন্যায়ের প্রতি বিশ্বাস, আত্মসংযম, দায়িত্ববোধ ও অসততার বিরুদ্ধে সচেতনতা গড়ে তুলতে হবে।
৫. যাঁরা সেবা দেন, তাঁরা যেন সম্মান ও নিরাপত্তা পান। অফিসের গাড়িচালক, বাসার সহকারী, পরিচ্ছন্নতাকর্মী কিংবা কৃষক—যাঁরা নীরবে সেবা দিয়ে যান—তাঁরা যেন অবহেলার শিকার না হন। তাঁদের জন্য পেনশন, চিকিৎসা ও অবসরের সুনির্দিষ্ট নিশ্চয়তা থাকা উচিত। এই অবহেলা মানবিকতাবিরোধী এবং রাষ্ট্রীয় নীতির চরম ব্যর্থতা।
এই শিক্ষার্থী-নেতৃত্বাধীন আন্দোলন একটি মূল্যবোধভিত্তিক রাষ্ট্র নির্মাণের ডাক দিয়েছে। এটি কেবল রাজনৈতিক নয়—এটি এক নৈতিক পুনর্জাগরণ। এখন সময় এই তরুণদের কণ্ঠস্বরকে সম্মানের সঙ্গে গ্রহণ করার। সময় এসেছে একটি বৈষম্যহীন, মানবিক ও ন্যায়ের বাংলাদেশ গড়ার।
এই আন্দোলন শুধু পাঁচটি দাবি পূরণের জন্য নয়—এটি রাষ্ট্রকে তার আয়নায় নিজের মুখ দেখানোর আহ্বান। আমরা কীভাবে এতদিন কিছু মানুষকে বিশেষ সুবিধার পাহাড়ে বসিয়ে রেখেছি, আর যারা প্রকৃত সেবা দিচ্ছেন, তাঁদের ঠেলে দিয়েছি অবহেলার প্রান্তে? তরুণরা সেই প্রশ্ন তুলছে, এবং সেই প্রশ্নের উত্তর না দেওয়া মানেই ভবিষ্যতের দায় এড়িয়ে যাওয়া।
এখন আর কেবল সরকারি নীতিমালার কসটিতে চলা চলবে না—চাই নতুন রাষ্ট্রচিন্তা, যেখানে মূল্যায়ন হবে সেবার ভিত্তিতে, সুবিধার নয়। এই আন্দোলনের অন্তরে যে নৈতিক সুর বাজছে, তা কোনো সময়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়; এটি বাংলাদেশের আত্মার গভীর থেকে উঠে আসা এক ধ্বনি—ন্যায়ের, মর্যাদার ও গণতন্ত্রের। যারা আজ রাস্তায় দাঁড়িয়েছে, তারা কেবল বিদ্রোহ করছে না—তারা আমাদের শিক্ষা দিচ্ছে।
এখন সময় এসেছে কানে শোনা নয়—হৃদয়ে ধারণ করার। এই তরুণ কণ্ঠস্বর যদি অবহেলা করা হয়, তবে রাষ্ট্র শুধু একটি প্রজন্ম নয়—হারাবে নিজের ভবিষ্যৎ, মানচিত্র ও আত্মপরিচয়।
নতুন বাংলাদেশ গড়তে হলে চাই ন্যায়ের ভিত্তিতে মর্যাদা, চাই মানুষকে মানুষ হিসেবে দেখা।
এই বিপ্লবের আত্মত্যাগ তখনই পূর্ণতা পাবে, যখন রাষ্ট্র নিজেই উচ্চারণ করবে— সবাই গুরুত্বপূর্ণ, কেবল সুবিধাভোগীরা নয়।
রহমান মৃধা
গবেষক, লেখক ও সাবেক পরিচালক, ফাইজার সুইডেন
Rahman.Mridha@gmail.com
মত দ্বিমত
নিজেকে প্রশ্ন করে দেখো না?
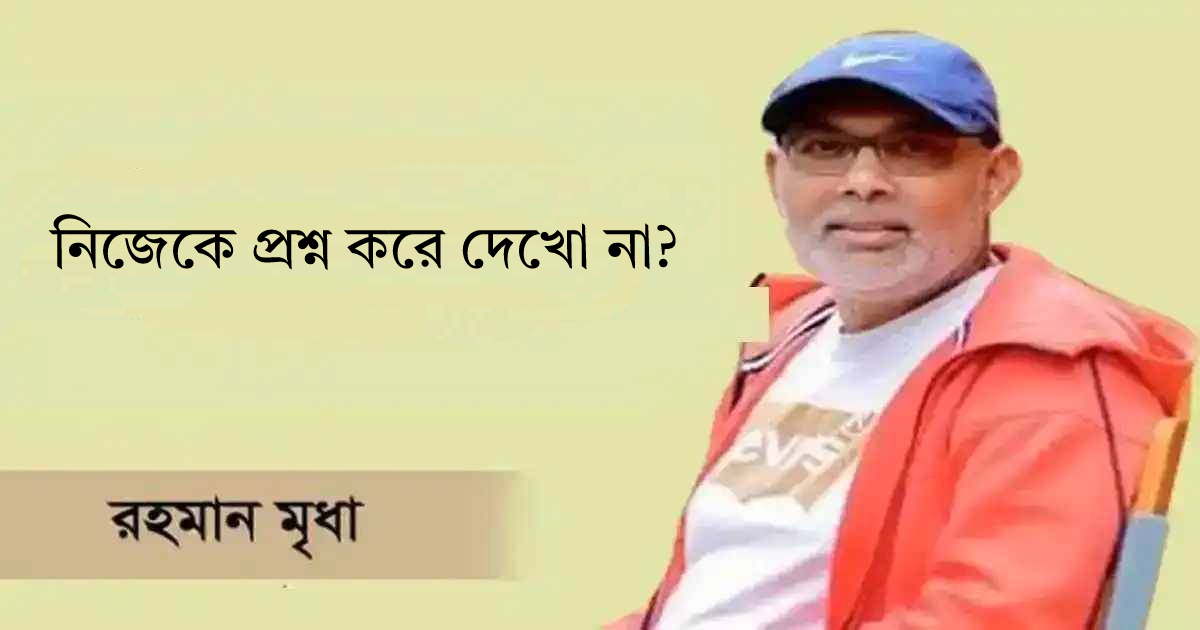
ভুলের স্মৃতি, ভালো কাজের আহ্বান, এবং বিবেকের এক নীরব সংলাপ। নিজেকে ফিরে দেখা: ভুলের প্রতিচ্ছবি। আমার জীবনে ভুল ছিল। কিছু ভুল ছিল আবেগে, কিছু সিদ্ধান্তে, কিছু নীরবতায়। কিন্তু আমি কখনোই তাদের অস্বীকার করিনি। কারণ আমি বিশ্বাস করি— ভুলের স্বীকারোক্তিই আত্মশুদ্ধির প্রথম ধাপ।
এই ভুলগুলোকেই আমি আজ স্মরণ করি, যেন অন্যরা আমার পথে হেঁটে সেই একই গর্তে না পড়ে। আমার অভিজ্ঞতা হয়তো কারও জন্য সতর্কবার্তা হতে পারে।
ভালো কাজ: নিজেকে ছাপিয়ে অন্যের জন্য। আমার কিছু কাজ ছিল—যেগুলো শুধু আমার জন্য ছিল না। আমি চেয়েছি, যেন সেই কাজগুলো অন্যের জীবনেও আলো ফেলে। ভালো কাজের সার্থকতা তখনই, যখন তা শুধু নিজের আত্মতৃপ্তি নয়—অন্যের কল্যাণে রূপ নেয়।
আমার কিছু সিদ্ধান্ত হয়তো কাউকে সাহস জুগিয়েছে, কেউ হয়তো আমার লেখায় খুঁজে পেয়েছে নিজের আত্মপ্রত্যয়। এই ছোট ছোট মুহূর্তগুলোই আমার জীবনের বড় অর্জন।
বিবেকের সাথে সংলাপ। আমরা কি বিবেকের সাথে কথা বলি? আমরা কি প্রতিদিনের কাজের পেছনে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করি—“আমি সঠিকটা করলাম তো?” আমি এই সংলাপ করি—প্রতিদিন না হোক, প্রহরে প্রহরে নিজের ভেতরের সেই নীরব কণ্ঠস্বর শুনি। তাতে আমি সব সময় উত্তম হতে পারি না, কিন্তু আমি সচেতন থাকি।
আমরা যখন “হ্যাঁ” বলি, তখন কি তার পেছনে সাহস থাকে? আমরা যখন “না” বলি, তখন কি বিবেক খুশি থাকে? এই চিন্তা আমাদের নৈতিকতা গড়ে দেয়, মানবিকতা জাগায়।
নিজের জীবনের আলো অন্যের পথ দেখাতে পারে। এই লেখাটি শুধু আত্মজিজ্ঞাসা নয়—এটি একটি ডাকে, যেখানে আমি চাই, আমার জীবনের যাত্রা যদি অন্যকে একটু ভাবায়, একটু আলো দেয়—তবেই তা অর্থপূর্ণ। আমরা সবাই ভুল করি, কিন্তু সবাই যদি সেই ভুল থেকে কিছু শিখি এবং অন্যকে বলি—“এই পথে যেয়ো না”, তখন সমাজ বদলায়।
আমি চাই, আমার অভিজ্ঞতা, আমার শিক্ষা, আমার ছোট ছোট উপলব্ধি। তোমার জন্য বড় কোনো সত্যের চাবিকাঠি হয়ে উঠুক।
এক নিঃশব্দ আহ্বান: নিজেকে জানো, অন্যকে জানতে দাও। এই জীবন এক প্রশিক্ষণ, প্রতিদিন নিজেকে জানার। যেখানে ভুলেরা শুধু কষ্ট নয়, শিক্ষাও দেয়। যেখানে ভালো কাজ কেবল বাহবা পাওয়ার জন্য নয়, অন্যকে জাগিয়ে তোলার জন্য।
তুমি যদি নিজের গল্প বলতে পারো, তাহলে কেউ না কেউ একদিন বলবে “তোমার অভিজ্ঞতা আমাকে বদলে দিয়েছে।”
তাই আজকে বলি— নিজেকে প্রশ্ন করে দেখো না? হয়তো তোমার উত্তরই অন্য কারও জীবনের সবচেয়ে জরুরি আলো হতে পারে।
রহমান মৃধা
গবেষক, লেখক ও সাবেক পরিচালক, ফাইজার সুইডেন
Rahman.Mridha@gmail.com
মত দ্বিমত
গণতন্ত্রের সঠিক পথে: সংসদ নয়, স্থানীয় সরকার হোক উন্নয়নের প্রধান বাহক
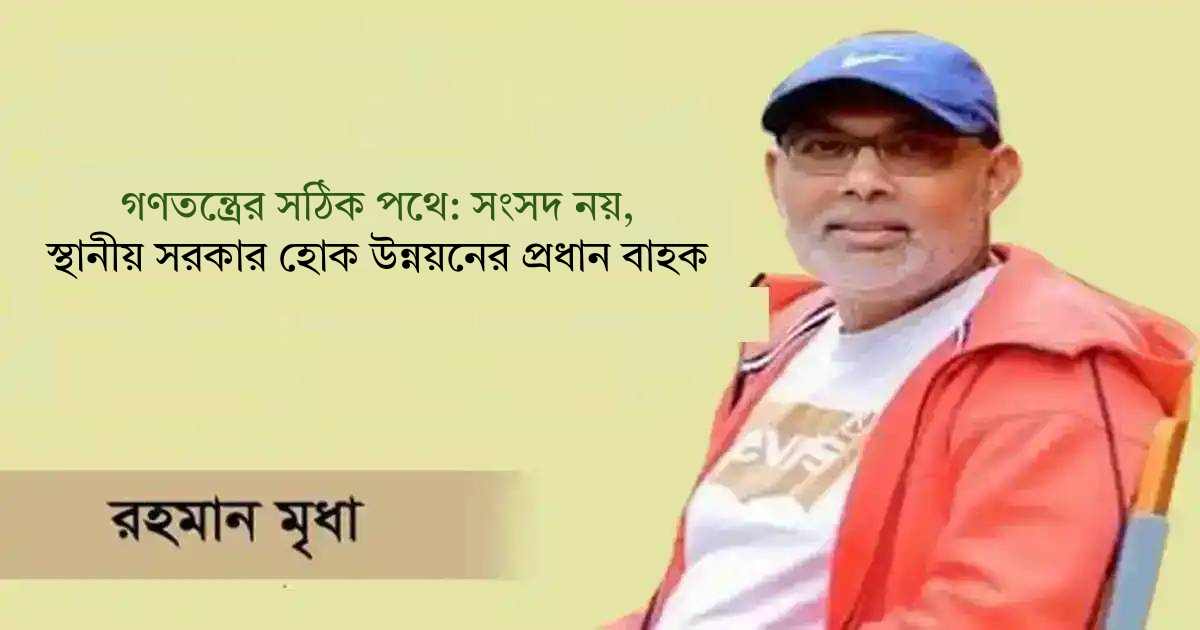
বাংলাদেশের গণতন্ত্র আজ কঠিন এক সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে। একদিকে আমরা সংবিধানে গণতন্ত্রের প্রতিশ্রুতি নিয়ে এগোই, অন্যদিকে বাস্তবে রাজনৈতিক দখলদারিত্ব, পরিবারতন্ত্র, দলীয় চাঁদাবাজি এবং একদলীয় কর্তৃত্ববাদী শাসনের বাস্তবতা আমাদের পথরোধ করে। নির্বাচন এখন আর গণরায় নয়—এটি হয়ে উঠেছে ক্ষমতা পাকাপোক্ত করার এক নিষ্ঠুর কৌশল। এই সংকট নিরসনে নির্বাচন পদ্ধতির কাঠামোগত পরিবর্তন এখন সময়ের দাবি।
বিশ্বের বহু গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে ব্যবহৃত প্রপোরশনাল রিপ্রেজেন্টেশন (PR) বা অনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব ভিত্তিক পদ্ধতি বাংলাদেশের জন্য এখন একটি সময়োপযোগী ও বাস্তবসম্মত বিকল্প। সুইডেনে আমার চার দশকের নাগরিক, গবেষক ও ভোটার অভিজ্ঞতায় আমি দেখেছি—কীভাবে PR ভিত্তিক সংসদীয় গণতন্ত্র একটি সমাজকে ন্যায়, শান্তি ও প্রগতির পথে নিয়ে যেতে পারে।
সুইডেনে কোনো একক দল সংসদে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পায় না, ফলে সরকার গঠনে জোট বাধ্যতামূলক। এতে গড়ে ওঠে রাজনৈতিক সহনশীলতা, আলোচনাভিত্তিক সংস্কৃতি ও পারস্পরিক দায়িত্ববোধ। প্রার্থী মনোনয়নে দলের অভ্যন্তরীণ গণতন্ত্র ও জনমত প্রাধান্য পায়, ফলে পরিবারতন্ত্র ও আর্থিক দখলদারিত্ব দুর্বল হয়। শিক্ষক, নারী, অভিবাসী, শ্রমজীবী—সকলেই যোগ্যতার ভিত্তিতে সংসদে আসার সুযোগ পান। ঘুষের কোনো দরকার নেই; টিকিট কিনে মনোনয়ন নেওয়ার ব্যবস্থা নেই—যোগ্যতা ও জনসম্পৃক্ততাই এখানে আসল মূলধন।
এখানে সংসদ সদস্যদের কাজ সীমিত—তাঁরা কেবল নীতিনির্ধারণ ও আইন প্রণয়নের দায়িত্ব পালন করেন। বরাদ্দ, চাকরি বা ব্যক্তিগত সুপারিশে হস্তক্ষেপের এখতিয়ার তাঁদের নেই। এর ফলেই গড়ে উঠেছে জনগণের উপর আস্থা এবং নির্বাচনে ৮০-৯০ শতাংশ ভোটার অংশগ্রহণ নিশ্চিত হয়।
বাংলাদেশের বাস্তবতা একেবারে উল্টো। এমপি পদটি হয়ে উঠেছে যেন একটি ‘বিনিয়োগের প্রজেক্ট’—যেখানে মনোনয়ন পেতে লাগে কোটি টাকার ঘুষ, যার উৎস দুর্নীতির অর্থও হতে পারে। এই অর্থ খরচ করে নির্বাচিত হওয়ার পর, এমপি-রা পরিণত হন স্থানীয় দানবে—তাঁরা বাজার কমিটি নিয়ন্ত্রণ করেন, সরকারি চাকরির সুপারিশ দেন, বরাদ্দ ভাগ করেন, এমনকি রাস্তার ইটের কন্ট্রাক্টেও হস্তক্ষেপ করেন। তাঁদের মূল উদ্দেশ্য হয়ে দাঁড়ায় বিনিয়োগ তোলা—জনগণের ভাগ্যের পরিবর্তন নয়।
ভোটের মূল্যও এখানে নষ্ট। নির্বাচনের আগেই টাকা দিয়ে ভোট কেনা হয়, রাতের আঁধারে প্রশাসনের সহায়তায় ভোট সম্পন্ন হয়, এবং ভোটার জানেন—তাঁর ভোটের কোনো দাম নেই। ফলে গণতন্ত্রের প্রতি বিশ্বাস হারিয়ে ফেলে জনগণ। এ এক পরস্পরবিনাশী চক্র—জনগণের আশা মর্যাদাহীন হয়ে পড়ে, আর রাজনীতির মঞ্চ হয়ে ওঠে লুটপাটের কেন্দ্র।
এই চক্র ভাঙতে হলে দরকার দুটি কাঠামোগত রূপান্তর—একসাথে ও সমান্তরালভাবে।
প্রথমত, PR পদ্ধতিতে নির্বাচন চালু করতে হবে। এতে দলীয় তালিকায় স্থান পাবে যোগ্য, জনসম্পৃক্ত প্রার্থীরা—not আর্থিকভাবে প্রভাবশালীরা। মনোনয়ন বাণিজ্য লোপ পাবে, কারণ মনোনয়ন নির্ধারিত হবে অভ্যন্তরীণ গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায়। নির্বাচিত এমপি-রা কেবল আইন প্রণয়নের দায়িত্বে থাকবেন—তাঁরা আর তদবির, বরাদ্দ বণ্টন বা চাকরির সুপারিশে জড়াবেন না।
দ্বিতীয়ত, উন্নয়নের দায়িত্ব দিতে হবে স্থানীয় সরকারকে। বরাদ্দ, প্রকল্প বাস্তবায়ন ও নাগরিক সেবা পরিচালিত হবে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের মাধ্যমে। স্থানীয় উন্নয়ন হবে জনগণের বাস্তব চাহিদা অনুযায়ী—not কোনো এমপি’র ইচ্ছেমাফিক নির্বাচনী প্রতিশ্রুতির ভিত্তিতে। প্রশাসন হবে সহযোগী—কিন্তু নিয়ন্ত্রক নয়। এই দুই কাঠামো—PR ভিত্তিক সংসদ নির্বাচন এবং ক্ষমতাবান স্থানীয় সরকার—একসাথে চালু হলে বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতি ও প্রশাসনিক কাঠামোতে এক নতুন যুগের সূচনা হবে। প্রশাসন হবে সহযোগী—কিন্তু নিয়ন্ত্রক নয়। এবং শুধু এতটুকু যোগ করা জরুরি যে, প্রথমে স্থানীয় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়া উচিত—অথবা সম্ভব হলে, সুইডেনের মতো একই দিনে স্থানীয় ও জাতীয় নির্বাচন একসাথে করা উত্তম হবে। এতে সময়, খরচ এবং প্রশাসনিক জটিলতা কমবে, পাশাপাশি জনগণের অংশগ্রহণও উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়ে যাবে। এতে করে জনগণ একসাথে দেশের ও নিজেদের এলাকার ভবিষ্যৎ নির্ধারণে কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারবে।
উন্নয়ন মানে কেবল রাস্তা-ঘাট নয়; উন্নয়ন মানে মানুষের জীবনে ন্যায়, সেবা, এবং সুযোগের প্রাপ্যতা নিশ্চিত করা। কিন্তু যে সংসদ সদস্য কোটি টাকা খরচ করে নির্বাচিত হন, তিনি জনগণের উন্নয়নের জন্য কাজ করবেন কেন?—তাঁর প্রথম লক্ষ্য থাকে বিনিয়োগ ফেরত আনা। এই মানসিকতা বদলাতে পারে PR পদ্ধতি—যেখানে নেতৃত্ব মানে জনসম্পৃক্ততা, আর ক্ষমতা মানে দায়িত্ব।
এবার প্রশ্ন, PR পদ্ধতি আসলে কী?
প্রপোরশনাল রিপ্রেজেন্টেশন (PR) বা অনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব হলো একটি গণতান্ত্রিক নির্বাচনী ব্যবস্থা, যেখানে রাজনৈতিক দলগুলো ভোটের শতকরা অনুপাতে সংসদে আসন পায়। কোনো দল যদি পায় ৩০% ভোট, তবে সে পায় ৩০% আসনও। এতে প্রতিটি ভোটের মূল্য থাকে, ভোট হারায় না।
বর্তমানের First-Past-The-Post (FPTP) পদ্ধতিতে শুধু সর্বোচ্চ ভোটপ্রাপ্ত প্রার্থী জয়ী হন, বাকি সব ভোট ‘অদৃশ্য’ হয়ে যায়। এতে রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্বহীনতা, আস্থা সংকট এবং বিভাজনমূলক রাজনীতির বিস্তার ঘটে।
PR পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য:
ন্যায়বিচার ও সমঅধিকার নিশ্চিত হয়।
সংলাপ ও সহনশীলতা গড়ে ওঠে।
মনোনয়নে স্বচ্ছতা আসে।
ভোটার আস্থা ও অংশগ্রহণ বাড়ে।
নেতৃত্বে বৈচিত্র্য সৃষ্টি হয়।
বাংলাদেশের বৈচিত্র্যময় বাস্তবতায় PR চালু করা আবশ্যক। কারণ FPTP পদ্ধতিতে—
বিরোধী কণ্ঠ দমন হয়,
ক্ষমতা পরিবার ও গোষ্ঠীর হাতে কেন্দ্রীভূত হয়,
ভোটার আস্থা ক্ষয়ে যায়,
সংসদ হয়ে ওঠে গোষ্ঠীস্বার্থের প্ল্যাটফর্ম।
সুইডেনে PR পদ্ধতির সফল বাস্তবায়ন দেখেছি নিজ চোখে। একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা না থাকায় বাধ্যতামূলক সংলাপ হয়। সংসদে আসে শিক্ষক, অভিবাসী, বাসচালকসহ সকল শ্রেণির প্রতিনিধিত্ব। ভোটার অংশগ্রহণ থাকে ৮৫-৯০%। রাজনৈতিক পরিবেশ ভদ্র, যুক্তিনির্ভর এবং সহানুভূতিশীল।
তবে PR কোনো যাদুর কাঠি নয়। এটি কেবল একটি দরজা, যার ভেতর দিয়ে যেতে হলে প্রয়োজন:
রাজনৈতিক সদিচ্ছা,
জবাবদিহিতাপূর্ণ প্রশাসন,
স্বাধীন ও সাহসী মিডিয়া,
সচেতন নাগরিক সমাজ,
এবং জাতিগত আত্মসমালোচনার সক্ষমতা।
PR শুধুই যান্ত্রিক সংস্কার নয়; এটি একটি সাংস্কৃতিক বিপ্লব। ১৯৪৫ সালে হিরোশিমা ধ্বংস হওয়ার পর জাপান বলেছিল: ‘We shall not repeat the evil.’
আজ আমরা কি দাঁড়িয়ে বলতে পারি: ‘আমরা আর নিজেদের সন্তানদের হাতেই জাতিকে ধ্বংস হতে দেব না’?
আমরা কি গড়তে পারি এমন একটি বাংলাদেশ— যেখানে ৩০ লক্ষ শহীদের আত্মা নিশ্চিন্তে বলতে পারে:
‘আমাদের রক্ত বৃথা যায়নি’?
যেখানে জুলাই মাস ফিরে আসবে স্বাধীনতার রোদের মতো— ভয়, গুম, দমন আর রক্ত নয়, বরং গণমানুষের গর্ব, মুক্তচিন্তা ও ভালোবাসার প্রতীক হয়ে। যেখানে জানুয়ারি থেকে ডিসেম্বর হবে রক্তের নয়—মুক্তির জয়গান।
প্রপোরশনাল রিপ্রেজেন্টেশন (PR) কেবল একটি ভোট গণনার পদ্ধতি নয়— এটি একটি পরিবর্তনের ঘোষণা, একটি নতুন মানসিকতার অভ্যুত্থান, একটি সাহসিকতার প্রতীক এবং এক মানবিক চেতনার পুনর্জন্ম।
যদি আমরা সত্যিকার অর্থে গণতন্ত্র চাই— যেখানে ক্ষমতা মানে দায়িত্ব, আর নেতৃত্ব মানে জনগণের সেবা, তাহলে PR পদ্ধতিই হবে আমাদের ভবিষ্যতের ভিত্তি।
এই মুহূর্তে প্রশ্ন একটাই— আপনি কি প্রস্তুত নিজের ঐতিহাসিক ভূমিকা পালনের জন্য?
রহমান মৃধা, গবেষক, লেখক ও সাবেক পরিচালক, ফাইজার সুইডেন। Rahman.Mridha@gmail.com
মত দ্বিমত
গণঅভ্যুত্থান-উত্তর ন্যায়ভিত্তিক রাষ্ট্র বিনির্মাণের স্বপ্ন
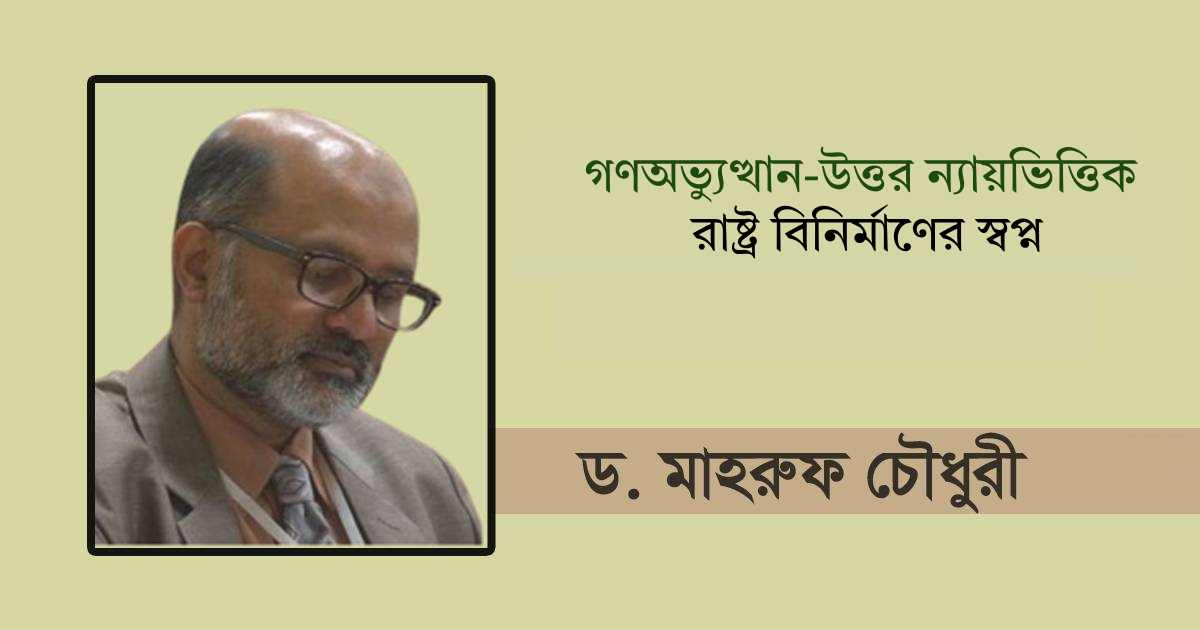
বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাস একান্তভাবেই গণমানুষের স্বপ্ন, সংগ্রাম ও আত্মত্যাগের ইতিহাস। ১৯৫২-এর ভাষা আন্দোলন, ১৯৬৯-এর গণঅভ্যুত্থান, ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধ কিংবা ১৯৯০-এর স্বৈরাচারবিরোধী গণআন্দোলন- দেশের প্রতিটি আন্দোলন ছিল ইতিহাসের একেকটি মোড় ঘোরানো ক্ষণ, যেখানে জনগণের আকাঙ্ক্ষা ছিল একটি ন্যায়ভিত্তিক, গণতান্ত্রিক ও কল্যাণমুখী রাষ্ট্রের সন্ধানে।
এই ধারাবাহিকতায় ২০২৪ সালের গণঅভ্যুত্থান আবারও প্রমাণ করেছে, রাষ্ট্র যখন নাগরিকদের ন্যায্যতা, সম্মান ও ভবিষ্যতের নিরাপত্তা দিতে ব্যর্থ হয়, তখন জনতার অভ্যুত্থানই হয়ে ওঠে পরিবর্তনের প্রধান নিয়ামক। তবে ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, প্রতিটি বিপ্লবের পরবর্তী সময়ই সবচেয়ে সংকটময়, কারণ তখনই শুরু হয় পুরনো কাঠামো ভাঙার ও নতুন কাঠামো নির্মাণের জটিল প্রক্রিয়া।
বর্তমানের বাংলাদেশ সেই বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ সময়ের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। স্বৈরশাসনের পতনের পরও দেশে এখনো সুসংহত ন্যায়ভিত্তিক রাষ্ট্র কাঠামোর ছাপ সুস্পষ্ট নয়। এই অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের কালপর্বে একদিকে যেমন পুরনো শাসনযন্ত্রের ভাঙন, অন্যদিকে তেমনি নতুন রাষ্ট্রচিন্তার অস্পষ্টতা- উভয়ের দ্বন্দ্বই জাতিকে এক অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। এই প্রেক্ষাপটে জাতি হিসেবে আমাদের প্রয়োজন গভীরতর আত্মবিশ্লেষণ, সুনির্দিষ্ট দিকনির্দেশনা ও ব্যাপক জনশিক্ষাভিত্তিক সাংস্কৃতিক নবজাগরণ।
এই বাস্তবতায় ‘গণঅভ্যুত্থান’ কেবলমাত্র একটি দমনমূলক শাসনব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিবাদী জনতার ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ নয়; এটি এক নতুন সমাজব্যবস্থা নির্মাণের গভীর আকাঙ্ক্ষারও প্রতীক। এই আকাঙ্ক্ষা একটি ন্যায়ভিত্তিক, গণমুখী ও মানবিক রাষ্ট্রব্যবস্থার স্বপ্নকে ধারণ করে, যেখানে নাগরিকের অধিকার ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠা পায় নৈতিকতা, যুক্তি ও মানবিক বোধের ভিত্তিতে। এখানে ইনসাফ বা ন্যায়ের ধারণাটি আবেগনির্ভর কোনো কল্পনা নয়, বরং এটি একটি রূপান্তরধর্মী দার্শনিক ও রাজনৈতিক চেতনা, যার শিকড় বিস্তৃত মানবসভ্যতার গভীরে। প্লেটোর ‘ন্যায়ভিত্তিক রাষ্ট্র’ দর্শন থেকে শুরু করে ইবনে খালদুনের ‘আসাবিয়্যাহ’-নির্ভর সমাজ বিন্যাস, রুশোর ‘সামাজিক চুক্তি’ তত্ত্ব, মার্ক্সের শ্রেণিবিন্যাসহীন রাষ্ট্রভাবনা, গান্ধীর অহিংস মানবিকতা এবং নেলসন মেন্ডেলার ক্ষমাশীলতা ও অন্তর্ভুক্তিমূলক নেতৃত্ব- সবই এক বিকল্প রাষ্ট্রচিন্তার দিকনির্দেশনা দেয়, যেখানে শাসনের কেন্দ্রবিন্দুতে থাকে ন্যায়, কল্যাণ ও মানবিক মর্যাদা। সুতরাং গণঅভ্যুত্থান যখন রাষ্ট্র পরিবর্তনের হাতিয়ার হয়ে ওঠে, তখন তা কেবল প্রতিক্রিয়া নয়; বরং একটি সুসংগঠিত, সুনির্দিষ্ট ন্যায়ভিত্তিক ভবিষ্যতের ডাক।
ন্যায়ভিত্তিক রাষ্ট্র বিনির্মাণের মৌলিক ভিত্তি হলো একটি স্বাধীন, নিরপেক্ষ ও বিশ্বাসযোগ্য বিচারব্যবস্থা যেখানে আইনের শাসন কেবল সাংবিধানিক ধারায় নয়, বরং নৈতিক ন্যায়ের বাস্তব রূপায়ণে প্রতিফলিত হয়। জন লক যেমন সতর্ক করে দিয়েছিলেন, ‘যেখানে আইন স্তব্ধ হয়, সেখানেই অত্যাচার জন্ম নেয়’। বাংলাদেশের বর্তমান বিচারব্যবস্থা এই সতর্কবাণীকে যেন শাসন-সংস্কৃতির এক বাস্তব অভিশাপে পরিণত করেছে। দলীয় প্রভাব, আমলাতান্ত্রিক জটিলতা, রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ এবং বিচারহীনতার সংস্কৃতি এখানে ন্যায় শব্দটিকেই প্রায় নিঃস্বার্থ প্রতীকে পরিণত করেছে। ইবনে খালদুন তাঁর ‘মুকাদ্দিমা’-তে গভীরভাবে উল্লেখ করেছিলেন, ‘অন্যায়ই সভ্যতার পতনের মূল কারণ’। এই কথাটি বর্তমান প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশে ভীষণভাবে প্রাসঙ্গিক। বিচারবহির্ভূত হত্যা, গুম, প্রতিহিংসামূলক মামলা, নিরীহ নাগরিকের হয়রানি ইত্যাদি যদি রাষ্ট্রীয় স্তরে প্রশ্রয় পায়, তবে তা কেবল বিচার ব্যবস্থার প্রতি আস্থার অবসান ঘটায় না; গণতন্ত্রের পথকে করে তোলে কন্টকাকীর্ণ। এর পরিণতিতে সমাজে সৃষ্টি হয় এক ভয়াবহ অনিশ্চয়তা ও নিরাপত্তাহীনতা, যা কেবল আইন নয়, নাগরিক আচার- আচরণের ভিতকেও ভেঙে দেয়। ইনসাফভিত্তিক রাষ্ট্রে বিচার হবে কেবল শাস্তির অনুশাসনে নয়, বরং তা হবে ন্যায়বোধ, মানবিকতা ও প্রক্রিয়াগত স্বচ্ছতার সম্মিলন যেখানে ন্যায় শুধু আদেশ নয়, বিচার ব্যবস্থার প্রতি জনগণের আস্থারও প্রতিফলন।
ন্যায়ভিত্তিক রাষ্ট্র নির্মাণে বিচার ব্যবস্থার পাশাপাশি একটি স্বচ্ছ, জবাবদিহিমূলক ও অংশগ্রহণমূলক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা অপরিহার্য। আধুনিক বিশ্বের উদাহরণে দেখা যায়, দক্ষিণ আফ্রিকার ট্রুথ অ্যান্ড রিকনসিলিয়েশন কমিশন কিংবা রুয়ান্ডার গ্যাকাকা আদালত এই দুই বিশেষ উদ্যোগই ইতিহাসের ভয়াবহ সহিংসতা ও নিপীড়নের পর ন্যায় ও পুনর্মিলনের পথ উন্মোচনে জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণ ও রাষ্ট্রের রাজনৈতিক সদিচ্ছার শক্ত সাক্ষ্য। এগুলো আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় যে ন্যায় কেবল একটি রাষ্ট্রীয় কাঠামোর ভিতরকার প্রক্রিয়া নয়, এটি একটি নৈতিক ও জনগণসম্পৃক্ত রাজনৈতিক সংস্কৃতি। কিন্তু আজকের বাংলাদেশে যখন নির্বাচনী ব্যবস্থা প্রশ্নবিদ্ধ, ভোটারহীন নির্বাচন কিংবা দলীয় প্রশাসনের ছত্রছায়ায় সংঘটিত একতরফা ভোট সম্পন্ন হয়, তখন গণতন্ত্র এক অভিনয়মাত্র হয়ে পড়ে। এ অবস্থাকে যেন অগ্রিম অনুমান করেছিলেন জ্যাঁ জাক রুশো, যিনি তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ ‘দ্যা সোসাল কন্ট্রাক্ট’ লেখেন, ‘ইংল্যান্ডের জনগণ একমাত্র সংসদ নির্বাচনের সময় স্বাধীন। বাকি সময় তারা দাস’। অনুরূপ চিত্র বাংলাদেশের বর্তমান রাজনৈতিক বাস্তবতায় যেন প্রতিবিম্বিত হচ্ছে যেখানে জনগণের মতামত নির্বাচনকেন্দ্রিক আনুষ্ঠানিকতায় সীমাবদ্ধ হয়ে গেছে, কার্যকর অংশগ্রহণ নির্বাসিত।
আসন্ন নির্বাচনের আগেই নবগঠিত নির্বাচন কমিশনের কার্যকলাপ নিয়ে জনমনে যে প্রশ্ন উঠছে, তা গণতন্ত্রের জন্য অশনিসংকেত। একটি ইনসাফভিত্তিক রাষ্ট্রে নির্বাচন কমিশন কেবল একটি প্রশাসনিক প্রতিষ্ঠান নয়, বরং এটি জনগণের আস্থা ও গণতান্ত্রিক চর্চার মূল স্তম্ভ। এর কার্যক্রম হতে হবে সর্বজনগ্রাহ্য, সম্পূর্ণ স্বাধীন, স্বচ্ছ এবং আধুনিক প্রযুক্তিনির্ভর, যাতে কোনো প্রকার দলীয় প্রভাব, প্রশাসনিক চাপ কিংবা অনিয়মের সুযোগ না থাকে। নির্বাচনের প্রকৃত অর্থ দাঁড়ায় জনগণের মতামতের প্রতিফলন, আর সে প্রক্রিয়ায় জনগণের অবাধ অংশগ্রহণ নিশ্চিত না হলে গণতন্ত্র রূপ নেয় একটি ফাঁপা খোলসে। বিশ্বজুড়ে গণতন্ত্রের পুনর্জাগরণে যেসব মডেল অনুকরণীয় হয়ে উঠেছে, তাদের মধ্যে চিলির গণভোট প্রক্রিয়া বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। একনায়কতান্ত্রিক শাসনের অবসান ঘটিয়ে জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণে যেভাবে সেখানে একটি নতুন গণতান্ত্রিক কাঠামো গড়ে তোলা হয়েছিল, তা আমাদের জন্য এক গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা। এই উদাহরণ প্রমাণ করে, নির্বাচন তখনই অর্থবহ হয় যখন তা হয় সর্বস্তরের মানুষের আস্থাভাজন, রাজনৈতিক সদিচ্ছা ও ন্যায়ের চর্চার বহিঃপ্রকাশ। আমাদের নির্বাচন প্রক্রিয়াও যেন কেবলমাত্র আইনত নয়, কার্যতও জনগণের মালিকানায় পরিচালিত হয়; আর এমন চেতনায় রাষ্ট্রযন্ত্রকে পুনর্গঠন করাই হবে একটি ইনসাফভিত্তিক রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ ন্যায়ভিত্তিক রাষ্ট্র নির্মাণে অর্থনৈতিক ইনসাফ বা ন্যায্যতা একটি অপরিহার্য ভিত্তি। এটি কেবল আয়বৈষম্য হ্রাস করার উদ্দেশ্য নয়, বরং সামগ্রিকভাবে সম্পদের উৎপাদন, মালিকানা ও বণ্টনে একটি ন্যায়সংগত ও অংশগ্রহণমূলক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার প্রশ্ন। এই দৃষ্টিভঙ্গি আমাদের নিয়ে যায় একটি গভীরতর নৈতিক ও দার্শনিক আলোচনায়। ইসলামি অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় ‘ইনসাফ’-এর ধারণা খুব স্পষ্ট, সম্পদের ‘মালিকানা স্রষ্টার, রক্ষণাবেক্ষণের দায়দায়িত্ব মানবের; ভোগে নির্ধারিত সীমা অনুসরণ, বণ্টনে ন্যায্যতা নিশ্চিতকরণ’। এর মাধ্যমে স্পষ্ট হয় যে, মানুষের অর্থনৈতিক স্বাধীনতা অপরিহার্য হলেও তা সমাজকল্যাণ ও ন্যায়বিচারের নীতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে। কার্ল মার্ক্স একটি সুস্পষ্ট বিকল্প সমাজব্যবস্থার কথা বলেছেন, যেখানে ‘প্রত্যেকের কাছ থেকে তার সামর্থ্য অনুযায়ী, প্রত্যেকের কাছে তার প্রয়োজন অনুযায়ী’ সম্পদ বণ্টিত হবে। এটি নিছক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা নয়, বরং ন্যায্যতার একটি আদর্শিক ভিত্তি যেখানে ব্যক্তিরা সমাজের প্রতি তাদের সামর্থ্য অনুযায়ী অবদান রাখবে এবং বিনিময়ে সমাজ তাদের প্রয়োজন মেটাবে। এর মাধ্যমে অর্থনীতির লক্ষ্য হবে শুধু মুনাফা নয়, বরং মানবিক মর্যাদা, সমতা এবং সামাজিক সাম্য নিশ্চিত করা।
বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে ইনসাফভিত্তিক অর্থনৈতিক কাঠামোর প্রয়োজনীয়তা আরও প্রকট হয়ে ওঠে, যখন দেখা যায় একদিকে অল্প কিছু মানুষের হাতে গচ্ছিত সম্পদের পাহাড়, অন্যদিকে সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠী ন্যূনতম মৌলিক চাহিদা পূরণে ব্যর্থ। এই বৈষম্য কেবল একটি অর্থনৈতিক ব্যর্থতা নয়, বরং রাষ্ট্রের ন্যায়ের নীতির সঙ্গে একটি ঘোরতর বিশ্বাসঘাতকতা। ইনসাফভিত্তিক অর্থনৈতিক কাঠামো কেবল করনীতির পুনর্বিন্যাস নয়; এটি একটি সমন্বিত জনকল্যাণকেন্দ্রিক রাষ্ট্রদর্শনের দাবিদার, যেখানে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বাসস্থান ও কর্মসংস্থানকে নাগরিকের অধিকার হিসেবে নিশ্চিত করা হয়; জনগণের প্রতি অনুগ্রহ হিসেবে নয়। এই কাঠামো গঠনের জন্য প্রয়োজন স্বচ্ছ, জবাবদিহিমূলক এবং জনগণের প্রতি দায়বদ্ধ একটি রাষ্ট্রব্যবস্থা। এর জন্য জরুরি করব্যবস্থার প্রগতিশীল সংস্কার, ঋণ ও ব্যাংক ব্যবস্থার ওপর রাজনৈতিক প্রভাবের অবসান, দুর্নীতির নির্মূল, এবং ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ও শ্রমজীবী মানুষের অধিকার নিশ্চিত করা। কৃষক ও শ্রমিক এই দুই প্রধান উৎপাদনশক্তিকে কেন্দ্র করে অর্থনীতিকে পুনর্গঠনের মধ্য দিয়েই প্রকৃত ইনসাফ প্রতিষ্ঠা সম্ভব।
লাতিন আমেরিকার বলিভিয়া ‘বুয়েন ভিভির’ বা ‘ভালোভাবে বেঁচে থাকা’ নামক দর্শনের মাধ্যমে এক বিকল্প উন্নয়ন চিন্তার পথ দেখিয়েছে, যার কেন্দ্রবিন্দুতে আছে প্রকৃতি, সম্প্রদায় ও আত্মমর্যাদার সহাবস্থান। এই দর্শন বলিষ্ঠভাবে প্রচলিত ভোগবাদী ও ব্যক্তিকেন্দ্রিক উন্নয়ন ধারণার বিপরীতে গিয়ে, সামষ্টিক কল্যাণ, পারস্পরিক নির্ভরতা এবং প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষার গুরুত্ব তুলে ধরে। এখানে মানুষকে প্রকৃতির শত্রু নয়, বরং সহযাত্রী ও রক্ষক হিসেবে কল্পনা করা হয়। এর মাধ্যমে একটি ন্যায্য সমাজ গঠনের প্রাকৃতিক-সামাজিক রূপরেখা হিসেবে বিবেচিত। বলিভিয়ার সংবিধানেও প্রকৃতিকে অধিকারসম্পন্ন সত্তা হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে, যা রাষ্ট্র ও নাগরিকদের উপর তার সংরক্ষণের নৈতিক ও আইনগত দায় আরোপ করে।
এই চিন্তাধারার সঙ্গে ইসলামী অর্থনীতির মৌলিক দর্শনের গভীর সাদৃশ্য রয়েছে। ইসলামে বলা হয়, দুনিয়ায় সম্পদের ‘মালিকানা স্রষ্টার, রক্ষণাবেক্ষনের দায়দায়িত্ব মানবের’ অর্থাৎ মানুষ ভোগদখলের চূড়ান্ত অধিকারী নয়, বরং সে এক দায়িত্বশীল তত্ত্বাবধায়ক (স্টুযার্ড)। তার প্রতি অর্পিত হয়েছে সম্পদের সুষম ব্যবহার, অপচয় রোধ এবং সমাজে সাম্য প্রতিষ্ঠার দায়। এই দৃষ্টিভঙ্গিতে ব্যক্তি নয়, বরং সমষ্টি, প্রকৃতি এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কল্যাণকে উন্নয়নের মূল পরিমাপক হিসেবে গণ্য করে। তাই বলিভিয়ার ‘বুয়েন ভিভির’ এবং ইসলামী অর্থনীতির এই দায়বদ্ধতাভিত্তিক দর্শন উভয়ই আমাদের উন্নয়ন ভাবনায় একটি ন্যায্যতাভিত্তিক, ইনসাফপূর্ণ বিকল্প কাঠামো গঠনের সম্ভাবনা তৈরি করে।
সুশিক্ষা ও সুস্বাস্থ্য কেবল ব্যক্তির উন্নয়নের উপাদান নয়, বরং রাষ্ট্রের ন্যায়ের ভিত্তিকে মজবুত করার প্রধান স্তম্ভ। অমর্ত্য সেন তাঁর ‘ক্যাপাবিলিটি অ্যাপ্রোচ’-এ সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন যে, উন্নয়ন বলতে বোঝায় মানুষের বাস্তব সুযোগ ও সক্ষমতা বৃদ্ধিকে যার ভিত্তি হলো মানসম্মত শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবা। কিন্তু বাংলাদেশের বাস্তবতায় আজ উচ্চমানের শিক্ষা কেবল শহরের কিছু সুবিধাপ্রাপ্ত শ্রেণির হাতে সীমাবদ্ধ, আর অধিকাংশ সরকারি হাসপাতাল সাধারণ মানুষের জন্য হয়ে উঠেছে অনিশ্চয়তা, দুর্নীতি ও অবহেলার প্রতীক। একটি ইনসাফভিত্তিক রাষ্ট্রব্যবস্থায় শিক্ষা ও স্বাস্থ্য হবে বাজারনির্ভর সুবিধা নয়, বরং রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রিত ও প্রদত্ত অধিকার। এই রাষ্ট্র সবার জন্য সমান মানের শিক্ষা নিশ্চিত করবে, যেখানে পাঠ্যক্রম হবে নৈতিকতা, মানবিকতা ও সমাজকল্যাণ-ভিত্তিক। ‘শিক্ষা মানে শুধু ডিগ্রি নয়, মানুষ গড়ার যথার্থ প্রক্রিয়া’ এই দর্শনকে ভিত্তি করে রাষ্ট্রীয় আদর্শ ‘বৈচিত্র্যের মাঝে ঐক্য’কে প্রধান্য দিয়ে শিক্ষা ব্যবস্থার পুনর্গঠন হচ্ছে সময়ের দাবি। একইভাবে স্বাস্থ্যসেবাকে হতে হবে সহজপ্রাপ্য, সুলভ, সর্বজনীন ও সম্মানজনক। ইউনেস্কোর মানব উন্নয়ন সূচকে অনেক পিছিয়ে থাকা দেশগুলোতেও দেখা গেছে যেখানে রাষ্ট্র মানসম্মত শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করেছে, সেখানে জনগণের আস্থা ও অংশগ্রহণ বেড়েছে, গণতন্ত্র হয়েছে কার্যকর। ইনসাফ কেবল আইনের বইয়ে লেখা একটি ধারণা নয়, এটি মানুষের প্রতিদিনের জীবনযাত্রায় বাস্তব, উপলব্ধিযোগ্য ন্যায়ের উপলব্ধি। তাই শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতের সংস্কার মানেই শুধু উন্নয়ন নয়, বরং একটি ন্যায়ভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠার পথে অগ্রগামী পদক্ষেপ।
সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইনসাফ মানে কেবল সকলের জন্য আইনগত সমতা নয়, বরং সমাজের প্রতিটি গোষ্ঠী ও ব্যক্তির মর্যাদা, পরিচয় ও বৈচিত্র্যের স্বীকৃতি। ন্যায় তখনই পূর্ণতা পায়, যখন তা শ্রেণি, ধর্ম, লিঙ্গ, ভাষা, পেশা কিংবা জাতিগোষ্ঠীর বিভাজনকে অতিক্রম করে সমানভাবে সকলকে মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করে। চার্লস টেইলর তাঁর ‘দ্যা পলিটিক্স অব রিকোগনিশন’ প্রবন্ধে যে বক্তব্য রেখেছেন, তা আজকের রাষ্ট্রচিন্তার জন্য অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। বিশেষ বিশেষ জনগোষ্ঠীর অস্তিত্ব ও পরিচয়কে স্বীকৃতি না দেওয়া কেবল তাদের আত্মমর্যাদার উপর আঘাত নয়, বরং এটি একধরনের সাংস্কৃতিক নিপীড়ন। বাংলাদেশের বাস্তবতায় ধর্মীয় ও জাতিগত সংখ্যালঘু, হিজড়া জনগোষ্ঠী (তৃতীয় লিঙ্গ), বেদে সম্প্রদায়, চা-শ্রমিকদের মত ভিন্ন জীবনধারার মানুষদের সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য, ভাষাগত বৈচিত্র্য এবং জীবনচর্যার ভিন্নতাকে সম্মান না দিলে ন্যায়ভিত্তিক রাষ্ট্র নির্মাণের কথা কেবল স্লোগানে সীমিত থাকবে। যেমন ব্রাজিল, কানাডা কিংবা দক্ষিণ আফ্রিকার মতো বহু-বৈচিত্র্যময় সমাজগুলো ইনসাফ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে সাংস্কৃতিক স্বীকৃতি ও অন্তর্ভুক্তির নীতি গ্রহণ করেছে, তেমনি আমাদের রাষ্ট্রেও দরকার একটি বহুমাত্রিক সাংস্কৃতিক পরিমন্ডল গঠন করা যেখানে নানান পরিচয় বিরোধ নয়, বরং সম্প্রীতির ভিত্তি হিসেবে কাজ করবে এবং রাষ্ট্রীয় আদর্শ ‘বৈচিত্র্যের মাঝে ঐক্য’-এর প্রতিফলন ঘটাবে। ন্যায়বিচার তখনই সুসংহত হয়, যখন রাষ্ট্র কেবল আইন প্রয়োগে নয়, বরং প্রতিটি মানুষের স্বাতন্ত্র্যকে মর্যাদা দিয়ে তাকে সম্মানিত নাগরিক হিসেবে স্বীকৃতি দেয়। এই দৃষ্টিভঙ্গি ছাড়া ইনসাফ কেবল একতরফা শাসন বা সংখ্যাগরিষ্ঠতার আধিপত্য হিসেবে রয়ে যাবে।
পরিবেশগত ন্যায্যতা কেবল একটি পরিবেশবাদী ধারণা নয়, এটি একটি নৈতিক ও আন্ত:প্রাজন্মিক দায়িত্ব। জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত যেমন বাংলাদেশের মতো উপকূলীয় ও নদীনির্ভর দেশে সবচাইতে গভীরভাবে অনুভূত হয়, তেমনি এর প্রতিকারে রাষ্ট্রীয় উদাসীনতা ন্যায়ের পরিপন্থী। ‘পরিবেশগত ন্যায়বিচার’-এর দর্শন অনুযায়ী, শুধু বর্তমান প্রজন্ম নয়, ভবিষ্যৎ প্রজন্মের অধিকারও বিবেচনায় নেওয়া কল্যাণমুখী রাষ্ট্রের কর্তব্য। জন রলস তাঁর ‘ন্যায়বিচারের তত্ত্ব’ (থিওরী অব জাস্টিস)-এ যে ‘আন্ত:প্রাজন্মিক ন্যায়বিচার’ (ইন্টারজেনারেশানাল জাস্টিস)-এর কথা বলেছেন, তা আমাদের রাষ্ট্রচিন্তার কেন্দ্রে থাকা উচিত যেখানে ভবিষ্যৎ নাগরিকদের জন্য সজীব,সতেজ ও বাসযোগ্য পৃথিবী রেখে যাওয়া একটি নৈতিক ও রাষ্ট্রীয় বাধ্যবাধকতা। বাংলাদেশে নদী দখল, বন উজাড়, পাহাড় কাটা, শহুরে দূষণ ও জলাভূমি ধ্বংসের পেছনে যেভাবে স্বার্থান্ধ উন্নয়ন ও রাজনৈতিক ছত্রছায়ায় লুটপাট কাজ করে, তা একপ্রকার পরিবেশগত বৈষম্য ও নিপীড়ন। শহর ও গ্রামের নাগরিকদের মধ্যকার পরিবেশগত অধিকারবিভাজন, কিংবা উপকূলীয় অঞ্চলে বসবাসকারী দরিদ্র মানুষের বাস্তুচ্যুতি এসবই প্রমাণ করে যে, ইনসাফ কেবল অর্থনীতিতে নয়, পরিবেশনীতি ও প্রাকৃতিক সম্পদের বণ্টনেও প্রয়োজনীয়। আদিবাসী সমাজের ‘প্রকৃতির সাথে যথাযোগ্য সহাবস্থান’ ধারণা এবং ধর্মীয় ঐতিহ্যে লোভ সংযমের তাগিদ আমাদের শেখায় যে প্রয়োজনের অতিরিক্ত ভোগ নয়, বরং পরিমিতিবোধ ও ভবিষ্যত প্রজন্মের প্রতি সহানুভূতির মধ্য দিয়েই পরিবেশগত ন্যায়ের পথে অগ্রসর হওয়া সম্ভব। ইনসাফভিত্তিক কল্যাণমুখী রাষ্ট্র গঠনে তাই পরিবেশবাদ একটি বিলাসিতা নয়, বরং তা একটি মৌলিক ন্যায্যতা ও অস্তিত্বের প্রশ্ন। গণঅভ্যুত্থান কখনোই কেবল প্রতিরোধ বা ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ নয়; এটি একটি নবজাগরণের আহ্বান, যেখানে জনগণ তাদের ন্যায্য অধিকার, সম্মান ও মর্যাদা ফিরে পাওয়ার সংগ্রামে আত্মনিয়োগ করে।
একটি ন্যায়ভিত্তিক রাষ্ট্র গঠনের স্বপ্ন কেবল সংবেদনশীলতা বা আবেগের বিষয় নয়, এটি একটি দার্শনিক, নৈতিক ও সাংগঠনিক প্রকল্প, যার ভিত্তি শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বিচার, অর্থনীতি, সংস্কৃতি, পরিবেশ ও রাজনীতিতে ন্যায়ের সুষম প্রতিফলন। এই ইনসাফভিত্তিক রাষ্ট্রের লক্ষ্য হবে ব্যক্তি নয়, জনগণ; ক্ষমতা নয়, দায়িত্ব; দখল নয়, সেবা। তাই বাংলাদেশের জন্য গণঅভ্যুত্থানের পরবর্তী চ্যালেঞ্জ হলো এই স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দিতে প্রয়োজনীয় নীতিনির্ধারণ, কাঠামোগত সংস্কার ও সর্বজনীন জনশিক্ষা কার্যক্রম শুরু করা। ন্যায়ের ভিত্তিতে রাষ্ট্র গড়ার এই প্রয়াসে যদি সমাজের প্রতিটি মানুষ তথা সাধারণ নাগরিক, নীতিনির্ধারক, পেশাজীবী, শিক্ষক, যুবক প্রত্যেকেই নিজ নিজ অবস্থান থেকে দায়িত্বশীল ভূমিকা নেয়, তবে একদিন এই স্বপ্নই হয়ে উঠবে একটি নতুন বাংলাদেশের বাস্তব প্রতিচ্ছবি। আমরা বাস্তবের সেই সোনালী দিনের অপেক্ষায় রইলাম।
ড. মাহরুফ চৌধুরী, ভিজিটিং ফ্যাকাল্টি, ইউনিভার্সিটি অব রোহ্যাম্পটন, যুক্তরাজ্য। mahruf@ymail.com

























