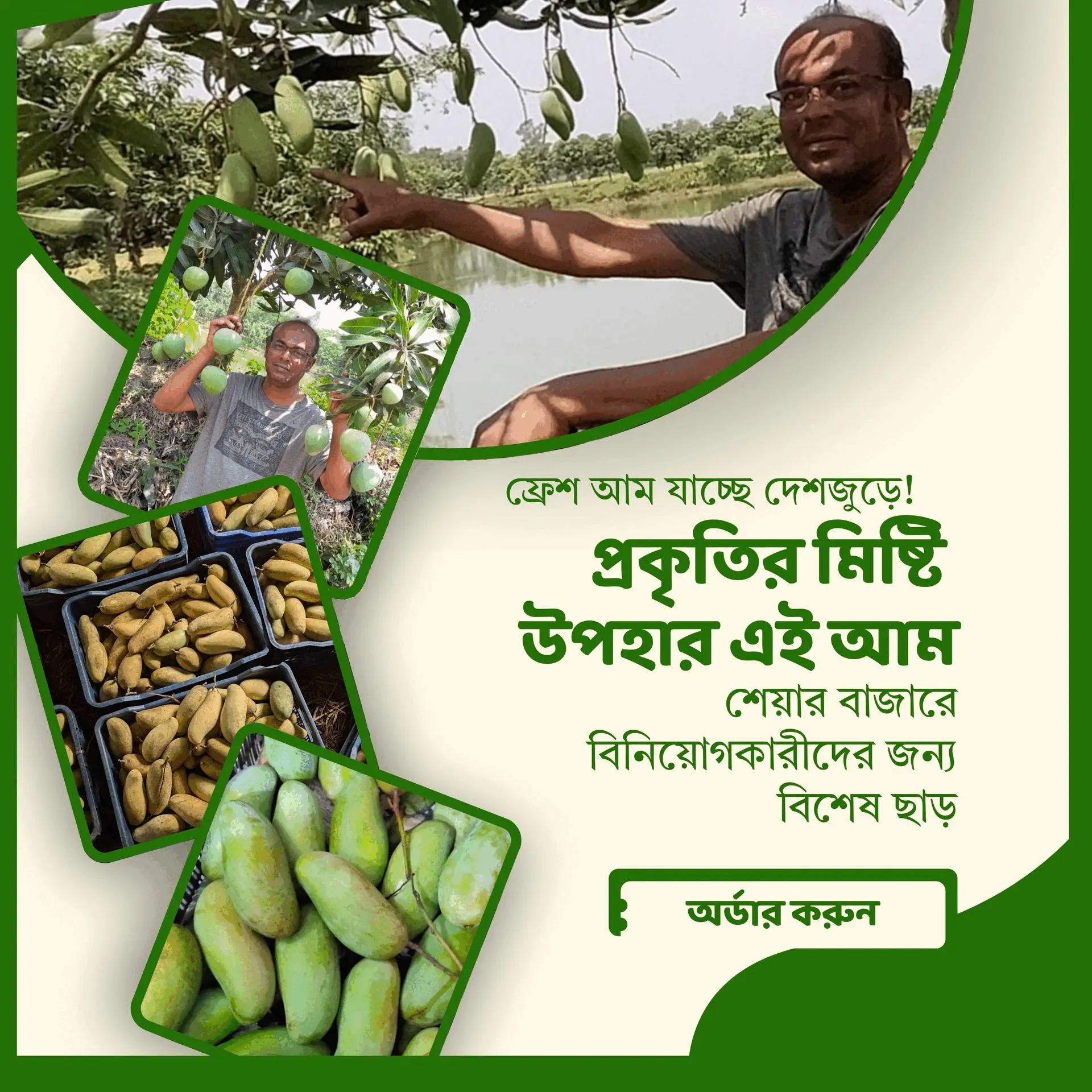মত দ্বিমত
পেশাগত দায় ও নৈতিকতা: লেখকের কৈফিয়ত ও সম্পাদকের দুঃখ প্রকাশ

ছোটবেলায় পাঠ্যপুস্তকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাটিকা ‘খ্যাতির বিড়ম্বনা’ পড়ে বেশ মজা পেয়েছিলাম। তখন মনের অজান্তে এক গভীর বোধও জন্ম নিয়েছিল যে খ্যাতি কখনো আশীর্বাদ, আবার কখনো অভিশাপও হতে পারে। সাম্প্রতিক ঘটনায় জীবনের এই পড়ন্তবেলায় সেই নাটিকাটির কথা আবার মনে পড়ে গেল। আমি অনুভব করছি যে, যারা নিয়মিত আমার লেখাগুলো পড়েন, ভাবেন, মূল্যায়ন করেন; তাঁদের কারো কারো নজরে আসা সাম্প্রতিক দু’টো ঘটনা আমাকে পীড়া দিচ্ছে। পাঠকদের কাছে একটি আন্তরিক কৈফিয়ত না জানিয়ে যেন আর কোনোভাবেই স্বস্তি পাচ্ছি না। তাই নিজেকে ভারমুক্ত করতে আজকের এই লেখার অবতারণা।
অনাকাঙ্খিত ঘটনা দু’টোর জন্য একটি আত্মজিজ্ঞাসার দায়ভার অনুভব করছি, যে দায় শুধুই পেশাগত নয়; নৈতিক এবং মানবিকও বটে। সংগত কারণে এই লেখাটিতে ঘটে যাওয়া অনাঙ্খিত ঘটনা দু’টোর ব্যাখ্যা, সেগুলোর জন্য কিছু অনুশোচনা, আর নিজের ব্যর্থতার জন্য দুঃখ প্রকাশ করছি।
দীর্ঘ এক দশকেরও বেশি সময় পত্রপত্রিকায় লেখালেখি করা থেকে দূরে থাকার পর, গণঅভ্যুত্থান-পরবর্তী এক নতুন গণতান্ত্রিক সম্ভাবনার আবহে আবারও কলম হাতে নিয়েছি। পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে মনে হয়েছিল সমাজ, রাষ্ট্র ও মানবিক মূল্যবোধের পক্ষে কিছু বলার, কিছু লেখার দায় এড়ানো উচিত নয়। সৌভাগ্যক্রমে কয়েকটি জাতীয় পত্রপত্রিকা আমার লেখা সাদরে গ্রহণ করেছে এবং আমাকে তাদের নিয়মিত লেখক হিসেবে পুনরায় জায়গা দিয়েছে। কিন্তু লেখালেখির জগতে এই প্রত্যাবর্তনের আনন্দের মাঝে সম্প্রতি দু’টি বিব্রতকর ঘটনা ঘটে গেছে। দুইটি জাতীয় দৈনিকে অসাবধনতাবশত আমার নামে অন্যের লেখা প্রকাশিত হয়েছে। যদিও উভয় ক্ষেত্রেই তা ছিল অনিচ্ছাকৃত ভুল এবং পত্রিকা কর্তৃপক্ষও বিষয়টি তাৎক্ষণিকভাবে স্বীকার করে দুঃখ প্রকাশ করেছেন ও পরবর্তী সংখ্যায় সংশোধনী প্রকাশ করেছে। তথাপি পেশাগত নৈতিকতার জায়গা থেকে ঘটনাগুলো আমাকে গভীর অস্বস্তিতে ফেলেছে।
পেশাগত জগতে বিশ্বাসযোগ্যতা কোনো তাৎক্ষণিক বা বাহ্যিক কৃতিত্ব নয়; এটি গড়ে ওঠে দীর্ঘ সময় ধরে শ্রম, আত্মবিশ্বাস ও নৈতিক দায়বোধের সম্মিলিত প্রয়াসের মাধ্যমে। বিশ্বাসযোগ্যতা, দায়িত্বশীলতা ও সুনাম অর্জনের পথে যেমন অধ্যবসায় ও সততা অপরিহার্য, তেমনি এক মুহূর্তের অসতর্কতা, ভুল সিদ্ধান্ত বা যথার্থ যোগাযোগের ঘাটতিতেও সেই বিশ্বাস বিনষ্ট হতে পারে। প্রাচীন গ্রিক দার্শনিক প্লেটো তাঁর ‘রিপাবলিক’ গ্রন্থে ন্যায়বিচার, দায়িত্ববোধ ও জ্ঞানভিত্তিক নেতৃত্বকে আদর্শ রাষ্ট্রের মূলভিত্তি হিসেবে যে গুরুত্ব দিয়েছিলেন, ঠিক তেমনি পেশাগত পরিসরেও নৈতিকতা ও দায়িত্বশীলতা কোনো অতিরিক্ত আনুষঙ্গিক নয়, বরং এটি পেশাগত চেতনা, আস্থা ও আন্তরিকতা রক্ষার অবিচ্ছেদ্য উপাদান। ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান—উভয়ের জন্যই এটি একটি নীতিগত স্তম্ভ। অতএব ভবিষ্যতে যেন এ ধরনের অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতি পুনরায় না ঘটে এবং পেশাগত সতর্কতার পাশাপাশি সততা, স্বচ্ছতা ও দায়বদ্ধতা অক্ষুণ্ণ থাকে, সে লক্ষ্যে কিছু বিষয়কে এখানে খোলামেলা ও স্পষ্টভাবে তুলে ধরা এবং নির্মোহভাবে আলোচনার প্রয়োজন অনুভব করছি।
রাষ্ট্রীয় কিংবা পেশাগত পরিসরে আমি কোনো খ্যাতিমান ব্যক্তি নই। আমি একজন সাধারণ মানুষ, জীবন পাঠশালার একজন সক্রিয় জীবনব্যাপী শিক্ষার্থী ও ঝঞ্জাবিক্ষুব্ধ চলার পথের এক অনুসন্ধিৎসু পথিক, সেই অর্থে আমৃত্যু শিক্ষানবিশ। তবে শিক্ষানবিশ হলেও, আমি পেশাগত পরিসরে যুক্ত এবং সেই কারণে এই ঘটনা দু’টো সম্পর্কে কৈফিয়ত প্রদান পেশাগত পরিচয় থেকেই আমার ওপর ন্যূনতম একটি নৈতিক দায় মনে করছি। আত্মগ্লানি লুকোতে সততার প্রশ্নে আপস করা আমার কাছে আত্মপরিচয়ের সঙ্গেই বিশ্বাসঘাতকতা। তাই কেউ যদি বলেন, ‘এটা তো খুবই সামান্য একটি ভুল’, পেশাজীবি হিসেবে আমি তা সহজে মেনে নিতে পারি না। কারণ এই ‘সামান্য’ ভুলই একজন পেশাজীবীর এবং তাঁর প্রতিষ্ঠানের ভাবমূর্তি ও দায়বোধের ভিত কাঁপিয়ে দিতে পারে। আর এই ছোট ছোট ভুলগুলোকে উপেক্ষা করার মধ্য দিয়েই আমরা আমাদের পেশাগত এবং মানবিক মূল্যবোধ, দায়-দায়িত্ব ও নীতি-নৈতিকতা ধ্বংশের রাজপথ তৈরি করি।
ঘটনাগুলো যে অনিচ্ছাকৃতভাবে সংগঠিত হয়েছে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু আমার ও সম্পৃক্ত অপর দুই লেখকের জন্য সেগুলোর অভিঘাত ছিল অনেক গভীর আর অস্বস্তিজনক। বিশেষ করে আমার কাছে মনে হয়েছে, আমি যেন নিজের অজান্তেই অন্য কারো ছায়ায় দাঁড়িয়ে আছি, যেখানে নিজের কণ্ঠস্বরটাই চাপা পড়েছে। অপর দিকে যাঁদের লেখা আমার নামে ছাপা হয়েছে জানার পর তাঁদের মনের অবস্থাটাও যে খুব একটা ভাল ছিল না, সেটা সহজেই অনুমেয়। এই অভিজ্ঞতা এক ধরনের অস্তিত্বগত অস্বস্তি তৈরি করেছে, যা শুধুই ব্যক্তিগত নয়; বরং বুদ্ধিবৃত্তিক ও নৈতিক সংকটেরও ইঙ্গিতবাহী। এই জায়গায় এসে রবীন্দ্রনাথের সেই বিড়ম্বিত উচ্চারণের প্রতিধ্বনি যেন শুনি, যেখানে খ্যাতি কোনো আরাধ্য নয়, বরং হয়ে ওঠে এক বোঝা যা বহনের দায়ে মানুষ ক্লান্ত, জর্জরিত, এমনকি নিজেকেই হারিয়ে ফেলে। যদিও আমার ক্ষেত্রে বিষয়টি খ্যাতির নয়; বরং এক বিভ্রান্তিকর প্রতিচ্ছবির, যা আমার চিহ্ন না রেখেই আমার হয়ে কথা বলছে। এই বিড়ম্বনা, এই অপার বেদনার ভিতর থেকেই এই ব্যাখ্যা দেওয়ার প্রয়োজন অনুভব করেছি; নিজেকে স্পষ্ট ও সৎভাবে উপস্থিত করার জন্য, এবং নিজের দায় নিজেই গ্রহণ করার দায়বদ্ধতা থেকে।
প্রথম ঘটনাটি ঘটে এক সুহৃদের আন্তরিক অনুরোধের সূত্রে। তিনি তাঁর একটি লেখা আমাকে পাঠিয়ে বলেন, একটি নির্দিষ্ট জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় তা প্রকাশে আমি যেন তাঁকে সহায়তা করি। আমি লেখাটি সংশ্লিষ্ট পত্রিকার সম্মানিত সম্পাদকের কাছে পাঠাই এবং সচেতনভাবে তাঁর ইমেইল ঠিকানাও সংযুক্ত করি, যেন তিনি সরাসরি লেখকের সঙ্গেই যোগাযোগ করতে পারেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে, মনে হয় তিনি আমার ইমেইল মনোযোগ দিয়ে পড়ার সুযোগ পাননি এবং ভেবেছিলেন যে ইমেইলে সংযুক্ত লেখাটি আমারই। যেমন ভাবা তেমন কাজ। ফলাফল হিসেবে যে সাপ্তাহে কর্মব্যস্ততায় আমি কোনো লেখা পাঠাতে পারিনি, সে সাপ্তাহে ওই লেখাটি তিনি আমার নামে প্রকাশ করেছেন এবং তিনি সেই প্রকাশিত লেখার অনলাইন ভার্সানের লিংকও আমাকে পাঠান।
লিংকে গিয়ে লেখাটির শিরোনাম পড়েই আমি চমকে উঠি। এই তো সেই মুহূর্ত, যখন পেশাগত সংকল্প আর মানবিক বিব্রতবোধ একসঙ্গে ধাক্কা দেয়। মনে পড়ল দার্শনিক ইমানুয়েল কান্টের সেই নীতিবাক্য: ‘নীতির মানদণ্ড হওয়া উচিত এমন আচরণ, যা তুমি চাও সবাই অনুসরণ করুক’। আমি কি এমন আচরণ অনুমোদন করি? না। কাজেই আমি লজ্জা ও বিব্রতবোধ থেকে সঙ্গে সঙ্গে সম্পাদককে আগে প্রেরিত ইমেইলটি ফরওয়ার্ড করি এবং অনুরোধ জানাই যেন অনলাইন সংস্করণে সংশোধন আনা হয় ও প্রকৃত লেখকের কাছে দুঃখ প্রকাশ করা হয়। পত্রিকা কর্তৃপক্ষ প্রশংসনীয় দ্রুততায় অনলাইনে সংশোধনী আনে এবং আমার সেই সুহৃদ তাতে এতটাই খুশি হন যে, তিনি আমাকে ‘পুরস্কৃত’ করতে চান! কিন্তু ততক্ষণে আমি এমন এক আত্মগ্লানিতে আচ্ছন্ন, এমন সংকোচে ডুবেছিলাম যে, তাঁর সঙ্গে স্বাভাবিকভাবে কথাও বলতে পারছিলাম না। এ যেন এমন এক লজ্জা, যা শুধু আত্মপ্রবঞ্চনার ভয় থেকে নয়, বরং নিজের নৈতিক অবস্থান থেকে কারো প্রশ্নের মুখে পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থেকে জন্ম নেয়।
দ্বিতীয় ঘটনাটি ঘটে রমজানের শেষ সপ্তাহে, যখন আত্মসংশ্লেষ ও আত্মনিয়ন্ত্রণের ভাবনাই মনোজগতকে আচ্ছন্ন করে রাখে। লেখালেখি থেকে তখন কিছুটা মনোযোগ সরে গিয়েছিল, ফলে সেই সাপ্তাহে কাউকেই কোনো লেখা পাঠানো হয়নি। এমন সময় ফেসবুকে অনুজপ্রতীম সতীর্থের একটি অসাধারণ পোস্ট নজরে আসে যেটা পড়ে চিন্তায়, ভাষায় ও সংবেদনায় মন ছুঁয়ে যায়। সেটি হুবহু কপি করে, যথাযথভাবে লেখকের নাম উল্লেখ করে, আমি আমার টাইমলাইনে শেয়ার করি এই ভেবে যে, এটাকে আরও বেশি মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া উচিত। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে, আমার ফেসবুক টাইমলাইনের সেই শেয়ারকৃত লেখাটিই আমার পরিচিত আরেক সম্পাদক সাহেব, সম্ভবত অসাবধানতাবশত লেখার নিচে লেখকের নাম তাঁর নজর এড়িয়ে গিয়েছে, আমার নামেই তাঁর দৈনিকে ছেপে দেন। এক অতিউৎসাহী পাঠক সেই পত্রিকার ই-পেপারের লিংক আমাকে পাঠালে লেখাটির শিরোনাম দেখে আমি বিব্রত হয়ে পড়ি। সাথে সাথে সম্পাদক সাহেবকে বিষয়টি অবহিত করি, তিনি দুঃখ প্রকাশ করেন এবং পরবর্তী সংখ্যায় এ বিষয়ে একটি সংশোধনী ছাপেন।
এখানে প্রশ্ন শুধু তথ্যগত সঠিকতা নয়, প্রশ্ন লেখার প্রকৃত স্বত্ত্বধিকার বা মালিকানা, এবং পেশাগত ও নৈতিক দায়বদ্ধতার পাশাপাশি চিন্তার উৎসকে যথাযথ সম্মান জানানো। হান্না আরেন্ড যে ‘নির্বাক নৈতিকতা’র বিরুদ্ধে সরব হতে বলেছিলেন, এই ঘটনা যেন তারই এক বাস্তব পাঠ। জ্ঞান বা চিন্তা যতই মূল্যবান হোক না কেন, তা যখন প্রকৃত লেখককে বাদ দিয়ে অন্যের নামে ছাপা হয়, তখন তা কেবল একজন লেখকের প্রতিই অবিচার নয়, বরং সেটা পাঠকের প্রতিও একপ্রকার বঞ্চনা। সেই বোধ থেকেই আমি সম্পাদক সাহেবের সঙ্গে যোগাযোগ করি, কোনো অভিযোগ করার জন্য নয়, বরং একটি নৈতিক অবস্থান থেকে বিষয়টাকে তুলে ধরার জন্য। এ কথা নিঃসন্দেহে সত্য যে, দু’টি ঘটনাই নিছক ভুল; কোনো অমঙ্গলজনক অভিপ্রায় থেকে ঘটেনি। তবু ইতিহাস আমাদের শেখায়, ভুলের দায় এড়িয়ে যাওয়া যেমন দৃষ্টিকটু, তেমনি ভুল থেকে শিক্ষালাভ না করাও একটি গুরুতর ব্যর্থতা। সেই বিবেচনায়, এই অনভিপ্রেত অভিজ্ঞতা থেকে কয়েকটি মূল্যবান শিক্ষা গ্রহণ করাকে আমি আমার পেশাগত ও নৈতিক দায়িত্ব বলে মনে করি।
প্রথমত, পত্রিকা কর্তৃপক্ষের উচিত লেখকের সঙ্গে নিবিড় যোগাযোগ স্থাপন ও সেটা রক্ষা করা। কোন নির্বাচিত লেখা চূড়ান্তভাবে প্রকাশের আগে লেখককে অবহিত করলে, যেকোনো বিভ্রান্তি বা সম্পাদনাগত মানবিক ও পেশাগত ভুল সংশোধনের একটি সুযোগ তৈরি হয়। লেখক-সম্পাদক সম্পর্ক কেবল কাগুজে যোগাযোগে সীমাবদ্ধ থাকলে ভুল বেড়ে যায়, আর তার দায় বর্তায় উভয় পক্ষের ওপরেই। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার আলোকে বলা যায়, আমাদের দেশের ছাপা গণমাধ্যমগুলোর পেশাদারিত্বকে আরো শানিত ও দায়িত্বশীল করা উচিত বলে মনে করছি। লেখকের লেখা পেলে তার জন্য প্রাপ্তি স্বীকার ও ছাপা আগে জানানো যে কোন লেখাটি কোন সংখ্যায় যাচ্ছে। তাতে নি:সন্দেহে এ ধরনের ভুল হওয়ার সম্ভাবনা কমে যাবে।
দ্বিতীয়ত, আমার নিজের পক্ষ থেকেও আরও স্পষ্টভাবে সম্পাদকের সাথে যোগাযোগ স্থাপনের চেষ্টা করা জরুরি ও সেখানে দু’পক্ষেরই আরো দায়িত্বশীল হওয়া দরকার। ভবিষ্যতে যখন অন্যের লেখা কোনো ছাপার গণমাধ্যমে প্রকাশের জন্য সুপারিশ করব, তখন আমাকে দ্ব্যর্থহীনভাবে জানাতে হবে যে, সেটি আমার নিজের লেখা নয়, যাতে করে সে লেখাটি প্রকাশের ক্ষেত্রে যেন কোনো সম্পাদনাগত, ব্যবস্থাপনাগত বা প্রশাসনিক ভুলের সুযোগ না থাকে। একইভাবে মনে রাখতে হবে যে, ফেসবুকে কোনো লেখা শেয়ার করার সময় শুধু লেখকের নাম উল্লেখ করলেই দায়িত্ব শেষ হয় না। যেহেতু লেখা আমার নয়, সেহেতু সেটাকে উদ্ধৃতির মাঝে রাখা উচিত। অপরদিকে যেকোনো পুনঃপ্রকাশ বা ভিন্ন পরিপ্রেক্ষিত থেকে ব্যাখ্যার সম্ভাব্য ঝুঁকির বিষয়েও আমাকে সতর্ক থাকতে হবে।
আসলে আমাদের দৈনন্দিন পেশাগত ও সামাজিক আচরণে সতর্কতার অভাব, দ্রুততা ও অনুমানভিত্তিক সিদ্ধান্তের যে প্রবণতা রয়েছে, এই দুটি ঘটনাই তার প্রতিফলন। সোফোক্লিস তাঁর ট্র্যাজেডিতে বলেন, ‘জ্ঞান থাকলেই ভুল হয় না, কিন্তু ভুল থেকেই জ্ঞান জন্ম নিতে পারে’—আমি এই ঘটনা দু’টো থেকে সেই শিক্ষাটিই গ্রহণ করতে চাই।
পরিশেষে স্পষ্ট করে বলতে চাই, এটি কোনো খ্যাতির বিড়ম্বনা নয়, বরং ব্যক্তি ও পেশার প্রতি আমার দায়িত্ববোধ থেকে জন্ম নেওয়া এক বিব্রতকর অভিজ্ঞতা। ভুলগুলো নিঃসন্দেহে অনিচ্ছাকৃত, কিন্তু সে কারণেই তা এড়ানো যেত যদি ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান উভয়পক্ষই পেশাগতভাবে আরো সতর্ক, সংবেদনশীল ও দায়বদ্ধ হতো। পেশাগত জগতে কখনো কখনো আমাদের আত্মপরিচয়ের বাইরে গিয়ে নতুন চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে হয়। এ অভিজ্ঞতা আমার জন্য তেমনই এক পাঠ, যা আমাকে আরও মননশীল, সংবেদনশীল ও দায়িত্বশীল হতে অনুপ্রাণিত ও সর্তক করবে। আমি বিশ্বাস করি, ভুল শুধরে নেওয়ার মধ্যে দুর্বলতা নয়, বরং তা সততা ও শক্তির প্রকাশ। প্রিয় পাঠক এবং পত্রিকা কর্তৃপক্ষ; আপনারা আমার লেখার সঙ্গী, আমার সংলাপ, বয়ান ও আলোচনার শ্রোতা, চিন্তাভাবনা ও চেতনার অংশীদার, আর তাই এই অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতিতে আপনাদের সবার আন্তরিক সহানুভূতিও আমার প্রাপ্য। আপনাদের সহৃদয় বিবেচনাবোধ ও ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে এই অনাঙ্খিত ভুলগুলোকে দেখার বিনীত অনুরোধ রইলো।
ড. মাহরুফ চৌধুরী, ভিজিটিং ফ্যাকাল্টি, ইউনিভার্সিটি অব রোহ্যাম্পটন, যুক্তরাজ্য। mahruf@ymail.com

মত দ্বিমত
উন্নত দেশে সন্তান সংকট, বাংলাদেশ কি সুযোগ নিতে পারবে?
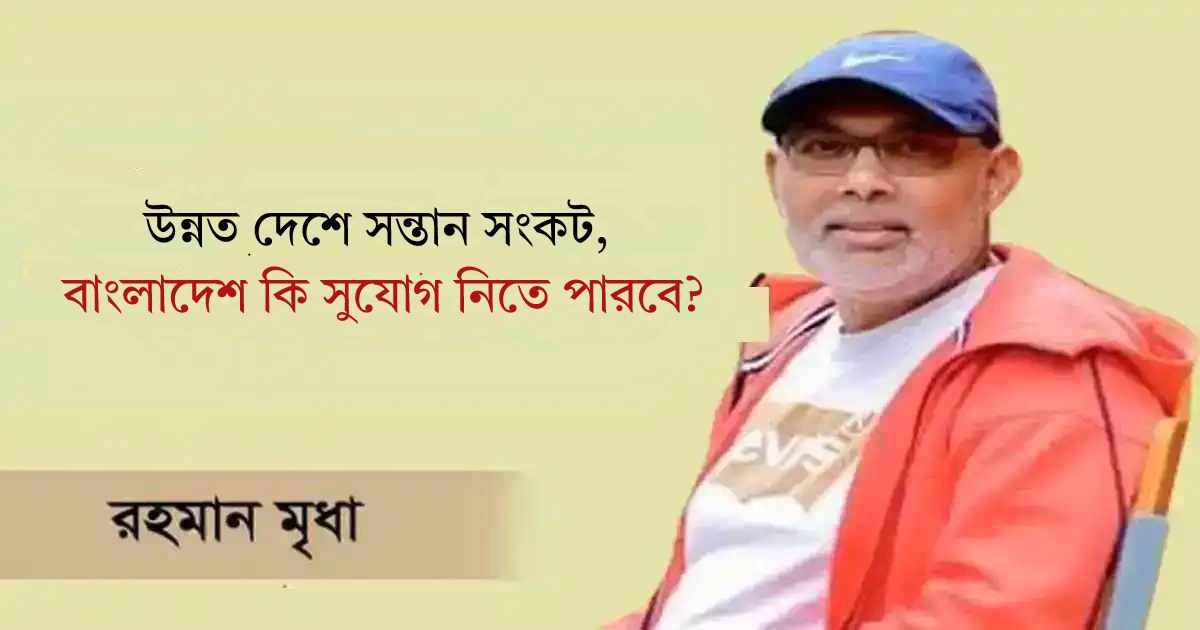
সুইডেন-বিশ্বের অন্যতম উন্নত ও মানবকল্যাণমুখী রাষ্ট্র। এখানে নাগরিকদের জন্য রয়েছে বিনামূল্যে স্বাস্থ্যসেবা, দীর্ঘমেয়াদী মাতৃত্ব ও পিতৃত্বকালীন ছুটি, সন্তানের জন্মের পর আর্থিক ভাতা, উন্নতমানের ডে-কেয়ার সুবিধা, এমনকি সন্তান পালনের সময় চাকরি হারানোর আশঙ্কাও নেই। তারপরও, আশ্চর্যজনকভাবে, এই দেশটিতেই জন্মহার আশঙ্কাজনকভাবে কমে যাচ্ছে।
২০২৪ সালে প্রতি নারী গড়ে মাত্র ১.৫৩টি সন্তানের জন্ম দিয়েছেন, যা জনসংখ্যা স্থিতিশীল রাখার জন্য প্রয়োজনীয় ২.১-এর অনেক নিচে। জনসংখ্যাবিদরা (demografiska experter) সতর্ক করে বলছেন—এই ধারা অব্যাহত থাকলে ভবিষ্যতে সুইডেনও পড়বে এক মারাত্মক শ্রমশক্তি সংকটে। বয়স বেড়ে যাওয়া জনগোষ্ঠীর ভারে ভেঙে পড়তে পারে তাদের সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা।
তাহলে প্রশ্ন দাঁড়ায়: কেন এই জন্মহ্রাস?
গবেষণা বলছে, শুধু আর্থিক সুযোগ-সুবিধা বাড়ালেই মানুষ সন্তান নিতে আগ্রহী হবে—এই ধারণা এখন আর বাস্তবসম্মত নয়। আধুনিক জীবনের জটিল বাস্তবতা, ব্যক্তিগত স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা, ক্যারিয়ার ও আত্ম-সিদ্ধির প্রতিযোগিতা, পারস্পরিক সম্পর্কের অনিশ্চয়তা এবং ভবিষ্যৎ নিয়ে গভীর উদ্বেগ—এসব মিলিয়ে তরুণ প্রজন্মের কাছে সন্তান নেওয়া হয়ে উঠেছে এক বিব্রতকর সিদ্ধান্ত।
অনেকেই এখন মনে করেন, সন্তান নেওয়া আর শুধু সামাজিক দায়িত্ব নয়, বরং এটি একটি কঠিন ও গভীর ব্যক্তিগত বিবেচনার বিষয়, যা জীবনের ছন্দ ও স্বাধীনতা পুরোপুরি পাল্টে দিতে পারে। সুইডেনের মতো সমাজে যেখানে “স্বাধীন জীবনধারা” ও “ব্যক্তিগত স্বাচ্ছন্দ্য” খুবই গুরুত্বপূর্ণ—সেখানে সন্তান জন্মদানের সিদ্ধান্ত নিতে মানুষ দারুণ দ্বিধায় পড়ে যায়।
একটি ঘোলাটে পৃথিবীর মুখোমুখি তরুণ প্রজন্ম
এই বাস্তবতা শুধু ব্যক্তিগত নয়—এটি বিশ্ব ব্যবস্থার প্রতিফলন। আজকের তরুণরা প্রশ্ন করছে: “এই পৃথিবী কি আদৌ নতুন প্রাণকে স্বাগত জানানোর জন্য উপযুক্ত?” বিশ্বজুড়ে রাজনৈতিক অস্থিরতা, যুদ্ধ, জলবায়ু সংকট, নিরাপত্তাহীনতা, দুর্নীতি ও লুটপাট, পরিবেশের ভয়াবহ অবনতি, এবং সর্বশেষ কোভিড-১৯ মহামারির অভিঘাত—সব মিলিয়ে পৃথিবীর চিত্র হয়ে উঠেছে অনিশ্চিত, বিভ্রান্তিকর ও ভীতিকর। এমন এক বাস্তবতায় অনেক তরুণই সন্তান নেওয়ার কথা চিন্তা করেই আতঙ্কিত হয়ে পড়ে।
সুইডেনের মতো শান্তিপূর্ণ ও কল্যাণমুখী রাষ্ট্রের তরুণরাও প্রশ্ন তুলছে: “আমি কি সন্তান আনবো এমন এক পৃথিবীতে, যেখানে মানুষ মানুষের জন্য নিরাপদ নয়? যেখানে রাজনীতি হয়ে উঠেছে এক ব্যক্তিগত প্রজেক্ট, এবং ভবিষ্যৎ যেন এক অন্ধকার গুহা?”
এই মানসিকতা আজ সমগ্র পশ্চিমা সমাজেই ছড়িয়ে পড়ছে। সন্তান জন্মদান এখন আর শুধু একটি জৈবিক সিদ্ধান্ত নয়—এটি হয়ে উঠেছে এক নৈতিক দ্বন্দ্ব। নতুন জীবন আনতে গেলে প্রথমে প্রশ্ন করা হচ্ছে—এই পৃথিবী কি আদৌ তার যোগ্য?
বাংলাদেশের জন্য কী শিক্ষা?
বাংলাদেশে এখনো জন্মহার তুলনামূলকভাবে বেশি, যদিও তা ধীরে ধীরে স্থিতিশীলতার দিকে যাচ্ছে। তবে প্রশ্ন হলো: আমরা কি শুধুই সংখ্যায় বড় হতে চাই, নাকি গুণে বড় হতে চাই?
সুইডেনের অভিজ্ঞতা আমাদের শেখায়—শুধু ভাতা, সুযোগ-সুবিধা বা অনুপ্রেরণামূলক পোস্টার দিয়ে সন্তান নেওয়ার হার বাড়ানো যায় না। প্রয়োজন রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক মনোভাবের পরিবর্তন, মানসিক নিরাপত্তা, নারী-পুরুষের দায়িত্ব ভাগাভাগির সংস্কৃতি এবং মাতৃত্ব-পিতৃত্বকে সম্মান করার প্রবণতা। বাংলাদেশে আজও বহু নারী সন্তান নেওয়ার পর কর্মজীবন থেকে ছিটকে পড়েন। শহরে সীমিত পরিসরে কিছু ডে-কেয়ার থাকলেও গ্রামে সেগুলোর অস্তিত্ব নেই বললেই চলে। একজন শিক্ষিত নারী মাতৃত্ব গ্রহণ করলেই যেন তার সামাজিক ও পেশাগত পরিচয় মুছে যায়। এই বাস্তবতা পাল্টাতে না পারলে শুধু ‘সংখ্যা’ দিয়ে দেশ গড়া সম্ভব নয়।
আমাদের করণীয় কী?
পারিবারিক সহায়তার সংস্কৃতি গড়ে তুলতে হবে, যেখানে মাতৃত্ব কেবল নারীর একক দায়িত্ব নয়, বরং পরিবার ও সমাজের সম্মিলিত দায়িত্ব। নারীর কর্মক্ষেত্রে অধিকার ও সুযোগ বাড়াতে হবে, বিশেষত মাতৃত্বকালীন সময় ও পরে। প্রজনন স্বাস্থ্য, যৌন শিক্ষা ও দায়িত্বশীল পিতৃত্ব বিষয়ে সচেতনতা গড়ে তুলতে হবে, যাতে সন্তান নেওয়ার সিদ্ধান্ত হয় সচেতন, যৌথ ও পরিকল্পিত। শিশুদের জন্য মানসম্মত সেবা নিশ্চিত করতে হবে—ডে-কেয়ার, পুষ্টি, প্রাথমিক শিক্ষা ও নিরাপত্তা।
কিন্তু সংকটের মাঝেই সম্ভাবনার দরজা
যেখানে পশ্চিমা বিশ্ব ধীরে ধীরে কর্মক্ষম জনসংখ্যার সংকটে নিপতিত হচ্ছে, সেখানে বাংলাদেশের রয়েছে বিশাল ও তরুণ জনগোষ্ঠী—যেটি একদিকে যেমন সম্ভাবনা, তেমনি আরেকদিকে বিশাল দায়িত্ব।
কিন্তু যদি আজই আমরা আমাদের তরুণ প্রজন্মকে—
• সময়োপযোগী ও চাহিদাভিত্তিক শিক্ষা,
• প্রযুক্তিনির্ভর ও বহুভাষিক দক্ষতা,
• নৈতিকতা ও আন্তর্জাতিক বাস্তবতায় কার্যকর প্রস্তুতি
দিয়ে গড়ে তুলতে পারি—তবে বাংলাদেশ হতে পারে ভবিষ্যতের জন্য বিশ্বের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মানবসম্পদ সরবরাহকারী দেশ।
জার্মানি, সুইডেন, জাপান, ইতালি, দক্ষিণ কোরিয়া বা চীন—এই দেশগুলো আগামী দশকে অভিবাসী কর্মীর জন্য চাহিদায় পরিপূর্ণ হবে। তখন বাংলাদেশ যদি প্রস্তুত থাকে, তবে শুধু রেমিট্যান্সের প্রবাহ নয়, বিশ্বব্যবস্থায় নেতৃত্ব দেওয়ারও সুযোগ তৈরি হবে।
ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত হলেও নেতৃত্বের সম্ভাবনা এখনই
একটি তরুণ শ্রমশক্তির জাতি হয়ে দাঁড়িয়ে বাংলাদেশ চাইলে দুটি কাজ একসাথে করতে পারে- নিজস্ব শ্রমবাজারে উৎপাদনশীলতা ও কর্মসংস্থানের সুযোগ বাড়ানো, এবং বিশ্বের জনসংখ্যা সংকটে সহানুভূতিশীল, দক্ষ, মানবিক ও আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন শ্রমশক্তি রপ্তানি করা।
এই যুগে যারা নেতৃত্ব দিতে চায়, তাদের শুধু সমস্যা দেখা যথেষ্ট নয়—সমাধান খুঁজে নেয়ারও সাহস থাকতে হয়। বাংলাদেশ সেই সাহস দেখাতে পারে। যেখানে বিশ্ব ভবিষ্যতের দোটানায় দিশেহারা, বাংলাদেশ সেখানে হয়ে উঠতে পারে আশা ও আত্মবিশ্বাসের প্রতীক। যেখানে অন্যরা নৈরাশ্যে স্তব্ধ, আমরা সেখানে হতে পারি সাহস, সদিচ্ছা ও সম্ভাবনার প্রতিনিধি।
শেষ কথা
সন্তান নেওয়া আজ আর নিছক ব্যক্তিগত বা পারিবারিক সিদ্ধান্ত নয়, এটি এক গভীর সামাজিক, রাষ্ট্রীয় ও নৈতিক প্রশ্ন। সুইডেনের অভিজ্ঞতা আমাদের শেখায়—আর্থিক প্রণোদনার পাশাপাশি, ভবিষ্যৎকে সত্যিই বাসযোগ্য করে তুলতে না পারলে নতুন প্রাণের আগমনে মানুষ দ্বিধায় পড়বেই। তবে বাংলাদেশের সামনে আজ এক দুর্লভ সুযোগ—এই ঘোলাটে বিশ্বে যদি আমরা নিজেদের প্রস্তুত করতে পারি, তবে আমরাই হয়ে উঠতে পারি সেই জাতি, যে বিশ্বকে শুধু শ্রমশক্তি নয়, নেতৃত্ব ও নৈতিকতার আলোকবর্তিকা দেবে। সারাদিন দুর্নীতিবাজ রাজনীতিবিদদের পেছনে সময় নষ্ট না করে নিজের ভবিষ্যতের কথা ভাবুন। ভাগ্যের চাকা ঘোরাতে হলে প্রয়োজন আত্মনির্ভরতা। গড়ে তুলুন নিজেকে একজন গ্লোবাল নাগরিক হিসেবে—ভাষায়, দক্ষতায় ও মানসিকতায়। এখনই সচেষ্ট হোন। দেখবেন, ভাগ্যের দরজা আপনার জন্য খুলে গেছে।
রহমান মৃধা
সুইডেন প্রবাসী বাংলাদেশি
গবেষক, লেখক ও সাবেক পরিচালক, ফাইজার
Rahman.Mridha@gmail.com
মত দ্বিমত
আগে ছিল ঘুষখোর, পরে দুর্নীতিবাজ, এখন হয়েছে চাঁদাবাজ: উন্নয়নের উল্টো পদচিহ্ন
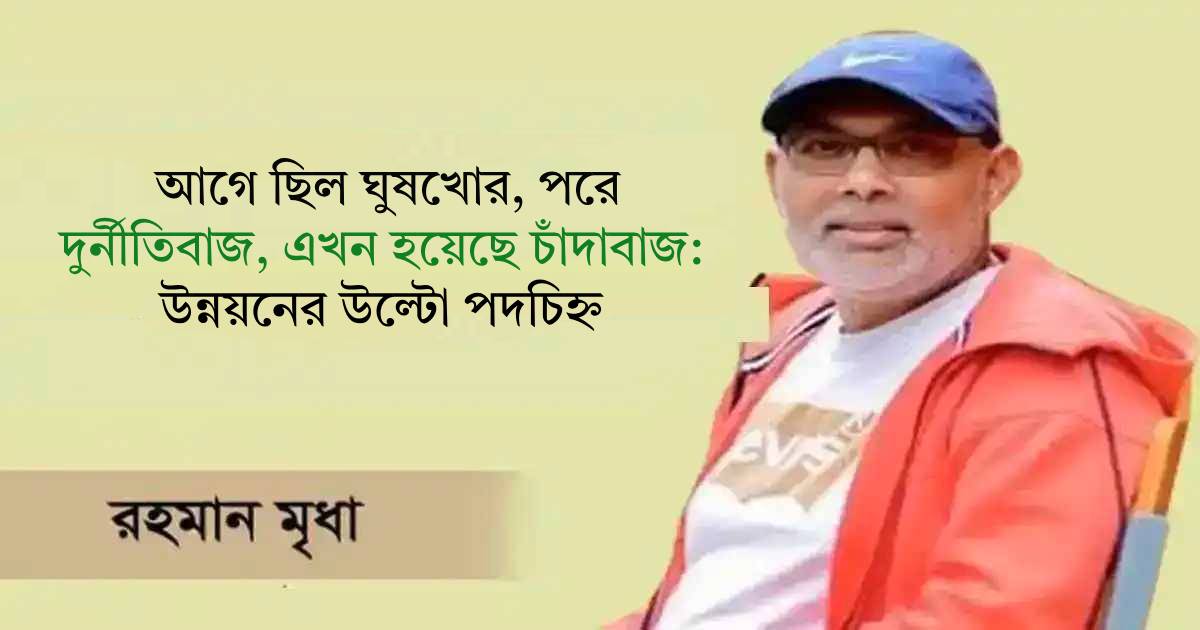
বাংলাদেশে রাষ্ট্রীয় উন্নয়নের গল্প আজকাল পত্রিকার পাতায়, টেলিভিশনের ঘোষণায় কিংবা নেতার মুখে মুখে শোনা যায়—‘দেশ বদলে গেছে’, ‘উন্নয়ন দৃশ্যমান’, ‘স্বপ্নের পদ্মা সেতু হয়েছে’, ‘ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তব’। কথাগুলো শুনতে যেমন চমকপ্রদ, বাস্তবে তেমনই একটা নির্মম প্রশ্নও উঁকি দেয়—এই উন্নয়নের সুবিধাভোগী কারা? এবং উন্নয়ন বলতে আমরা কি কেবল ভবন, সেতু, কিংবা GDP বুঝি, নাকি মানুষ ও মনুষ্যত্বেরও কোনো মানদণ্ড আছে? একসময় যাদের আমরা বলতাম ঘুষখোর, তারা ছিল লোকচক্ষুর আড়ালে; একটা টেবিলের নিচে টাকার খাম গলিয়ে দিতো, লজ্জা একটু ছিল, ভয়ও ছিল আইনের। তারপর তারা হলো দুর্নীতিবাজ—পদে বসে ক্ষমতার খোলস গায়ে দিয়ে টেন্ডার ভাগাভাগি, ব্যাংক লোন লুট, প্রজেক্ট বাজেট ফাঁকি—সবই নীতির নামে বৈধ করে ফেললো। এখন তারা চাঁদাবাজ, যারা আর লুকায় না, প্রকাশ্যেই বলে—‘এক্সট্রা দিতে হবে ভাই, নাহলে কাজ হবে না।’ এটা শুধু দুর্নীতির বিবর্তন নয়, এটা একটা জাতির বিবেক হারানোর ইতিহাস।
বাংলাদেশের সংবিধানে লেখা আছে— ‘রাষ্ট্রের প্রধান দায়িত্ব হবে জনগণের কল্যাণ সাধন।’ কিন্তু বাস্তবে রাষ্ট্র যেন এক সিন্ডিকেট চালিত পণ্যবাজার—যেখানে প্রশাসন, পুলিশ, রাজনীতি, ব্যবসা এমনকি বিচারব্যবস্থাও অনেক ক্ষেত্রে একটি জালায় বাঁধা, যার মধ্যে সৎ থাকতে গেলে ডুবে যেতে হয়। ১৯৭১-এর যুদ্ধ ছিল একটি মুক্তির স্বপ্ন। তখন সেনাবাহিনীর সর্বোচ্চ পদ ছিল মেজর জেনারেল, সীমিত শক্তি, সীমিত সুযোগ, কিন্তু ছিল একরকম দেশপ্রেম। সময়ের সাথে সাথে যখন পদোন্নতি হলো—লেফটেন্যান্ট জেনারেল, তারপর জেনারেল—তখন কি শুধু দপ্তর বড় হলো, নাকি লোভও বড় হলো? একদিকে জিপি লাইন, পাজেরো, প্রটোকল, অন্যদিকে গরিব রিকশাচালক, অসুস্থ কৃষক, চাকরির জন্য হাহাকার করা তরুণ। উন্নয়নের তুলাদণ্ড কি দু’পাশে সমান ভার বহন করেছে? রাষ্ট্র যখন নাগরিকের ভরণপোষণের দায়িত্ব পালন করতে ব্যর্থ হয়, তখন নাগরিক হয় নিঃস্ব—অথবা বিক্রি হয়ে যায়। আজকের যুবক চাকরির আশায় ঘুষ দেয়, শিক্ষকতা পেতে ঘুষ দেয়, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্য হতে ঘুষ দেয়। তারপর যখন সে চাকরিটা পায়, তখন প্রথম কাজ হয় সেই ঘুষের টাকা সুদে আসলে তুলতে হবে—ঘুষ খেতে হবে, চাঁদা তুলতে হবে, মানুষকে জিম্মি করতে হবে। এভাবে দুর্নীতি একটা চাকরির অনুষঙ্গ হয়ে যায়, আর চাঁদাবাজি হয়ে যায় নৈতিকতার পরিণতি।
যে রাষ্ট্রের হাসপাতাল অচল, শিক্ষাব্যবস্থা লুটেরাদের হাতে, বিচারব্যবস্থা পক্ষপাতদুষ্ট, গণমাধ্যম ভীত, সেই রাষ্ট্র কিসের উন্নয়ন দেখাচ্ছে? রাষ্ট্র যদি মানুষকে সুশিক্ষা, সুবিচার, এবং নিরাপদ জীবন দিতে না পারে, তাহলে সেটা কেবল একটি ক্ষমতার যন্ত্র—যা দুর্নীতিবাজ, ঘুষখোর, আর চাঁদাবাজদের জন্য অপারেশনাল। একটা সময় ছিল—স্কুলের দেওয়ালে লেখা থাকত, “জ্ঞানই শক্তি”, কিংবা “কৃষিই জাতির মেরুদণ্ড”। কিন্তু আজকে এই কথাগুলো কেবল দেয়ালে রয়ে গেছে, বাস্তবতায় তারা মুছে গেছে। বরং এখন যেন রাষ্ট্রের অদৃশ্য সংবিধান হচ্ছে—‘ঘুষ দাও, চাঁদা দাও, অন্যথায় তোমার অস্তিত্ব থাকবে না।’
আমরা যে প্রজন্ম তৈরি করছি, তারা চোখ থাকতেও অন্ধ। একদিকে প্রশ্নপত্র ফাঁস, অন্যদিকে স্কুলশিক্ষকের গায়ে হাত তোলা—এই সবই একই সমাজের চিত্র। আজকের শিক্ষা ব্যবস্থায় নেই নৈতিকতা, নেই চিন্তার স্বাধীনতা, নেই কর্মমুখী দিকনির্দেশনা।
বিশ্ববিদ্যালয় এখন দলীয় অফিসে রূপ নিয়েছে, আর ছাত্ররাজনীতি মানে অস্ত্র, দখল আর ভয় দেখানো। শিক্ষক হয়ে উঠেছেন শোষণ ও নিয়ন্ত্রণের যন্ত্র, আর ছাত্র হয়ে উঠেছে ক্ষমতাবানের ভবিষ্যৎ বাহিনী।
জেনে হোক কিংবা না জেনে, আমরা গড়ে তুলছি এক নিষ্প্রভ, মেধাহীন ও চাটুকার প্রজন্ম—যাদের হাতে তুলে দিচ্ছি প্রশ্নফাঁস, গাইড বই, কোচিং নির্ভরতা, ঘুষ দিয়ে পাওয়া নিয়োগপত্র, আর ক্যাম্পাসজুড়ে দলীয় ক্যাডারতন্ত্র। যে শিক্ষার হাত ধরে জাতি গড়ার কথা ছিল, সেই শিক্ষাই আজ জাতি ভাঙার কারখানায় পরিণত হয়েছে।
আমরা মুখে সৃজনশীলতার কথা বলি, অথচ পাঠ্যবই মুখস্থ ছাড়া পাসের সুযোগ নেই। আমরা নৈতিকতার কথা বলি, অথচ শিক্ষকের চাকরি হয় টাকার বিনিময়ে। যেখানে শিক্ষকই ঘুষ দিয়ে আসেন শ্রেণিকক্ষে, সেখানে ছাত্র কেন শিখবে সততার পাঠ? আর যখন রাষ্ট্র নিজেই শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে ‘তেল মন্ত্রণালয়’তে রূপ দেয়, তখন তরুণ প্রজন্মের মেরুদণ্ড ভেঙে যাওয়াটাই তো স্বাভাবিক।
আমরা দেশজ উৎপাদনের চেয়ে আমদানিকে বড় করে তুলেছি। কৃষক যখন মাঠে ফসল পচিয়ে ফেলে দেয়, তখনই বাজারে ঢুকে পড়ে বিদেশি চাল, ডাল, পেঁয়াজ। কৃষকের পাশে দাঁড়ায় না কেউ—না সরকার, না মিডিয়া, না ব্যাংক। ঘুষ দিয়ে তাকে কিনতে হয় সেচের পানি, দালালের কাছ থেকে নিতে হয় সরকারি বীজ-সার। আর সে ফসল যখন ফলায়, তখন বাজারে দাম থাকে না।
শিল্পখাতের চিত্র আরও করুণ। একের পর এক কলকারখানা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, দক্ষ জনশক্তি পাড়ি জমাচ্ছে বিদেশে—দেশে রয়ে যাচ্ছে শুধু অব্যবস্থা আর আমলাতন্ত্রের জঞ্জাল। আমরা এখন একটা “ভোগী জাতি”—নিজে কিছু উৎপাদন না করেই শুধু ভোগ করতে চাই। চীন, ভারত কিংবা তুরস্কের ওপর নির্ভর করেই চলছে আমাদের অর্থনীতি। অথচ সরকার বলে—“আমরা মধ্যম আয়ের দেশে পৌঁছেছি।” প্রশ্ন হলো—এই উন্নয়ন কার জন্য? যেখানে গার্মেন্টস শ্রমিক ১২ ঘণ্টা খেটে ১২ হাজার টাকা পায়, আর এক প্রকল্প পরিচালক ১ কোটি টাকায় গাড়ি কেনে—সেটি কি উন্নয়ন, নাকি লুণ্ঠনের ছদ্মবেশ? সবচেয়ে ভয়াবহ চিত্র যুবসমাজে। তারা শিক্ষিত হচ্ছে, কিন্তু কর্মসংস্থান পাচ্ছে না। মেধাবী যুবক যখন মাসের পর মাস, বছরের পর বছর বেকার থাকে, তখন একসময় সে বাধ্য হয় বিকল্প খুঁজতে—আর সেই বিকল্পের নাম হয় ‘যুবলীগ’ বা ‘যুবদল’। সেখানে চাকরি নেই, কিন্তু পিস্তল আছে; বেতন নেই, কিন্তু চাঁদা আছে; ভবিষ্যৎ নেই, কিন্তু মাদক আছে। রাষ্ট্র তার সবচেয়ে সম্ভাবনাময় শক্তি—তরুণ সমাজকে—নিজেই অস্ত্র তুলে দিচ্ছে, গডফাদারদের ছত্রছায়ায় গড়ে তুলছে একেকটি সন্ত্রাসী ইউনিট।
আজকের ছাত্র রাজনীতি মানেই চাঁদাবাজি, নিয়োগ বাণিজ্য, টিকটকে ‘লাইভ মারামারি’। একজন তরুণ যখন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাস করেও তিন বছর ধরে চাকরি খুঁজে পায় না, তখন তার স্বপ্ন আর কৃষি, স্টার্টআপ, প্রযুক্তি কিংবা শিল্পের দিকে যায় না—গিয়ে পড়ে রাজনৈতিক ছত্রছায়ার বন্দুকের নিচে। রাষ্ট্র যখন তার যুবসমাজকে স্বপ্ন না দিয়ে অস্ত্র দেয়, তখন সে রাষ্ট্র কেবল মেরুদণ্ডহীনই হয় না—সে আত্মঘাতী হয়ে ওঠে।
গণতন্ত্রে বলা হয়, “মানুষই মালিক।” কিন্তু বাংলাদেশের বাস্তবতায় সাধারণ মানুষ যেন কেবল ভোটের দিনই মানুষ, তারপর সে হয়ে যায় এক নির্বাক, অধিকারহীন ভিখারি। রাস্তা বানানো হয় ভিআইপি’র জন্য, হাসপাতালের উন্নয়ন হয় বিশেষ গোষ্ঠীর জন্য, আর নীতি নির্ধারিত হয় কর্পোরেট ক্লাবের কাচঘেরা কক্ষে বসে। কৃষক, শ্রমিক, প্রবাসী শ্রমজীবী—তারা যেন কেবল উন্নয়নের ভাষণকে অলংকৃত করার জন্য ব্যবহৃত হয়, কিন্তু নীতির কেন্দ্রে নয়।
প্রশ্নটা বারবার ফিরে আসে—এই রাষ্ট্রটা কার? যাদের ঘামে পথ তৈরি হয়, গায়ে রোদ লাগে, তারাই কি এই রাষ্ট্রের মালিক? না কি তারা, যাদের টাকা সুইস ব্যাংকে, সন্তান বিদেশে পড়ে, বছরে একবার দেশে আসে, আর টকশোতে দেশের ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করে? রাষ্ট্র হওয়া উচিত সেই মানুষের, যিনি অন্যের ঘর তৈরি করতে গিয়ে নিজের ঘর বানাতে পারেন না। রাষ্ট্র হওয়া উচিত সেই শিক্ষকের, যিনি ছাত্রকে স্বপ্ন দেখান অথচ বেতন পান দেরিতে। রাষ্ট্রের কাজ হলো অসম্ভবকে সম্ভব করা, প্রতিভাকে জায়গা করে দেওয়া, শ্রমিকের ঘামে মাথা উঁচু করা। কিন্তু আজ রাষ্ট্র বন্দি—ধনীদের হাতে, ক্ষমতাবানদের শিকলে। আর যারা রাষ্ট্র চালায়, তারা মানুষকে দেখে ভোটের সংখ্যা হিসেবে, হৃদয়ের সত্তা হিসেবে নয়।
এই প্রশ্ন আজ আমাদের সামনে দাঁড় করিয়েছে—আমরা কাদের জন্য রাষ্ট্র গড়ছি? এমন এক রাষ্ট্র, যেখানে ঘুষ ছাড়া চাকরি হয় না, হাসপাতালে সেবা নয় বরং রাজনৈতিক সভার জন্য স্টেজ বানানো জরুরি, যেখানে মেধার চেয়ে পরিচয়, সততার চেয়ে সদস্যপদ বেশি কার্যকর। সেই রাষ্ট্রের কোনো গর্ব থাকতে পারে না। কেন এক সৎ শিক্ষক হতাশ হয়ে আত্মহত্যা করেন, আর এক চাঁদাবাজ যুবক জনপ্রতিনিধি হয়ে ওঠে? কেন উন্নয়ন মানেই হয় ভবন, রাস্তা, ব্যানার আর বিজ্ঞাপন—কিন্তু সেই উন্নয়নে থাকে না সাধারণ মানুষের স্বপ্ন, কান্না, জীবন?
আমরা চাই এমন এক রাষ্ট্র, যেখানে শিক্ষক হবেন জাতির শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি, যুবক হবে হিরো, কৃষক হবে গর্বের প্রতীক। যেখানে পুলিশ হবে মানুষের রক্ষক, কোনো দলের নয়। বিশ্ববিদ্যালয় হবে আলোর মিনার, যেখানে ছড়াবে জ্ঞানের শক্তি, মাদকের ভয় নয়। এখন সময় প্রশ্ন তোলার। এখন সময় “না” বলার। না ঘুষকে, না দুর্নীতিকে, না চাঁদাবাজিকে। রাষ্ট্র যদি মানুষের না হয়—তবে মানুষকেই রাষ্ট্র হয়ে উঠতে হবে।
আসুন, আমরা ভণ্ড মুখোশটা সরাই। জিডিপি নয়, আমরা বিচার করি—মানুষ হাসছে কি না। যদি মানুষ না থাকে, তাহলে উন্নয়ন কিসের জন্য? আজ দুর্নীতি আর অপরাধ নয়, সামাজিক দক্ষতা হয়ে উঠেছে। সৎ মানুষকে আমরা বলি বোকা, নির্লজ্জ চাঁদাবাজকে বলি স্মার্ট। এই মানসিকতা না বদলালে ‘উন্নয়ন’ কেবল কাগজে থাকবে—মানুষের জীবনে আসবে না।
আজ প্রয়োজন একটি নৈতিক মুক্তিযুদ্ধ—একটি সাহসী, সৎ ও গণমুখী সংগ্রাম, যেখানে চাঁদাবাজিকে ঘৃণা করা হবে, ঘুষখোরদের জনতার কাঠগড়ায় দাঁড় করানো হবে, আর রাষ্ট্র একদিন সাহস করে নিজের আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে বলবে— জনগণ রাষ্ট্রের কর্মচারীদের সেবক নয়, বরং কর্মচারীরাই জনগণের সেবক; এটাই একটি মানবিক, গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সত্যিকার আত্মা। যদি প্রতিজ্ঞা করি—আমি আবার জনগণের রাষ্ট্র হতে চাই। আমরা কি প্রস্তুত সেই প্রতিশ্রুতি পালন করতে?
রহমান মৃধা, সুইডেন প্রবাসী বাংলাদেশি, গবেষক, লেখক ও সাবেক পরিচালক, ফাইজার। Rahman.Mridha@gmail.com
মত দ্বিমত
রিজার্ভ বাড়ছে অথচ রেমিট্যান্স যোদ্ধারা উপেক্ষিত: কৃতজ্ঞতার মুখোশে জাতীয় বিস্মরণ?
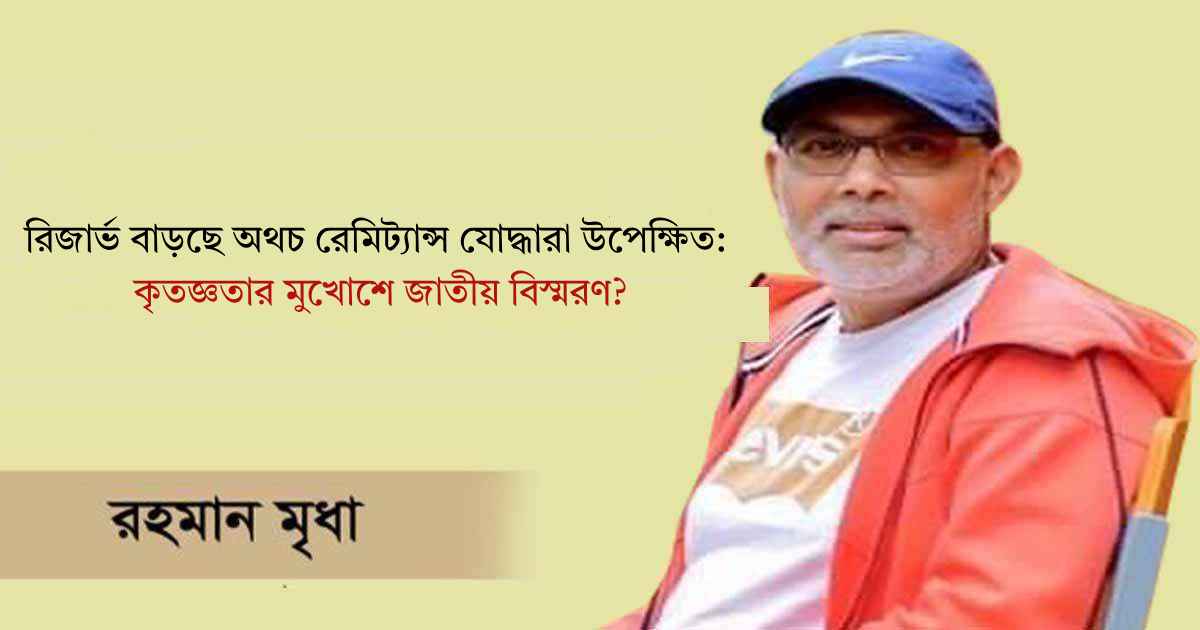
বাংলাদেশের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ আবারও ৩০ বিলিয়ন ডলার ছাড়িয়ে গেছে। নিঃসন্দেহে এটি একটি অর্থনৈতিক মাইলফলক। কিন্তু এই সাফল্যের পেছনে যারা দিনরাত ঘাম ঝরিয়ে, প্রবাসের মাটিতে কষ্ট সয়ে একেকটি ডলার পাঠাচ্ছেন, সেই রেমিট্যান্স যোদ্ধাদের যথার্থ স্বীকৃতি কোথায়? কে তাদের নাম উচ্চারণ করছে? কে তাদের জন্য দাঁড়াচ্ছে?
রাজনীতিবিদরা যখন এ অর্জনের কৃতিত্ব নিজেদের কাঁধে তুলে নিতে ব্যস্ত, তখন প্রকৃত নায়করা থেকে যাচ্ছেন অগোচরে, অবহেলিত এক শ্রেণি হিসেবে। রাষ্ট্র যেন ইচ্ছাকৃতভাবেই ভুলে যাচ্ছে, এই অর্থনীতির মূল চালিকাশক্তি আসলে কারা।
প্রবাসজীবনের প্রতিটি দিনই যুদ্ধ—অচেনা সমাজে টিকে থাকার যুদ্ধ, পরিবার থেকে বিচ্ছিন্নতার কষ্ট, বৈষম্য ও দুর্ব্যবহার সহ্য করার লড়াই। এই যোদ্ধারা মাথার ঘাম পায়ে ফেলে যে বৈদেশিক মুদ্রা দেশে পাঠান, তাতেই সচল থাকে আমাদের বাজেট, উন্নয়নের রাস্তাঘাট, প্রকল্প আর জনকল্যাণ। অথচ, এর বিনিময়ে তারা পান না রাষ্ট্রীয় মর্যাদা, সামাজিক সম্মান কিংবা ভবিষ্যতের কোনও নিরাপত্তা।
আজও তারা ভোট দিতে পারেন না—যেন দেশের ভাগ্য নির্ধারণে তাদের কোন অধিকার নেই। রাষ্ট্রের দায়িত্ব হওয়া উচিত ছিল এই অধিকার নিশ্চিত করা, কিন্তু বছরের পর বছর পেরিয়ে গেলেও সেই ন্যূনতম মানবাধিকারটুকু তারা পাচ্ছেন না। এটি কি কেবল প্রশাসনিক ব্যর্থতা, নাকি পরিকল্পিত উপেক্ষা?
তাদের পরিবারগুলোর দিকেও রাষ্ট্রের নজর খুবই কম। দেশে থাকা রেমিট্যান্স যোদ্ধাদের পরিবারের আর্থিক সহায়তা, চিকিৎসা, শিক্ষা, কিংবা জীবননিরাপত্তা — এসব নিয়ে কোনো সুসংহত পরিকল্পনা কি সরকারের আছে? যদি থাকে, তবে তা কি আমরা জানি? আর যদি না থাকে, তাহলে কেন নেই?
সরকার কি কখনও পেনশন পরিকল্পনার কথা ভাবছে এই রেমিট্যান্স যোদ্ধাদের জন্য? তাদের সন্তানদের জন্য কি কোনো বিশেষ সুযোগ-সুবিধা, শিক্ষা বৃত্তি, কোটা বা রাষ্ট্রীয় সহায়তা রয়েছে? যদি থাকে, তাহলে তা জনসম্মুখে প্রকাশ হোক। আর না থাকলে, এখনই সময় তাদের প্রাপ্য সম্মান ও নিরাপত্তা দেওয়ার জন্য একটি রাষ্ট্রীয় দায়িত্বশীল অবস্থান গ্রহণ করার।
এই বাস্তবতায় প্রশ্ন জাগে—বাংলাদেশ কি সত্যিই কৃতজ্ঞ? নাকি কেবল সেই কৃতজ্ঞতার মুখোশ পরে বসে আছে, যেটার নিচে লুকিয়ে আছে চরম স্বার্থপরতা?
রিজার্ভের সংখ্যা বাড়া বড় কথা নয়—কৃতজ্ঞতা, সম্মান আর ন্যায়ের ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে রাষ্ট্র নির্মাণ করাই বড় কথা। এই রেমিট্যান্স যোদ্ধারা যদি আজ না থাকতেন, তবে আমাদের বাজেটের অঙ্কগুলো কেমন হতো, সে প্রশ্ন আমাদের প্রতিটি নীতিনির্ধারক ও নাগরিকের নিজেকে জিজ্ঞেস করা উচিত।
আমরা কি শুধু সুযোগসন্ধানী এক জাতি? নাকি সত্যিকার অর্থেই শ্রদ্ধাশীল, কৃতজ্ঞ ও ন্যায়বোধসম্পন্ন জাতি হয়ে উঠতে চাই?
রহমান মৃধা
গবেষক ও লেখক
(সাবেক পরিচালক, ফাইজার, সুইডেন)
Rahman.Mridha@gmail.com
মত দ্বিমত
চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়ে ঢাকাতেই বসবাস করতে হবে
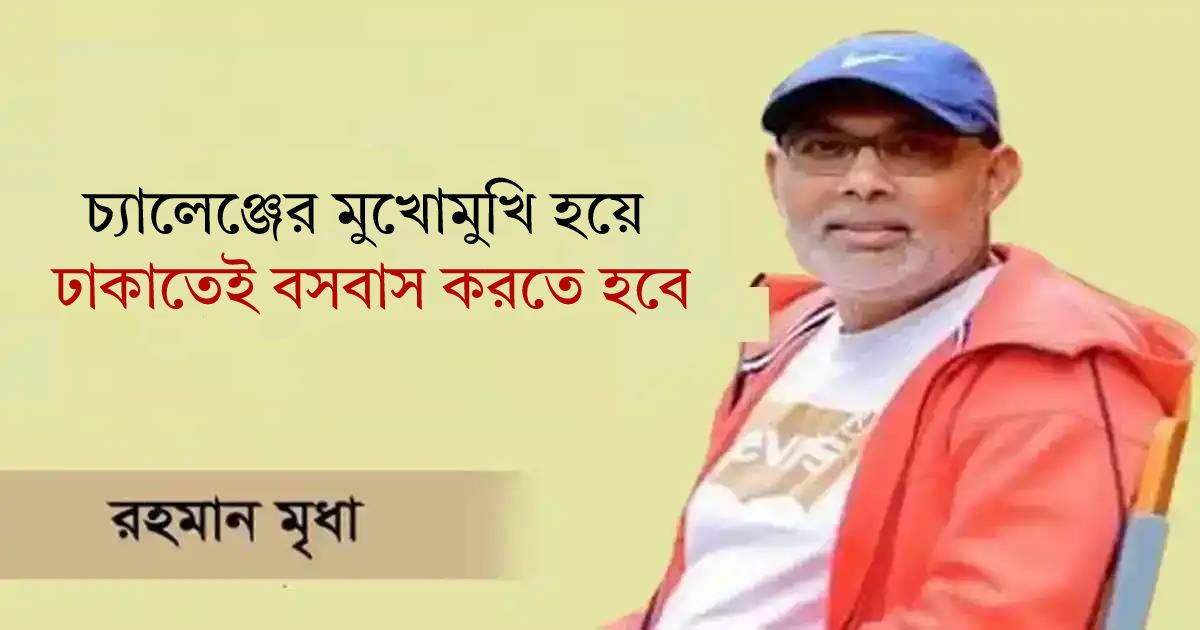
এখন যদি নিরাপত্তাহীনতা, অব্যবস্থা বা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে ভাবি—তবে বেঁচে থাকাটাই কঠিন হয়ে যাবে। কারণ গোটা বিশ্বেই আজ স্থিতি ও শান্তির অভাব। ইউক্রেন, গাজা, আফগানিস্তান, সুদান—প্রত্যেকটি অঞ্চল আমাদের শেখাচ্ছে: আজ কোথাও নিরাপদ আশ্রয় নেই। তবুও, যখন গাজার বুলেটবৃষ্টি দেখি, মনে হয় আমরা যারা ঢাকায় বা অন্য কোথাও থাকি, তারা তুলনায় অনেক ভালো আছি। কিন্তু কতদিন?
কয়েক দিন আগেই ঢাকার বিমান দুর্ঘটনায় ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট তৌকির ইসলামের করুণ মৃত্যু আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে—আমরা যেন এক ঘুণে ধরা রাষ্ট্রে বসবাস করছি, যেখানে দুর্নীতি শুধু একটি শব্দ নয়, বরং এটি রক্তের মধ্যেও মিশে গেছে। এই দুর্ঘটনা কোনো দুর্ঘটনা ছিল না—এটি ছিল একটি অপরাধ, একটি মৃত্যুর পূর্বঘোষণা, যা রক্ষণাবেক্ষণের নামে লুটপাট, নিরাপত্তার নামে অবহেলা, আর দায়িত্বের নামে দুর্নীতির হাত ধরে আসছিল বহুদিন ধরে।
দুর্নীতি কীভাবে প্রতিরক্ষা বাহিনী পর্যন্ত পৌঁছে গেছে, সেটাই এখন আরেকটি বড় প্রশ্ন। বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ থেকে শুরু করে সামরিক বাহিনীর ভেতরের রক্ষণাবেক্ষণ ব্যবস্থায়ও আজ প্রশ্নের জন্ম হচ্ছে। দুর্নীতি, গাফিলতি ও অপেশাদারিত্ব মিলিয়ে আজ পুরো নিরাপত্তা খাতটাই নৈতিকভাবে ভেঙে পড়েছে।
তাহলে কে রক্ষা করবে বাংলাদেশকে? সরকার? বিরোধী দল? সামরিক বাহিনী? বুদ্ধিজীবী সমাজ? নাকি সেই সাধারণ মানুষ, যারা প্রতিদিন টিকে থাকার লড়াই লড়ছে? এই প্রশ্নের উত্তর হয়তো এখনো মেলেনি। কিন্তু আরেকটি প্রশ্ন আজকের বাংলাদেশকে কাঁপিয়ে তুলছে—
কী পরিমাণ দুর্নীতি হলে একটি দেশের হাসপাতাল থেকে শুরু করে প্রতিরক্ষা বাহিনী পর্যন্ত রন্ধ্রে রন্ধ্রে ঘুণে ধরে?
আপনি কি কখনো ভেবে দেখেছেন?
যখন—
• হাসপাতাল রোগী মারে,
• চিকিৎসক হয়ে ওঠে দালাল,
• শিক্ষক হয়ে ওঠে সেশন ফি ব্যবসায়ী,
• প্রশাসন হয়ে ওঠে চাঁদাবাজ,
• মসজিদে উঠে আসে রাজনীতির চোরাগলি,
• মন্দিরে বাজে তদবিরের সুর,
• ঘরে নেই শান্তি,
• বাইরে নেই নিরাপত্তা,
• আর কবর পর্যন্ত নিতে হয় ঘুষ—
তখন বলুন, কোথায় যাবেন আপনি? আর কোথায় আপনি নিরাপদ? এই দেশ, এই রাষ্ট্র, এই ঢাকা—সবই কি কিছু সুবিধাভোগী আর দুর্নীতিবাজদের জন্যই? নাকি এখনো কিছু মানুষ বাকি আছে, যারা বলবে—না, আর না। এবার সত্যকে ঢেকে রাখব না। এবার জেগে উঠতেই হবে। এতকিছুর পরেও কি সবকিছু ঢাকতেই থাকবে, হতে থাকবে? নাকি এবার ঢাকায় থেকেই আমরা বলব—এখান থেকেই শুরু হবে পরিবর্তনের ঝড়?
বিশ্বের কোথাও এখন আর শান্তিপূর্ণ, নিরাপদ বা ন্যায়ভিত্তিক সমাজব্যবস্থার নিশ্চয়তা নেই। ইউক্রেন-রাশিয়া যুদ্ধ, গাজা-ইসরায়েল সংঘাত, আমেরিকার অভ্যন্তরীণ বিভাজন, ফ্রান্সের দাঙ্গা, আফ্রিকার রাষ্ট্রগুলোর অভ্যুত্থান—সবকিছু বলে দিচ্ছে, নিরাপত্তাহীনতা এখন কেবল কোনো একটি দেশের সমস্যা নয়—এটি এক বৈশ্বিক ব্যাধি। কিন্তু এই প্রেক্ষাপটের মধ্যেই বাংলাদেশের পরিস্থিতি আলাদা, কারণ এখানে অভ্যন্তরীণ দুর্নীতি, অব্যবস্থা ও নৈতিক দেউলিয়াপনা রাষ্ট্রকে ভিতর থেকে গিলে খাচ্ছে।
এবং এই গিলে খাওয়ার প্রক্রিয়া এখন আর রাজনৈতিক গণ্ডিতে সীমাবদ্ধ নেই। এটি ঢুকে পড়েছে প্রশাসন, প্রতিরক্ষা, পরিবহন, চিকিৎসা, শিক্ষা—সব খাতে। সবচেয়ে বড় কথা, এখন দুর্নীতি ঢুকে পড়েছে বিশ্বাস, মূল্যবোধ ও জাতীয় আত্মার ভেতরেও।
সুতরাং, যদি আমরা কিছু না করি, তাহলে কী দাঁড়াবে শেষটায়?
• দুর্নীতি অব্যাহত থাকবে
• অব্যবস্থাপনার কারণেই মৃত্যু ‘দুর্ঘটনা’ হিসেবে ধামাচাপা পড়বে
• গাজা আমাদের জন্য এক রূপক হয়ে উঠবে — “আমরাও এক অন্তর্জাত যুদ্ধক্ষেত্র”
• রাষ্ট্র ক্রমশ তার আত্মাকে হারাবে, নাগরিক হারাবে বিশ্বাস, আশা, এবং সর্বোপরি—জীবনের অর্থ
আপনি যদি প্রশ্ন করেন—কে রক্ষা করবে বাংলাদেশকে? উত্তর একটাই—আপনি। আপনার বিবেক, আপনার কণ্ঠস্বর, আপনার প্রতিবাদই পারে এই দেশকে রক্ষা করতে। বাকি কেউ আসবে না।
এতকিছুর পরেও সব কিছু কী ঢাকতেই থাকতে হবে, হতে হবে? একটি দেশের আকাশে আগুন জ্বলে—আর আমরা তার ধোঁয়া ছড়িয়ে পড়া পর্যন্ত অপেক্ষা করি। একটি পাইলট মৃত্যুর আগমুহূর্ত পর্যন্ত চেষ্টা করেন শহর বাঁচাতে—কিন্তু তার আত্মত্যাগ ধামাচাপা পড়ে যায় দায়সারা তদন্ত আর অপ্রকাশিত রিপোর্টের আড়ালে। আমাদের চারপাশে প্রতিদিনই ঘটে যাচ্ছিল ছোট ছোট বিপর্যয়—আর আমরা বলছিলাম, “এটাই তো বাংলাদেশ!”
কিন্তু আজ যখন এই মৃত্যুর কণ্ঠস্বর আমাদের ঘুম ভাঙায়, তখন অন্তত প্রশ্নটা তোলা জরুরি হয়ে পড়ে:
এতকিছুর পরেও কি সবকিছু ঢাকতেই থাকবে? সরকারি বিবৃতি দিয়ে? সামরিক গোপনীয়তার নামে? জাতীয় ভাবমূর্তির কথা বলে? না কি জনতার নিরবতা দিয়ে? বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ কি শুধুই ঢাকার উপর নির্ভর করবে—অর্থাৎ, রাজধানী ঢাকার, কিছু ক্ষমতাবান ব্যক্তির, কিছু নামমাত্র প্রতিষ্ঠানের দয়া বা দৌরাত্ম্যের ওপর? না কি সেই ঢাকা একদিন সত্যিই হবে বিবেকের রাজধানী—যেখানে প্রতিটি মৃত্যু প্রশ্ন তোলে, প্রতিটি অন্যায় প্রতিরোধ পায়, প্রতিটি নাগরিক জবাবদিহি দাবি করে?
আমরা কী শুধুই একটি দুর্নীতিপরায়ণ ব্যবস্থার ভেতরে বেঁচে থাকবো? নাকি বেছে নেবো বেঁচে ওঠার সাহস? এই লেখার শেষ পঙক্তি যদি আপনি মন দিয়ে পড়েন—তবে এটিই আপনার কাছে আমার অনুরোধ, আমার আহ্বান:
তথ্য ঢেকে রাখার সংস্কৃতি শেষ হোক। সত্য কথা বলার সাহস শুরু হোক। বাংলাদেশের প্রাণটুকু যেন শুধু ঢাকায় আটকে না থাকে-সে ছড়িয়ে পড়ুক জনগণের চেতনায়, হৃদয়ে, এবং শেষমেশ—প্রতিবাদে।
রহমান মৃধা
গবেষক ও লেখক
(সাবেক পরিচালক, ফাইজার, সুইডেন)
Rahman.Mridha@gmail.com
মত দ্বিমত
দুর্ঘটনাজনিত দুর্যোগ-পরবর্তী আমাদের করণীয় কী?
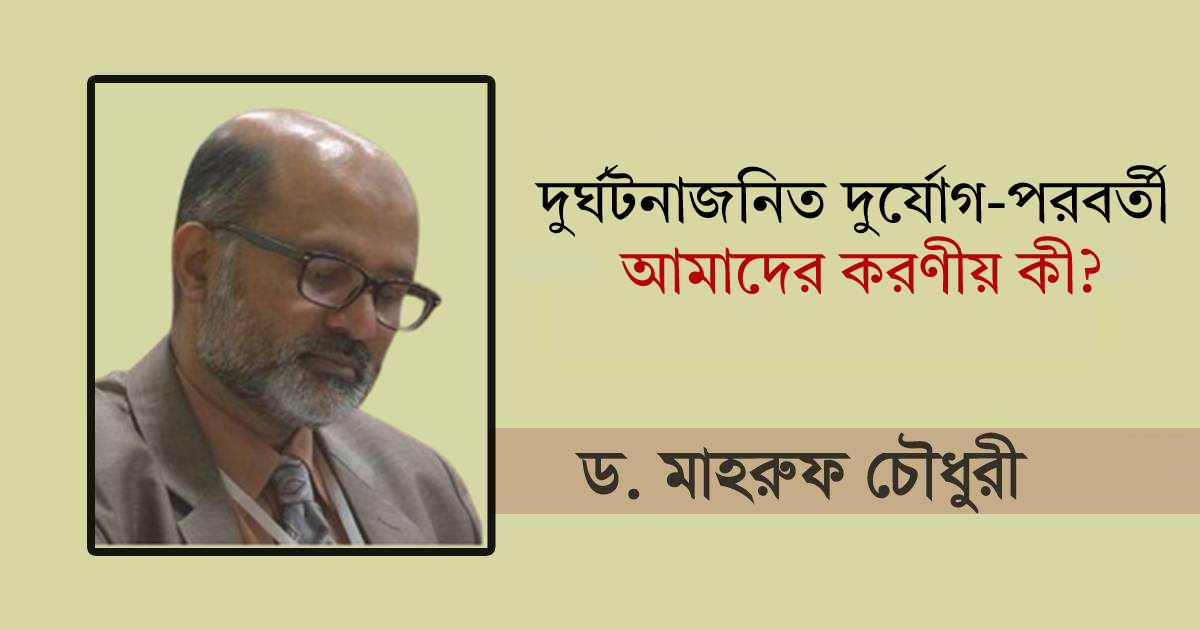
যুদ্ধবিমান বিধ্বস্ত হয়ে রাজধানী ঢাকার মাইলস্টোন নামক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানটির ওপর আছড়ে পড়ার ভয়াবহ ও মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় আমরা শুধু হতবাকই নই, বরং গভীরভাবে ক্ষুব্ধ ও ভবিষ্যৎ অনিশ্চয়তায় শঙ্কিত। এ ঘটনা আমাদের শুধু হতবিহ্বলই করেনি, বরং দুর্ঘটনা-উত্তর প্রতিক্রিয়ায় রাষ্ট্রযন্ত্রের দক্ষতা, প্রশাসনিক দায়বদ্ধতা, রাজনৈতিক দায়িত্বশীলতা, পেশাগত নীতি-নৈতিকতা এবং দুর্যোগ মোকাবিলায় আমাদের জাতীয় প্রস্তুতির ঘাটতি নিয়ে সাধারণ নাগরিকদের মনে গভীর উদ্বেগ ও ক্ষোভের জন্ম দিয়েছে। এই দুর্ঘটনা নিছক কোনো প্রযুক্তিগত ত্রুটি কিংবা বিভ্রান্তি নয়; এটি রাষ্ট্র পরিচালনায় আমাদের সামগ্রিক অদক্ষতা, পূর্বপ্রস্তুতির অভাব এবং দায়িত্বশীলতার সংকটকে নগ্নভাবে প্রকাশ করেছে। এতে করে সবচেয়ে বড় যে প্রশ্নটি সামনে এসেছে তা হলো: সরকারের, প্রশাসনের ও রাজনৈতিক নেতৃত্বের হাতে নাগরিক নিরাপত্তা আদৌ কতটা সুরক্ষিত? জনস্বার্থের প্রশ্নে যখন নিরাপত্তা, প্রস্তুতি ও প্রতিক্রিয়ার দায় আসে, তখন দায়িত্বশীলতার মানদণ্ডে কে কোথায় দাঁড়ায় এখনই সময় সেই কঠিন প্রশ্নের জবাব খোঁজার। এই নিবন্ধ সেই প্রশ্নের মুখোমুখি হওয়ার এক আন্তরিক প্রয়াস।
এই দুর্ঘটনার পর আমরা যেভাবে সরকারের কর্তাব্যক্তি (শাসকশ্রেণি), পেশাজীবী এবং রাজনীতিবিদদের একাংশের দায়িত্বজ্ঞানহীন আচরণ প্রত্যক্ষ করেছি, তাতে একটি বৃহৎ দুর্যোগ মোকাবিলায় আমাদের রাষ্ট্রীয় সক্ষমতা কতটা কার্যকর সে বিষয়ে জনমনে গভীর সন্দেহ দেখা দিয়েছে। দুর্ঘটনার পরপরই সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের অনুমতি ছাড়াই হাসপাতাল ও দুর্ঘটনাস্থলে যেভাবে রাজনৈতিক নেতা-কর্মী ও দায়িত্ববহির্ভূত পেশাজীবীরা অবিবেচকের মতো ভিড় জমিয়েছেন, তা শুধু উদ্ধার ও চিকিৎসা কার্যক্রম ব্যাহত করেনি, বরং জননিরাপত্তা ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার মৌলিক নীতিমালাকেই প্রশ্নবিদ্ধ করেছে। বিশেষ করে আগুনে ঝলসে যাওয়া রোগীদের চিকিৎসায় যে সংবেদনশীলতা ও শৃঙ্খলা জরুরি, সেই প্রেক্ষাপটে এমন হঠকারী আচরণ চরম অজ্ঞতা, আত্মপ্রচারপ্রবণতা এবং রাজনৈতিক অপসংস্কৃতির ভয়ানক বহিঃপ্রকাশ হিসেবে বিবেচিত হতে বাধ্য। এখানে ‘সহযোগিতা’ বা ‘সহমর্মিতা’র নাম করে দুর্ঘটনাস্থলে ও হাসপাতালে ঊদেশ্যপ্রণোদিত ‘উপস্থিতি’ নিশ্চিত করাই যেন মুখ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে, অথচ সেখানে প্রয়োজন ছিল প্রশিক্ষিত পেশাজীবীদের নির্বিঘ্ন কাজ করার উপযোগী পরিবেশ নিশ্চিত করা। দুর্যোগকালীন সময়ের এই অবিবেচনাপ্রসূত হস্তক্ষেপ শুধু দৃষ্টিকটু নয়, বরং তা এক ধরনের ‘নৈতিক সহিংসতা’ বলেও চিহ্নিত করা যায়।
ফলে দেশের অধিকার সচেতন নাগরিকেরা প্রশ্ন তুলতেই পারেন, আমরা কি সত্যিই দুর্যোগ মোকাবিলায় প্রস্তুত? এই প্রশ্নটি শুধু প্রতীকী নয়, বরং আমাদের রাষ্ট্রীয় পরিমন্ডলে একেবারে বাস্তব ও নীতিনির্ধারণের কেন্দ্রবিন্দুতে থাকা দরকার। দুর্যোগ মোকাবিলাকে আমরা এখনো অনেকাংশে একটি কারিগরি, সামরিক কিংবা বিশেষ বাহিনিনির্ভর কার্যক্রম হিসেবে ভাবি যেন এটি শুধু শান্তি-শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা বাহিনী পাঠিয়ে সমস্যার তাৎক্ষণিক সমাধান করার বিষয়। অথচ বাস্তবে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা একটি সর্বাঙ্গীন ও সমন্বিত জাতীয় প্রস্তুতির বিষয় যেখানে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা ও সামর্থ নিয়োগের প্রতিফলন থাকা চাই। এটি রাষ্ট্রীয় অবকাঠামো, স্বাস্থ্য ও মনো-সামাজিক সহায়তা, প্রশাসনিক সমন্বয়, নাগরিক শিক্ষা এবং রাজনৈতিক সদিচ্ছার এক সম্মিলিত ফসল। প্রশ্ন হচ্ছে, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বা জনগুরুত্বপূর্ণ স্থানে দুর্ঘটনা ঘটলে, আমাদের হাতে কি আছে সুনির্দিষ্ট ও দ্রুত গতিসম্পন্ন উদ্ধার উপকরণ ও সমন্বিত দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা? কোথায় ছিল দুর্ঘটনার পর পরই জরুরি প্রাথমিক চিকিৎসা দল? কোথায় ছিল পুড়ে যাওয়া কিংবা আতঙ্কগ্রস্ত শিক্ষার্থীদের জন্য মনো-সামাজিক পরামর্শ (কাউন্সেলিং)-এর ব্যবস্থা? এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, কোথায় ছিল দুর্যোগকালীন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব, নির্দেশনা ও সমন্বয় যা একটি দুর্যোগ মুহূর্তে দেশের নাগরিকদের আস্থা ও কার্যকর সাড়া দেওয়ার প্রধান শর্ত? ঘটনার দিন বাস্তবে এই শূন্যতাগুলো দেখিয়ে দেয়, দুর্যোগ আমাদের কাছে এখনো পরিকল্পনা নয়, কেবল প্রতিক্রিয়ার বিষয় হয়ে রয়ে গেছে।
এই দুর্ঘটনা আমাদের সামনে যেটি অনিবার্যভাবে তুলে ধরেছে, তা হলো এখনই সময় আত্মসমালোচনার এবং তার ভিত্তিতে ভবিষ্যতের জন্য সুনির্দিষ্ট, বাস্তবসম্মত ও নৈতিকভাবে সুসংহত দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার প্রস্তুতি নেওয়ার। এই পরিপ্রেক্ষিতে নিচে কিছু জরুরি করণীয় তুলে ধরা হলো:
১. রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে দুর্যোগ মুকাবিলার নীতিমালা প্রণয়ন ও দুর্যোগকালীন সময়ে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার জন্য কেন্দ্রীয় সমন্বয় সেল গঠন জরুরি। দুর্যোগের মুখোমুখি হয়ে বারবার সমন্বিত ব্যবস্থাপনার দুরাবস্থা ও মানুষের হাহাকার দেখে হাত তুলে শোক প্রকাশ করাই যথেষ্ট নয়, বরং প্রয়োজন রাজনৈতিক সদিচ্ছা, নীতিগত স্পষ্টতা এবং সংবেদনশীল প্রশাসনিক কাঠামো। এ লক্ষ্যে কিছু জরুরি করণীয় এখনই নির্ধারণ করতে হবে, যার প্রথম ধাপ হলো দুর্যোগ মুকাবিলার জন্য একটি সমন্বিত জাতীয় নীতিমালা প্রণয়ন। এই নীতিমালায় স্পষ্টভাবে নির্দেশ থাকতে হবে দুর্যোগের মুহূর্তে কোন সংস্থা কী দায়িত্ব পালন করবে, কে কোথায় থাকবে, কে কোথায় যাবে, কার ঘটনাস্থলে যাওয়ার অধিকার আছে আর কার নেই এবং কোন কর্তৃপক্ষের অধীনে উদ্ধার কার্যক্রম পরিচালিত হবে। এটি কেবল প্রশাসনিক বা সামরিক মহড়ার অনুশীলন বা সক্ষমতার প্রদর্শনী নয়, বরং এটা হবে এক ধরনের ‘নাগরিক নিরাপত্তা কাঠামো’ যা দুর্যোগে দায়িত্ব ও সীমারেখা নির্ধারণ করে সমাজের সর্বস্তরের জন্য সুরক্ষা নিশ্চিত করবে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিষয়টি আর শান্তি-শৃঙ্খলা বা নিরাপত্তা বাহিনির দক্ষতার উপর ছেড়ে দিলে চলবে না। এটি একটি যৌথ, নীতিনির্ভর এবং মূল্যবোধভিত্তিক কাঠামোর দাবি রাখে যা সমন্বিত উদ্যোগে কাজ করতে হবে, যার মূল লক্ষ্য হবে মানুষের জীবন রক্ষা, রাষ্ট্রীয় পরিমন্ডলে শৃঙ্খলা বিধান এবং নাগরিক আস্থা পুনর্গঠন।
২. রাজনৈতিক দল ও পেশাজীবীদের জন্য আচরণবিধি ও বাধ্যতামূলক প্রশিক্ষণ চালু করা এখন সময়ের দাবি। দুর্যোগকালীন সময়ে শৃঙ্খলা ও পেশাদারিত্ব বজায় রাখতে হলে রাজনৈতিক ও পেশাগত পরিসরে আচরণগত নীতিনৈতিকতা প্রতিষ্ঠা করা জরুরি। এজন্য রাজনৈতিক দলগুলোর নেতা-কর্মীদের জন্য বিশেষ ‘আচরণবিধি’ প্রণয়ন করতে হবে, যাতে দুর্যোগকালে কী করতে হবে এবং কী করা যাবে না তা সুস্পষ্টভাবে নির্ধারিত থাকে। এই আচরণবিধির বাস্তব প্রয়োগ নিশ্চিত করতে হবে বাধ্যতামূলক প্রশিক্ষণ ও সচেতনতামূলক কর্মসূচির মাধ্যমে। আচরণবিধি লঙ্ঘন করলে তাদেরকে আইনের আওতায় শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে। রাজনীতি কেবল বক্তৃতা, উপস্থিতি আর ব্যানার টানানোর কাজ নয়; এটি এক ধরনের সামাজিক দায়দায়িত্ব ও জননিরাপত্তা সংরক্ষণের অঙ্গীকার। একইভাবে চিকিৎসক, সাংবাদিক, প্রশাসনিক কর্মকর্তা, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীসহ সব পেশাজীবীদের জন্যও এমন প্রশিক্ষণমূলক কর্মসূচি চালু করা দরকার, যেখানে তারা শিখবেন সংকটকালে কীভাবে দায়িত্বশীল, মানবিক এবং পেশাগত আচরণ ও শৃঙ্খলা বজায় রাখতে হয়। এটি শুধু উদ্ধার কাজের কার্যকারিতার জন্য নয়, বরং নৈতিকতার প্রশ্ন যেখানে জনস্বার্থই হবে সর্বোচ্চ বিবেচ্য। দুর্যোগকালীন দায়িত্বজ্ঞানহীন আচরণ কোনো ব্যক্তিগত ভুল নয়; এটি একটি কাঠামোগত ব্যর্থতা, যার প্রতিকারে এখনই যথাযথ উদ্যোগ নেওয়া জরুরি।
৩. শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য দুর্যোগ মোকাবিলার গাইডলাইন প্রণয়ন এবং বাধ্যতামূলক প্রস্তুতি প্রশিক্ষণ চালু করা। আমাদের মনে রাখতে হবে যে, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান শুধু পাঠদানের স্থান নয়। এগুলোর সাথে আমাদের ভবিষ্যত প্রজন্মের শিশু, কিশোর ও তরুণদের শারীরিক, মানসিক ও আত্মিক নিরাপত্তা জড়িত। ফলে দুর্যোগ বা দুর্ঘটনার সময় তাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার পাওয়া উচিত। এজন্য প্রতিটি স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য দুর্যোগকালীন ও দুর্যোগ-পরবর্তী প্রতিক্রিয়ার একটি সুনির্দিষ্ট ও বাস্তবমুখী গাইডলাইন প্রণয়ন করতে হবে, যাতে তারা জানে দুর্ঘটনার সময় কীভাবে দ্রুত এবং শৃঙ্খলার সঙ্গে কাজ করতে হবে। এই গাইডলাইনে থাকবে জরুরি নির্গমনপথ, প্রাথমিক চিকিৎসার ব্যবস্থা, দিকনির্দেশনামূলক সংকেতচিহ্ন, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মীদের তালিকা এবং সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ পদ্ধতি। শুধু গাইডলাইন থাকা যথেষ্ট নয়, এর বাস্তব প্রয়োগ নিশ্চিত করতে শিক্ষক, কর্মকর্তা, কর্মচারী এবং শিক্ষার্থীদের নিয়মিত প্রশিক্ষণ দেওয়াও বাধ্যতামূলক করতে হবে। দুর্যোগ প্রতিক্রিয়াকে যদি আমরা সামাজিক শিক্ষার অংশ হিসেবে বিবেচনা করি, তাহলে এর চর্চা শুরু হওয়া উচিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকেই কারণ ভবিষ্যতের সচেতন নাগরিক তৈরি হয় এখানেই।
৪. দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিষয়ে গণশিক্ষা ও নাগরিক সচেতনতা কার্যক্রম জোরদার করা অত্যাবশ্যক। আগেই বলা হয়েছে, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কেবল পেশাদার বাহিনী ও প্রতিষ্ঠানের কাজ নয়। এটি একটি সামাজিক চর্চা, যেখানে সাধারণ নাগরিকদের সক্রিয় ও সচেতন অংশগ্রহণ অপরিহার্য। তাই দুর্যোগ বিষয়ে গণশিক্ষার মাধ্যমে জনগণের মাঝে সচেতনতা সৃষ্টি করতে হবে, যেন তারা সঠিক সময়ে সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারেন এবং উদ্ধার ও চিকিৎসা কাজে অনভিপ্রেত বাধা সৃষ্টি না করেন। দুর্যোগকালে বহু মানুষ ভুল তথ্যের ভিত্তিতে, আবেগতাড়িত হয়ে বা ভিড়ের চাপে দিশেহারা হয়ে অনাকাঙ্ক্ষিত আচরণ করেন। ফলে উদ্ধার ও প্রাণরক্ষাকারী প্রাথমিক চিকিৎসা কার্যক্রম ব্যাহত হয়, এবং অনেক ক্ষেত্রে প্রাণহানি ও সম্পদের ক্ষয়ক্ষতিও বাড়ে। গুজব, আতঙ্ক ও দায়িত্বহীন প্রচারপ্রপাগান্ডা যেন ছড়িয়ে না পড়ে, সেজন্য সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম, ডিজিটাল মিডিয়া এবং স্থানীয় পর্যায়ে গণসংযোগের মাধ্যমে সচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে। এ ধরনের কর্মকান্ড প্রতিরোধে গণশিক্ষাকে শুধু সামাজিক অভিযান হিসেবে না দেখে, এটি নাগরিকত্ব শিক্ষার অংশ হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে হবে যাতে মানুষ জানেন, কীভাবে দায়িত্ব নিয়ে দুর্যোগের মুহূর্তে নিজের এবং অন্যের জান, মাল ও সম্মানের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হয়। যেমনভাবে প্রাচীন গ্রিসে ‘সক্রিয় নাগরিকত্ব’ (একটিভ সিটিজেনশিপ) মানে ছিল ‘অবস্থা অনুধাবন ও প্রতিক্রিয়া জানার সক্ষমতা’, তেমনি আজকের নাগরিককেও গড়ে তুলতে হবে এমনভাবে যাতে সে দুর্যোগের সময় আতঙ্কে ভেঙে না পড়ে, বরং সংবেদনশীলতা ও বুদ্ধিবৃত্তিক প্রস্তুতিতে নিজের ও অন্যের নিরাপত্তা নিশ্চিত করে সমাজকে এগিয়ে নিতে পারেন।
৫. গণমাধ্যম ও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ব্যবহারকারীদের জন্য নৈতিক আচরণবিধি তৈরি এবং পেশাগত বিধিনিষেধের বাধ্যতামূলক প্রয়োগ ব্যবস্থা চালু করা। দুর্যোগকালীন সময়ে তথ্যের গতিপ্রবাহ শুধু জনগণের আচরণ নয়, উদ্ধার ও চিকিৎসা কার্যক্রমের সফলতাকেও সরাসরি প্রভাবিত করে। এই বাস্তবতায় গণমাধ্যম এবং সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের ভূমিকা দায়িত্বশীল, সংবেদনশীল এবং নীতিনির্ভর হওয়া উচিত। এজন্য একটি সুনির্দিষ্ট নৈতিক আচরণবিধি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন জরুরি, যাতে সংবাদকর্মী, ডিজিটাল কনটেন্ট নির্মাতা, ব্লগার কিংবা সাধারণ ব্যবহারকারীরা জানেন দুর্যোগকালীন সময়ে কী তথ্য প্রকাশ করা উচিত, কীভাবে সেটি প্রকাশ করতে হবে এবং কোন তথ্য প্রচার বিভ্রান্তিকর কিংবা একেবারেই বর্জনীয়। কারণ ভুল বা অতিরঞ্জিত তথ্য সেটা চিকিৎসা, উদ্ধার তৎপরতা কিংবা জননিরাপত্তা সংশ্লিষ্ট হোক তা জনগণের মাঝে বিভ্রান্তি, আতঙ্ক ও আবেগোন্মত্ততা (হিস্টেরিয়া) তৈরি করতে পারে, যা কখনো কখনো সংঘবদ্ধ সহিংসতায়ও রূপ নিতে পারে। এমন পরিস্থিতিতে একটি অসতর্ক পোস্ট, একটি বিভ্রান্তিকর শিরোনাম বা একটি গুজব গোটা ব্যবস্থাকে বিপর্যস্ত করে তুলতে পারে। তাই এ খাতে শুধু স্বেচ্ছাপ্রণোদিত সততা নয়, রাষ্ট্রীয় পর্যায় থেকে দিকনির্দেশনা, প্রশিক্ষণ ও প্রয়োজনে নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাও গ্রহণ করতে হবে যাতে বাকস্বাধীনতা ও জনস্বার্থের মধ্যে সঠিক ভারসাম্য রক্ষা করে সংবাদ ও তথ্যপ্রবাহ মানবিক, কল্যাণমুখী ও গঠনমূলক ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। দুর্যোগ-পরবর্তী মুহূর্তে মিডিয়ার নৈতিকতা কেবল সাংবাদিকতার প্রশ্ন নয়, এটি এখন নাগরিক দায়িত্বেরও অন্তর্গত।
৬. ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য উন্নত চিকিৎসা ও মনো-সামাজিক সহায়তা নিশ্চিত করা। দুর্ঘটনায় আহতদের উন্নত ও টেকসই চিকিৎসার নিশ্চিত করার পাশাপাশি বিশেষ করে অভিজ্ঞতাজনিত আতঙ্ক (ট্রমা) নিরসনে অব্যাহত পরামর্শ দেওয়া অত্যাবশ্যক। দুর্যোগ বা দুর্ঘটনার শারীরিক ক্ষতির পাশাপাশি যে অনির্দেশ্য ও গভীর ক্ষত মানুষের মনোজগতে সৃষ্টি হয়, তা আরও দীর্ঘমেয়াদি ও মারাত্মক হতে পারে। তাই কেবল আহতদের শারীরিক চিকিৎসা নয়, দুর্ঘটনাকবলিত ব্যক্তি ও তাঁদের পরিবারের জন্য মনো-সামাজিক পরামর্শ সহায়তা ও মানসিক স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করাও রাষ্ট্রের মানবিক দায়িত্ব। আধুনিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় ‘মনো-সামাজিক প্রাথমিক চিকিৎসা’ (সাইকো-সোসাল ফাস্ট এইড) একটি অপরিহার্য অংশ হিসেবে স্বীকৃত। বিশেষ করে শিশু, কিশোর ও তরুণদের জন্য যারা এমন দুর্ঘটনার পর মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। শুধু উন্নত হাসপাতাল নয়, প্রয়োজন মাঠপর্যায়ে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কাউন্সেলর, কমিউনিটি সাপোর্ট সেন্টার, এবং দীর্ঘমেয়াদি পুনর্বাসন পরিকল্পনা। রাষ্ট্রের উচিত ক্ষতিগ্রস্তদের পাশে কেবল দাতা বা করুণাদৃষ্টিতে নয়, মানবাধিকারের ভিত্তিতে সহানুভূতিশীল ও ন্যায়ভিত্তিক অবস্থান নেওয়া যেখানে প্রত্যেক মানুষ তাঁর পূর্ণ মর্যাদা নিয়ে পুনরায় সমাজে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে যেতে পারেন। এই দায় শুধু প্রশাসনিক নয়, এটি একটি সভ্য রাষ্ট্রের নৈতিক অবস্থানগত কর্তব্য।
রাষ্ট্রীয় পরিসরে নাগরিকের জান, মাল ও মর্যাদা রক্ষার দায়িত্ব কোনো গৌণ বা আনুষ্ঠানিক প্রতিশ্রুতি নয়, এটি একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের মৌলিক শপথ। এই দায় এড়ানোর সুযোগ নেই; বরং রাষ্ট্র এবং তার বিভিন্ন অঙ্গের উচিত নিজেদের সীমাবদ্ধতা ও ব্যর্থতার স্বরূপ শনাক্ত করে এখনই কার্যকর ও মানবিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা। প্রতিটি দুর্ঘটনা আমাদের সামনে সীমাবদ্ধতা ও ভুলত্রুটিগুলো তুলে ধরে একটি আয়নার মত যেখানে প্রতিফলিত হয় দুর্যোগ মুকাবিলার প্রস্তুতির ঘাটতি, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় নেতৃত্বের শূন্যতা, এবং দুর্যোগকালীন সংকট অনুধাবনের ব্যর্থতা। বিশেষ করে যুদ্ধবিমানের মতো উচ্চ প্রযুক্তির যন্ত্র কীভাবে একটি স্কুল ভবনের ওপর আছড়ে পড়ে সেই প্রশ্নটিকে শুধুই যান্ত্রিক বিভ্রাট হিসেবে দেখা আত্মপ্রবঞ্চনা মাত্র। এটি একটি প্রাতিষ্ঠানিক ও নৈতিক ব্যর্থতার নগ্ন প্রতিচ্ছবি যেখানে নিরাপত্তা ব্যবস্থা, পূর্বপ্রস্তুতি, সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং জবাবদিহিতার প্রতিটি স্তরে ঘাটতি বিদ্যমান। যদি আমরা এসব থেকে শিক্ষা না নিই, যদি প্রতিটি বিপর্যয়কে কেবল কিছুদিনের ক্ষোভ আর শোকের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখি, তাহলে ভবিষ্যতের আরও ভয়াবহ বিপর্যয়ের দায় গোটা জাতিকে বহন করতে হবে।
রাষ্ট্র যদি আত্মসমালোচনার সাহস না দেখায়, যদি নেতৃত্ব নিজেকে দায়মুক্ত রাখে, তাহলে আমাদের নাগরিক অধিকারের ভবিষ্যৎ প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে পড়ে। তাই সময় এসেছে আত্মপক্ষ সমর্থনের ভাষা পরিহার করে আত্মশুদ্ধির পথে সাহসী পদক্ষেপ গ্রহণ করার যাতে প্রত্যেক দুর্ঘটনার পেছনে থাকা কাঠামোগত দুর্বলতা চিহ্নিত ও সংস্কার করা যায়।
আমরা কি সত্যিই পরিবর্তন চাই? এই প্রশ্নের উত্তর আমাদের ভাষায় নয়, কর্মে স্পষ্ট হতে হবে। যদি সত্যিই আমরা পরিবর্তন চাই তবে প্রয়োজন নেতৃত্বে নৈতিক শুদ্ধতা, পেশাগত জীবনে দায়বদ্ধতা, এবং নাগরিক চেতনায় সক্রিয় সচেতনতা। দুর্যোগ-পরবর্তী আবেগ দিয়ে নয়, বরং দুর্যোগ-প্রতিরোধে রূপরেখা তৈরি করেই আমাদের রাষ্ট্রচিন্তা এগিয়ে নিতে হবে। এখনই সময় চোখ মেলে দেখার, সাহস করে প্রশ্ন তোলার, এবং সুসংগঠিত পরিকল্পনার মাধ্যমে ভবিষ্যতের বিপর্যয় রোধের। আমাদের মনে রাখতে হবে যে, প্রতিটি নির্লিপ্ত প্রতিক্রিয়া আমাদেরকে আরেকটি দুর্ঘটনার দিকে ঠেলে দেয়। প্রতিটি ব্যর্থতা থেকে শিক্ষা না নিলে তা শুধু ভুল হয়ে থাকবে না, অপরাধে পরিণত হবে যার দায় এড়াতে পারবে না কেউই। রাষ্ট্র যদি না জাগে, নাগরিক যদি না জাগে, তাহলে ইতিহাস আমাদের ক্ষমা করবে না। আজকে শিক্ষা না নিলে, কাল আর বাঁচার সুযোগ থাকবে না।
ড. মাহরুফ চৌধুরী
ভিজিটিং ফ্যাকাল্টি, ইউনিভার্সিটি অব রোহ্যাম্পটন, যুক্তরাজ্য
Email: mahruf@ymail.com