মত দ্বিমত
বাংলাদেশের রাজনীতিতে দফা বনাম বাস্তবতা

আল্লাহর সৃষ্টির সবকিছুর পেছনে কারণ রয়েছে। সংখ্যা ৪০ ইসলামী শিক্ষায় বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ; নবী মুহাম্মদ (সা.)-এর ওহী প্রাপ্তি, মূসা (আ.)-এর ৪০ দিনের প্রশিক্ষণ এবং অন্যান্য নবীদের জীবনধারায় এটি পরিপক্বতা, ধৈর্য ও আল্লাহর নৈকট্যের প্রতীক।
বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকেও দেখা যায়, কোনো নতুন অভ্যাস গড়ে তুলতে বা নেতিবাচক প্রবণতা বদলাতে ধারাবাহিক প্রচেষ্টা দরকার, যা প্রায় ৪০ দিনের মতো সময়ে স্থায়ী রূপ নেয়। সুতরাং, জীবনের কোনো পরিবর্তন তাড়াহুড়ো করে সম্ভব নয়; সময়, ধৈর্য এবং নিয়মিত চর্চা ছাড়া সত্যিকারের রূপান্তর অর্জন করা যায় না, বিশেষ করে যদি আমরা যৌথ উদ্যোগে কোনো ভালো কাজ করতে চাই।
২৪-এর গণঅভ্যুত্থানের পর আমরা সবাই একমত হয়েছি—বাংলাদেশকে সুন্দর করে গড়ে তুলতে হবে। কিন্তু শুধুমাত্র ভালো ইচ্ছে যথেষ্ট নয়; দরকার স্পষ্ট পদক্ষেপ এবং কার্যকর সংস্কার। গত এক বছরে অনেক কিছু হয়েছে, কিন্তু সংস্কার—যা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ—প্রায় অসম্পূর্ণই রয়ে গেছে। দেশে দফার ছড়াছড়ি দেখলে মনে হয়, রাজনীতি মানেই কেবল দফা বানানোর প্রতিযোগিতা।
দফাগুলোতে বলা হয় কী করা হবে আর কী করা হবে না, বিশেষ করে ক্ষমতায় গেলে কী করা হবে—এ নিয়ে হৈচৈ লেগেই থাকে। কিন্তু প্রশ্ন হলো—যদি ক্ষমতায় যাওয়া না হয়, তখন কী হবে? এর কোনো রূপরেখা কি আমরা কখনো শুনেছি? না। মানে দাঁড়ালো, সব দফাই ক্ষমতার সঙ্গে শর্তযুক্ত। তাহলে জনগণের সামনে এসব প্রতিশ্রুতির মানেটা কী? ভোটের আগে আশ্বাস, বাস্তবে ব্যর্থতা—এটি কি বিভ্রান্তি, নাকি শুধু নাটক?
ইতিহাসে উদাহরণ স্পষ্ট। শেখ মুজিবের সময় ছিল ৬ দফা—সর্বোচ্চ স্পষ্ট ও লক্ষ্যভিত্তিক। স্বাধীনতার পর তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি পাল্টানোর কারণে স্বাধীনতার চেতনা বাস্তবায়িত হলো না। জাতি হারালো বিশ্বাস—বাকি সব হলো ইতিহাস।
বর্তমানের ৩১ দফা বা অন্যান্য দলের দফা—সবই বড়, কিন্তু বাস্তবতার সঙ্গে সামঞ্জস্য নেই। চাঁদাবাজি, দুর্নীতি—যা দফায় নেই—ও বাস্তবে ঘটছে। এর মানে—দফা শুধু মঞ্চের বুলি; কাজ হচ্ছে উল্টো।
আমি বিএনপির উদাহরণ দিয়েছি, কিন্তু এখানে যেকোনো দলের নাম বসানো যায়। এমনকি অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের কাজও ছিল সংস্কার আনা, কিন্তু তারা সেই সংস্কারকে বাদ দিয়ে প্রায় সবই করেছে—দুর্নীতি, লুটপাটসহ আরও কত কী। এতে স্পষ্ট হয়, শুধু নির্বাচিত সরকার নয়, রাজনীতির যে কোনো স্তরে স্বার্থপরতা ও দায়িত্বহীনতা রূপ নিচ্ছে।
দফা ও প্রতিশ্রুতির কাগজে লেখা সব ভালো শোনায়, কিন্তু বাস্তব কাজের সঙ্গে মিল নেই। চাঁদাবাজি, স্বার্থপরতা ও দুর্নীতি—এসব তখনও চলতে থাকে, যখন সরকার (নির্বাচিত বা অন্তর্বর্তীকালীন) দায়িত্ব নেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেয়। ফলোআপ ও বাস্তবায়ন ছাড়া, সব দফা কেবল মঞ্চের বুলি হয়ে যায়, আর জনগণ বিভ্রান্ত হয়।
আমার শিল্পকারখানার অভিজ্ঞতা এখানে প্রাসঙ্গিক। প্রতিদিনের টু-ডু লিস্ট তৈরি করতাম। দিনশেষে মিলিয়ে দেখতাম—যত দ্রুত সম্ভব গুরুত্বপূর্ণ মনে করা কাজগুলোও প্রায়ই করা হতো না, তবুও বড় সমস্যা হত না। এটি শিখিয়েছে—কোন কাজ সত্যিই জরুরি, আর কোন কাজ কেবল তাড়াহুড়োর কারণে গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়েছে। ফলোআপ তখনই দরকার হয়; এটি শুধু আনুষ্ঠানিকতা নয়, আত্মসমালোচনার মাধ্যম।
রাজনীতিতেও একই প্রশ্ন প্রযোজ্য। রাজনৈতিক দলের দফা আসলে টু-ডু লিস্টের মতো—যা করা হবে, তা যদি বাস্তবে ফলোআপ না হয়, তবে তা কেবল শব্দের খেলা। ৩১ দফার ঘোষণার পর কি কোনো আপডেট বা বাস্তবায়ন হয়েছে? না। বাস্তবতা দেখায়—চাঁদাবাজি, দুর্নীতি, স্বার্থপরতা চলছেই। ফলোআপ ও দায়বদ্ধতা ছাড়া, দফা কেবল কাগজে লেখা।
আমাদের মনে রাখা দরকার—আমরা ততক্ষণই স্মার্ট, যতক্ষণ অন্য কেউ আমাদের চালাকি ধরতে পারছে না। চোরও ততক্ষণ সাধু, যতক্ষণ সে ধরা পড়ে না। যদি সত্যিই সবাই দেশকে উন্নত করতে চায়, আর সবাই একমত হয়, তাহলে সমস্যা কোথায়? সময় যদি একটু বেশি লাগে, ক্ষতি কী? তাড়াহুড়ো কেন? নির্বাচনের ব্যস্ততায় রাজনীতিবিদদের মুখের জিভ শুকিয়ে গেছে। সংস্কারের অঙ্গীকার করা হয়েছে, কিন্তু পদক্ষেপ নেই। দফা বানানো হয়েছে অনেক, কিন্তু বাস্তবে কোনো দফাই মানা হয়নি। প্রতিশ্রুতির কাগজে লেখা আর বাস্তবের কাজ—আকাশ-পাতাল ফারাক।
সুতরাং প্রশ্ন উঠে—রাজনৈতিক দলের নেতা-কর্মীদের আদৌ দেশের প্রয়োজন আছে কি? নাকি উল্টো, এই নেতা-কর্মীরাই দেশের মূল সমস্যা? জনগণ চায় সরাসরি উত্তর। তারা দেখেছে—যেখানে কথা আর কাজের মধ্যে ফারাক, সেখানে আস্থা চূর্ণ হয়। দফা বা নির্বাচনী ভাষণ সমস্যা সমাধান করতে পারে না; সত্যিকার পরিবর্তন আসে তখনই, যখন নেতা-কর্মীরা প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী কাজ করবে, দায়িত্ব নেবে এবং নিয়মিত ফলোআপ করবে।
কিন্তু যদি ভণ্ড রাজনীতিবিদরা সংস্কারে অনাগ্রহী থাকে এবং নিজেদের স্বার্থকেই প্রাধান্য দেয়, তবে তারা কীভাবে জনগণের কল্যাণে আন্তরিকভাবে কাজ করবে? আজকের বাস্তবতা একেবারেই স্পষ্ট—দফা ও প্রতিশ্রুতি রয়েছে অগণিত, কিন্তু বাস্তব কর্ম, স্বচ্ছতা ও সততার চর্চা নেই বললেই চলে। দুর্নীতি ও স্বার্থপরতা যেন অঘোষিত নিয়মে পরিণত হয়েছে। জনগণ আর নাটক দেখতে চায় না; তারা চায় প্রমাণিত পরিবর্তন, সত্যিকারের কর্ম এবং দায়িত্বশীল নেতৃত্ব। অবশ্যই, একটি জাতির দীর্ঘকালীন রাজনৈতিক সংকট রাতারাতি সমাধান সম্ভব নয়। কিন্তু ৪০ দিনে না হোক, ৪০ মাসের আগেই সেই পরিবর্তনের যাত্রা শুরু হবে—এমন একটি আশা আমরা করতেই পারি।
রহমান মৃধা, সাবেক পরিচালক, ফাইজার, সুইডেন। Rahman.Mridha@gmail.com
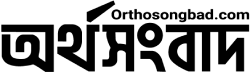
মত দ্বিমত
হাটে জন বিক্রি আধুনিক দাসত্বের অন্ধকার ও রাষ্ট্রীয় দায়
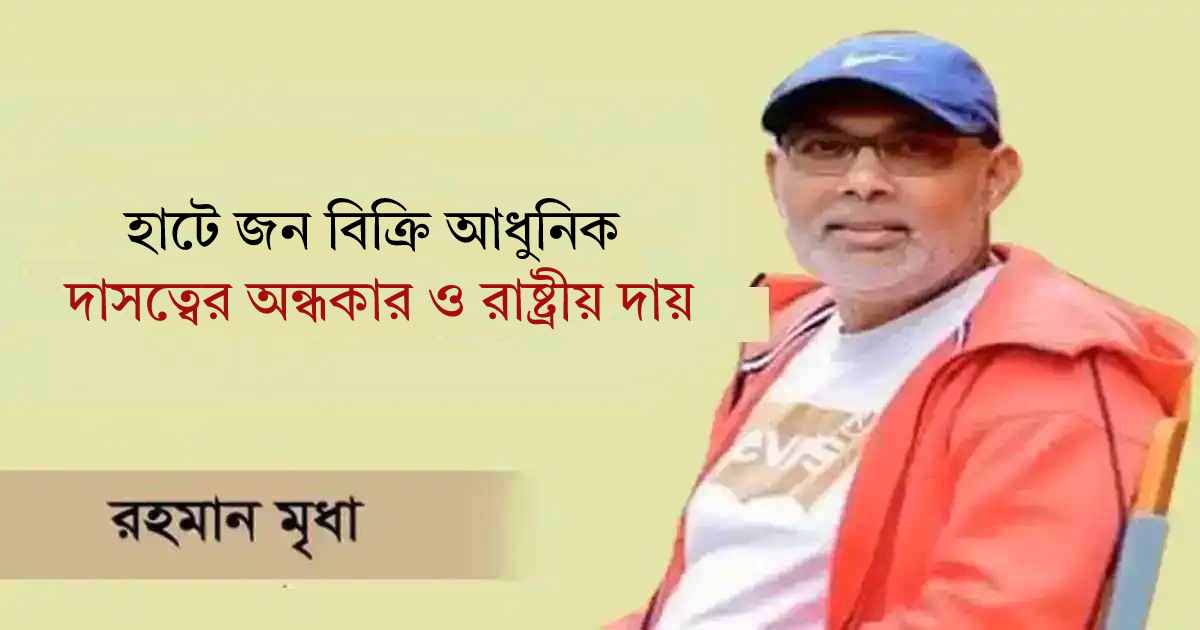
বাংলাদেশের গ্রামীণ সমাজে আজও “নহাটার হাটে জন (কৃষিশ্রমিক বা কিষাণ) বিক্রি” এক বিভীষিকাময় বাস্তবতা। এই হাটে মৌসুমি জনেরা সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত দাঁড়িয়ে থাকে-অপেক্ষায় থাকে নিজেদের শ্রমকে নগদ মূল্যে বিকিয়ে দেওয়ার। আর জমির মালিক বা কৃষকরা দরদাম করে তাদের কিনে নেয় দিনের বা মৌসুমের জন্য। আমার শৈশবের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় নহাটার হাটে জন বিক্রির ভয়াবহ দৃশ্য চোখে দেখেছি, যা আজও নির্মমভাবে চলমান। একবার হাটে দাসত্বের এই বাণিজ্যে বিক্রি হয়ে গেলে শ্রমিকেরা নিয়োগকর্তার খেয়াল-খুশি পূরণ না হওয়া পর্যন্ত নিজ বাড়িতে ফিরে যেতে পারে না। এই প্রথা শ্রমিকদের স্বাধীনতা সম্পূর্ণভাবে গ্রাস করে, তাদের অস্তিত্বকে অবমানবিক দাসত্বের গহ্বরে নিক্ষেপ করে।
জন হাটের ইতিহাস গভীর শোষণ ও অমানবিকতার অন্ধকারে নিমজ্জিত। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনে গ্রামীণ অঞ্চলে চালু ছিল কুলি বাজার—যেখানে মৌসুমি শ্রমিকদের সস্তায় বিক্রি হতো। পাকিস্তান আমলেও জমিদাররা মৌসুমি শ্রমিক কেনাবেচার মাধ্যমে তাদের আধিপত্য বজায় রাখত। স্বাধীনতার পরও এই প্রথা এক বিকৃত উত্তরাধিকার হিসেবে টিকে আছে। জন হাট তাই কোনো আকস্মিক উদ্ভাবন নয়; বরং এটি শোষণ, পরাধীনতা ও ক্ষমতাবাদী নিপীড়নের ধারাবাহিক কাঠামোর নগ্ন প্রকাশ।
জন বা কৃষিশ্রমিকদের জীবনযাত্রা একেবারেই ঐতিহাসিক দাসত্বের সমতুল্য। তাদের খাবার অপ্রতুল—এক মুঠো ভাত, সামান্য ডাল, বা কখনো রুটি। ঘুমাতে হয় অস্থায়ী ছাউনিতে বা খোলা আকাশের নিচে। অসুস্থ হলে আয় বন্ধ হয়ে যায়, চিকিৎসার ন্যূনতম সুযোগ মেলে না। হাটে দাঁড়িয়ে শ্রম বিক্রি করা তাদের জন্য সামাজিক কলঙ্ক, এক অদৃশ্য শৃঙ্খল। অতীতে দাসেরা যেমন প্রভুর দয়ার উপর নির্ভরশীল ছিল, আজকের জনেরাও নিয়োগকর্তার করুণার দাস। শর্ত পূরণ না হওয়া পর্যন্ত তারা নিজের বাড়িতে ফিরতে পারে না। গার্মেন্টস শিল্পের উত্থান হয়তো এই শৃঙ্খল কিছুটা আলগা করেছে, দৈনিক মজুরি কিছুটা বেড়েছে—কিন্তু মৌলিক কাঠামো আজও দাসত্বেরই নামান্তর।
আমার ছোটবেলার এক করুণ স্মৃতি—মধুমতি নদীর নৌকাডুবির ঘটনা—প্রমাণ করে জন সম্প্রদায়ের জীবনের তুচ্ছতা ও অবমাননা। সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছিল, ঐ দুর্ঘটনায় ছয়জনের মৃত্যু হয়, যাদের মধ্যে চারজন ছিল জন সম্প্রদায়ের। রাষ্ট্রীয় এবং সামাজিক মূল্যায়নের বিচারে তাদের মৃত্যু কেবল পরিসংখ্যান হয়ে গিয়েছিল; যেন তারা পূর্ণ মানুষ নয়, অবহেলার ভারে চূর্ণিত আধা-অস্তিত্ব।
ঐতিহাসিক দাসত্বের সঙ্গে জন হাটের তুলনা সুস্পষ্ট। অতীতে দাসেরা ছিল প্রভুর চিরস্থায়ী সম্পত্তি—তাদের কোনো মজুরি ছিল না, স্বাধীনতা ছিল না, মর্যাদা ছিল শূন্য। জন হাটের শ্রমিকরা অল্প মজুরি পেলেও তাদের জীবনযাত্রা অমানবিক, সামাজিক মর্যাদা প্রায় অনুপস্থিত। খাদ্যের অনটন, নিরাপদ ঘুমের অভাব, স্বাস্থ্যসেবার অনুপস্থিতি, সর্বত্র অবহেলা—সব মিলিয়ে তারা আধুনিক ক্রীতদাস ছাড়া আর কিছু নয়। স্বাধীনতার ঘোষণার সময় বলা হয়েছিল মানুষ মানুষের জন্য হবে, শোষণহীন সমাজ গঠিত হবে। কিন্তু অর্ধশতক পেরিয়েও বাংলাদেশে জন প্রথার অবসান ঘটেনি; বরং শোষণ আরও সূক্ষ্ম, আরও নির্মম হয়েছে।
রাজনীতিবিদদের দুর্নীতি এই বৈষম্যকে রক্তক্ষরণময় ক্ষত হিসেবে আরও গভীর করেছে। সাধারণ মানুষ ক্ষুধার্ত, অনাহারী, অমানবিক অবস্থায় দিনাতিপাত করছে—অপরদিকে রাজনীতির তথাকথিত অভিভাবকেরা লুটতরাজে মত্ত। সরকারি প্রকল্প থেকে টাকা আত্মসাৎ, টেন্ডারবাজি, বিদেশে অবৈধ সম্পদ পাচার—সবই রাষ্ট্র ও সমাজকে বিষাক্ত করেছে। বিচারব্যবস্থা, যা ন্যায়বিচারের সর্বোচ্চ আসন হওয়ার কথা, আজ দুর্নীতি, পক্ষপাত ও ক্ষমতার দাসত্বে নিমজ্জিত। এই প্রতিষ্ঠান ন্যায়কে নির্বাসনে পাঠিয়ে অবিচারকে অভ্যাসে পরিণত করেছে। এক কথায়—বাংলাদেশের বিচার বিভাগ আজ পবিত্রতার মুখোশে লুকানো সবচেয়ে অপবিত্র ক্ষেত্র।
সমাধানের পথ স্পষ্ট, কিন্তু বাস্তবায়নের ইচ্ছা অদৃশ্য। ন্যায্য মজুরি নিশ্চিত করা, শ্রমিকদের নিবন্ধন ও সামাজিক সুরক্ষা প্রদান, নিরাপদ আবাসন ও খাদ্যের নিশ্চয়তা, স্বাস্থ্যবিমা ও বয়স্কভাতা চালু করা, স্থানীয় সরকারের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা, শ্রম আইন ও মানবাধিকার আইন কঠোরভাবে প্রয়োগ করা, এবং সর্বোপরি সমাজের মানসিকতার পরিবর্তন—এসব ছাড়া মুক্তি নেই।
কিন্তু নহাটার মতো সারা বাংলাদেশের অগণিত হাটে আজও জন বিক্রি প্রথা নির্মমভাবে বহাল রয়েছে। মধুমতি নদীর নৌকাডুবি, রাজনীতির দুর্নীতি ও চরম বৈষম্য প্রমাণ করে—শুধু নহাটায় নয়, বাংলাদেশের সর্বত্র কৃষিশ্রমিকরা আধুনিক দাসত্বের অন্ধকারে বন্দি। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক দাসপ্রথার উত্তরসূরি আজকের এই জন হাট; ধনী-দরিদ্রের চরম বৈষম্য, রাষ্ট্রীয় উদাসীনতা এবং রাজনীতির কদর্য চরিত্র মিলে এই বর্বরতাকে অমর করে রেখেছে।
প্রশ্ন জাগে—কবে ভাঙবে এই অভিশপ্ত প্রথা? কবে জনরা স্বাধীন বাংলাদেশের প্রকৃত নাগরিক হিসেবে পূর্ণ মর্যাদা পাবে? আজ তারা কেবল জীবনের ঝুঁকি, নিরাপত্তাহীনতা ও অবহেলার বোঝা বইছে। সমাজে ন্যায়বিচার, ন্যায্য মজুরি, নিরাপদ জীবন ও শ্রমিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠা ছাড়া এই অভিশাপ মোচনের কোনো পথ নেই। কিন্তু রাষ্ট্র কি সত্যিই এই দায় স্বীকার করবে? আজও আমি তা দেখি না। তবে একান্ত সাধ জাগে—একদিন যেন সত্যিই তা দেখি!
রহমান মৃধা
গবেষক ও লেখক
সাবেক পরিচালক, ফাইজার, সুইডেন
Rahman.Mridha@gmail.com
মত দ্বিমত
নরওয়ের অভিজ্ঞতা বনাম বাংলাদেশের বাস্তবতা: জবাবদিহিহীন রাজনীতির অন্তরায়
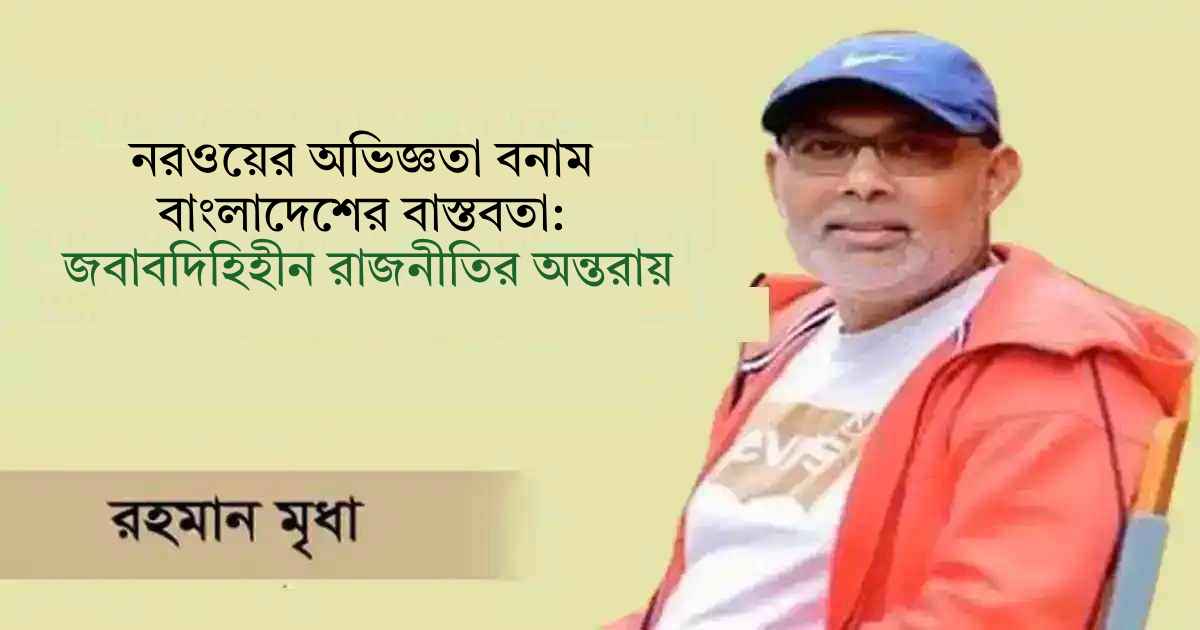
নরওয়ের অভিজ্ঞতা: জবাবদিহির এক দৃষ্টান্ত
নরওয়ে সদ্য একটি জাতীয় নির্বাচন সম্পন্ন করেছে। পুরো প্রক্রিয়াটি ছিল স্বচ্ছ, শান্তিপূর্ণ এবং গণতান্ত্রিক মানদণ্ডে উদাহরণস্বরূপ। ফলাফল ঘোষণার পর সেখানে এক চমৎকার রাজনৈতিক সংস্কৃতির প্রকাশ ঘটে। বিজয়ী দল নির্বাচনী সাফল্যের আনন্দে উচ্ছ্বসিত হলেও তারা দায়িত্বশীল আচরণ করেছে—প্রতিপক্ষকে অপমান না করে বরং ভবিষ্যতের কাজের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে।
অন্যদিকে, পরাজিত দলগুলো জনগণের রায় খোলাখুলিভাবে মেনে নিয়েছে। কেউ কেউ নিজেদের অবস্থান পুনর্মূল্যায়নের ঘোষণা দিয়েছে। আরও তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় হলো—কিছু নেতা ব্যক্তিগত দায় স্বীকার করে পদত্যাগ করেছেন, এমনকি কেউ কেউ রাজনীতি থেকে সরে দাঁড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। কারণ তাদের কাছে রাজনীতি মানে শুধু ক্ষমতা নয়, জনগণের আস্থা রক্ষা করা। ব্যর্থতাকে তারা পরাজয় নয়, বরং নৈতিক দায়িত্ব হিসেবে গ্রহণ করেছেন।
এই আচরণই সুস্থ রাজনৈতিক সংস্কৃতির প্রতিফলন। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে নির্বাচন কেবল ক্ষমতা পরিবর্তনের প্রক্রিয়া নয়, এটি নৈতিকতা, দায়বদ্ধতা ও জনগণের প্রতি সম্মানেরও পরীক্ষা। নরওয়ের অভিজ্ঞতা প্রমাণ করে—জবাবদিহির চর্চা থাকলে গণতন্ত্র কেবল শক্তিশালী হয় না, রাষ্ট্র ও সমাজের ভিত্তিও হয় আরও সুদৃঢ়।
বাংলাদেশের বাস্তবতা: দায় স্বীকারের সংস্কৃতি অনুপস্থিত
বাংলাদেশে এর উল্টো দৃশ্যপট। এখানে পরাজয় মানে শত্রু তৈরি করা, অজুহাত দাঁড় করানো, প্রতিপক্ষ বা প্রশাসনকে দায়ী করা। যেমন একজন শিক্ষার্থী খারাপ ফল করলে নিজের দায় না নিয়ে অজুহাত খোঁজে—সিলেবাসের বাইরে প্রশ্ন এসেছে, আগের রাতে ঘুম হয়নি, কিংবা অসুস্থ ছিল। রাজনৈতিক ময়দানে একই প্রবণতা দেখা যায়।
বাংলাদেশের বেহায়া ও বেশরম রাজনীতির অবসান হোক—এই প্রত্যাশা প্রতিদিনই জনমনে ঘুরপাক খায়। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে সেই পরিবর্তনের কোনো আলামত এখনো দৃশ্যমান নয়। এর বিপরীতে উন্নত গণতন্ত্র চর্চাকারী দেশগুলোতে আমরা এক ভিন্ন চিত্র দেখি, যা বাংলাদেশের জন্য এক বড় শিক্ষা হয়ে উঠতে পারে।
ডাকসু বা জাকসু নির্বাচনের ইতিহাস স্পষ্ট করে দেয়, যখনই কোনো ছাত্রসংগঠন বুঝেছে যে পরাজয় অনিবার্য, তখনই তারা নির্বাচন বয়কট করেছে। জনগণ বা শিক্ষার্থীদের আস্থা হারানোর বিষয়টি কখনো স্বীকার করেনি। বরং দায় চাপিয়েছে প্রতিপক্ষ, প্রশাসন, এমনকি আন্তর্জাতিক শক্তির ওপরও। সাম্প্রতিক জাকসু নির্বাচনেও একই ঘটনা ঘটেছে—পরাজয়ের মুখোমুখি হয়ে ছাত্রদল সমর্থিত প্রার্থীরা অংশগ্রহণ সীমিত করেছে বা শেষ মুহূর্তে বয়কট করেছে। এরপরও আত্মসমালোচনার বদলে বিভিন্ন অভিযোগই সামনে এনেছে।
ফলাফল হলো—শিক্ষার্থীদের কাছে রাজনীতির একটি নেতিবাচক প্রতিচ্ছবি গড়ে উঠছে। তারা দেখছে, রাজনীতিতে দায়বদ্ধতা বা নৈতিকতার জায়গা নেই। অথচ উন্নত গণতন্ত্রে নেতারা ব্যর্থতা স্বীকার করে নতুন প্রজন্মকে জায়গা দেন। বাংলাদেশের রাজনীতিতে সেই স্বচ্ছতা, জবাবদিহি ও নৈতিক দায়বদ্ধতা এখনো অনুপস্থিত।
ছাত্ররাজনীতির সংকট: বিকৃত নেতৃত্বের ঝুঁকি
তত্ত্ব অনুযায়ী ছাত্ররাজনীতি হওয়া উচিত স্বচ্ছ, নিরপেক্ষ ও গণতান্ত্রিক। কিন্তু বাস্তবে দুর্নীতিগ্রস্ত ও ক্ষমতালোভী রাজনীতিবিদদের হস্তক্ষেপ শিক্ষার্থীদের রাজনৈতিক বিকাশকে বাধাগ্রস্ত করছে। কুৎসিত কৌশল, ভোট কারচুপি ও অনৈতিক প্রভাব প্রয়োগের ফলে দেশের ভবিষ্যত নেতৃত্ব বিকৃত হচ্ছে।
পুরোনো প্রথায় রাজনৈতিক দলগুলোর অতিরিক্ত প্রভাব শিক্ষার্থীদের অধঃপতিত করছে। এতে তারা দায়িত্বশীল নেতৃত্ব শেখার পরিবর্তে দেখে—ক্ষমতা অর্জনের জন্য অনৈতিকতাই কার্যকর। ফলে নতুন প্রজন্মের মধ্যে নৈতিকতার অভাব তৈরি হচ্ছে। এর পরিণতি দীর্ঘমেয়াদে ভয়াবহ: একটি রাষ্ট্র যখন নৈতিক নেতৃত্ব হারায়, তখন শুধু রাজনীতি নয়, সমাজ ও প্রশাসনের প্রতিটি স্তর দুর্বল হয়ে পড়ে।
বাংলাদেশের নতুন জন্ম ও নেপালের শিক্ষা
বাংলাদেশের নতুন জন্ম হলো ২০২৪-এর গণঅভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে। কিন্তু প্রশ্ন হলো—কেন এই অভ্যুত্থান সদ্য ঘটে যাওয়া নেপালের গণঅভ্যুত্থানের ধরন থেকে এত ভিন্ন? নেপাল দেখিয়ে দিয়েছে, পরিবর্তনের মানে কেবল ক্ষমতা দখল নয়—পরিবর্তনের মানে হলো ভেতরের পরিশুদ্ধি। সেখানে আন্দোলনের নেতৃত্ব দেওয়ার পর শিক্ষার্থীরা আবার ক্লাসে ফিরেছে, আবার বই হাতে নিয়েছে। যাওয়ার আগে তারা ভাঙা রাস্তাঘাট মেরামত করেছে, আগুনে পোড়া জায়গা পরিষ্কার করেছে। আর সবচেয়ে বড় কথা—নিজেদের ভুলের জন্য তারা পুরো জাতির কাছে ক্ষমা চাইতে দ্বিধা করেনি।
অন্তর্বর্তী সরকারের নেতৃত্বে উঠে আসেন সাবেক প্রধান বিচারপতি সুশিলা কারকি। মাত্র তিনজন সহযোগী নিয়ে তিনি দায়িত্ব নিয়েছেন। এমনকি যাকে মেয়র পদে বসানোর কথা ছিল, সেই ব্যক্তি বিনয়ের সঙ্গে প্রস্তাব ফিরিয়ে দেন। ৫ মার্চ নেপালের জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে—পরিষ্কার সময়সূচি, নির্দিষ্ট লক্ষ্য, আর জনগণের আস্থার ওপর দাঁড়িয়ে।
এর বিপরীতে বাংলাদেশের অভিজ্ঞতা সম্পূর্ণ আলাদা। আমরা এত প্রত্যাশা নিয়ে যাকে ক্ষমতায় বসালাম, তিনি ও তার উপদেষ্টারা ব্যক্তিগত স্বার্থ ছাড়া কিছুই ভাবলেন না। আমি নিজেও একসময় ড. ইউনুসকে আইডল মানতাম—কিন্তু সময় আমাকে শিখিয়েছে, কেবল নাম বা খ্যাতির কারণে কাউকে অন্ধভাবে অনুসরণ করা যায় না।
আমাদের ক্ষোভের জায়গা থেকে শেখ হাসিনাকে বিদায় দিলাম, কিন্তু সেই একই কোটা অনেকের কাছে হয়ে উঠলো আলাদিনের চেরাগ। হঠাৎ করে ভাগ্য বদলে গেল কারো, দামী সানগ্লাস চোখে, ব্যান্ডের ঘড়ি হাতে, কোটি টাকার গাড়ি নিয়ে রাস্তায় নামলো তারা। অথচ কিছুদিন আগেও একই মানুষ বলতো—“আমরা এত গরিব, বাবাও খাওয়াতে কষ্ট পান।” এই বৈপরীত্যই বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় সংকট। এখানে একজনের চোখ নেই, কিন্তু আরেকজনের চোখে দামী চশমা; একজনের হাতে কিছুই নেই, আরেকজনের হাতে কোটি টাকার বিলাসিতা। তাই এদেশে সেই মনের মতো বীর জন্ম নেয় না—যাকে কবি স্বপ্ন দেখেছিলেন: “আমাদের দেশে হবে সেই ছেলে কবে, কথায় না বড় হয়ে কাজে বড় হবে।”
বাংলাদেশের অভ্যুত্থান তাই এখনো অসম্পূর্ণ। শুধু ক্ষমতার পালাবদল নয়, প্রয়োজন ভেতরের নৈতিক পরিশুদ্ধি—যা নেপাল আমাদের সামনে জীবন্ত দৃষ্টান্ত হিসেবে রেখে গেছে।
তাহলে কেন জবাবদিহির অভাব এত ভয়ঙ্কর?
• গণতন্ত্র দুর্বল হয়: জনগণের আস্থা হারালে গণতন্ত্র কাগুজে খোলসে পরিণত হয়।
• রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান ভেঙে পড়ে: জবাবদিহি না থাকলে বিচারব্যবস্থা, নির্বাচন কমিশন, প্রশাসন—সবকিছুই দলীয় প্রভাবে দুর্বল হয়ে যায়।
• প্রজন্মের বিশ্বাস হারিয়ে যায়: তরুণরা রাজনীতিকে ঘৃণা করতে শেখে এবং নেতৃত্ব থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়।
• দুর্নীতি বাড়ে: দায় স্বীকার না করে সব দায় অন্যের ওপর চাপালে দুর্নীতি প্রাতিষ্ঠানিক রূপ নেয়।
পরিবর্তনের পথ: আশার আলো কোথায়?
বাংলাদেশের রাজনীতিতে এখন সবচেয়ে জরুরি হলো আত্মসমালোচনা, নৈতিকতা ও জবাবদিহির সংস্কৃতি গড়ে তোলা। নেতাদেরই বুঝতে হবে—দায়িত্ব মানে কেবল ক্ষমতার আসনে বসা নয়, জনগণের আস্থা রক্ষা করা। জনগণের আস্থা হারালে সরে দাঁড়ানোই প্রকৃত নৈতিকতা।
• পরাজয়কে লজ্জা নয়, শিক্ষা হিসেবে গ্রহণ করতে হবে।
• নতুন প্রজন্মকে নেতৃত্বের সুযোগ দিতে হবে।
• ছাত্ররাজনীতিকে দলীয় নিয়ন্ত্রণমুক্ত করতে হবে।
• নির্বাচন ব্যবস্থাকে স্বচ্ছ ও জবাবদিহিমূলক করতে হবে।
যেদিন বাংলাদেশে নেতারা বলবেন—“আমি ব্যর্থ হয়েছি, তাই আরেকজন নতুন মানুষকে সুযোগ দেওয়া হোক”—সেদিনই শুরু হবে প্রকৃত গণতন্ত্রের যাত্রা। পরাজয়কে লজ্জা নয়, শিক্ষা হিসেবে গ্রহণ করার দিনই শেষ হবে বাংলাদেশের বেহায়া ও বেশরম রাজনীতির। আর সেই দিনই রাজনীতি হয়ে উঠবে জনগণের আস্থা ও বিশ্বাসের প্রকৃত প্রতিফলন।
রহমান মৃধা, সাবেক পরিচালক, ফাইজার, সুইডেন। Rahman.Mridha@gmail.com
মত দ্বিমত
শেয়ারবাজার উন্নয়নে শক্তিশালী ও বাস্তবমুখী পদক্ষেপ নিতে হবে

শেয়ারবাজার ভালো করার শক্তিশালী বাস্তব ভিত্তিক পদক্ষেপ এবং সেই অনুযায়ী বেশকিছু ভবিষ্যত কর্ম পরিকল্পনা ও নীতি সরকারিভাবে গ্রহণ করার উদ্যোগ নেওয়া যেতে পারে। তা নিচে দেওয়া হলো-
যেসব কোম্পানি পরিক্ষিত খারাপ এবং জেড গ্রুপে পাঠানো হয়েছে অথবা বন্ধ কোম্পানি এবং সেরকম কোম্পানিগুলো অনতিবিলম্বে আইডেন্টিফাই করে এবং অবশ্যই ঐ গলার কাটা গুলো বাজার থেকে অপসারণ করতে হবে।
প্রথম পদক্ষেপ বাস্তবায়নের আগে অবশ্যই সরকারের পক্ষ থেকে ঐসব কোম্পানির বিনিয়োগকারীদেরকে অবশ্যই ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করতে হবে। কারণ যেসকল কোম্পানিগুলো শেয়ারবাজারে আসার উদ্দেশ্য-ই ছিলো বাজার থেকে টাকা লুট করা এবং প্রকারান্তরে বিনিয়োগকারীর ক্ষতি; যা আজ দিনের আলোর মতো পরিস্কার; সেগুলোর খেসারত কোনো ভাবেই বিনিয়োগকারী বহন করতে পারে না।
(দিনের আলোর মতো পরিস্কারের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ দেবার জন্য বড়ো পরিসরে লিখতে হবে এবং সেখানে আইপিওয়ের সাথে সম্পৃক্ত মার্চেন্ট ব্যাংক; সেই সাথে অডিটর, অডিট এবং একাউন্টস, প্রাইমারি এবং সেকেন্ডারি রেগুলেটরস, ডিএসই বোর্ড মেম্বার্স, ডিবিএ সহ আরও অনেক পক্ষের কার্যক্রম এখানে প্রশ্নবিদ্ধ মনে হতে পারে। তাই সেই আলোচনার জন্য আরও সময় নিয়ে এবং গবেষণা করে সেই গবেষণা ভিত্তিক রিপোর্ট প্রদান করা অসম্ভব নয়।)
সরকারি নীতি সহায়তায় জরুরি ভিত্তিতে পুঁজিবাজারের স্বার্থে অন্তত ৫০০ পরিক্ষিত কোম্পানি (ওয়েল ম্যানেজড অ্যান্ড প্রফিটেবলে কোম্পানি সিলেক্ট করে) দেশি-বিদেশি সহ পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্তির জরুরি নির্দেশনা জারি করতে হবে এবং সেটা হতে হবে অত্যন্ত যৌক্তিক মূল্যে। যাতে করে বিনিয়োগকারীরা নির্বিঘ্নে সেসব কোম্পানিতে বিনিয়োগ করতে দ্বিধাবোধ করবেনা। ঠিক যেভাবে আমানতকারীরা ভালো ব্যাংকে নির্বিঘ্নে তাদের সঞ্চয়টা গচ্ছিত রাখে।
শেয়ার সাপ্লাই বাড়ানোর সাথে সাথে এবং ঐসব কোম্পানিগুলোতে বিনিয়োগ করতে বিশেষ কিছু সুযোগ/প্রণোদনা থাকতে হবে। এখানে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং বিশেষভাবে উল্লেখ্য সেটা হলো- ঐসব কোম্পানিতে বিনিয়োগ করলে সেই টাকার সোর্স খোঁজা যাবে না।
ভবিষ্যতে বাজারে সুশাসন প্রতিষ্ঠা এবং সেটা ধরে রাখা জরুরি। বিএসইসির চেয়ারম্যান পরিবর্তন হলেই যে মার্কেট ঠিক হবে, আস্থা আসবে, বিনিয়োগকারী লাভবান হবে, সবকিছুই ঠিক হবে সেটা আমি মনে করি না।
আপাতত এগুলো বাস্তবায়ন হলে পুঁজিবাজারে গতিশীলতা ফিরে আসবে ইনশাআল্লাহ।
লেখক: খাজা আসিফ আহমেদ
ব্যবস্থাপনা পরিচালক, কান্ট্রি স্টক লিমিটেড
মত দ্বিমত
তরুণ প্রজন্মের চোখে আজকের বাংলাদেশ গুজব, বিভ্রান্তি আর অনিশ্চয়তায় ভরা
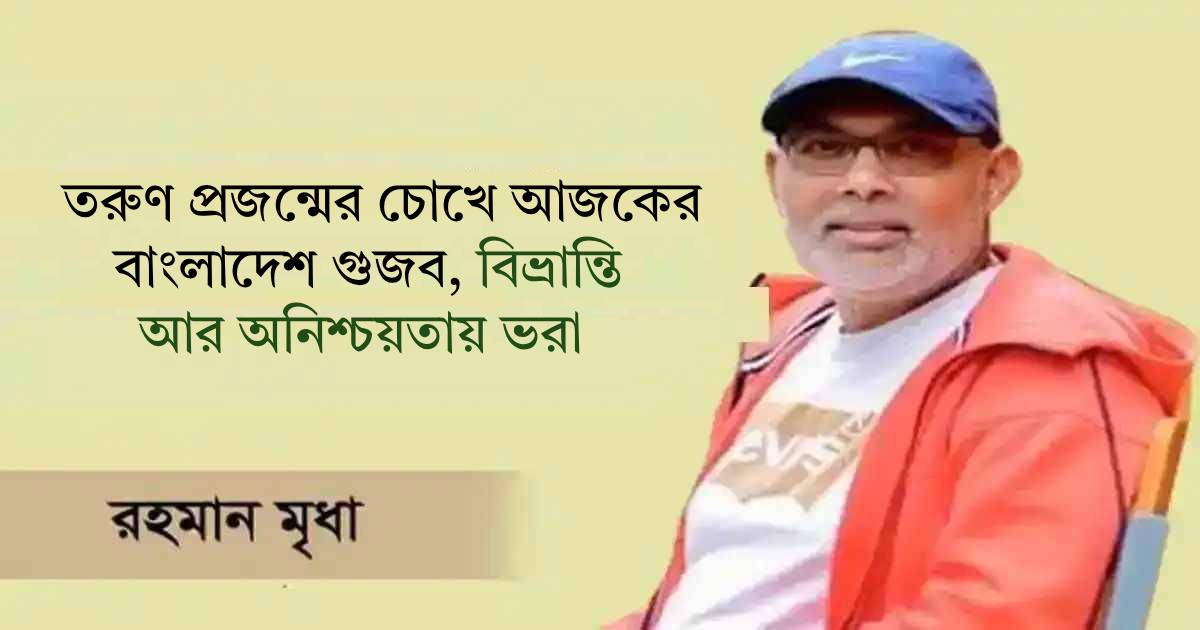
ডাকসু নির্বাচন শেষ না হতেই জাকসু নির্বাচন শুরু হয়েছে। কিন্তু নির্বাচন মানেই এখন আর স্বচ্ছতা কিংবা আস্থার জায়গা নয়, বরং গুজব, পাল্টা গুজব আর দলীয় রাজনীতির ছায়ায় ঢাকা এক নাট্যমঞ্চ। এর মধ্যেই শোনা যাচ্ছে—বিএনপি সহ কয়েকটি দল নির্বাচনে অংশ নিলেও পরে তা প্রত্যাখ্যান করেছে। এদিকে ভোট গণনার কাজ চলছে, কিন্তু চূড়ান্ত ফলাফল কী হবে—সেটি নিয়েই প্রশ্নের শেষ নেই।
প্রশ্ন উঠছে আরও বড় একটি জায়গায়—জামাত কি তাহলে বাংলাদেশের রাষ্ট্র গঠনের স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছে? আবার শোনা যাচ্ছে এমনও গুঞ্জন—স্বয়ং স্বৈরাচারী শেখ হাসিনার নির্দেশে আওয়ামী লীগের সমর্থক শিক্ষার্থীরা নাকি শিবিরের হয়ে নির্বাচনে নেমেছে এবং তাদের জয় নিশ্চিত করেছে। গত ডাকসু নির্বাচনের সময়ও শুনেছি, স্বতন্ত্র প্রার্থী শামীম হোসেন নাকি র’এর এজেন্ট হয়ে প্রার্থী হয়েছিলো।
সব মিলিয়ে এক অদ্ভুত রাজনৈতিক নাটক। কে সত্য বলছে আর কে মিথ্যা, সেটা বোঝা প্রায় অসম্ভব। কারও কাছে তথ্য নেই, কারও কাছে আছে শুধু গল্প। অথচ সত্যিটা চাপা পড়ে আছে—কেউ আসল কথা বলতে চায় না, কিংবা বলার সুযোগ পাচ্ছে না।
এই বাস্তবতা শুধু শিক্ষাঙ্গন নয়, বরং পুরো দেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতির প্রতিচ্ছবি। যে প্রজন্মের এখন বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে ভবিষ্যৎ রাষ্ট্রের নেতৃত্ব গড়ার কথা, তারা আজ গুজব, ষড়যন্ত্র আর অন্ধকার রাজনীতির চক্রে বন্দি। ফলাফল হলো—বিভ্রান্ত তরুণ সমাজ, আস্থাহীন রাজনৈতিক সংস্কৃতি, আর এক প্রশ্নবিদ্ধ বাংলাদেশ।
আমাদের বর্তমান প্রজন্ম তাই একটাই প্রশ্ন তুলতে বাধ্য—what’s going on? কিন্তু সঠিক উত্তর মেলে না।
দেশের কেন্দ্রবিন্দুগুলো হচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয়। এগুলো শুধু শিক্ষার জায়গা নয়, বরং ভবিষ্যৎ রাষ্ট্রনেতা তৈরির কারখানা। অথচ সেই বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানে যদি এতো বিভ্রান্তি, এতো গুজব আর এতো রাজনৈতিক কৌশল ঢুকে পড়ে, তাহলে পুরো বাংলাদেশের অবস্থা কী হবে—এ প্রশ্ন কি আমরা ভেবেছি কখনও?
বর্তমান অন্তর্বর্তীকালীন সরকার যেন জাতিকে আশ্বস্ত করতে চায়—সব ঠিক আছে, সব নিয়ন্ত্রণে আছে। কিন্তু বাস্তবতা ভিন্ন সংকেত দিচ্ছে। অন্যদিকে বিএনপির ডিজিটাল নেতা তারেক রহমান কী ভাবছেন? লন্ডনের নিরাপদ দূরত্ব থেকে তিনি কি দেশে ফেরার ঝুঁকি নেবেন, নাকি “ডিজিটাল নিরাপত্তা”র আড়ালেই থেকে যাবেন? প্রশ্ন উঠছে যখন তাঁর যোগ্যতা নিয়ে, তখনই আলোচনায় আসছে তাঁর অতীত—অপরাধীর প্রত্যাবর্তন ও রাজনৈতিক সংস্কৃতির গভীর সংকট।
একজন দণ্ডপ্রাপ্ত রাজনীতিবিদ দেশে ফিরছেন—এ খবরেই রাজনৈতিক অঙ্গনে উত্তেজনা ছড়িয়েছে। দুর্নীতি, অবৈধ সম্পদ অর্জন এবং নানা অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডের অভিযোগে তাঁর বিরুদ্ধে আদালতের রায় রয়েছে। তবুও তিনি একটি বৃহৎ রাজনৈতিক দলের নেতৃত্বে আসীন, আর তাঁর সমর্থকরা বর্ণাঢ্য সংবর্ধনার প্রস্তুতিতে ব্যস্ত।
মূল সমস্যা নিহিত আছে নেতৃত্বের যোগ্যতা ও নৈতিক ভিত্তির প্রশ্নে। যাঁর নেই কোনো প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা, নেই স্বাভাবিক পেশা বা বৈধ আয়ের উৎস, তিনি কীভাবে একটি জাতীয় দলের নেতৃত্বের দাবিদার হতে পারেন? তাঁর একমাত্র পরিচয়—তিনি মুক্তিযোদ্ধা ও রাষ্ট্রপতির সন্তান এবং সাবেক প্রধানমন্ত্রীর ছেলে। অর্থাৎ নেতৃত্বের ভিত্তি তাঁর ব্যক্তিগত অবদান নয়, বরং উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত পরিচয়।
এই চিত্র শুধু একজনকে ঘিরে নয়; বরং এটি আমাদের রাজনৈতিক সংস্কৃতির অন্তর্নিহিত সংকটকে উন্মোচিত করে। দল ও নেতার প্রতি অন্ধ আনুগত্য, ব্যক্তিত্বপূজা এবং বংশকেন্দ্রিক রাজনীতির কারণে অপরাধপ্রবণতা বারবার আড়াল হয়ে যায়। সমর্থকরা অপরাধের সত্যকে উপেক্ষা করে, বরং রাজনৈতিক আবেগে তা “নায়কোচিত প্রত্যাবর্তন” বলে আখ্যা দেয়।
কিন্তু একটি দেশের গণতন্ত্র টিকে থাকে যোগ্যতা, সততা ও জবাবদিহিতার ওপর। যদি অপরাধপ্রবণ ব্যক্তি কেবল পারিবারিক পরিচয়ের কারণে নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত হন, তবে তা রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলোর দুর্বলতাকেই প্রতিফলিত করে। যতই জাঁকজমকপূর্ণ সংবর্ধনা দেওয়া হোক না কেন, এটি আসলে আমাদের রাজনৈতিক ও নৈতিক মানদণ্ডের অবক্ষয়ের প্রতিচ্ছবি।
অতএব, এ মুহূর্তে জাতির সামনে সবচেয়ে বড় প্রশ্ন—আমরা কী ধরনের নেতৃত্ব চাই? অপরাধীকে বরণ করা নাকি যোগ্য ও সৎ নেতৃত্বকে প্রতিষ্ঠা করা? দেশের দীর্ঘমেয়াদী ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে এই প্রশ্নের সঠিক উত্তরের ওপর।
আরেকটি অদ্ভুত প্রশ্ন উঠে আসে—যদি আওয়ামী লীগ শিবিরকে সমর্থন করে, তবে কি বিএনপির যুবদলকে ছাত্রলীগ সমর্থন করবে? নাকি উল্টো, তারা একদিন আবার জামায়াতের সঙ্গে গোপন জোট গড়ে তুলবে? আমাদের রাজনীতির ইতিহাস বলছে—অসম্ভব কিছুই নেই।
তাহলে আসল চিত্র কী? উত্তর নেই। শুধু প্রশ্ন, শুধু গুজব, শুধু অবিশ্বাস। শত প্রশ্নে দেশ ভরে গেছে, অথচ একটিরও সঠিক উত্তর মেলে না। কারণ দেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতি দীর্ঘদিন ধরে মিথ্যার চর্চায় অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে। সত্যকে আড়াল করে মিথ্যাকে জাহির করাই এখন যেন প্রাত্যহিক রুটিন।
এই অবস্থায় সাধারণ মানুষ, বিশেষ করে তরুণ প্রজন্ম, ভীষণ হতাশ। তারা রাজনীতিকে আর ভবিষ্যতের ভরসা মনে করে না। তাদের চোখে রাজনীতি মানে দুর্নীতি, সুবিধা আর ক্ষমতার খেলা।
আমার দৃঢ় বিশ্বাস, এখন যদি দেশের রাজনীতিবিদদের জবাবদিহিতার আওতায় আনা না যায়, তবে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম পুরোপুরি রাজনীতি থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে। হয়তো সময় এসেছে সকল দুর্নীতিবাজ রাজনীতিবিদদের ধরে ধরে জেলে ঢোকানোর—একটি পরিশুদ্ধ রাজনৈতিক সংস্কৃতি গড়ে তোলার জন্য। আমরা অতিষ্ঠ হয়ে গেছি। আর নয়—এবার যথেষ্ট হয়েছে।
বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর থেকে বারবার এক করুণ সত্য সামনে এসেছে—রাজনৈতিকভাবে এই জাতি একের পর এক পরাজয়ের গল্প শুনে চলেছে। মুক্তির স্বপ্ন ছিল যে স্বাধীনতায়, সেই স্বপ্নকে কলুষিত করেছে দুর্নীতি, মিথ্যা প্রতিশ্রুতি আর অযোগ্য নেতৃত্ব। যারা দীর্ঘদিন ক্ষমতায় থেকেও মানুষের আস্থা ফিরিয়ে আনতে ব্যর্থ হয়েছে, তাদের হাতে আর কোনোদিন এই দেশকে নিরাপদ রাখা সম্ভব নয়।
প্রকৃতপক্ষে, এই দুর্নীতিগ্রস্ত রাজনীতিবিদদের মানসিক চিকিৎসার আওতায় আনা উচিত—কারণ তারা সত্যকে ভুলে গিয়ে মিথ্যাকে এতটাই চর্চা করেছে যে, আজ বাস্তবতা ও ভ্রান্তির ফারাকও তারা চিনতে পারে না। এদের হাতে দেশকে চালনা করা মানে ভবিষ্যৎকে অন্ধকারে ঠেলে দেওয়া।
তাহলে সামনে পথ কী?
দেশকে এগিয়ে নিতে হলে একমাত্র ভরসা সাধারণ জনগণ। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়—এই জনগণই বারবার অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছে। এখন প্রয়োজন তাদের ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টা, প্রয়োজন একটি নৈতিক বিপ্লব। আমাদের সময়ের দাবি হচ্ছে—সৎ, সাহসী এবং দায়িত্বশীল মানুষের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর। কেবল তারাই পারবে ভাঙা আস্থা মেরামত করতে, দেশকে সত্যিকার অর্থে গণতন্ত্র ও উন্নয়নের পথে এগিয়ে নিতে।
আজ বাংলাদেশ দাঁড়িয়ে আছে এক নতুন রাজনৈতিক কল্পনার দোরগোড়ায়। যদি আমরা সাহস করে মিথ্যার রাজনীতি থেকে বেরিয়ে আসতে পারি, যদি আমরা দুর্নীতির শৃঙ্খল ছিন্ন করতে পারি, তবে এই দেশ আবারও স্বপ্ন দেখবে—একটি স্বাধীন, ন্যায়ভিত্তিক, সমৃদ্ধ বাংলাদেশের।
আমার দৃঢ় বিশ্বাস—এখনই সময়। আর নয় আপস, আর নয় প্রতারণা। এখন দরকার সত্য, ঐক্য, আর নতুন নেতৃত্বের পথে অগ্রযাত্রা।
রহমান মৃধা, সাবেক পরিচালক, ফাইজার, সুইডেন। Rahman.Mridha@gmail.com
মত দ্বিমত
কেন শিবিরের বিরুদ্ধে এত প্রপাগান্ডা?
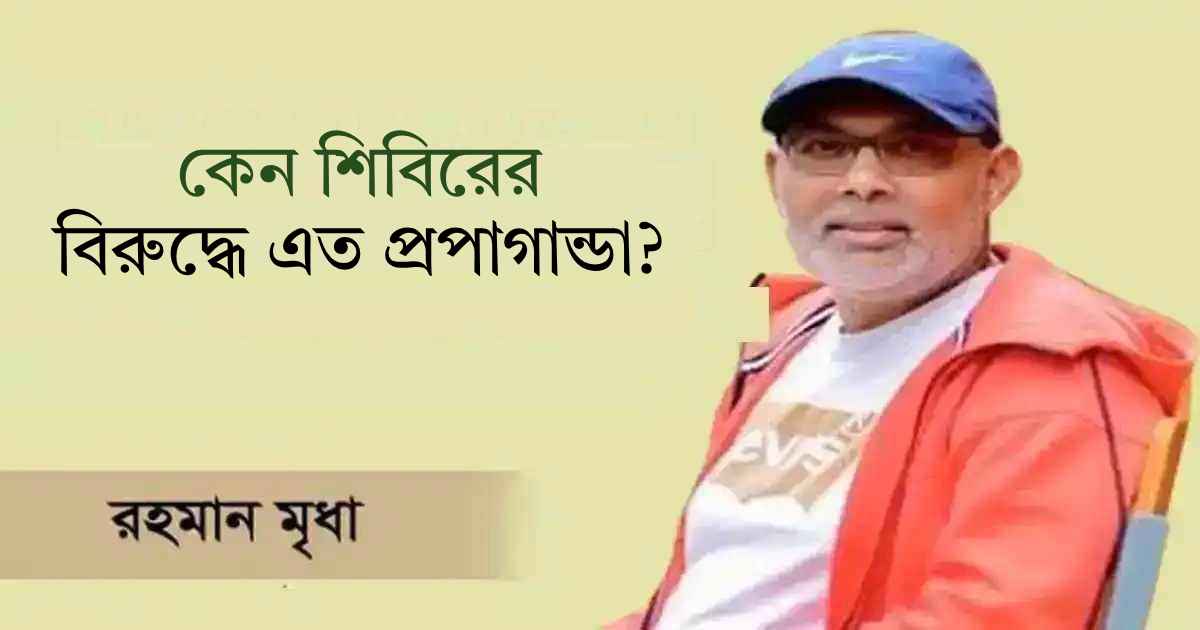
আমি চল্লিশ বছরেরও বেশি সময় ইউরোপে বসবাস করছি। এই দীর্ঘ সময়ে কখনো শুনিনি শিবির কোনো ভালো কাজ করেছে। বরং সবসময় শুনেছি তারা নৃশংস—মানুষের পায়ের রগ কেটে দেয়, নারীদের ধর্ষণ করে, সন্ত্রাসী বানায় ইত্যাদি। কিন্তু আমি দেশের বাইরে থাকলেও, বাংলাদেশের খবর–ঘটনায় সবসময় সচেতন থাকি। আন্দাজে বা গুজবের ওপর নির্ভর করি না। যাচাই–বাছাই ছাড়া কিছু লিখতেও চাই না। কারণ আমি জানি, ভ্রান্ত তথ্যের ভিত্তিতে লিখলে তা শুধু ভুল বার্তাই ছড়ায়।
ডাকসু নির্বাচনের সময় বেশ কিছু ঘটনা আমি লক্ষ্য করেছি। দেখলাম একজন শিক্ষার্থী ভিসিকে টেবিলে আঘাত করে হুমকি দিচ্ছে। একদল বহিরাগত গুণ্ডা ভাড়া করে বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢুকানো হয়েছে। আবার অন্য একটি পক্ষ ক্যাম্পাসের বাইরে দাঁড়িয়ে স্লোগান দিচ্ছে— শিবিরের চৌদ্দগুষ্টি উদ্ধার কর।
এমন সময়েই আমার মনে প্রশ্ন জাগল— যে সংগঠনকে নিয়ে এত নেতিবাচক প্রচারণা, তাদের সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা কীভাবে সম্পর্ক রাখছে? অবাক হয়ে দেখলাম, অনেক ছাত্রী শিবিরের নেতাকর্মীদের কাছে এসে ‘ভাইয়া’ বলে সম্বোধন করছে, সেলফি তুলছে। অথচ অন্য ছেলেরা ভদ্রভাবে কথা বললেও মেয়েরা তাড়াহুড়ো করে সরে যাচ্ছে। বিষয়টি আমাকে সত্যিই বিস্মিত করল।
আমি ভাবলাম— এখানে নিশ্চয়ই কোনো ভিন্ন সত্য লুকিয়ে আছে। রহস্য উদঘাটন করার আগেই সহধর্মিণীর সঙ্গে বিষয়টি আলোচনা করলাম। তিনি সুইডিশ। আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, “আচ্ছা বলো তো, কী কারণে একজন নারী কোনো পুরুষকে দেখে অস্বস্তি বোধ করে?”
তিনি বললেন, নারীদের মধ্যে বিশেষ এক ধরনের ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় কাজ করে। এই অনুভূতি তাদেরকে বুঝতে সাহায্য করে কে ভদ্র, কে কপট, কার সঙ্গে নিরাপদ। ভদ্রতা, নম্রতা, স্বাভাবিক ব্যবহার—এসব মেয়েরা খুব দ্রুত বুঝতে পারে।
আমি আবার তাঁকে কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, “তুমি আমাকে কীভাবে পছন্দ করলে?” তিনি হেসে উত্তর দিলেন, “তুমি তোমার আচরণ দিয়ে আমাকে পছন্দ করতে বাধ্য করেছিলে।”
সেখান থেকেই বুঝলাম—নারীরা আস্থার জায়গা থেকে সিদ্ধান্ত নেয়। ভয় বা বাহ্যিক ভদ্রতার আড়ালে লুকানো চরিত্র তারা টের পায়।
আমি আগে কখনো শিবির কী, তা ভালোভাবে জানতাম না। শুধু নেতিবাচক প্রচারণার ফলেই তাদের চিনি। কিন্তু লেখালেখির সুবাদে খোঁজখবর নিতে গিয়ে দেখলাম, ইসলামের মৌলিক কিছু অধিকার যেমন—শিক্ষার অধিকার, নারীর মর্যাদা, দুর্নীতির বিরুদ্ধে অবস্থান—এসব বিষয় তারা তাদের আদর্শের অংশ হিসেবে ধরে রেখেছে।
বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবিরের গঠনতন্ত্রে নারী শিক্ষার ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া আছে। তাদের ছাত্রীসংগঠন নারীদের মধ্যে নৈতিক শিক্ষা, আত্মমর্যাদা ও সামাজিক কাজের প্রচারে যুক্ত। যদিও রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের চাপে এই তথ্যগুলো প্রায়ই আড়ালে থাকে, কিন্তু যারা ভেতর থেকে চেনে তারা ভিন্ন অভিজ্ঞতার কথা বলে।
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মেয়েরা নিশ্চয়ই অজ্ঞ নন, তারা বোঝেন কোথায় নিরাপদ। অথচ প্রচারণায় শিবিরকে সবসময় অমানবিক ও হিংস্র হিসেবে দেখানো হয়। ডাকসু নির্বাচনের সময় আমি যদি নিজ চোখে দৃশ্যগুলো না দেখতাম, তাহলে হয়তো আমিও ধরে নিতাম—শিবির সত্যিই একটি সন্ত্রাসী সংগঠন।
তাহলে প্রশ্ন জাগে—সত্যকে এত ভয় পায় কেন? বিশেষ করে আওয়ামী লীগ ও বিএনপি নামের দুই বড় দল কেন শিবিরকে নির্মূল করার জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করে? নিশ্চয়ই এখানে অন্য কোনো রাজনৈতিক হিসাব আছে।
গতবছর আমি আমার ছোটবেলার বিদ্যালয়ের সভাপতি নির্বাচনে বিএনপির নেতাকর্মীদের দুর্নীতি দেখেছি। পরে ২০০৪ সালের গণঅভ্যুত্থানের পর থেকে দেখছি, যখন কেউ ভয়ে প্রতিবাদ করতে সাহস করে না, তখনই বুঝতে পেরেছি—আওয়ামী লীগের মতো বিএনপিরও পতন নিশ্চিত।
আমি সরাসরি তারেক রহমান ও তার দলের কিছু শীর্ষ নেতার সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলাম। বলেছিলাম, “আমরা সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে দেশকে দ্বিতীয়বার মুক্ত করেছি। এখনো যদি সন্ত্রাসীরাই দেশ দখল করে, তবে আগের সন্ত্রাসীদের অপরাধ কোথায় ভিন্ন?” কিন্তু কোনো লাভ হয়নি।
অত্যন্ত দুঃখের বিষয়, বঙ্গবন্ধুর মতো জিয়াউর রহমানের সঙ্গেও আমার ছোটবেলায় মেলামেশার সুযোগ হয়েছিল। তাই হয়তো মনে অজান্তেই তাঁদের প্রতি এক ধরনের শ্রদ্ধা জন্মেছিল। কিন্তু তাঁদের পরিবার ও উত্তরসূরিদের কর্মকাণ্ডে সেই শ্রদ্ধা মুছে গেছে।
দেশটা কারো বাপের নয়। আমি শুধু আমার দেশের মানুষের কথাই ভাবি। তাদের বিপদে–আপদে পাশে থাকার চেষ্টা করি। চাই—সবাই ভালো থাকুক। চাই—নতুন প্রজন্মকে বিশ্বাস করা হোক এবং দেশ পরিচালনার দায়িত্ব তাদের হাতে দেওয়া হোক।
আওয়ামী লীগ, বিএনপির মতো শিবিরও একটা নাম। শুধু নাম দিয়ে কাজ হয় না, সে প্রমাণ আমরা পেয়েছি। তবে মিথ্যাচার বা প্রপাগান্ডা না ছড়িয়ে বরং কাজের মাধ্যমে বিচার হওয়া উচিত। আজকের বাংলাদেশে দুর্নীতি ছেড়ে সত পথে চললে, সত্য কথা বললে শিবিরের মতো অন্যরাও আপনাকে অনুসরণ করবে।
পরনিন্দা, পরচর্চা ছেড়ে নিজের উন্নতির দিকে মন দিন। অন্তত আখেরাতের টিকিটটা সাথে নিতে পারবেন।
উপদেশ দেওয়ার প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু যেমন রেমিট্যান্স পাঠাতে কেউ আমাকে বলে না, তবু আমি পাঠাই—তেমনি উপদেশ দিতেও কেউ বলেনা, তবুও দিই—ক্ষতি কী?
রহমান মৃধা, সাবেক পরিচালক, ফাইজার, সুইডেন। Rahman.Mridha@gmail.com



























