মত দ্বিমত
গণঅভ্যুত্থান-উত্তর ন্যায়ভিত্তিক রাষ্ট্র বিনির্মাণের স্বপ্ন
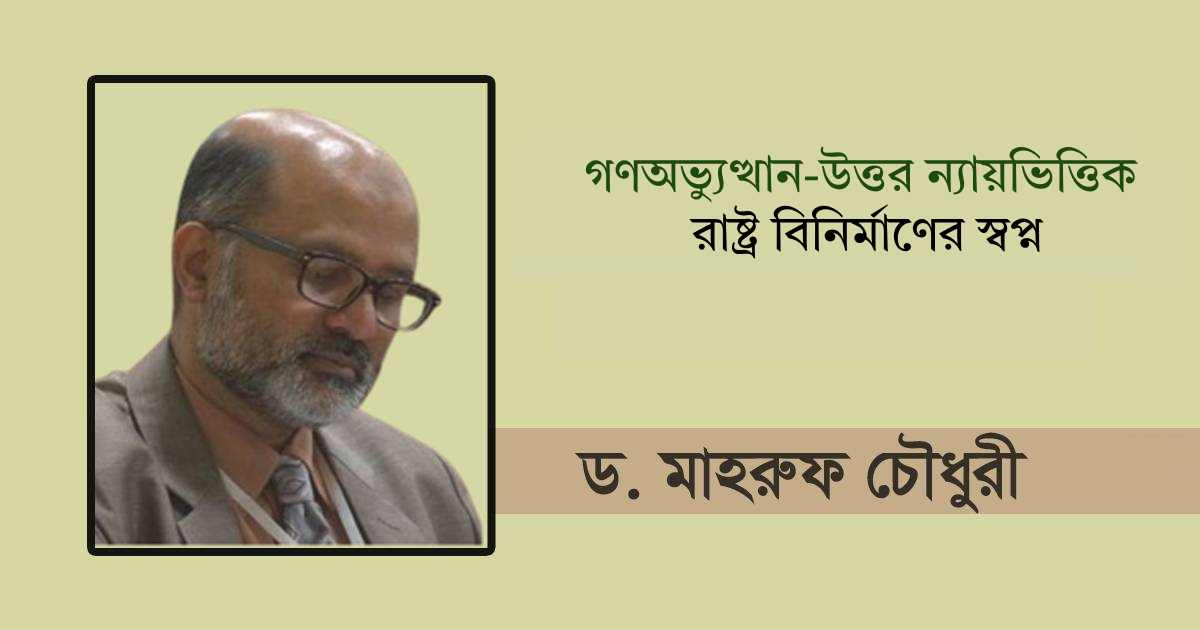
বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাস একান্তভাবেই গণমানুষের স্বপ্ন, সংগ্রাম ও আত্মত্যাগের ইতিহাস। ১৯৫২-এর ভাষা আন্দোলন, ১৯৬৯-এর গণঅভ্যুত্থান, ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধ কিংবা ১৯৯০-এর স্বৈরাচারবিরোধী গণআন্দোলন- দেশের প্রতিটি আন্দোলন ছিল ইতিহাসের একেকটি মোড় ঘোরানো ক্ষণ, যেখানে জনগণের আকাঙ্ক্ষা ছিল একটি ন্যায়ভিত্তিক, গণতান্ত্রিক ও কল্যাণমুখী রাষ্ট্রের সন্ধানে।
এই ধারাবাহিকতায় ২০২৪ সালের গণঅভ্যুত্থান আবারও প্রমাণ করেছে, রাষ্ট্র যখন নাগরিকদের ন্যায্যতা, সম্মান ও ভবিষ্যতের নিরাপত্তা দিতে ব্যর্থ হয়, তখন জনতার অভ্যুত্থানই হয়ে ওঠে পরিবর্তনের প্রধান নিয়ামক। তবে ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, প্রতিটি বিপ্লবের পরবর্তী সময়ই সবচেয়ে সংকটময়, কারণ তখনই শুরু হয় পুরনো কাঠামো ভাঙার ও নতুন কাঠামো নির্মাণের জটিল প্রক্রিয়া।
বর্তমানের বাংলাদেশ সেই বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ সময়ের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। স্বৈরশাসনের পতনের পরও দেশে এখনো সুসংহত ন্যায়ভিত্তিক রাষ্ট্র কাঠামোর ছাপ সুস্পষ্ট নয়। এই অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের কালপর্বে একদিকে যেমন পুরনো শাসনযন্ত্রের ভাঙন, অন্যদিকে তেমনি নতুন রাষ্ট্রচিন্তার অস্পষ্টতা- উভয়ের দ্বন্দ্বই জাতিকে এক অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। এই প্রেক্ষাপটে জাতি হিসেবে আমাদের প্রয়োজন গভীরতর আত্মবিশ্লেষণ, সুনির্দিষ্ট দিকনির্দেশনা ও ব্যাপক জনশিক্ষাভিত্তিক সাংস্কৃতিক নবজাগরণ।
এই বাস্তবতায় ‘গণঅভ্যুত্থান’ কেবলমাত্র একটি দমনমূলক শাসনব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিবাদী জনতার ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ নয়; এটি এক নতুন সমাজব্যবস্থা নির্মাণের গভীর আকাঙ্ক্ষারও প্রতীক। এই আকাঙ্ক্ষা একটি ন্যায়ভিত্তিক, গণমুখী ও মানবিক রাষ্ট্রব্যবস্থার স্বপ্নকে ধারণ করে, যেখানে নাগরিকের অধিকার ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠা পায় নৈতিকতা, যুক্তি ও মানবিক বোধের ভিত্তিতে। এখানে ইনসাফ বা ন্যায়ের ধারণাটি আবেগনির্ভর কোনো কল্পনা নয়, বরং এটি একটি রূপান্তরধর্মী দার্শনিক ও রাজনৈতিক চেতনা, যার শিকড় বিস্তৃত মানবসভ্যতার গভীরে। প্লেটোর ‘ন্যায়ভিত্তিক রাষ্ট্র’ দর্শন থেকে শুরু করে ইবনে খালদুনের ‘আসাবিয়্যাহ’-নির্ভর সমাজ বিন্যাস, রুশোর ‘সামাজিক চুক্তি’ তত্ত্ব, মার্ক্সের শ্রেণিবিন্যাসহীন রাষ্ট্রভাবনা, গান্ধীর অহিংস মানবিকতা এবং নেলসন মেন্ডেলার ক্ষমাশীলতা ও অন্তর্ভুক্তিমূলক নেতৃত্ব- সবই এক বিকল্প রাষ্ট্রচিন্তার দিকনির্দেশনা দেয়, যেখানে শাসনের কেন্দ্রবিন্দুতে থাকে ন্যায়, কল্যাণ ও মানবিক মর্যাদা। সুতরাং গণঅভ্যুত্থান যখন রাষ্ট্র পরিবর্তনের হাতিয়ার হয়ে ওঠে, তখন তা কেবল প্রতিক্রিয়া নয়; বরং একটি সুসংগঠিত, সুনির্দিষ্ট ন্যায়ভিত্তিক ভবিষ্যতের ডাক।
ন্যায়ভিত্তিক রাষ্ট্র বিনির্মাণের মৌলিক ভিত্তি হলো একটি স্বাধীন, নিরপেক্ষ ও বিশ্বাসযোগ্য বিচারব্যবস্থা যেখানে আইনের শাসন কেবল সাংবিধানিক ধারায় নয়, বরং নৈতিক ন্যায়ের বাস্তব রূপায়ণে প্রতিফলিত হয়। জন লক যেমন সতর্ক করে দিয়েছিলেন, ‘যেখানে আইন স্তব্ধ হয়, সেখানেই অত্যাচার জন্ম নেয়’। বাংলাদেশের বর্তমান বিচারব্যবস্থা এই সতর্কবাণীকে যেন শাসন-সংস্কৃতির এক বাস্তব অভিশাপে পরিণত করেছে। দলীয় প্রভাব, আমলাতান্ত্রিক জটিলতা, রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ এবং বিচারহীনতার সংস্কৃতি এখানে ন্যায় শব্দটিকেই প্রায় নিঃস্বার্থ প্রতীকে পরিণত করেছে। ইবনে খালদুন তাঁর ‘মুকাদ্দিমা’-তে গভীরভাবে উল্লেখ করেছিলেন, ‘অন্যায়ই সভ্যতার পতনের মূল কারণ’। এই কথাটি বর্তমান প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশে ভীষণভাবে প্রাসঙ্গিক। বিচারবহির্ভূত হত্যা, গুম, প্রতিহিংসামূলক মামলা, নিরীহ নাগরিকের হয়রানি ইত্যাদি যদি রাষ্ট্রীয় স্তরে প্রশ্রয় পায়, তবে তা কেবল বিচার ব্যবস্থার প্রতি আস্থার অবসান ঘটায় না; গণতন্ত্রের পথকে করে তোলে কন্টকাকীর্ণ। এর পরিণতিতে সমাজে সৃষ্টি হয় এক ভয়াবহ অনিশ্চয়তা ও নিরাপত্তাহীনতা, যা কেবল আইন নয়, নাগরিক আচার- আচরণের ভিতকেও ভেঙে দেয়। ইনসাফভিত্তিক রাষ্ট্রে বিচার হবে কেবল শাস্তির অনুশাসনে নয়, বরং তা হবে ন্যায়বোধ, মানবিকতা ও প্রক্রিয়াগত স্বচ্ছতার সম্মিলন যেখানে ন্যায় শুধু আদেশ নয়, বিচার ব্যবস্থার প্রতি জনগণের আস্থারও প্রতিফলন।
ন্যায়ভিত্তিক রাষ্ট্র নির্মাণে বিচার ব্যবস্থার পাশাপাশি একটি স্বচ্ছ, জবাবদিহিমূলক ও অংশগ্রহণমূলক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা অপরিহার্য। আধুনিক বিশ্বের উদাহরণে দেখা যায়, দক্ষিণ আফ্রিকার ট্রুথ অ্যান্ড রিকনসিলিয়েশন কমিশন কিংবা রুয়ান্ডার গ্যাকাকা আদালত এই দুই বিশেষ উদ্যোগই ইতিহাসের ভয়াবহ সহিংসতা ও নিপীড়নের পর ন্যায় ও পুনর্মিলনের পথ উন্মোচনে জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণ ও রাষ্ট্রের রাজনৈতিক সদিচ্ছার শক্ত সাক্ষ্য। এগুলো আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় যে ন্যায় কেবল একটি রাষ্ট্রীয় কাঠামোর ভিতরকার প্রক্রিয়া নয়, এটি একটি নৈতিক ও জনগণসম্পৃক্ত রাজনৈতিক সংস্কৃতি। কিন্তু আজকের বাংলাদেশে যখন নির্বাচনী ব্যবস্থা প্রশ্নবিদ্ধ, ভোটারহীন নির্বাচন কিংবা দলীয় প্রশাসনের ছত্রছায়ায় সংঘটিত একতরফা ভোট সম্পন্ন হয়, তখন গণতন্ত্র এক অভিনয়মাত্র হয়ে পড়ে। এ অবস্থাকে যেন অগ্রিম অনুমান করেছিলেন জ্যাঁ জাক রুশো, যিনি তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ ‘দ্যা সোসাল কন্ট্রাক্ট’ লেখেন, ‘ইংল্যান্ডের জনগণ একমাত্র সংসদ নির্বাচনের সময় স্বাধীন। বাকি সময় তারা দাস’। অনুরূপ চিত্র বাংলাদেশের বর্তমান রাজনৈতিক বাস্তবতায় যেন প্রতিবিম্বিত হচ্ছে যেখানে জনগণের মতামত নির্বাচনকেন্দ্রিক আনুষ্ঠানিকতায় সীমাবদ্ধ হয়ে গেছে, কার্যকর অংশগ্রহণ নির্বাসিত।
আসন্ন নির্বাচনের আগেই নবগঠিত নির্বাচন কমিশনের কার্যকলাপ নিয়ে জনমনে যে প্রশ্ন উঠছে, তা গণতন্ত্রের জন্য অশনিসংকেত। একটি ইনসাফভিত্তিক রাষ্ট্রে নির্বাচন কমিশন কেবল একটি প্রশাসনিক প্রতিষ্ঠান নয়, বরং এটি জনগণের আস্থা ও গণতান্ত্রিক চর্চার মূল স্তম্ভ। এর কার্যক্রম হতে হবে সর্বজনগ্রাহ্য, সম্পূর্ণ স্বাধীন, স্বচ্ছ এবং আধুনিক প্রযুক্তিনির্ভর, যাতে কোনো প্রকার দলীয় প্রভাব, প্রশাসনিক চাপ কিংবা অনিয়মের সুযোগ না থাকে। নির্বাচনের প্রকৃত অর্থ দাঁড়ায় জনগণের মতামতের প্রতিফলন, আর সে প্রক্রিয়ায় জনগণের অবাধ অংশগ্রহণ নিশ্চিত না হলে গণতন্ত্র রূপ নেয় একটি ফাঁপা খোলসে। বিশ্বজুড়ে গণতন্ত্রের পুনর্জাগরণে যেসব মডেল অনুকরণীয় হয়ে উঠেছে, তাদের মধ্যে চিলির গণভোট প্রক্রিয়া বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। একনায়কতান্ত্রিক শাসনের অবসান ঘটিয়ে জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণে যেভাবে সেখানে একটি নতুন গণতান্ত্রিক কাঠামো গড়ে তোলা হয়েছিল, তা আমাদের জন্য এক গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা। এই উদাহরণ প্রমাণ করে, নির্বাচন তখনই অর্থবহ হয় যখন তা হয় সর্বস্তরের মানুষের আস্থাভাজন, রাজনৈতিক সদিচ্ছা ও ন্যায়ের চর্চার বহিঃপ্রকাশ। আমাদের নির্বাচন প্রক্রিয়াও যেন কেবলমাত্র আইনত নয়, কার্যতও জনগণের মালিকানায় পরিচালিত হয়; আর এমন চেতনায় রাষ্ট্রযন্ত্রকে পুনর্গঠন করাই হবে একটি ইনসাফভিত্তিক রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ ন্যায়ভিত্তিক রাষ্ট্র নির্মাণে অর্থনৈতিক ইনসাফ বা ন্যায্যতা একটি অপরিহার্য ভিত্তি। এটি কেবল আয়বৈষম্য হ্রাস করার উদ্দেশ্য নয়, বরং সামগ্রিকভাবে সম্পদের উৎপাদন, মালিকানা ও বণ্টনে একটি ন্যায়সংগত ও অংশগ্রহণমূলক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার প্রশ্ন। এই দৃষ্টিভঙ্গি আমাদের নিয়ে যায় একটি গভীরতর নৈতিক ও দার্শনিক আলোচনায়। ইসলামি অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় ‘ইনসাফ’-এর ধারণা খুব স্পষ্ট, সম্পদের ‘মালিকানা স্রষ্টার, রক্ষণাবেক্ষণের দায়দায়িত্ব মানবের; ভোগে নির্ধারিত সীমা অনুসরণ, বণ্টনে ন্যায্যতা নিশ্চিতকরণ’। এর মাধ্যমে স্পষ্ট হয় যে, মানুষের অর্থনৈতিক স্বাধীনতা অপরিহার্য হলেও তা সমাজকল্যাণ ও ন্যায়বিচারের নীতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে। কার্ল মার্ক্স একটি সুস্পষ্ট বিকল্প সমাজব্যবস্থার কথা বলেছেন, যেখানে ‘প্রত্যেকের কাছ থেকে তার সামর্থ্য অনুযায়ী, প্রত্যেকের কাছে তার প্রয়োজন অনুযায়ী’ সম্পদ বণ্টিত হবে। এটি নিছক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা নয়, বরং ন্যায্যতার একটি আদর্শিক ভিত্তি যেখানে ব্যক্তিরা সমাজের প্রতি তাদের সামর্থ্য অনুযায়ী অবদান রাখবে এবং বিনিময়ে সমাজ তাদের প্রয়োজন মেটাবে। এর মাধ্যমে অর্থনীতির লক্ষ্য হবে শুধু মুনাফা নয়, বরং মানবিক মর্যাদা, সমতা এবং সামাজিক সাম্য নিশ্চিত করা।
বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে ইনসাফভিত্তিক অর্থনৈতিক কাঠামোর প্রয়োজনীয়তা আরও প্রকট হয়ে ওঠে, যখন দেখা যায় একদিকে অল্প কিছু মানুষের হাতে গচ্ছিত সম্পদের পাহাড়, অন্যদিকে সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠী ন্যূনতম মৌলিক চাহিদা পূরণে ব্যর্থ। এই বৈষম্য কেবল একটি অর্থনৈতিক ব্যর্থতা নয়, বরং রাষ্ট্রের ন্যায়ের নীতির সঙ্গে একটি ঘোরতর বিশ্বাসঘাতকতা। ইনসাফভিত্তিক অর্থনৈতিক কাঠামো কেবল করনীতির পুনর্বিন্যাস নয়; এটি একটি সমন্বিত জনকল্যাণকেন্দ্রিক রাষ্ট্রদর্শনের দাবিদার, যেখানে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বাসস্থান ও কর্মসংস্থানকে নাগরিকের অধিকার হিসেবে নিশ্চিত করা হয়; জনগণের প্রতি অনুগ্রহ হিসেবে নয়। এই কাঠামো গঠনের জন্য প্রয়োজন স্বচ্ছ, জবাবদিহিমূলক এবং জনগণের প্রতি দায়বদ্ধ একটি রাষ্ট্রব্যবস্থা। এর জন্য জরুরি করব্যবস্থার প্রগতিশীল সংস্কার, ঋণ ও ব্যাংক ব্যবস্থার ওপর রাজনৈতিক প্রভাবের অবসান, দুর্নীতির নির্মূল, এবং ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ও শ্রমজীবী মানুষের অধিকার নিশ্চিত করা। কৃষক ও শ্রমিক এই দুই প্রধান উৎপাদনশক্তিকে কেন্দ্র করে অর্থনীতিকে পুনর্গঠনের মধ্য দিয়েই প্রকৃত ইনসাফ প্রতিষ্ঠা সম্ভব।
লাতিন আমেরিকার বলিভিয়া ‘বুয়েন ভিভির’ বা ‘ভালোভাবে বেঁচে থাকা’ নামক দর্শনের মাধ্যমে এক বিকল্প উন্নয়ন চিন্তার পথ দেখিয়েছে, যার কেন্দ্রবিন্দুতে আছে প্রকৃতি, সম্প্রদায় ও আত্মমর্যাদার সহাবস্থান। এই দর্শন বলিষ্ঠভাবে প্রচলিত ভোগবাদী ও ব্যক্তিকেন্দ্রিক উন্নয়ন ধারণার বিপরীতে গিয়ে, সামষ্টিক কল্যাণ, পারস্পরিক নির্ভরতা এবং প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষার গুরুত্ব তুলে ধরে। এখানে মানুষকে প্রকৃতির শত্রু নয়, বরং সহযাত্রী ও রক্ষক হিসেবে কল্পনা করা হয়। এর মাধ্যমে একটি ন্যায্য সমাজ গঠনের প্রাকৃতিক-সামাজিক রূপরেখা হিসেবে বিবেচিত। বলিভিয়ার সংবিধানেও প্রকৃতিকে অধিকারসম্পন্ন সত্তা হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে, যা রাষ্ট্র ও নাগরিকদের উপর তার সংরক্ষণের নৈতিক ও আইনগত দায় আরোপ করে।
এই চিন্তাধারার সঙ্গে ইসলামী অর্থনীতির মৌলিক দর্শনের গভীর সাদৃশ্য রয়েছে। ইসলামে বলা হয়, দুনিয়ায় সম্পদের ‘মালিকানা স্রষ্টার, রক্ষণাবেক্ষনের দায়দায়িত্ব মানবের’ অর্থাৎ মানুষ ভোগদখলের চূড়ান্ত অধিকারী নয়, বরং সে এক দায়িত্বশীল তত্ত্বাবধায়ক (স্টুযার্ড)। তার প্রতি অর্পিত হয়েছে সম্পদের সুষম ব্যবহার, অপচয় রোধ এবং সমাজে সাম্য প্রতিষ্ঠার দায়। এই দৃষ্টিভঙ্গিতে ব্যক্তি নয়, বরং সমষ্টি, প্রকৃতি এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কল্যাণকে উন্নয়নের মূল পরিমাপক হিসেবে গণ্য করে। তাই বলিভিয়ার ‘বুয়েন ভিভির’ এবং ইসলামী অর্থনীতির এই দায়বদ্ধতাভিত্তিক দর্শন উভয়ই আমাদের উন্নয়ন ভাবনায় একটি ন্যায্যতাভিত্তিক, ইনসাফপূর্ণ বিকল্প কাঠামো গঠনের সম্ভাবনা তৈরি করে।
সুশিক্ষা ও সুস্বাস্থ্য কেবল ব্যক্তির উন্নয়নের উপাদান নয়, বরং রাষ্ট্রের ন্যায়ের ভিত্তিকে মজবুত করার প্রধান স্তম্ভ। অমর্ত্য সেন তাঁর ‘ক্যাপাবিলিটি অ্যাপ্রোচ’-এ সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন যে, উন্নয়ন বলতে বোঝায় মানুষের বাস্তব সুযোগ ও সক্ষমতা বৃদ্ধিকে যার ভিত্তি হলো মানসম্মত শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবা। কিন্তু বাংলাদেশের বাস্তবতায় আজ উচ্চমানের শিক্ষা কেবল শহরের কিছু সুবিধাপ্রাপ্ত শ্রেণির হাতে সীমাবদ্ধ, আর অধিকাংশ সরকারি হাসপাতাল সাধারণ মানুষের জন্য হয়ে উঠেছে অনিশ্চয়তা, দুর্নীতি ও অবহেলার প্রতীক। একটি ইনসাফভিত্তিক রাষ্ট্রব্যবস্থায় শিক্ষা ও স্বাস্থ্য হবে বাজারনির্ভর সুবিধা নয়, বরং রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রিত ও প্রদত্ত অধিকার। এই রাষ্ট্র সবার জন্য সমান মানের শিক্ষা নিশ্চিত করবে, যেখানে পাঠ্যক্রম হবে নৈতিকতা, মানবিকতা ও সমাজকল্যাণ-ভিত্তিক। ‘শিক্ষা মানে শুধু ডিগ্রি নয়, মানুষ গড়ার যথার্থ প্রক্রিয়া’ এই দর্শনকে ভিত্তি করে রাষ্ট্রীয় আদর্শ ‘বৈচিত্র্যের মাঝে ঐক্য’কে প্রধান্য দিয়ে শিক্ষা ব্যবস্থার পুনর্গঠন হচ্ছে সময়ের দাবি। একইভাবে স্বাস্থ্যসেবাকে হতে হবে সহজপ্রাপ্য, সুলভ, সর্বজনীন ও সম্মানজনক। ইউনেস্কোর মানব উন্নয়ন সূচকে অনেক পিছিয়ে থাকা দেশগুলোতেও দেখা গেছে যেখানে রাষ্ট্র মানসম্মত শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করেছে, সেখানে জনগণের আস্থা ও অংশগ্রহণ বেড়েছে, গণতন্ত্র হয়েছে কার্যকর। ইনসাফ কেবল আইনের বইয়ে লেখা একটি ধারণা নয়, এটি মানুষের প্রতিদিনের জীবনযাত্রায় বাস্তব, উপলব্ধিযোগ্য ন্যায়ের উপলব্ধি। তাই শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতের সংস্কার মানেই শুধু উন্নয়ন নয়, বরং একটি ন্যায়ভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠার পথে অগ্রগামী পদক্ষেপ।
সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইনসাফ মানে কেবল সকলের জন্য আইনগত সমতা নয়, বরং সমাজের প্রতিটি গোষ্ঠী ও ব্যক্তির মর্যাদা, পরিচয় ও বৈচিত্র্যের স্বীকৃতি। ন্যায় তখনই পূর্ণতা পায়, যখন তা শ্রেণি, ধর্ম, লিঙ্গ, ভাষা, পেশা কিংবা জাতিগোষ্ঠীর বিভাজনকে অতিক্রম করে সমানভাবে সকলকে মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করে। চার্লস টেইলর তাঁর ‘দ্যা পলিটিক্স অব রিকোগনিশন’ প্রবন্ধে যে বক্তব্য রেখেছেন, তা আজকের রাষ্ট্রচিন্তার জন্য অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। বিশেষ বিশেষ জনগোষ্ঠীর অস্তিত্ব ও পরিচয়কে স্বীকৃতি না দেওয়া কেবল তাদের আত্মমর্যাদার উপর আঘাত নয়, বরং এটি একধরনের সাংস্কৃতিক নিপীড়ন। বাংলাদেশের বাস্তবতায় ধর্মীয় ও জাতিগত সংখ্যালঘু, হিজড়া জনগোষ্ঠী (তৃতীয় লিঙ্গ), বেদে সম্প্রদায়, চা-শ্রমিকদের মত ভিন্ন জীবনধারার মানুষদের সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য, ভাষাগত বৈচিত্র্য এবং জীবনচর্যার ভিন্নতাকে সম্মান না দিলে ন্যায়ভিত্তিক রাষ্ট্র নির্মাণের কথা কেবল স্লোগানে সীমিত থাকবে। যেমন ব্রাজিল, কানাডা কিংবা দক্ষিণ আফ্রিকার মতো বহু-বৈচিত্র্যময় সমাজগুলো ইনসাফ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে সাংস্কৃতিক স্বীকৃতি ও অন্তর্ভুক্তির নীতি গ্রহণ করেছে, তেমনি আমাদের রাষ্ট্রেও দরকার একটি বহুমাত্রিক সাংস্কৃতিক পরিমন্ডল গঠন করা যেখানে নানান পরিচয় বিরোধ নয়, বরং সম্প্রীতির ভিত্তি হিসেবে কাজ করবে এবং রাষ্ট্রীয় আদর্শ ‘বৈচিত্র্যের মাঝে ঐক্য’-এর প্রতিফলন ঘটাবে। ন্যায়বিচার তখনই সুসংহত হয়, যখন রাষ্ট্র কেবল আইন প্রয়োগে নয়, বরং প্রতিটি মানুষের স্বাতন্ত্র্যকে মর্যাদা দিয়ে তাকে সম্মানিত নাগরিক হিসেবে স্বীকৃতি দেয়। এই দৃষ্টিভঙ্গি ছাড়া ইনসাফ কেবল একতরফা শাসন বা সংখ্যাগরিষ্ঠতার আধিপত্য হিসেবে রয়ে যাবে।
পরিবেশগত ন্যায্যতা কেবল একটি পরিবেশবাদী ধারণা নয়, এটি একটি নৈতিক ও আন্ত:প্রাজন্মিক দায়িত্ব। জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত যেমন বাংলাদেশের মতো উপকূলীয় ও নদীনির্ভর দেশে সবচাইতে গভীরভাবে অনুভূত হয়, তেমনি এর প্রতিকারে রাষ্ট্রীয় উদাসীনতা ন্যায়ের পরিপন্থী। ‘পরিবেশগত ন্যায়বিচার’-এর দর্শন অনুযায়ী, শুধু বর্তমান প্রজন্ম নয়, ভবিষ্যৎ প্রজন্মের অধিকারও বিবেচনায় নেওয়া কল্যাণমুখী রাষ্ট্রের কর্তব্য। জন রলস তাঁর ‘ন্যায়বিচারের তত্ত্ব’ (থিওরী অব জাস্টিস)-এ যে ‘আন্ত:প্রাজন্মিক ন্যায়বিচার’ (ইন্টারজেনারেশানাল জাস্টিস)-এর কথা বলেছেন, তা আমাদের রাষ্ট্রচিন্তার কেন্দ্রে থাকা উচিত যেখানে ভবিষ্যৎ নাগরিকদের জন্য সজীব,সতেজ ও বাসযোগ্য পৃথিবী রেখে যাওয়া একটি নৈতিক ও রাষ্ট্রীয় বাধ্যবাধকতা। বাংলাদেশে নদী দখল, বন উজাড়, পাহাড় কাটা, শহুরে দূষণ ও জলাভূমি ধ্বংসের পেছনে যেভাবে স্বার্থান্ধ উন্নয়ন ও রাজনৈতিক ছত্রছায়ায় লুটপাট কাজ করে, তা একপ্রকার পরিবেশগত বৈষম্য ও নিপীড়ন। শহর ও গ্রামের নাগরিকদের মধ্যকার পরিবেশগত অধিকারবিভাজন, কিংবা উপকূলীয় অঞ্চলে বসবাসকারী দরিদ্র মানুষের বাস্তুচ্যুতি এসবই প্রমাণ করে যে, ইনসাফ কেবল অর্থনীতিতে নয়, পরিবেশনীতি ও প্রাকৃতিক সম্পদের বণ্টনেও প্রয়োজনীয়। আদিবাসী সমাজের ‘প্রকৃতির সাথে যথাযোগ্য সহাবস্থান’ ধারণা এবং ধর্মীয় ঐতিহ্যে লোভ সংযমের তাগিদ আমাদের শেখায় যে প্রয়োজনের অতিরিক্ত ভোগ নয়, বরং পরিমিতিবোধ ও ভবিষ্যত প্রজন্মের প্রতি সহানুভূতির মধ্য দিয়েই পরিবেশগত ন্যায়ের পথে অগ্রসর হওয়া সম্ভব। ইনসাফভিত্তিক কল্যাণমুখী রাষ্ট্র গঠনে তাই পরিবেশবাদ একটি বিলাসিতা নয়, বরং তা একটি মৌলিক ন্যায্যতা ও অস্তিত্বের প্রশ্ন। গণঅভ্যুত্থান কখনোই কেবল প্রতিরোধ বা ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ নয়; এটি একটি নবজাগরণের আহ্বান, যেখানে জনগণ তাদের ন্যায্য অধিকার, সম্মান ও মর্যাদা ফিরে পাওয়ার সংগ্রামে আত্মনিয়োগ করে।
একটি ন্যায়ভিত্তিক রাষ্ট্র গঠনের স্বপ্ন কেবল সংবেদনশীলতা বা আবেগের বিষয় নয়, এটি একটি দার্শনিক, নৈতিক ও সাংগঠনিক প্রকল্প, যার ভিত্তি শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বিচার, অর্থনীতি, সংস্কৃতি, পরিবেশ ও রাজনীতিতে ন্যায়ের সুষম প্রতিফলন। এই ইনসাফভিত্তিক রাষ্ট্রের লক্ষ্য হবে ব্যক্তি নয়, জনগণ; ক্ষমতা নয়, দায়িত্ব; দখল নয়, সেবা। তাই বাংলাদেশের জন্য গণঅভ্যুত্থানের পরবর্তী চ্যালেঞ্জ হলো এই স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দিতে প্রয়োজনীয় নীতিনির্ধারণ, কাঠামোগত সংস্কার ও সর্বজনীন জনশিক্ষা কার্যক্রম শুরু করা। ন্যায়ের ভিত্তিতে রাষ্ট্র গড়ার এই প্রয়াসে যদি সমাজের প্রতিটি মানুষ তথা সাধারণ নাগরিক, নীতিনির্ধারক, পেশাজীবী, শিক্ষক, যুবক প্রত্যেকেই নিজ নিজ অবস্থান থেকে দায়িত্বশীল ভূমিকা নেয়, তবে একদিন এই স্বপ্নই হয়ে উঠবে একটি নতুন বাংলাদেশের বাস্তব প্রতিচ্ছবি। আমরা বাস্তবের সেই সোনালী দিনের অপেক্ষায় রইলাম।
ড. মাহরুফ চৌধুরী, ভিজিটিং ফ্যাকাল্টি, ইউনিভার্সিটি অব রোহ্যাম্পটন, যুক্তরাজ্য। mahruf@ymail.com
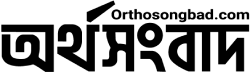
মত দ্বিমত
নির্বাচনের প্রাক্কালে নুরুল হকের ওপর হামলা: রাজনৈতিক অস্থিরতার নতুন সংকেত
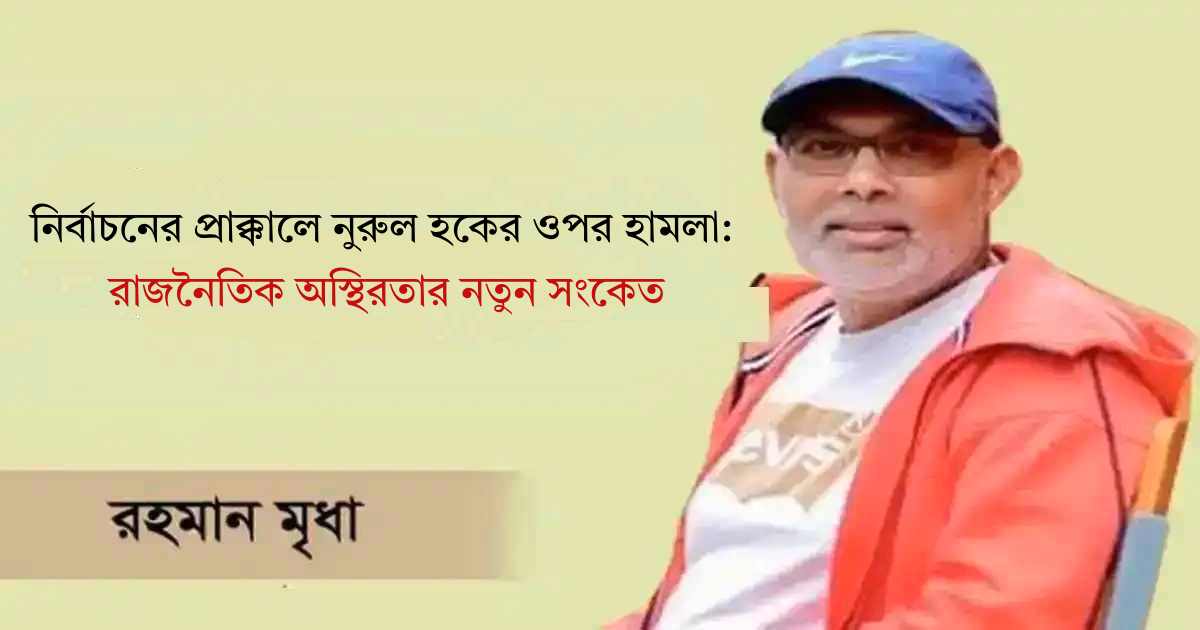
সারাদেশে যখন নানা অপ্রীতিকর ঘটনার পর প্রশাসন নীরব ভূমিকা পালন করছে, তখন হঠাৎ করে নুরুল হক নুরের ওপর হামলার ঘটনা দেশজুড়ে নতুন করে আলোড়ন তুলেছে। প্রত্যক্ষ ভিডিওচিত্র ও প্রত্যক্ষদর্শীদের বর্ণনায় দেখা গেছে, হামলায় সেনা এবং পুলিশের সদস্যরাও সরাসরি অংশ নিয়েছে। নুর বর্তমানে ঢাকা মেডিকেল কলেজের আইসিইউতে মুমূর্ষু অবস্থায় চিকিৎসাধীন। এ ঘটনা শুধু একটি রাজনৈতিক হামলা নয়, বরং আসন্ন জাতীয় নির্বাচনের প্রেক্ষাপটে একটি বড় ধরনের রাজনৈতিক সংকেত বহন করছে।
সরকার সদ্য ঘোষণা করেছে যে জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে ২০২৬ সালের ফেব্রুয়ারির প্রথম সপ্তাহে। এই সময়সীমা নিয়ে আগে থেকেই নানা রাজনৈতিক বিতর্ক ছিল। সেনাপ্রধান জেনারেল ওয়াকার-উজ-জামান এর আগে নির্বাচন দ্রুত আয়োজনের পক্ষে মত দিয়েছেন। অপরদিকে প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস সময় নিয়ে সুষ্ঠু ও অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন আয়োজনের ওপর গুরুত্ব দিয়েছেন। এই দ্বন্দ্বপূর্ণ প্রেক্ষাপটেই নুরের ওপর হামলার ঘটনা পরিস্থিতিকে আরও উত্তপ্ত করে তুলেছে।
হামলার ঘটনার পর জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় দফতর থেকে পাঠানো বিবৃতিতে জাতীয় পার্টির সন্ত্রাসীদের দায়ী করা হয়েছে এবং এটিকে আওয়ামী ফ্যাসিবাদের দোসরদের কাজ হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। জামায়াত গভীর উদ্বেগ ও তীব্র নিন্দা জানিয়ে আহতদের প্রতি সমবেদনা প্রকাশ করেছে এবং দোষীদের গ্রেফতার ও শাস্তির দাবি জানিয়েছে। অন্যদিকে গণঅধিকার পরিষদের নেতাকর্মীরা বলছেন, এটি একটি পরিকল্পিত আক্রমণ যা তরুণ প্রজন্মের রাজনীতিকে স্তব্ধ করার চেষ্টা।
গণঅধিকার পরিষদের উচ্চতর পরিষদ সদস্য ও গণমাধ্যম সমন্বয়ক আবু হানিফ সংবাদমাধ্যমকে জানিয়েছেন যে, প্রধান উপদেষ্টা ড. ইউনূস নুরুল হক নুরের শারীরিক অবস্থার খোঁজ নিয়েছেন এবং তদন্ত করে হামলায় জড়িতদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দিয়েছেন।
এছাড়া, অ্যাটর্নি জেনারেল মো. আসাদুজ্জামান নুরের ওপর হামলাকে গভীর ষড়যন্ত্রের অংশ হিসেবে উল্লেখ করেছেন এবং জাতীয় পার্টির বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়ার কথা বলেছেন। উচ্চতর পরিষদ সদস্য ও গণমাধ্যম সমন্বয়কের মন্তব্যে জানা গেছে- “হামলার পরপরই প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস নুরুল হক নুরের সঙ্গে ফোনে কথা বলেন। তিনি নুরকে আশ্বাস দেন যে, ঘটনাটি তদন্ত করে দোষীদের বিরুদ্ধে দ্রুত বিচারিক ব্যবস্থা নেওয়া হবে।” ড. ইউনূসের এই ফোনালাপকে অনেকেই ইতিবাচক ইঙ্গিত হিসেবে দেখছেন। বিশেষ করে রাজনৈতিক সহিংসতার পরিবেশে এটি একটি আস্থা ফেরানোর প্রতীকী বার্তা। তবে পর্যবেক্ষকদের মতে, এই আশ্বাস কার্যকর প্রমাণিত হবে কি না তা নির্ভর করবে সরকারের পরবর্তী পদক্ষেপের ওপর। অতীতে বহুবার আশ্বাস দেওয়া হলেও বিচার হয়নি—তাই এবার সত্যিকার অর্থে সেনা ও পুলিশের সদস্যরা যদি দায়ী প্রমাণিত হন এবং তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হয়, তবে এটি নতুন সরকারের বিশ্বাসযোগ্যতা বাড়াবে। অন্যথায় এটি উল্টো ড. ইউনূসের নিরপেক্ষতা নিয়েই প্রশ্ন তুলবে।
এই ঘটনার সঙ্গে আরও একটি তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় হলো, সেনাপ্রধানের সদ্যসমাপ্ত চীন সফরের পরপরই এই অপ্রত্যাশিত হামলা সংঘটিত হলো। রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা মনে করছেন, এই প্রেক্ষাপট ঘটনার পেছনে আন্তর্জাতিক কূটনৈতিক বার্তাও বহন করতে পারে। ফলে দেশীয় রাজনীতি যেমন অস্থিরতার মধ্যে পড়েছে, তেমনি আন্তর্জাতিক অঙ্গনেও এ ঘটনা নজর কাড়বে।
বর্তমান পরিস্থিতিতে সবচেয়ে বড় প্রশ্ন হচ্ছে, নির্বাচনের আগে দেশে স্থিতিশীল রাজনৈতিক পরিবেশ নিশ্চিত করা যাবে কি না। নুরের ওপর হামলার মতো ঘটনা যদি অব্যাহত থাকে, তবে তা নির্বাচনের গ্রহণযোগ্যতা ও অংশগ্রহণকে গুরুতরভাবে প্রভাবিত করবে। রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে সমঝোতা এবং সহিংসতা নিয়ন্ত্রণের জন্য সরকারের আন্তরিকতা এখন সবচেয়ে বড় পরীক্ষার মুখে।
রহমান মৃধা
গবেষক ও লেখক
(সাবেক পরিচালক, ফাইজার, সুইডেন)
Rahman.Mridha@gmail.com
মত দ্বিমত
প্রকৌশল খাতে বৈষম্য কাটাতে হবে লাইসেন্স ও জবাবদিহির মাধ্যমে
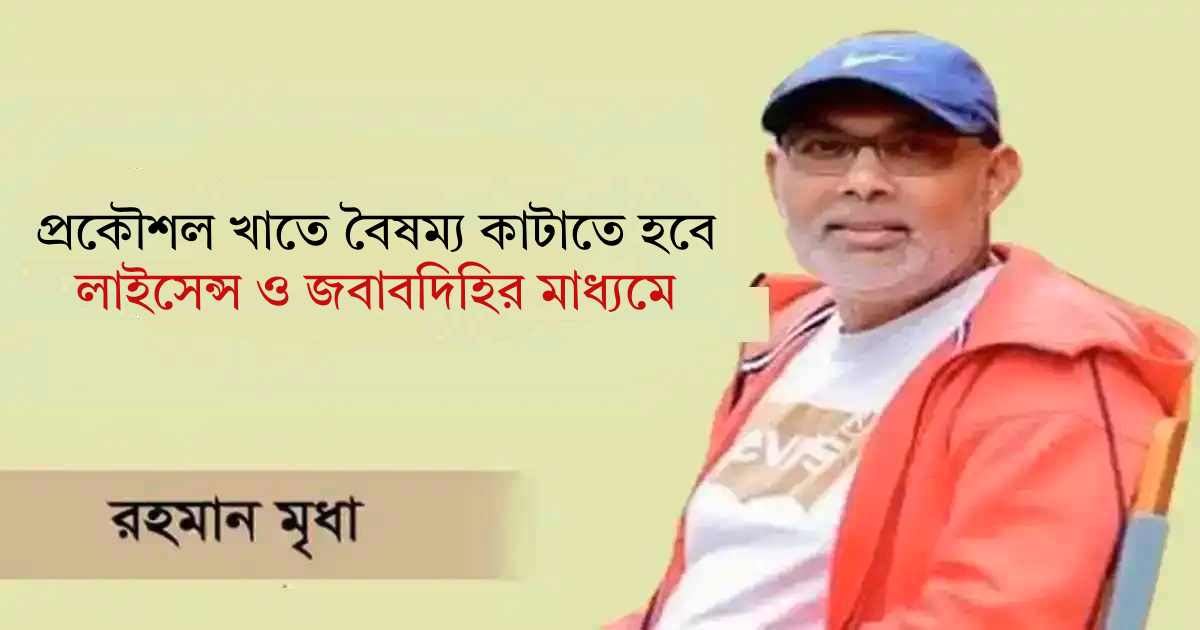
বাংলাদেশ আজ উন্নয়নের এক সংযোগস্থলে দাঁড়িয়ে। শিল্পায়ন, অবকাঠামো নির্মাণ ও প্রযুক্তি খাতে প্রকৌশলীরা মেরুদণ্ডস্বরূপ। কিন্তু সাম্প্রতিক সময়ে প্রকৌশলীদের দুই শাখা—স্নাতক প্রকৌশলী এবং প্রকৌশলে ডিপ্লোমাধারীদের মধ্যে টানাপোড়েন আমাদের উন্নয়নযাত্রাকে অকারণে জটিল করে তুলেছে।
শাহবাগে স্নাতক প্রকৌশলীদের তিন দফা দাবির আন্দোলন, পুলিশের হামলা এবং পাল্টা আন্দোলনে ডিপ্লোমাধারীদের অংশগ্রহণ—সব মিলিয়ে প্রকৌশল খাত এখন এক অস্থির বাস্তবতার মুখোমুখি। তবে এ সংকট কেবল বাংলাদেশি বাস্তবতায় সীমাবদ্ধ নয়। বিশ্বজুড়ে প্রকৌশল পেশাকে কীভাবে নিয়ন্ত্রণ ও মানসম্মত করা হয়, তা থেকে শিক্ষা নিয়ে আমরা সমাধানের পথ খুঁজতে পারি। ইউরোপ ও আমেরিকায় ‘ইঞ্জিনিয়ার’ শব্দটি কেবল ডিগ্রি অর্জনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়।
যুক্তরাষ্ট্রে Professional Engineer (PE) লাইসেন্স ছাড়া কেউ সরকারি প্রকল্পে সই করতে বা ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে পরিচয় দিতে পারেন না। জার্মানিতে ‘Ingenieur’ উপাধি আইন দ্বারা সংরক্ষিত। শুধু ডিগ্রি থাকলেই চলবে না, প্রফেশনাল রেজিস্ট্রেশন বাধ্যতামূলক। যুক্তরাজ্যে Chartered Engineer (CEng) হতে হলে বহু বছরের অভিজ্ঞতা, দক্ষতা যাচাই এবং নৈতিকতার শর্ত পূরণ করতে হয়। অর্থাৎ, উন্নত বিশ্বে প্রকৌশলীরা শিক্ষা, অভিজ্ঞতা, নৈতিকতা এবং লাইসেন্স-এই চার ধাপ পেরিয়েই প্রকৌশলী পরিচয় পান। বাংলাদেশে এখনো এ ধরনের কাঠামো না থাকায় দ্বন্দ্ব ও দুর্নীতির সুযোগ তৈরি হয়েছে।
বাংলাদেশে স্নাতক প্রকৌশলীরা বলছেন, ডিপ্লোমাধারীরা কোটার মাধ্যমে তাদের পদ দখল করছে। এতে মেধাবী স্নাতকরা কর্মক্ষেত্রে বঞ্চিত হচ্ছেন। অন্যদিকে ডিপ্লোমাধারীরা মনে করেন, তারাও প্রকৌশলী পরিচয়ের অধিকারী এবং তাদের জন্য বাড়তি পদায়ন দরকার। ফলে উভয়পক্ষেই তীব্র রেষারেষি তৈরি হয়েছে, অথচ বাস্তবে দুই দলের কাজই পরিপূরক।
প্রশ্ন হচ্ছে-এই বিভাজন কাটিয়ে কীভাবে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনা যায়? বাংলাদেশে দুর্নীতিগ্রস্ত প্রকৌশলীর সংখ্যা কম নয়। কেউ কোটি টাকার বালিশ সরবরাহে অনিয়ম করেন, কেউ সেতু নির্মাণে খরচ ফুলিয়ে দেন। ডিগ্রিধারী হওয়া সত্ত্বেও তারা দেশের ক্ষতির কারণ হন। অন্যদিকে ইতিহাস বলে, অনেক মহৎ স্থাপনা—যেমন তাজমহল—গড়ে উঠেছিল এমন মানুষের হাতে, যাদের আধুনিক অর্থে ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রি ছিল না। তারা মেধা, সৃজনশীলতা ও নিষ্ঠার মাধ্যমে ইতিহাস সৃষ্টি করেছিলেন।
অতএব প্রশ্নটা ডিগ্রির নয়; প্রশ্নটা হচ্ছে নৈতিকতা, দায়বদ্ধতা ও দেশপ্রেমের। একজন মাঝারি মানের কিন্তু সৎ প্রকৌশলী দেশের জন্য অনেক বেশি মঙ্গলজনক, একজন উচ্চ ডিগ্রিধারী দুর্নীতিবাজ প্রকৌশলীর চেয়ে। প্রতিবছর হাজার হাজার বাংলাদেশি প্রকৌশলী ইউরোপ-আমেরিকায় পাড়ি দিচ্ছেন। বিদেশে কঠোর নিয়ম ও জবাবদিহির মধ্যেও তারা সফল হচ্ছেন, অথচ দেশে থাকলে দুর্নীতির জালে জড়িয়ে পড়তে হয় বা হতাশায় পেশা ছাড়তে হয়। এর ফলে বাংলাদেশে দক্ষ জনশক্তির সংকট তৈরি হচ্ছে, যা দীর্ঘমেয়াদে অর্থনীতি ও উন্নয়নের পথে বড় বাধা হয়ে দাঁড়াবে। এই সংকট থেকে উত্তরণের জন্য প্রথমত প্রকৌশলীদের জন্য লাইসেন্স ও নৈতিকতা কোড চালু করতে হবে। প্রকৌশলী হতে হলে শুধু ডিগ্রি নয়, পরীক্ষিত দক্ষতা ও নৈতিক মানদণ্ডে উত্তীর্ণ হতে হবে। লাইসেন্স ছাড়া কেউ ‘প্রকৌশলী’ পরিচয় ব্যবহার করতে পারবে না।
দ্বিতীয়ত স্নাতক প্রকৌশলী ও ডিপ্লোমাধারীদের জন্য আলাদা কিন্তু মর্যাদাপূর্ণ ক্যারিয়ার পথ তৈরি করতে হবে। এতে রেষারেষি কমবে, কাজের দক্ষতা বাড়বে। তৃতীয়ত প্রশাসনিক ক্যাডার দিয়ে প্রকৌশল সংস্থা চালালে পেশাগত সমস্যা সমাধান হয় না, তাই প্রকৌশলীদের নেতৃত্বে আলাদা ক্যাডার গড়ে তুলতে হবে। চতুর্থত ডিপ্লোমাধারীদের জন্য উচ্চশিক্ষার সেতুবন্ধন তৈরি করতে হবে-কারিগরি বোর্ডের আওতায় সমমান সনদ ও ক্রেডিট ট্রান্সফারের সুযোগ দিলে দক্ষ ডিপ্লোমাধারীরা চাইলে দ্রুত স্নাতক হতে পারবেন।
অবশেষে সবার জন্য নিয়মিত প্রশিক্ষণ বাধ্যতামূলক করতে হবে এবং দুর্নীতির দায়ে প্রকৌশলীদের লাইসেন্স বাতিলের ব্যবস্থা রাখতে হবে। বাংলাদেশে আজ প্রকৌশল খাত এক সড়কবাঁকে দাঁড়িয়ে। দ্বন্দ্ব, কোটা, দুর্নীতি আর মেধাপাচারের এই সংকট কাটাতে হলে আমাদের বুঝতে হবে-শুধু ডিগ্রি বা পদবী নয়, প্রকৌশলীর প্রকৃত পরিচয় হলো মেধা, সততা, দায়িত্বশীলতা ও দেশপ্রেম। যেদিন বাংলাদেশ প্রকৌশল পেশাকে আন্তর্জাতিক মানদণ্ডে দাঁড় করাতে পারবে, সেদিনই আমাদের উন্নয়ন টেকসই হবে।
রহমান মৃধা
গবেষক ও লেখক
(সাবেক পরিচালক, ফাইজার, সুইডেন)
Rahman.Mridha@gmail.com
মত দ্বিমত
বাংলাদেশের নির্বাচন: এক অদৃশ্য গণতন্ত্রের গল্প
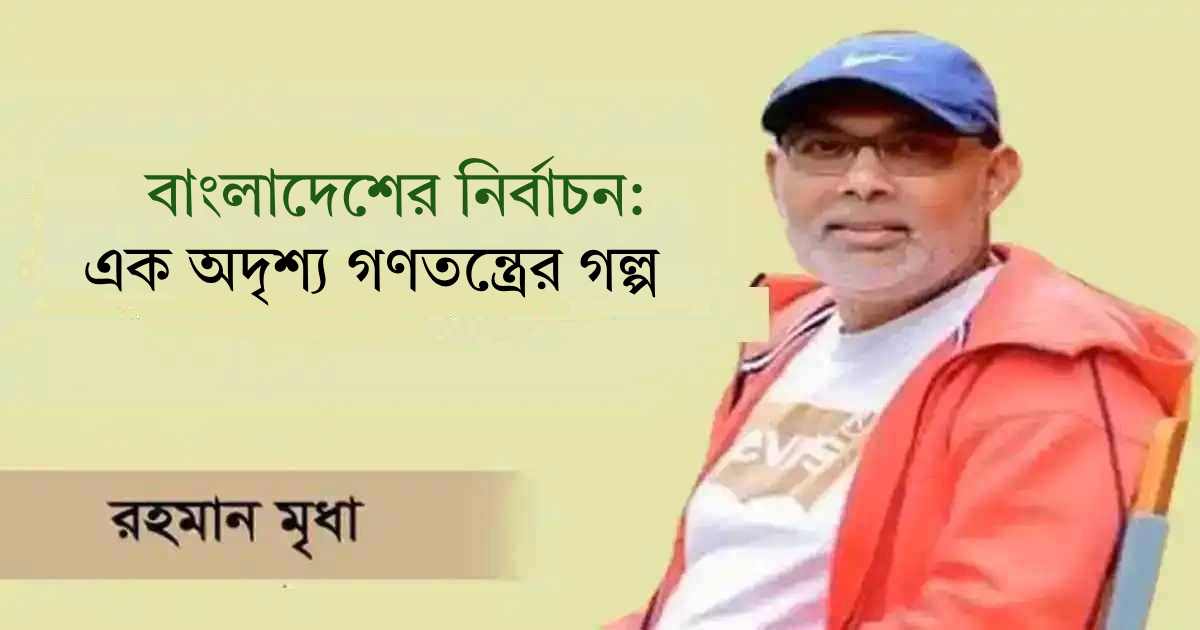
যেকোনো সময় নির্বাচনের দিন ঘোষণা হতে পারে, কিন্তু নির্বাচন বাস্তবে অনুষ্ঠিত হবে না। রাজধানীর রাস্তায় দিনভর মানুষ, যানবাহন আর সন্ত্রাসের আতঙ্ক যেন এক অদৃশ্য যুদ্ধের ময়দান তৈরি করেছে। যে দেশের রাষ্ট্রনীতি ভেজাল, দুর্নীতি ও স্বার্থপরতার মিশ্রণে ভরা, সেখানে প্রকৃত গণতন্ত্রের জন্ম অসম্ভব। রাজনৈতিক দলগুলো চাঁদাবাজি, ধান্দাবাজি এবং একে অপরকে নিপীড়নের ওপর দাঁড়িয়ে দৌড়ায়—এমন দেশে নির্বাচন সুষ্ঠু হবে বলে ধারণা রাখা অমূলক। দূরপরবাসী হলেও আমি নিয়মিত দেশের পরিস্থিতি খুঁটিয়ে যাচাই করছি, সংবাদ খুঁটিয়ে দেখছি, তাই বলতে বাধ্য হচ্ছি—এবারের নির্বাচন সঠিক সময়ে হচ্ছে না।
বর্তমান পরিস্থিতি স্পষ্ট করে দেখাচ্ছে, ড. ইউনূসকে দিয়ে হয়ত হুকুম চালানো হচ্ছে, পুলিশ বাহিনীকে দিয়ে দমন করা হচ্ছে এবং রাস্তায় চাঁদাবাজি ও সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের সুযোগ সৃষ্টি করা হচ্ছে। স্কুলফেরত যুবক থেকে রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকা বেকার—সবাই যেন সেই অন্ধকারের নৃশংস খেলার অংশ। রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে অরাজকতা ও অস্থিরতা বৃদ্ধি পাচ্ছে, আর নির্বাচনের পথ ক্রমশ বাধাগ্রস্ত হয়ে উঠছে।
ড. ইউনূস আশা করেছিলেন, নতুন প্রজন্ম শেখ হাসিনার সরকারের পতন ঘটিয়ে দেশের নেতৃত্ব নতুনভাবে গ্রহণ করতে পারবে। কিন্তু বাস্তবতা ভিন্ন—রাস্তায় নামা অধিকাংশ মানুষ ছিল টোকাই, যুবলীগ, যুবদল, শিবিরসহ দিনমজুরি; এরা জীবনকে ঝুঁকিতে ফেলে, গুলির আঘাতের ভয় উপেক্ষা করে লড়েছে। স্বৈরাচার সরকারের পতনের পর দেশের নেতৃত্ব এলিট সম্প্রদায়ের হাতে চলে গেছে—এভাবেই মূল সিদ্ধান্তগ্রহণ চলছে। নতুন দল গঠনের স্বপ্নের কর্মীরা এখন সীমিত সংখ্যক, তাদের শক্তি ও প্রভাব আগের মতো নেই। অন্যদিকে, তারেক জিয়ার যুবদলের সদস্যসংখ্যা দ্বিগুণ, কারণ এখানে যুবলীগও যোগ দিয়েছে। বিদেশে বসে গডফাদার হিসেবে তারেক জিয়া চাঁদাবাজি চালাচ্ছেন, কোনো প্রতিকূলতা ছাড়াই, আর দেশের রাজনৈতিক অঙ্গনে তার প্রভাব অদৃশ্যভাবে বিরাজ করছে।
তারেক জিয়ার বিরুদ্ধে গ্রেনেড হামলার মামলা ছিল মূল অভিযোগ। যদি এটি সত্য হয়, তাহলে আরও স্পষ্ট—তিনি সন্ত্রাসীর সঙ্গে সম্পৃক্ততা বজায় রেখে বিদেশে অবস্থান করার সময়ও সেই প্রভাব ধরে রেখেছেন এবং প্রবাস থেকে দেশের রাজনৈতিক লড়াই নিয়ন্ত্রণ করছেন। ড. ইউনূস লন্ডনে তার সঙ্গে দেখা করেছেন এবং রাজনৈতিক কৌশল ও পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা করেছেন। দেশে ফিরে, ড. ইউনূস একটি চাঞ্চল্যকর রাজনৈতিক রোডম্যাপ উপস্থাপন করেছেন। যদিও নির্বাচনের রোডম্যাপ নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে অরাজকতা সৃষ্টি হয়েছিল, নির্বাচনের সময় নির্ধারিত হওয়ার পরও বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের মধ্যে মতপার্থক্য ও দ্বন্দ্ব দেখা দিয়েছে। সম্ভবত এটাই মূল উদ্দেশ্য—দেশে আপাতত নির্বাচন হওয়া সম্ভব হচ্ছে না।
রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতার আভাস যখন ঘনীভূত হয়, তখন সবার দৃষ্টি চলে যায় সশস্ত্র বাহিনীর দিকে। তাদের মূল দায়িত্ব হলো দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষা করা, আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখা এবং সন্ত্রাস দমন করা। কিন্তু বাস্তবতার চাপ ও রাজনৈতিক খেলার মধ্যে তাদের ভূমিকা হয়ে ওঠে অপেক্ষমাণ, আর নির্বাচনী প্রক্রিয়ার ওপর তাদের প্রভাবও অনিশ্চিত। তারা কি কেবল সীমান্ত রক্ষা করবে, নাকি দেশের রাজনৈতিক অস্থিরতায় সক্রিয় হস্তক্ষেপ করবে—এই প্রশ্ন এখনও উন্মুক্ত, প্রতিটি মুহূর্তে পরিস্থিতি বদলে যেতে পারে।
অনেকে মনে করেন, ড. ইউনূস ইচ্ছাকৃতভাবে সময় নষ্ট করছেন। তিনি পুরনো জেনারেলদের অবসরের অপেক্ষা করছেন, যাতে নতুন নেতৃত্বের সঙ্গে সমন্বয় সহজ হয়। পাশাপাশি, তারেক জিয়ার গ্রেনেড হামলার মামলার গোপন তথ্য এবং রাজনৈতিক দরকষাকষির দিকে নজর রাখছেন। এভাবে, শর্তের ভিত্তিতে, তারেক জিয়ার রাজনৈতিক দুর্বলতাকে কাজে লাগিয়ে সম্ভবত তাকে নিরাপদভাবে দেশে ফেরার সুযোগ তৈরি করা হচ্ছে।
এদিকে, দেশের রাজনৈতিক ও সামাজিক অস্থিরতার সবচেয়ে বড় শিকার হচ্ছে যুবসমাজ। বেকারত্ব, শিক্ষার অভাব ও সামাজিক সুযোগের ঘাটতি অনেক যুবককে চাঁদাবাজি, সন্ত্রাস এবং অপরাধের পথে ঠেলে দিচ্ছে। বিশেষ করে যুবলীগ, যুবদলসহ যারা দিনমুজুরি করে বা রাস্তায় ঘুরে সহিংস রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে লিপ্ত, তারা শুধু রাজনৈতিকই নয়, সামাজিকভাবেও বিপর্যয় সৃষ্টি করছে। একদিকে স্কুলফেরত ছাত্র, অন্যদিকে রাস্তায় অস্ত্র হাতে—এই চরম দৃশ্য প্রতিদিন শহরকে আতঙ্কিত করছে, আর সাধারণ মানুষ যেন নিরস্ত্র অবস্থায় এই অরাজকতার সাক্ষী হয়ে দাঁড়াচ্ছে।
নিষিদ্ধ বা হিংসাত্মক রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড, অপকর্মকে রাজনৈতিকভাবে উৎসাহিত করা, এবং যুবসমাজকে কেবল অপরাধী হিসেবে আখ্যায়িত করা—এই সমস্ত প্রথা অবশ্যই বর্জনীয়। এগুলো রাষ্ট্র ও সমাজের জন্য ক্ষতিকর এবং গণতান্ত্রিক সংস্কারের পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়।
অন্যদিকে করণীয়গুলো স্পষ্ট। প্রথমে শিক্ষার ও কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি করতে হবে, যাতে যুবসমাজ জীবিকার সন্ধানে অপরাধে না জড়িয়ে পড়ে। নৈতিক ও নাগরিক শিক্ষা দিতে হবে, শৃঙ্খলা, গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ ও সামাজিক দায়বোধের সঙ্গে পরিচিত করতে হবে। রাজনৈতিক দলের স্বচ্ছতা ও নিয়ন্ত্রণ নিশ্চিত করা জরুরি—যুবরাজনীতিতে চাঁদাবাজি ও সহিংসতা সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ হতে হবে। সামাজিক পুনর্বাসন ও মেন্টরশিপের মাধ্যমে অপরাধে জড়িত যুবকদের পুনর্গঠন করা এবং তাদের ইতিবাচক দিকনির্দেশনা দেওয়া প্রয়োজন। পাশাপাশি মানসিক ও সামাজিক সহায়তা প্রদান করতে হবে, যাতে যুবকরা মানসিক চাপ ও বিভ্রান্তি থেকে বের হয়ে সচেতন ও সৎ পথে চলতে পারে।
সব মিলিয়ে দেখা যাচ্ছে, দেশের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে সশস্ত্র বাহিনী অপেক্ষমাণ, ড. ইউনূস সময়ক্ষেপণ করছেন, তারেক জিয়া আড়ালে গডফাদার হিসেবে সক্রিয়, যুবসমাজ বেকারত্ব ও অরাজকতায় আক্রান্ত, আর সাধারণ জনগণ অস্থিরতার বন্দি। বাংলাদেশের গণতন্ত্র এখনও ‘অদৃশ্য চুক্তি’ ও ‘গোপন আলোচনার’ ওপর নির্ভরশীল। রাষ্ট্র ভেজালে ভরা থাকলে নির্বাচন থেকে সংসদ পর্যন্ত খাঁটি গণতন্ত্রের জন্ম নেওয়া সম্ভব নয়।
ভবিষ্যতে গণতন্ত্রের পুনরুদ্ধার সম্ভব, তবে এর জন্য প্রয়োজন সশস্ত্র বাহিনীর নিরপেক্ষ ভূমিকা, নতুন নেতৃত্বের উত্থান যেখানে শিক্ষিত, নীতিনিষ্ঠ ও স্বার্থবিহীন প্রজন্ম দেশের নেতৃত্ব গ্রহণ করবে, আন্তর্জাতিক নজরদারি ও চাপের মাধ্যমে নির্বাচনের স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা, রাজনৈতিক সংস্কারের উদ্যোগ গ্রহণ করে দলগুলোকে পুনর্গঠন ও স্বচ্ছতা ও দায়িত্বশীলতা নিশ্চিত করা এবং যুবসমাজকে পুনঃনির্দেশনা, শিক্ষা, কর্মসংস্থান, নৈতিক শিক্ষা ও সামাজিক সুযোগের মাধ্যমে অপরাধ ও সহিংসতা থেকে দূরে রাখা। এই শর্তগুলো পূরণ হলে তবেই বাংলাদেশে খাঁটি গণতান্ত্রিক নির্বাচন ও স্থিতিশীল সমাজ প্রতিষ্ঠা সম্ভব হবে; নাহলে নির্বাচন ও রাজনৈতিক প্রক্রিয়া কেবল প্রতারণা ও অরাজকতার খেলা হয়ে থাকবে।
রহমান মৃধা, সাবেক পরিচালক, ফাইজার, সুইডেন। Rahman.Mridha@gmail.com
মত দ্বিমত
চাঁদাবাজির লাইসেন্স: বাংলাদেশের রাজনীতির কালো খোলস
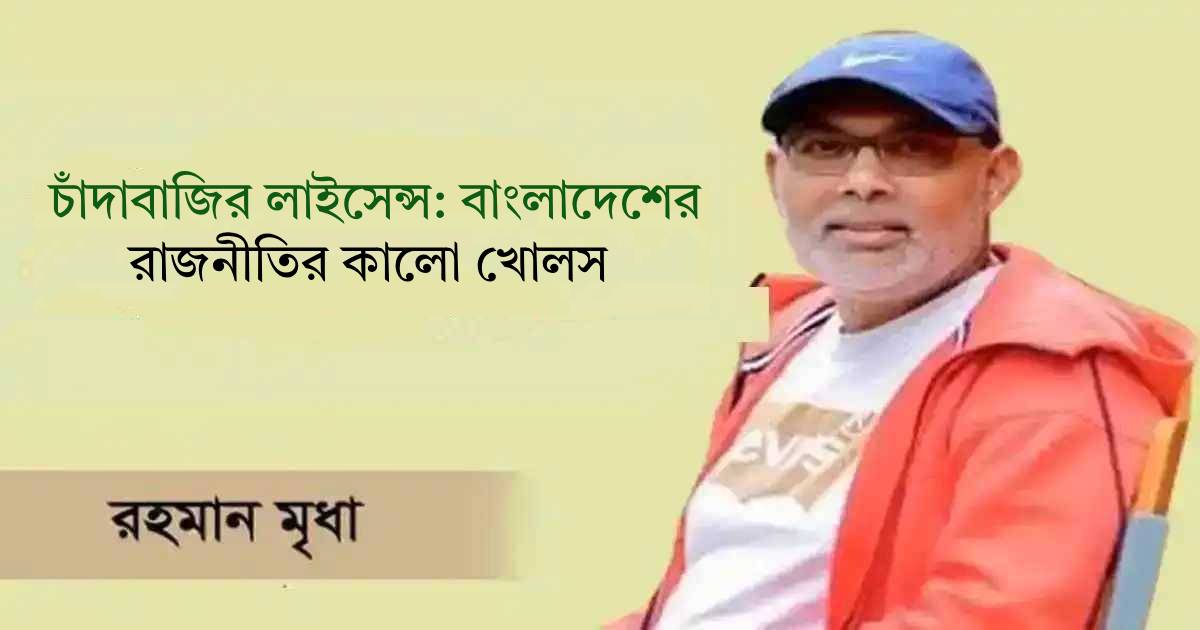
চাঁদাবাজি বাদ দিয়ে কাজ করুন, দেখবেন সংস্কার এমনিতেই হয়ে গেছে।
কেউ রাজনীতি করবে না বাংলাদেশে, যেদিন দেখবেন দুর্নীতি আর চাঁদাবাজি বন্ধ হয়ে গেছে। কিন্তু এই বন্ধ করার জন্য যে সংস্কার প্রয়োজন, সেটি হলো রাজনীতি অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত করা—মানে লাইসেন্স বাতিল করা। লাইসেন্সটা কী জানেন? রাজনীতি। সব চাঁদাবাজিই কোনো না কোনো রাজনৈতিক ছত্রছায়ায় জন্ম নেয়। তার মানে কি বুঝাতে পারলাম?
স্বপ্ন দেখছেন এবং আপনাকে স্বপ্ন দেখানো হচ্ছে—একজন দেশের বড় নেতা হবেন প্রধানমন্ত্রী। অথচ তিনি জীবনে কোনো কাজ করেননি! মানুষ হিসেবে তো আমাদের জন্ম হয়েছে কাজ করার জন্য। এখন যদি কাজ বলতে কেবল চাঁদাবাজির সংগঠন চালানো বোঝায়, তবে বন্ধ করে দেওয়া হোক সকল সৃজনশীল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, শিল্প প্রতিষ্ঠান এমনকি আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থাসহ দেশের প্রতিটি প্রতিষ্ঠান। বাংলাদেশ এগুলোর কিছুই ডিজার্ভ করে না।
আশ্চর্য লাগে, এআই প্রযুক্তির যুগেও বাংলাদেশে দিনদুপুরে চাঁদাবাজি হয়, আর প্রতিটি রাজনৈতিক লাইসেন্সধারী সংগঠন বিদ্যমান আইন অনুযায়ী চলতে থাকে—এর চেয়ে লজ্জার আর কী হতে পারে! এখন সবাই উঠে পড়ে লেগেছে পুরো দেশটিই যেন চাঁদাবাজদের নেত্রাধীন হয়ে যায়। আর সেই গুরুত্বপূর্ণ কাজটি সম্পন্ন করার দায়িত্ব যাকে দেওয়া হয়েছে, তিনি আর কেউ নন—তিনি হচ্ছেন নোবেল বিজয়ী প্রফেসর ড. মুহাম্মদ ইউনূস। ভাবতেই গা শিউরে ওঠে!
কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে—কোথায় থামবে এই দুর্নীতি ও চাঁদাবাজির মহোৎসব? মানুষ কি সত্যিই রাজনীতি ছাড়া চলতে পারবে না? উত্তর হচ্ছে, পারবেই। শর্ত হচ্ছে, রাজনৈতিক লাইসেন্স বাতিল করে দেশের প্রতিটি প্রতিষ্ঠানকে জনগণের সেবার জন্য খাঁটি পেশাগত নীতির ভিত্তিতে পুনর্গঠন করতে হবে। তখনই বোঝা যাবে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কীভাবে আলোকিত মানুষ গড়তে পারে, শিল্প প্রতিষ্ঠান কীভাবে নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি করতে পারে, এবং আইনশৃঙ্খলা বাহিনী কীভাবে সত্যিকারের ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করতে পারে।
আমরা ভুলে গেছি—রাষ্ট্র হলো মানুষের জন্য, মানুষের শ্রম ও মেধার বিকাশের জন্য। অথচ এখানে রাষ্ট্র যেন কেবল একদল লুটেরার সম্পত্তি। প্রতিটি রাস্তায়, প্রতিটি বাজারে, প্রতিটি প্রশাসনিক দপ্তরে দেখা যায় চাঁদাবাজির অশুভ ছায়া। যে ছায়ার কারণে এক কৃষক তার ফসলের দাম পায় না, এক শিক্ষক তার প্রাপ্য সম্মান পায় না, এক যুবক তার স্বপ্ন পূরণের সুযোগ পায় না।
তাহলে পথ কী? পথ একটাই—রাজনীতির নামে চাঁদাবাজির বাজার বন্ধ করতে হবে। রাষ্ট্রকে এমন এক নতুন সামাজিক চুক্তির পথে হাঁটতে হবে যেখানে নাগরিকের কাজই হবে রাজনীতি, কিন্তু সেটা হবে কর্ম ও সৃজনশীলতার রাজনীতি। যেখানে ভোট মানে দলবাজি নয়, বরং কাজের হিসাব। যেখানে নেতা মানে ক্ষমতার আসনে বসা ব্যক্তি নয়, বরং সেবার মানদণ্ডে দাঁড়ানো একজন প্রকৃত মানুষ।
যদি এই সংস্কার না হয়, তবে বাংলাদেশ কখনোই দুর্নীতি ও চাঁদাবাজির কালো খোলস ভেদ করতে পারবে না। আমরা কেবল এক প্রজন্ম থেকে আরেক প্রজন্মের হাতে হস্তান্তর করব হতাশা, ব্যর্থতা আর অচল রাজনীতির অভিশাপ।
কিন্তু যদি হই আমরা দৃঢ়, যদি সত্যিই চাই পরিবর্তন—তাহলে নতুন প্রজন্মকেই নেতৃত্ব নিতে হবে। রাজনীতির লাইসেন্স বাতিল করে নাগরিক সমাজকে করতে হবে জবাবদিহির আসল শক্তি। তখনই চাঁদাবাজি থামবে, দুর্নীতি ভাঙবে, এবং বাংলাদেশ তার প্রকৃত সম্ভাবনায় উন্মোচিত হবে।
অন্যথায়, একদিন মানুষ বলবে— “বাংলাদেশ ছিল এক সম্ভাবনার দেশ, কিন্তু তার সম্ভাবনা শেষ করে দিয়েছে রাজনীতির নামে চাঁদাবাজির লাইসেন্স।”
রহমান মৃধা, সাবেক পরিচালক, ফাইজার, সুইডেন। Rahman.Mridha@gmail.com
মত দ্বিমত
সামান্য কিছু বালু আমেরিকা থেকে আনতে দিলো না, অথচ…
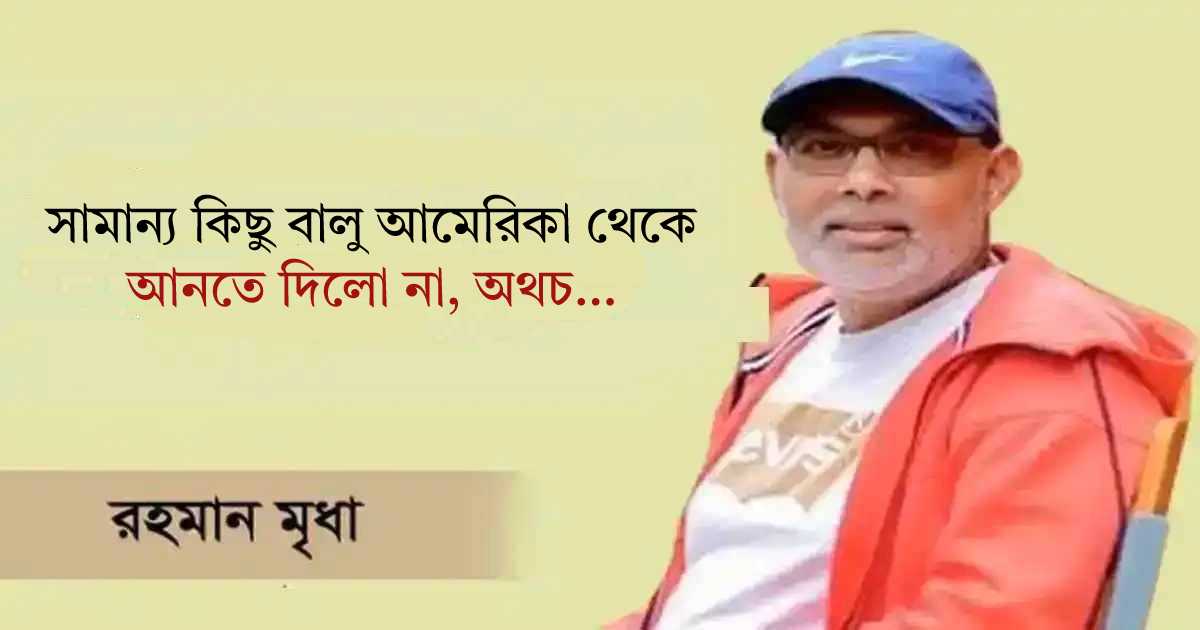
সামারে সুইডেনে পাকিস্তানি আম পাওয়া যায়, খেতেও বেশ ভালো। ছোটবেলায় বাংলাদেশে গ্রামেই বেশি সময় কেটেছে। আম, জাম, লিচু, কাঠাল, খেজুরের রস—এসব ছিলো সেই বেহেস্তের খাবারের মতো, যাকে বলে অমৃত। তো বহু বছর দেশের বাইরে থাকতে থাকতে দই-এর সাধ ঘোলে মেটাতে হয় মাঝেমধ্যে। যার ফলে সামারে আমদুধ দিয়ে মুড়ি খাওয়ার সাধ জাগে। আম যেমনই হোক, তা মেলে, তবে সেই মুড়ি কোথায়? শেষে স্টকহোমের একটি বাংলাদেশি দোকান থেকে মুড়ি কিনলাম। ওমা! মুড়ি তেলে ভেজেছে, কেমন একটা বিশ্রী গন্ধ! মেজাজটাই খারাপ হয়ে গেল। দোকানে গিয়ে বিষয়টি বলতেই ভদ্রলোক বললেন, “বাংলাদেশ থেকে এগুলোই আসে।” আমি শুধু বললাম—ঘটনা কী? শাকসবজি, মাছ-ফলে ফরমালিন, মুড়িতে তেলের গন্ধ, মসলায় ইটের গুঁড়া—এসব সাত সমুদ্র তের নদী পার হয়ে কীভাবে এলো? ভদ্রলোক হেসে বললেন, “যেভাবে আমরা এসেছি ভাই।” আমার আর বলার কিছু ছিল না।
পরে বেশ কয়েক বছর কেটে গেছে। সম্ভবত ১৯৯৬ সালের দিকে ছুটিতে গিয়েছিলাম ক্যালিফোর্নিয়ার লস এঞ্জেলসে। সাগরের বালু এত পরিষ্কার এবং সাদা দেখে মনে পড়ে গেলো ছোটবেলার কথা। মাকে দেখেছি পরিষ্কার বালু গরম করে চাল দিয়ে মুড়ি ভাজতে। ভাবলাম, কিছু বালু সুইডেনে নিয়ে যাবো। যে ভাবনা, সেই কাজ। ব্যাগ ভরে কয়েক কেজি বালু নিয়ে লস এঞ্জেলস বিমানবন্দরে হাজির। চলছে চেকিং—নানা ধরনের প্রশ্ন: ব্যাগে কী আছে, কে প্যাক করেছে, অস্ত্রপাতি আছে কি না ইত্যাদি। ব্যাগের ওজন একটু বেশি হয়ে গেছে। কিছু ওজন কমাতে হবে অথবা অতিরিক্ত চার্জ দিতে হবে।
আমি ডেস্কে জিঙ্গেস করলাম, “কত?”
উত্তরে বলল, “২০০ ডলার।”
ভাবলাম, তাহলে কিছু বালু রেখে যাই। একটু সাইডে গিয়ে বালু ঢালছি আরেকটি পলিথিনের ব্যাগে। হঠাৎ পুলিশ এসে হাজির। তারা জিজ্ঞেস করল, “এটা কী? কোথা থেকে এলো?” আমি সব বললাম। পুলিশ তো হতবাক! বলল, “জীবনে অনেক কিছু চোরাচালান হতে দেখেছি, কিন্তু বালু চোরাচালান এই প্রথম। তবে কী নিয়মকানুন আছে, সেটা জানা নেই। তোমাকে অপেক্ষা করতে হবে, তদন্ত করতে হবে।”
আমি বললাম, “আরে ভাই, এটা খাঁটি বালি, কোনো ভেজাল নেই। আমি নিজে হাতে সাগর থেকে তুলেছি।”
পুলিশ বলল, “তবুও পরীক্ষা করতে হবে। অন্য কিছু এর সঙ্গে জড়িত আছে কিনা তা জানতে হবে। রাষ্ট্রের প্রাকৃতিক সম্পদ পাচার—এটা তদন্তের বিষয়।”
আমি তো হঠাৎ অবাক! ঘাম ছুটে গেল শরীরে। এ যেন মহাবিপদ! এদিকে প্লেন ছেড়ে দেবে, ফ্লাইট মিস হবে, সাথে বালু চোরের খেতাব, জেল-জরিমানা—আর কত কী! আমি আছি আমার রাজ্যে—কে কী বলবে, কী হবে না হবে এসব নিয়ে। এরমধ্যে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ এল। হঠাৎ কোনো যান্ত্রিক সমস্যার কারণে প্লেন এক ঘণ্টা দেরিতে ছাড়বে—এটাও কেউ এসে জানিয়ে গেল। একটু স্বস্তি পেলাম, কিন্তু আমার কী হবে সেটা নিয়ে ভাবছি।
কর্তৃপক্ষের সাথে বেশ কিছুক্ষণ কথা হলো। আমার পরিচয়সহ সব ঘটনা জানার পর বিষয়টি বুঝতে পেরে আমাকে ছেড়ে দিলো, তবে বালু রেখে দিল। শুধু বললো, রাষ্ট্রের সম্পদ এভাবে নেওয়া উচিত নয়। যদিও বালুর বিষয়ে প্লেনে ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য নির্দিষ্ট কোনো নির্দেশনা নেই, তবুও নিতে পারবে না। আমি মনে মনে ভাবলাম—তুই তোর বালু নে, আমার আর মুড়ি ভাজার শখ নেই। বালু রেখে চলে এলাম।
ঘটনাটি পরে সুইডেনে এসে আলোচনা করেছি, কিন্তু বিষয়টি নিয়ে আর ভাবিনি। যদিও সেদিন লস এঞ্জেলস বিমানবন্দরে আমার বারোটা বাজতে গিয়েছিল, ভাগ্যিস মানসিক চাপ, শ্বাসকষ্ট আর ঘাম ছাড়া অন্য কোনো বিপদ হয়নি। তবে আমদুধ দিয়ে মুড়ি খাওয়ার শখ সেদিন লস এঞ্জেলসের বিমানবন্দরে রেখে এসেছি।
ভেজাল খাবার এড়াতে এবং দেশি খাবারের টান মেটাতে আমি এখানে নিজের মতো কৃষিপণ্য উৎপাদন করি। তবে আম আর ধান এখনও উৎপাদন সম্ভব হয়নি। সময়-সুযোগ হলে চেষ্টা করবো, ইনশাআল্লাহ। আজ হঠাৎ বাংলাদেশের প্রাকৃতিক সম্পদ—পাথর উত্তোলন আর সেগুলো রাতারাতি শেষ হয়ে যাওয়ার খবর পড়ে সেই দিনের ঘটনার কথা মনে পড়ে গেল। মনে হলো, বেচারা দেশবাসীর হয়তো ঘর-দুয়ার সাজানোর শখ হয়েছিল পাথর দিয়ে—যেমনটি আমার হয়েছিল বালু দিয়ে মুড়ি ভাজার। প্রকৃতির সম্পদ লুট করে যেমন দেশ ফাঁকা হয়, তেমনি ভেজাল খাবারে মানুষের মনও শূন্য হয়ে যায়।
রহমান মৃধা
গবেষক ও লেখক
সাবেক পরিচালক, ফাইজার, সুইডেন
Rahman.Mridha@gmail.com



























