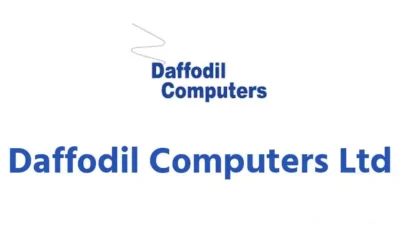মত দ্বিমত
জিয়ার উত্তরাধিকার: এক জাতির দ্বন্দ্বপূর্ণ প্রতিবিম্ব
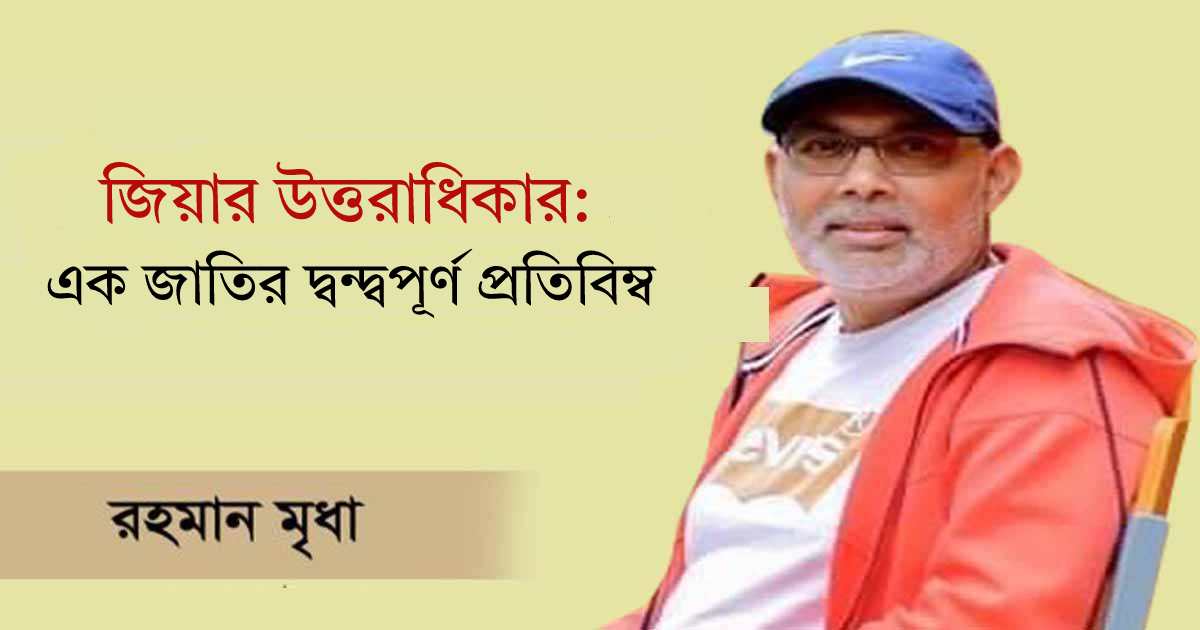
বাংলাদেশের ইতিহাসে এমন কিছু নাম আছে যাদের অবদান ও বিতর্ক একই ছায়ার নিচে বিরাজমান। মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান এমন এক চরিত্র। তিনি শুধু মুক্তিযুদ্ধের সাহসী নেতা ছিলেন না, একজন অপরাজেয় সামরিক কমান্ডার ও কার্যকর প্রশাসক হিসেবেও দেশকে গড়ার পথে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন। তবে তার নেতৃত্ব ছিল শক্তিশালী রাষ্ট্র পরিচালনার প্রতীক, পাশাপাশি ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণ, মতপ্রকাশের সীমাবদ্ধতা ও দলীয় রাজনীতিরও প্রতীক। এই নিবন্ধে তার ব্যক্তিগত ও রাজনৈতিক জীবন মূল্যায়ন করবো এবং আমার স্মৃতিতে একটি মানবিক রাষ্ট্রনায়কের প্রতিচ্ছবি ফুটিয়ে তুলবো।
১৯৭১ সালের ২৭ মার্চ, চট্টগ্রামের কালুরঘাট রেডিও স্টেশনে মেজর জিয়াউর রহমান বাংলাদেশের পক্ষে স্বাধীনতার ঘোষণা দেন। এটি শুধু সামরিক ঘোষণা ছিল না, এটি এক অসাধারণ নেতৃত্বের উন্মেষের প্রতীক ছিল। তখনকার শেখ মুজিবুর রহমানের গ্রেফতার পর নেতৃত্বহীন সময়ে জিয়ার এই ঘোষণা সাহস, দিশা ও কৌশলগত বার্তা হিসেবে কাজ করেছিল। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে মুক্তিযুদ্ধের গতিবেগ বাড়াতে এটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিল।
মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন তিনি সেক্টর ২ এর কমান্ডার হিসেবে নেতৃত্ব দিয়েছেন এবং পরে জি ফোর্স গঠন করে গেরিলা যুদ্ধ পরিচালনায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। তার নেতৃত্ব শুধু সামরিক সফলতা নয়, একটি আদর্শিক সংকল্পের প্রকাশ ছিল। ‘বীর উত্তম’ খেতাবে ভূষিত একমাত্র কমিশন্ড অফিসার হিসেবে তার অবদান ঐতিহাসিক স্বীকৃতি পেয়েছে। এই সময়ে তিনি পেশাদার সৈন্য থেকে আদর্শবাদী স্বাধীনতাকামী নেতা হয়ে উঠেছিলেন— যার সিদ্ধান্ত, শৃঙ্খলা ও দৃঢ়তা যুদ্ধের বিজয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিল।
১৯৭৫ সালের রাজনৈতিক সংকট ও নেতৃত্ব শূন্যতায় জিয়াউর রহমান সেনাবাহিনীর প্রধান হিসেবে ক্ষমতায় এসেছিলেন। প্রথমদিকে সামরিক শৃঙ্খলা ও প্রশাসনিক কঠোরতা ছিল সরকারের মূল ভিত্তি। কিন্তু তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, দীর্ঘমেয়াদী রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য সামরিক নীতির চেয়েও বেশি কিছু দরকার। তাই তিনি ‘বাংলাদেশি জাতীয়তা’, ‘উৎপাদনমুখী অর্থনীতি’ এবং ‘সেবামূলক প্রশাসন’ ধারণা প্রবর্তন করেন। কৃষি বিপ্লব, খাল খনন, গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন, ইসলামী অনুভূতিকে শ্রদ্ধা এবং আন্তর্জাতিক সম্পর্কের সামঞ্জস্য স্থাপন তার কার্যকর রাষ্ট্রনায়কের পরিচয় বহন করেছিল।
তবে এই সাফল্যের আড়ালে কিছু সীমাবদ্ধতা ও বিতর্কও লুকিয়ে ছিল। বিশেষ করে ১৯৭৭ সালের বিমান বাহিনী বিদ্রোহ দমন, যেখানে প্রায় একশত পনের জনেরও বেশি সদস্যকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছিল, তা মানবাধিকার লঙ্ঘনের গুরুতর অভিযোগের শিকার হয়। মতপ্রকাশের স্বাধীনতা ক্ষুণ্ন হয় এবং গণমাধ্যম নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে গণতান্ত্রিক অধিকার হ্রাস পায়। একই সঙ্গে, সেনাবাহিনী সমর্থিত বিএনপি গঠনের মাধ্যমে শাসন ব্যবস্থা গণতান্ত্রিক পরিবর্তনের পথে থেকে সরে যায়।
১৯৭৫ থেকে ১৯৮১ সালের মধ্যে প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের শাসনামলে দেশে রাজনৈতিক দমন-পীড়ন, বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড এবং সামরিক অভ্যুত্থানের ছায়া প্রকট ছিল। এই সময়কাল ব্যাপক মানবাধিকার লঙ্ঘন ও রাষ্ট্রীয় নির্যাতনের জন্য স্মরণীয়।
১৯৭৭ সালের বিমান বাহিনী অভ্যুত্থানের পর প্রায় এক হাজার সদস্যকে গ্রেপ্তার করা হয় এবং গোপন সামরিক ট্রাইব্যুনালের মাধ্যমে শতাধিককে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়। অনেকের অবস্থান পরিবার-পরিজন পর্যন্ত অজানা ছিল। Amnesty International ও Asia Watch-এর রিপোর্টে এই বিচারগুলোকে ‘নির্যাতনমূলক ও অস্বচ্ছ’ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে।
রাষ্ট্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা যেমন DGFI ও NSI বিরোধী রাজনৈতিক দল, ছাত্র সংগঠন এবং মুক্তিযুদ্ধপন্থী সেনা কর্মকর্তাদের ওপর নজরদারি ও নির্যাতন চালিয়েছিল। সাবেক সেনা কর্মকর্তা মেজর জলিল, কর্নেল আবু তাহের ও ক্যাপ্টেন হকসহ অনেক মুক্তিযোদ্ধার বিরুদ্ধে নির্মম নির্যাতনের অভিযোগ ছিল। কর্নেল আবু তাহেরকে একটি গোপন সামরিক ট্রাইব্যুনালে বিচার করে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়, যাকে অনেকে ‘বিচারবহির্ভূত’ ও ‘প্রহসন’ মনে করেন।
এই সময়কালে গোপনীয়তার ছায়ায় গণতান্ত্রিক বিরোধীদের গুম, শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন, পরিবারকে হয়রানি এবং আতঙ্ক সৃষ্টি করা হয়েছিল। নির্যাতন ও দমন-পীড়নের এই কৌশল রাষ্ট্র ক্ষমতা ধরে রাখার জন্য ব্যবহার করা হয়েছিল।
জিয়াউর রহমানের শাসনামলে রাজনৈতিক পুনর্গঠন ও স্থিতিশীলতার আড়ালে এই কালো অধ্যায় মানবাধিকার লঙ্ঘন এবং বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের জন্য স্মরণীয় হয়ে আছে। মুক্তিযোদ্ধা ও বামপন্থী গোষ্ঠীগুলো সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। ইতিহাস বলে দেয়, একাধারে ক্ষমতা কেবল শক্তি নয়, ন্যায় ও মানবিকতা থেকেও বিচ্যুত হলে রাষ্ট্র দুর্বল ও অমানবিক হয়ে ওঠে।
সত্যকে স্বীকার করা জরুরি—যে জিয়াউর রহমান, মুজিব, এরশাদ,খালেদা জিয়া ও শেখ হাসিনা প্রত্যেকেই এক ধরনের ক্ষমতার খেলা খেলেছেন। ভবিষ্যতের নেতৃবৃন্দও এই একই ভুলের পুনরাবৃত্তি করবে—যা দুঃখজনক, কিন্তু এ থেকেই আমরা শিক্ষা নিতে পারি।
জিয়ার মৃত্যুর পর বিএনপি সংগঠনগতভাবে শক্তিশালী হলেও আদর্শগতভাবে দুর্বল হয়ে পড়ে। পারিবারিক ক্ষমতার ধারাবাহিকতা, নৈতিকতা বিহীন ক্ষমতার লড়াই, বিদেশি প্রভাব পার্টির অবস্থান জটিল করে তোলে। জিয়ার প্রতিষ্ঠিত ‘উৎপাদনমুখী গণতন্ত্র’ ও ‘জনকেন্দ্রিক উন্নয়ন’ শাসনের ভিত্তি দুর্নীতি, গোষ্ঠী দ্বন্দ্ব ও রাজনৈতিক সহিংসতায় দুর্বল হয়ে যায়। আজকের বিএনপি তার আদর্শ ও মানবিক রাষ্ট্রনায়কত্ব থেকে অনেক দূরে।
জিয়াউর রহমান ছিলেন কঠোর বাস্তববাদী। তিনি সামরিক শৃঙ্খলা, প্রশাসনিক দক্ষতা ও কূটনৈতিক সামঞ্জস্যের মাধ্যমে স্থিতিশীলতা ফিরিয়ে এনেছিলেন। তবে পূর্ণ গণতন্ত্রের স্বপ্ন তিনি পূরণ করতে পারেননি, আর তার দল তা আরও দুর্বল করেছে। ইতিহাস তাকে ‘বিবাদময় রাষ্ট্রনায়ক’ হিসেবে দেখছে— একদিকে সফল নেতা, অন্যদিকে ক্ষমতার রাজনীতির স্থপতি।
১৯৮০ সালে একদিন জিয়াউর রহমান হেলিকপ্টারে করে মাগুরার নবগঙ্গা নদীর তীরে বাটাজর নামক এক অজানাগাঁওয় পৌঁছান। সেখানে খাল খনন ও গ্রামের স্থানীয় প্রশাসনের অবস্থা নিজ চোখে দেখতে এসেছিলেন তিনি। সেই সময় আমি এক দুরন্ত কিশোর ছিলাম, এবং সেই মুহূর্তে প্রেসিডেন্টকে সরাসরি দেখার সৌভাগ্য হয়েছিল— শুধুমাত্র শীর্ষ নেতাই নয়, এক মানবিক মানুষ হিসেবে যার উপস্থিতি স্মৃতিতে গভীর দাগ কেটেছে।
আজও মনে পড়ে সেই দৃশ্য— জনগণের সমাবেশ, হেলিকপ্টার ছেড়ে হাঁটাহাঁটি করে সাত মাইল পথ পাড়ি দেওয়া, গ্রামের মানুষের সাথে আন্তরিক আলাপ। রাষ্ট্রনায়ক হলেও তিনি সহজ ও মানবিক ছিলেন। আমি ব্যক্তিগতভাবে দেখেছি কিভাবে একজন মানুষ অন্যের কষ্ট বুঝতে, শ্রদ্ধা করতে এবং ভালোবাসতে পারে।
সর্বোপরি, শত্রুজিতপুর স্কুলে তিনি বলেছিলেন, “আমি কিছু খাবো না, শুধু লেবুর শরবত চাই।” এটি ছিল একটি অনন্য বার্তা— সর্বোচ্চ ক্ষমতার মাঝেও আত্মসংযম হলো নেতার মৌলিক গুণ, যা জিয়া বহন করতেন।
তার অপ্রত্যাশিত মৃত্যু আমাকে স্তব্ধ করেছিল। আজও মনে হয়, সেদিনের সেই রে-ব্যান পাইলট চশমা পরা মানুষটি শুধু প্রেসিডেন্ট নয়, এক মানবিক ভ্রমণকারী ছিলেন।
জিয়াউর রহমান বাংলাদেশের রাজনৈতিক নেতৃত্বের দ্বৈত চরিত্রের প্রতীক— একদিকে সাহসী মুক্তিযোদ্ধা ও প্রগতিশীল রাষ্ট্রনায়ক, অন্যদিকে ক্ষমতা কেন্দ্রীকরণ ও দলীয় রাজনীতির স্থপতি। তিনি শৃঙ্খলাবদ্ধ সামরিক মনোভাব, প্রশাসনিক বাস্তববাদ ও উন্নয়ন চিন্তাকে মিলিয়েছিলেন।
কিন্তু মৃত্যুর পর তার প্রতিষ্ঠিত রাজনৈতিক দল তার রাষ্ট্রনায়কত্বের ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে পারেনি। আদর্শের পরিবর্তে এসেছে পারিবারিক কর্তৃত্ব, জনগণের উন্নয়নের পরিবর্তে রাজনৈতিক পেশাদারিত্ব, স্বাধীন কূটনীতি বাদ দিয়ে বিদেশি নির্ভরতা।
আজকের বাংলাদেশ যখন রাজনৈতিক অস্থিরতা, দুর্নীতি ও আদর্শ সংকটে আছে, জিয়ার ‘দুর্নীতিমুক্ত প্রশাসন,’ ‘জনকেন্দ্রিক উন্নয়ন’ ও ‘আন্তর্জাতিক সামঞ্জস্য’ নীতিগুলো শুধুমাত্র প্রাসঙ্গিক নয়, দেশের পুনর্গঠনের জন্য অপরিহার্য।
স্মৃতির পটে, সুদূর সুইডেনের এর এক গ্রামে নির্জন জীবন যাপন করার সময় হঠাৎ করেই বাংলাদেশের সেই উজ্জ্বল দিনগুলো মনে পড়ে, যখন আমি জিয়াউর রহমানের পাশে হেসেছি। তার চোখে ছিল দেশের জন্য অদম্য ভালোবাসা, যা আজও আমার অন্তরে আলোর শিখা জ্বালায়। প্রতিটি কুয়াশাচ্ছন্ন সকালের শুরুতে সেই স্মৃতি ফিরে আসে— এক মানুষের, যিনি প্রেসিডেন্ট হলেও আমাদেরই একজন ছিলেন: সাধারণ এবং সংবেদনশীল।
এই বিদেশী মাটিতে আমি যখন শাকসবজি চাষ করি, সেখানে লুকিয়ে থাকে ছোট্ট একটা বাংলাদেশ— সেই বাংলাদেশ যা তিনি গড়তে চেয়েছিলেন। সমালোচনার পরেও তিনি আমার স্মৃতিতে জীবন্ত একজন রাষ্ট্রনায়ক, মানবিক, দূরদর্শী ও অনড়।
জিয়াউর রহমান শুধু আমার কাছে একজন সাবেক নেতা নয়, এক পথিকৃৎ যার আদর্শ, ত্যাগ ও দেশপ্রেম আজও হৃদয়ে জ্বলছে। আমি আশা করি তার পরিবার সেই মহান চেতনা ধরে রাখবে ও আগামী প্রজন্মের কাছে পৌঁছে দেবে— তখনই তার স্বপ্ন সত্যিই বাঁচবে। হয়তো একদিন, এই নির্বাসিত জীবনে আমি নতুন প্রজন্মের চোখে সেই আলো দেখতে পাব যা একদিন জিয়ার চোখে দেখেছিলাম। এই স্মৃতির মাঝে আমি নিজেকেই খুঁজে পাই— ইতিহাসে সংরক্ষিত রাষ্ট্রনায়কদের পাশে নিঃশব্দ এক সঙ্গী হিসেবে।
রহমান মৃধা, গবেষক ও লেখক
(সাবেক পরিচালক, ফাইজার, সুইডেন)
Rahman.Mridha@gmail.com
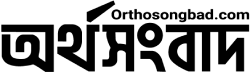
মত দ্বিমত
জুলাই এসেছে ফিরে- সতর্কবার্তা নিয়ে
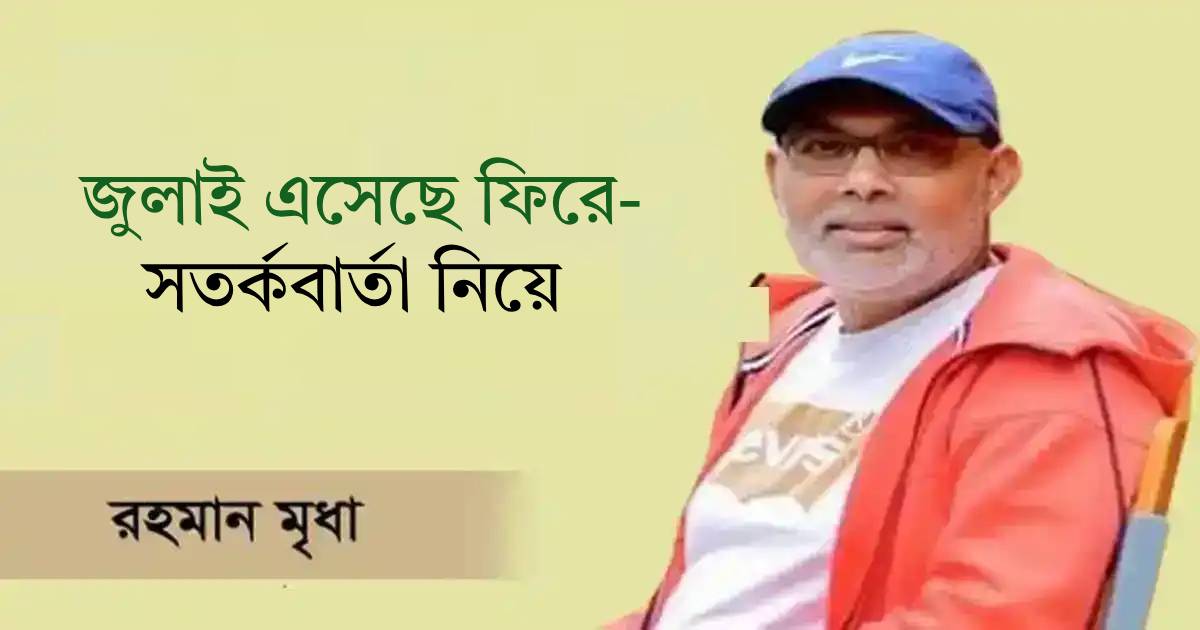
সব মাস দিন গুনে চলে, কিন্তু কিছু মাস জাতির বুক চিরে রেখে যায় রক্তের দাগ। জুলাই এখন তেমনই এক মাস—যেখানে কাগজে লেখা তারিখ নয়, বরং খোদাই করা এক জাতিগত জাগরণের স্মারক। যে মাসে রাষ্ট্র তার সন্তানদের দিকে বন্দুক তাক করেছিল, আর সেই গুলির প্রতিধ্বনি পৌঁছে গিয়েছিল প্রবাসের আকাশেও— প্রমাণ করে দিয়েছিল, আমরা কেবল দেশে নয়, হৃদয়ে দেশ বয়ে চলি।
আমাদের ইতিহাসে এমন কিছু মাস আছে, যেগুলো কেবল স্মৃতির নয়—চেতনার দীপ্ত আলোকস্তম্ভ হয়ে জ্বলতে থাকে অনন্তকাল। ২১ ফেব্রুয়ারি আমাদের ভাষার অহংকার, ২৬ মার্চ স্বাধীনতার অগ্নিপরীক্ষা, ১৬ ডিসেম্বর বিজয়ের সূর্যোদয়, আর ১৫ আগস্ট ইতিহাসের সবচেয়ে যন্ত্রণাবিদ্ধ শোকরেখা। এবার সেই চিরস্মরণীয় দিনের পাশে স্থায়ীভাবে জুড়ে বসেছে আরেকটি মাস—জুলাই।
২০২৪ সালের জুলাই। এক রক্তাক্ত বিবেক-জাগরণের মাস। এই মাসটিকে আমরা আর কোনোদিন ভুলে যেতে পারি না। ভুলে গেলে ইতিহাস আমাদের ক্ষমা করবে না—বরং সেই ইতিহাসই একদিন আমাদের প্রতিটি সন্তানকে আবার রক্তাক্ত করে তুলবে।
জুলাই মাসের এক বিকেলে রাষ্ট্রের হাতে কিশোরদের বুক বিদীর্ণ হয়ে যায়। তাদের ন্যায্য প্রশ্ন ছিল—চাকরির কোটা সংস্কার। তার জবাবে এসেছিল রাষ্ট্রের সর্বগ্রাসী প্রতিশোধ—অর্থ, অস্ত্র, ও পোষা বাহিনীর সম্মিলিত আগ্রাসন। জনগণের করের টাকায় যারা তৈরি হয়েছে জনগণের রক্ষক হিসেবে—তারা সেদিন রূপ নিয়েছিল এক ভয়ঙ্কর দানবে। পুলিশ, র্যাব, বিজিবি, গোয়েন্দা বাহিনী, এমনকি সেনাবাহিনী পর্যন্ত নামিয়ে এনেছিল এই রাষ্ট্র, যেন জনগণ নয়, যুদ্ধ করছে কোনো দখলদার শক্তির বিরুদ্ধে।
সাদা পোশাকে হত্যা, কালো পোশাকে নিধন, আর ছদ্মবেশে চালানো হয় গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে এক নগ্ন অভিযান। ছাত্র, তরুণ, পথচারী—কারো বুকে গুলি থেমে থাকেনি। হেলিকপ্টার থেকেও গুলি চালানো হয়েছিল, যেন কেউ পালাতে না পারে, কেউ রক্ষা না পায়। এই হামলা কেবল শারীরিক ছিল না—এটা ছিল রাষ্ট্রের তরফে নিজের নাগরিকদের বিরুদ্ধে এক প্রতীকী যুদ্ধ। রাস্তা, অলিগলি, ফুটপাত, ও হাসপাতালের করিডোর—সবখানে লাশ। রক্ত। কান্না। অসহায়তা।
আর সেই নিথর শরীরগুলো রেখে গেছে একটাই প্রশ্ন: ‘আমাদের সন্তানদের গুলি করার অধিকার কে দিল তোমাদের?’ হাসপাতালের বারান্দায় তরুণদের রক্তে ভিজে যাওয়া কাপড়। দেশজুড়ে ইন্টারনেট বন্ধ, মোবাইল ফোন বন্ধ, পরিবার-পরিবার বিচ্ছিন্ন। কেউ কথা বলতে পারে না, কেউ ছবি পাঠাতে পারে না। তবু রক্ত থামে না। ছাত্র, কিশোর, সাধারণ মানুষ—সবাই তখন অন্ধকারে। এই অন্ধকার কেবল বিদ্যুতহীনতা নয়, এটা ছিল রাষ্ট্রীয় নিষ্ঠুরতার এক পরিকল্পিত নিস্তব্ধতা।
কিন্তু এই নৈঃশব্দ্যে এক অনন্য জাগরণ শুরু হয়—দেশের বাইরে। প্রবাসীরা তখন কেবল নিঃশব্দে কাঁদেননি, তারা প্রতিবাদে গর্জে উঠেছিলেন। লাখো রেমিট্যান্স যোদ্ধা, যারা দিনের পর দিন ঘাম ঝরিয়ে দেশের অর্থনীতি বাঁচিয়ে রেখেছেন, তারা সেই মুহূর্তে তাদের সবচেয়ে বড় অস্ত্র ব্যবহার করলেন—অর্থপ্রবাহ। তারা টাকা পাঠানো বন্ধ করলেন। কেউ বললেন, “আমার পাঠানো টাকায় যদি গুলি কেনা হয়, তাহলে আমি আর পাঠাব না।” এই ছিল এক নতুন ধরণের যুদ্ধ—টাকার বিরুদ্ধে টাকার প্রতিবাদ, শক্তির বিরুদ্ধে সচেতনতা, নিরস্ত্র নাগরিকের এক সর্বোচ্চ আত্মমর্যাদাবোধ।
এই যুদ্ধ ছিল নৈতিকতা দিয়ে পরিচালিত। কেউ রাস্তায় গুলি খায়নি, কিন্তু সেই প্রবাসীরা তাদের ঘামে-ভেজা শ্রমের শক্তিকে রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে এক আয়নার মতো তুলে ধরেছিলেন। তারা বিশ্বকে জানিয়ে দিলেন—এই রাষ্ট্র আর তাদের প্রতিনিধিত্ব করে না। এই রাষ্ট্র আর তাদের মাতৃভূমির সম্মান ধরে রাখে না। তাই তারা রাষ্ট্রের ভেতরে না থেকেও, রাষ্ট্রকে থামিয়ে দিতে জানে।
এটাই আজকের নতুন বাংলাদেশ। যেখানে প্রবাসীরা শুধু রেমিট্যান্স পাঠান না, তারাও এখন রাষ্ট্রচালনার এক গোপন শক্তি। তারা শুধু অর্থনীতির চাকায় জ্বালানি যোগান না, তারা প্রয়োজনে সেই ইঞ্জিন বন্ধ করে দিতে জানেন। তারা শুধু পরিবার চালান না, আন্দোলনের ব্যানারও টানেন। ইউরোপ-আমেরিকার রাস্তায় দাঁড়িয়ে তারা শুধু প্ল্যাকার্ড তোলেন না, বরং শিখিয়ে দেন পরবর্তী প্রজন্মকে—কীভাবে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে হয়, কোন অন্যায়ের সামনে মাথা নোয়ানো যায় না।
তারা এখন কেবল ‘প্রবাসী’ নন—তারা ‘রেমিট্যান্স সৈনিক’। এই নতুন শ্রেণিকে আমাদের স্বীকৃতি দিতে হবে। তাদের হাতেই তো আছে সেই চাবিকাঠি, যেটা দিয়ে দেশের ভেতরের পচে যাওয়া রাজনৈতিক কাঠামো নড়ে উঠে। তারা যদি টাকা বন্ধ করে দেয়, তাহলে কোটি কোটি টাকার বাজেট মুখ থুবড়ে পড়ে। তারা যদি সোশ্যাল মিডিয়ায় সত্য লিখে ফেলে, তাহলে সরকার বানানো মিথ্যা প্রচার ফেটে পড়ে। তারা যদি বিশ্ব গণমাধ্যমে চিঠি লেখে, তাহলে আল-জাজিরা, বিবিসি, নিউইয়র্ক টাইমস হঠাৎ করে বাংলাদেশের নাম উচ্চারণ করতে শুরু করে।
তাই আজ আমাদের উচিত, এই সাহসী ভূমিকা, এই নৈতিক বিপ্লব, এই অর্থনৈতিক প্রতিবাদ—সবকিছুকে একটি জাতীয় স্বীকৃতির আওতায় আনা। আমরা দাবি করি—এই জুলাই মাসের একটি দিনকে ঘোষণা করা হোক “জাতীয় বিবেক দিবস” হিসেবে। কারণ এই মাসে আমরা দেখেছি রাষ্ট্র কীভাবে রূপ নেয় দানবে, আবার এই মাসেই আমরা দেখেছি নাগরিক কীভাবে রূপ নেয় লড়াকু নায়ক হিসেবে। এই মাসে ছাত্ররা প্রাণ দিয়েছে, প্রবাসীরা হাত গুটিয়ে নিয়েছে, এবং সর্বোপরি, জাতি একটি নিরব আত্মঘোষণায় বলেছে— ‘আমরা আর ভুল করব না।’
এই দিবসে শহীদ ছাত্রদের স্মরণ হোক, রেমিট্যান্স সৈনিকদের সম্মান দেওয়া হোক, স্কুল-কলেজে গণতন্ত্র নিয়ে খোলামেলা আলোচনা হোক, সোশ্যাল মিডিয়ায় গণচেতনার জোয়ার উঠুক। আর হ্যাঁ, যেন রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী এই দিনে দাঁড়িয়ে জাতির কাছে উত্তর দেন—“তোমাদের সন্তানদের গুলি কেন চালানো হয়েছিল?”
জুলাই মাস এখন আর একটি সাধারণ তারিখের নাম নয়। এটি এখন এক সাংবিধানিক চেতনার নাম। একটি জাতির আত্মসমালোচনার মুহূর্ত। একটি জাতির আত্মশুদ্ধির যাত্রা। এটি ইতিহাসের পৃষ্ঠা নয়, এটি ইতিহাসের আয়না।
আজ যারা বিদেশে, তারা শুধু প্রবাসী নয়, তারা প্রতিরোধের স্থপতি। তারা শুধু অর্থ পাঠান না, প্রয়োজন হলে থামিয়ে দেন। তারা শুধু প্ল্যাকার্ড ধরেন না, তারা নিজেদের সন্তানদের শেখান কীভাবে ইতিহাস মনে রাখতে হয়। তাদের হাতেই লেখা হচ্ছে নতুন বাংলাদেশের খসড়া। আর আমরা যারা দেশে আছি, তাদের উচিত—এই খসড়া পড়া, শেখা, এবং তাতে স্বাক্ষর করা। যাতে আর কোনোদিন আমাদের ছেলেমেয়ের বুকে গুলি না চলে।
জুলাই ফিরে আসবে প্রতিবছর। আমরা তাকে স্মরণ করব না শুধু বেদনার মাস হিসেবে, বরং প্রতিষ্ঠা করব বিবেকের মাস হিসেবে। একটি এমন মাস, যেখান থেকে প্রতিবাদ শুরু হয়, আর তাতে জন্ম নেয় মুক্তি।
রহমান মৃধা, সাবেক পরিচালক, ফাইজার, সুইডেন Rahman.Mridha@gmail.com
মত দ্বিমত
কথা ছিলো, কিন্তু কেউ কথা রাখেনি: বিশ্বব্যবস্থার প্রতিশ্রুতিহীনতা ও বাংলাদেশের অন্তর্গত প্রশ্ন
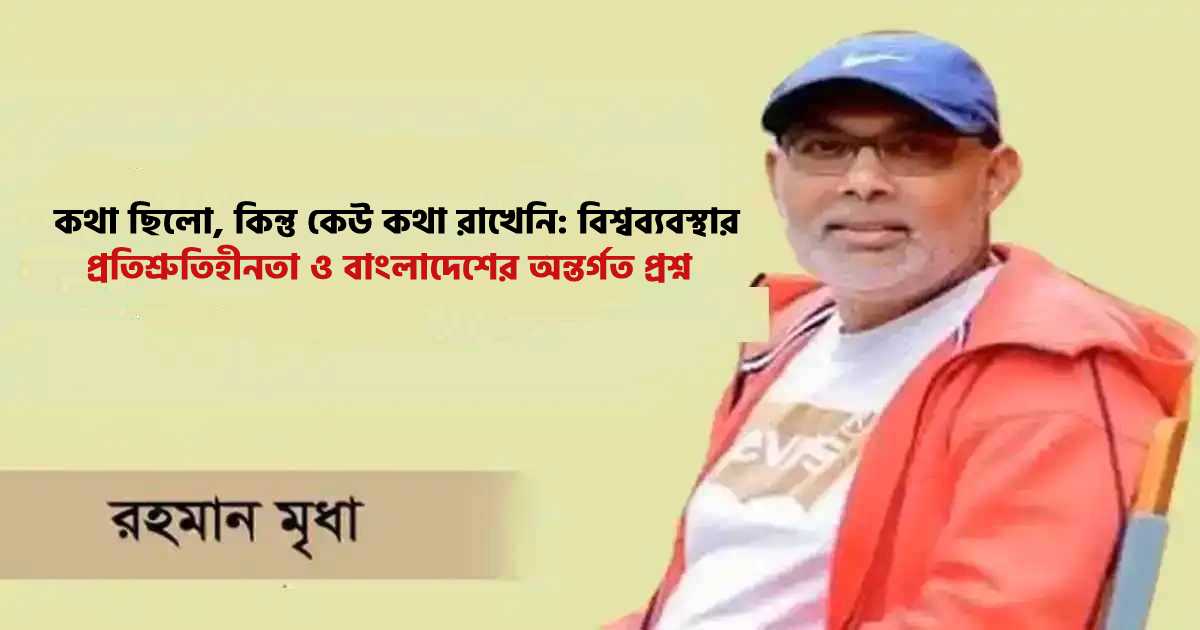
রাতের আকাশে আগুন ছড়িয়েছে আবার। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইরানে বোমা বর্ষণ করেছে। গুঁড়িয়ে গেছে কেমিক্যাল স্থাপনা, দাউ দাউ করে জ্বলছে আগ্নেয় প্রতিশোধের আগুন। ইউক্রেনের যুদ্ধ থামেনি; রাশার গর্জন এখনও ইউরোপের কানে বিদ্যুৎ হয়ে বাজে। আর ইসরাইল গাজায় চালাচ্ছে নিধনযজ্ঞ—হামাসের লড়াইয়ের নামে, সাধারণ মানুষের প্রাণহানি আজ অজস্র। অথচ প্রতিশ্রুতি ছিলো-শান্তির, ন্যায়ের, মানবাধিকারের। কিন্তু কেউ কথা রাখেনি।
চীন নিশ্চুপ, কৌশলে ব্যস্ত। ভারত দক্ষিণ এশিয়ায় তার বলয় রচনা করছে, আর বাংলাদেশের কাঁধে জমে উঠছে সীমান্ত হত্যা, পানি সমস্যা, অর্থনৈতিক শ্বাসরোধ। দেশের ভেতরে চলছে এক অসহ্য অস্থিরতা, এক ভয়াবহ সামাজিক এবং নৈতিক ভাঙন। এই হলো আমাদের বাস্তবতা। এই হলো সেই পৃথিবী, যার দিকে তাকিয়ে এখন প্রশ্ন ওঠে—এ কোন পৃথিবী আমরা দেখতে পাচ্ছি? কী কথা ছিলো আর কী করছি?
স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় মানুষ স্বপ্ন দেখেছিলো এমন এক রাষ্ট্রের, যেখানে মানুষ শুধু মানুষ হিসেবেই বাঁচবে। যেখানে রাষ্ট্র তাদের রক্ষা করবে, সম্মান দেবে, পথ দেখাবে। সেই স্বাধীনতা দিবসে, সংবিধান রচনার মুহূর্তে, দেশের প্রতিটি ছাত্র, কৃষক, শ্রমিকের হৃদয়ে ছিলো একটাই বিশ্বাস—এই রাষ্ট্র কথা রাখবে। কিন্তু আজ, বারবার ফিরে আসে সেই প্রশ্ন—কেউ কথা রাখেনি, কিন্তু কেনো?
বাংলাদেশ আজ যেন এক ব্যবহৃত ভূখণ্ড। কখনো ভারতের রাজনৈতিক বলয়ে, কখনো চীনের অর্থনৈতিক রাস্তার পাশে, কখনো পশ্চিমা বিশ্বে ‘স্ট্যাটেজিক পার্টনারশিপ’-এর শর্তাধীন অবস্থানে—আমরা আছি, কিন্তু আমরা নিজেরা কোথায় দাঁড়িয়ে আছি, তা জানি না। এই রাষ্ট্র কি শুধুই দুর্নীতি করেই খুশি? নাকি এখনও কোনো বিকল্প পথের সন্ধান চায়?
বাংলাদেশের প্রশাসনিক কাঠামো, বিশেষত বিসিএস ক্যাডারগণ—যাঁদের হবার কথা ছিলো জনগণের সেবক, ন্যায়বিচারের রক্ষক—তাঁরাও আজ আর সেই দায়িত্ব পালনে অগ্রগামী নন। আজ তাঁদের ভূমিকা প্রায়শই সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েছে সিস্টেমকে রক্ষা করা, জনগণের মুখে তালা পরানো এবং ক্ষমতার নির্দেশ পালন করার মধ্যে। এটাই কি তাঁদের জাতিগত অ্যাসাইনমেন্ট ছিলো?
আর যদি বহিঃশত্রু এসে দাঁড়ায় সীমান্তে, যদি দক্ষিণ এশিয়ায় সংঘর্ষ ছড়িয়ে পড়ে, যদি বাংলাদেশ কোনো বৃহৎ শক্তির চাপে পড়ে—তাহলে কি বাংলার সাগর, বাংলার আকাশ, বাংলার এই ভূখণ্ড প্রস্তুত আছে আত্মরক্ষার জন্য? শুধু অস্ত্র দিয়েই তো রক্ষা হয় না কোনো দেশ; রক্ষা হয় মানুষ দিয়ে, মানুষের সম্মান দিয়ে, নেতৃত্বের সততা দিয়ে। আর সেসবের কি এখন সামান্য অবশিষ্ট আছে?
এই মুহূর্তে বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় সংকট হলো—তা নিজেকে নিরপেক্ষভাবে বিশ্লেষণ করতে জানে না। না রাষ্ট্র, না নাগরিক—কেউই নিজেদের জবাবদিহির কাঠগড়ায় দাঁড়াতে রাজি নয়। আর তাই এই প্রশ্ন, যা আজ শুধু এক ব্যক্তির নয়, এক জাতির, এক সময়ের: বাংলাদেশ কি শুধুই ব্যবহারযোগ্য শরিক হিসেবে থাকবে? না কি সে তার নিজের পরিপূর্ণ আত্ম-নির্ভর অস্তিত্ব খুঁজে নেবে?
আমরা এখন এমন এক যুগে প্রবেশ করেছি, যেখানে রাষ্ট্ররা নিজেদের কথা রাখে না, বিশ্বনেতারা কথা রাখে না, এমনকি আন্দোলনকারীরাও মাঝে মাঝে নিজেদের স্বপ্ন থেকে সরে যায়। তাই এই লেখার উদ্দেশ্য শুধু শোক প্রকাশ নয়, বরং তা এক রাজনৈতিক ও নৈতিক পুনরাবিষ্কারের আহ্বান।
সত্যি বলতে, প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ এখন কৌশলের অংশ। যুদ্ধের নামে শান্তি, মিত্রতার নামে ব্যবহার, উন্নয়নের নামে শোষণ—এই হলো বৈশ্বিক রাজনীতির নতুন ব্যাকরণ। আর এ ব্যাকরণ বোঝার দায় এখন আমাদের। একমাত্র জনগণই পারে এই মুখোশ ছিঁড়ে ফেলে রাষ্ট্র ও বিশ্বব্যবস্থাকে নতুন প্রশ্নে দাঁড় করাতে—কথা রাখবে কে? কবে? আর রাখবে কি আদৌ?
এই প্রশ্নে আমাদের থেমে গেলে চলবে না। আমাদের ইতিহাস আছে—স্বাধীনতা যুদ্ধ, গণঅভ্যুত্থান, ভাষা আন্দোলন। আমাদের সংগ্রাম আছে। দরকার আছে কেবল একটি দৃশ্যমান জাতীয় পুনর্নির্মাণের পরিকল্পনা—যেখানে কথার চেয়ে কাজ, প্রতিশ্রুতির চেয়ে দায়িত্ব বড় হয়ে উঠবে।
অতএব, এই জাতির সামনে এখন শুধু একটিই করণীয়—নিজেদের কথা নিজে রাখতে শেখা। কারণ আর যদি কেউ কথা না রাখে, তবে আমাদেরও বাঁচার আর কোনো কথা থাকবে না।
রহমান মৃধা
গবেষক ও লেখক
(সাবেক পরিচালক, ফাইজার, সুইডেন)
Rahman.Mridha@gmail.com
প্রবাস
টোকাই যখন রক্ষক, আর সেনাবাহিনী হয়ে দাঁড়ায় দর্শক: একটি রাষ্ট্রদ্রোহের জবাব কোথায়?

বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্রটি কি শুধু রাজনীতিবিদদের ক্যারিয়ার গড়ার জন্য জন্ম নিয়েছিল? এই প্রশ্নটি আজ কেবল বুদ্ধিবৃত্তিক নয়—এটি একটি রাষ্ট্রব্যবস্থা ও জাতির অস্তিত্বঘন প্রশ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে। একদিকে রয়েছে লুটপাট, অন্যদিকে রয়েছে নির্বিকারতা। একদিকে দুর্নীতিতে হাবুডুবু খাওয়া প্রশাসন, অন্যদিকে নিজের রক্ত দিয়ে, হাড়-মাংস দিয়ে এই রাষ্ট্রকে রক্ষা করে চলেছে যে জনগণ—বিশেষত সেই ‘টোকাই’ শ্রেণি—তারা আজও জানে না, রাষ্ট্রটা আদৌ তাদের জন্য কিনা।
২০২৪ সালের জুলাইয়ে যখন এক নতুন ইতিহাস রচিত হয়—স্বৈরাচার পতনের জন্য গোটা জাতি রাস্তায় নামে, তখন সশস্ত্র বাহিনী কিংবা রাষ্ট্রের প্রতিরক্ষা কাঠামো এক বিরাট প্রশ্নের মুখে পড়ে। দীর্ঘকাল ধরে যে বাহিনীর পিছনে জনগণের অর্থে রাষ্ট্রীয় বাজেটের বৃহত্তর অংশ ব্যয় হয়, যারা রাষ্ট্রীয় প্রতিরক্ষার প্রতীক বলে বিবেচিত, তারা তখন কেন নীরব ছিল? শুধু নীরব নয়—প্রকৃতপক্ষে তারা একটি অবৈধ ও গণবিচ্ছিন্ন শাসনের রক্ষাকবচ হিসেবেই কাজ করেছে বছরের পর বছর। অথচ যাদের নামে আমরা একসময় ‘অনুন্নত’ বলতাম, যাদের কোনো রাজনৈতিক স্ট্যাম্প নেই, যাদের অস্ত্র কেবল রাগ আর ক্ষুধা—সেই ‘টোকাই’ শ্রেণির মানুষেরাই দেশের ভবিষ্যৎ বদলের প্রধান চালিকা হয়ে উঠেছে।
তাহলে সেনাবাহিনীর প্রয়োজনীয়তা কোথায়?
এই প্রশ্নের উত্তর শুধু একটি বাহিনীর গায়ে কালি লাগানো নয়। এটি জাতির সামনে একটি মূল প্রশ্ন উপস্থাপন: রাষ্ট্র কার? রক্ষার দায়িত্ব কাদের? জনগণের পয়সায় যাদের প্রশিক্ষণ ও অস্ত্র কিনে দেওয়া হয়, তারা বিপদের সময় কোন ভূমিকায় থাকে? এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া না গেলে ভবিষ্যতে বাংলাদেশে আর কোনো প্রতিষ্ঠানিক ন্যায়বিচার বা গঠনমূলক রাষ্ট্রচিন্তা টিকে থাকবে না।
স্বৈরতন্ত্রের দীর্ঘ যাত্রায় দেখা গেছে—সেনাবাহিনী কখনোই জনগণের পক্ষে অবস্থান নেয়নি। তারা শুধু রাষ্ট্রক্ষমতার ভারসাম্য রক্ষা করতে চেয়েছে—এমনকি সেটা যদি স্বৈরাচারী ও বিদেশপন্থী শাসকদের পক্ষে হয় তবুও। এ ক্ষেত্রে বাংলাদেশ মিশর, পাকিস্তান বা মিয়ানমারের চেয়ে কোনো আলাদা দেশ নয়। বরং বাংলাদেশের সেনাবাহিনী আরও দক্ষতায় স্বৈরতন্ত্রকে কাস্টমাইজড করে টিকিয়ে রেখেছে—সীমান্তে অস্ত্র নয়, কাঁধে বাণিজ্যের ব্যাগ নিয়ে তাদের দায়িত্ব পালন হয়েছে।
অন্যদিকে, এই দেশের সবচেয়ে নিরস্ত্র ও নিরুপায় মানুষরাই যখন রাজপথে রক্ত দেয়, লাশ পড়ে, গুম-খুন সহ্য করে দেশ রক্ষা করে—তখন রাষ্ট্র তাদের কী দিয়েছে? রাষ্ট্র কখনো তাদের ‘নিরাপত্তা বাহিনী’ বলেছে? না, রাষ্ট্র তাদের ‘উসকানিদাতা’, ‘জঙ্গি’, ‘রাজাকার’ বা ‘বাম চরমপন্থী’ আখ্যা দিয়েছে। অথচ ইতিহাস সাক্ষী—বাংলাদেশের সবচেয়ে বিপ্লবী ও প্রতিরক্ষামূলক ভূমিকা পালন করেছে এই টোকাই শ্রেণির মানুষরাই, যারা প্রশাসন, কূটনীতি কিংবা বড় পুঁজির সুবিধা ছাড়াই দেশপ্রেমকে বাস্তবতার মাটিতে নামিয়ে এনেছে।
এই ভয়ানক বৈপরীত্যের জবাব কে দেবে?
রাজনীতিবিদরা? যাদের অধিকাংশের অস্তিত্বই জনগণের নামে অথচ জনগণবিরোধী অপকৌশলের ওপর দাঁড়িয়ে? যারা নিজের দলীয় পৃষ্ঠপোষকতাকে রাষ্ট্রের চেয়ে বড় করে দেখে? না, তারা পারবে না। কারণ তারা নিজেরাও সেনা-আধিপত্য, আমলাতন্ত্র আর বিদেশি অনুগ্রহের কাছে আত্মসমর্পণ করে নিজেদের রাজনৈতিক সুবিধা হাসিল করতে চায়। যারা রাজপথে রক্ত দেয় না, তাদের হাতে ‘নাগরিক চুক্তি’ স্বাক্ষরের নৈতিকতা নেই।
সেনাবাহিনী দেবে? তারা তো পেশাগতভাবে প্রশিক্ষিত, কিন্তু নৈতিকভাবে শূন্য। যদি সেনা কর্মকর্তা রাস্তায় পড়ে থাকা টোকাইদের জীবনের চেয়ে নিজের ব্যারাকের নিরাপত্তাকে বড় করে দেখে, তাহলে সেই সেনাবাহিনীর অস্তিত্ব নিয়েই প্রশ্ন তোলা সময়ের দাবি।
রাষ্ট্রের মালিক কারা—জনগণ, সেনা, নাকি ধনিক চক্র? টোকাই জাতির বিচারের সময় এসেছে
বাংলাদেশের সংবিধান বলে, “এই প্রজাতন্ত্রের মালিক জনগণ।” কিন্তু বাস্তবতা বলে ভিন্ন কিছু। যদি জনগণই রাষ্ট্রের মালিক হতো, তাহলে রাষ্ট্রীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণে তাদের কণ্ঠস্বর আজ এভাবে নিষ্পেষিত হতো না। যদি এই দেশের আসল মালিক হতো কৃষক, মজুর, গার্মেন্ট শ্রমিক কিংবা রাস্তার টোকাই—তাহলে একতরফাভাবে জাতির উপর চেপে বসা সরকার কিংবা বিদেশি এজেন্ডা বাস্তবায়নকারী আমলা-জেনারেল-পুঁজিপতিদের এমন রক্তচোষা শাসন চালানো সম্ভব হতো না।
আসলে বাংলাদেশ এখন আর কোনো গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র নয়, বরং এটি একটি ব্যক্তিমালিকানাধীন কর্পোরেট কোম্পানি, যেখানে রাজনীতি মানে ঠিকাদারি, প্রতিরক্ষা মানে সীমান্ত বাণিজ্য আর আমলাতন্ত্র মানে বিদেশি পরামর্শে জনগণকে কাবু করার কৌশল। এই কোম্পানির মালিকানা রয়েছে কিছু পরিবারের হাতে, যাদের নিরাপত্তার জন্য সেনাবাহিনী, যাদের বিলাসিতার জন্য বাজেট, যাদের অপকর্ম ঢাকার জন্য আদালত ও মিডিয়া প্রস্তুত। আর এই ‘নতুন কোম্পানি রাষ্ট্রে’ সবচেয়ে অপ্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছে জনগণ—বিশেষ করে যাদের রক্ত ঘামে এই রাষ্ট্রের উৎপাদনশীলতা তৈরি হয়েছে।
এখন প্রশ্ন: যদি জনগণ রাস্তায় নামে, নির্বাচন চায়, অধিকার চায়—তাদের পিঠে গুলি চলে কেন? কেন সেনাবাহিনী তখন চুপ থাকে? কেন মিডিয়া তখন বলে ‘বিদেশি ষড়যন্ত্র’? এই প্রশ্নগুলো কোনো কবিতা বা চেতনার কথা নয়—এগুলো রাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় স্বরূপ উন্মোচনের প্রশ্ন।
জুলাই ২০২৪-এর গণজাগরণ তার সর্বোচ্চ সত্য দিয়ে আমাদের চোখ খুলে দিয়েছে—সেখানে প্রতিরক্ষা বাহিনী নিষ্ক্রিয়, পুলিশ প্রশাসন দুর্নীতিপরায়ণ আর টোকাইদের হাতেই দেশ বাঁচে। অর্থাৎ, রাষ্ট্রপ্রতিরক্ষা ও রাষ্ট্রনির্মাণ—দুটোরই আসল মালিক এখন ‘অবৈধভাবে’ পথের মানুষ হয়ে উঠেছে।
এই বাস্তবতায় দাঁড়িয়ে জনগণ এখন জবাব চায়:
• যারা বেতন নেয় দেশের প্রতিরক্ষার নামে, তারা কোথায় ছিলেন?
• যারা কথায় কথায় ‘জাতীয় নিরাপত্তা’র কথা বলেন, তারা কার নিরাপত্তা নিশ্চিত করেছেন—দেশের, না ক্ষমতাবানদের?
• যারা বারবার নির্বাচন ছিনিয়ে নিয়েছে, তারা কী সত্যিই রাষ্ট্রকে ভালোবেসে ক্ষমতায় ছিল, নাকি এটা ছিল লুটপাটের লাইসেন্স?
এত বছরের রাষ্ট্রচক্র আর শোষণ যন্ত্রপাতির বিপরীতে যে টোকাই শ্রেণি রাজপথে দাঁড়িয়েছে, তার নৈতিক শক্তি কত বিশাল, তা বুঝতে হলে দেখতে হবে—তারা কোনো পদ, পদবী, ক্ষমতা বা বৈদেশিক অনুদানের জন্য রাজপথে নামেনি। তারা নেমেছে কেবল নিজের ভবিষ্যতের জন্য, নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য। এই শক্তি যদি আজ অবধি গণ্য না হয়, তাহলে জাতি হিসেবে আমাদের অস্তিত্ব নিয়ে প্রশ্ন ওঠে।
সেনাবাহিনী, আমলাতন্ত্র এবং রাজনৈতিক নেতৃত্ব—এই ত্রয়ী যদি এই সংকটেও জবাব না দেয়, তাহলে সেই নীরবতা নিজেই রাষ্ট্রদ্রোহের প্রমাণ হয়ে থাকবে।
এই রাষ্ট্রের নাম ‘গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ’—কিন্তু এখন এটি হয়ে দাঁড়িয়েছে ‘লুটপ্রজাতন্ত্রী কোম্পানি’। আর এই লুটের সাম্রাজ্যে যারা রক্ত দিয়ে দেয়, তারাই এখন ন্যায়বিচার চায়। এই চাওয়া কোনো আবেগ নয়, এটি ইতিহাসের দাবি।
টোকাই জনগণের রাষ্ট্র ফেরতের ঘোষণা—একটি নতুন রাষ্ট্রচেতনার রূপরেখা
যে রাষ্ট্রে শ্রমজীবী মানুষ, শিক্ষার্থী, পথবাসী, ফুটপাতের ফেরিওয়ালা, ভ্যানচালক, ক্ষুধার্ত মা কিংবা বস্তির শিশু রাষ্ট্রীয় নীতিনির্ধারণে একটুও ভূমিকা রাখতে পারে না, সেই রাষ্ট্র কোনোভাবেই গণপ্রজাতন্ত্রী হতে পারে না। এ এক নিছক প্রতারণা। বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণায় বলা হয়েছিল, “এই রাষ্ট্র হবে গণতন্ত্র, সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক ন্যায়ের ভিত্তিতে।” কিন্তু কী নির্মম ট্র্যাজেডি—আজ থেকে ৫৪ বছর পরও সেই রাষ্ট্রের সবচেয়ে বড় গালাগালি হলো ‘টোকাই’—মানে রাষ্ট্রহীন নাগরিক!
তাদের না আছে নাগরিক মর্যাদা, না আছে আইনি সুরক্ষা, না আছে স্বাস্থ্য, শিক্ষা বা ভোটাধিকার। অথচ তারা শুধু বাঁচে না, দেশকেও বাঁচিয়ে রাখে। জুলাই অভ্যুত্থানে রাষ্ট্র যখন হোঁচট খাচ্ছিল, জেনারেলরা যখন মৌন, আমলারা যখন বিভ্রান্ত আর বড় রাজনৈতিক দলগুলো যখন চেয়ারে কে বসবে সেই হিসেব কষছিল—তখন এই ‘টোকাই’ জনগণই রাস্তায় নামল, রক্ষাকবচহীন, খাবার ছাড়া, আশ্রয়হীন, কিন্তু সাহসে ভরপুর। তারা না থাকলে এই রাষ্ট্র হয়তো আজও চোরের হাতেই পড়ে থাকত।
তাই এখন আর সময় নেই ‘দায়’ এড়িয়ে যাওয়ার। এবার সময় এসেছে রাষ্ট্রকাঠামো পুনর্গঠনের। পরিস্কার করে বলি—এটি কেবল ভোটাধিকার ফিরিয়ে দেওয়ার আন্দোলন নয়। এটি রাষ্ট্রের মালিকানা জনগণের হাতে ফিরিয়ে দেওয়ার অনিবার্য ইতিহাস-প্রসূত প্রয়োজন।
একটি চারস্তর বিশিষ্ট ন্যায্য রাষ্ট্রকাঠামোর দাবি:
১. রাষ্ট্রক্ষমতার উৎস হবে সরাসরি জনগণ—মৌখিকভাবে নয়, কার্যকরভাবে। যার মানে, স্থানীয় সরকার থেকে কেন্দ্র পর্যন্ত গণপর্যবেক্ষণ ও জনগণের প্রত্যাহার অধিকারে সাজানো প্রশাসনিক কাঠামো গড়া। আজ যারা ভোট দেয়, তারা পাঁচ বছর পরও তার প্রভাব ফেলতে পারে না—এটা গণতন্ত্র হতে পারে না।
২. দুই মেয়াদের প্রেসিডেন্সিয়াল পদ্ধতি চালু করা—যাতে এককেন্দ্রিকতা আর দলীয় ভাড়াটে ব্যবস্থার অবসান ঘটে। জনগণ যাতে সরকারপ্রধানকে সরাসরি নির্বাচনে ঠিক করতে পারে, এবং আবার প্রত্যাহার করতেও পারে, সেই অধিকার তাকে দিতে হবে। শেখ হাসিনা অথবা কোনো দলের হাতে অনির্দিষ্টকালের ক্ষমতা থাকা দেশের জন্য আত্মঘাতী।
৩. বিচার বিভাগ ও সেনাবাহিনীকে সাংবিধানিক জবাবদিহিতার আওতায় আনা—আমরা আর কোনো ‘অদৃশ্য শক্তি’র চোখ রাঙানিতে দেশ চালাতে চাই না। জনগণের অর্থে বেতন নেওয়া প্রতিরক্ষা বাহিনীকে জনগণের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে, লুটপাটকারীদের নিরাপত্তা নয়। বিচারপতি ও জেনারেলরা যদি জনগণের মুখোমুখি হন না, তাহলে তারা জনগণের নয়, ফ্যাসিবাদের হাতিয়ার।
৪. টোকাই জনগণের সমগ্রিক নাগরিকত্ব ঘোষণা—রাস্তার শিশু, বস্তির মা, ময়লা কুড়ানো কিশোরী, গার্মেন্টে কর্মরত কিশোরী—এই রাষ্ট্র তাদের নয় বলেই প্রতিদিন তাদের জীবন এমন বিপন্ন। এদের জন্য স্বতন্ত্র নাগরিক সুরক্ষা কমিশন, বিনা ব্যয়ে শিক্ষা ও চিকিৎসা, এবং রাজনৈতিক প্রতিনিধি হিসেবে নির্ধারিত সংরক্ষিত আসন চাই। শুধু ‘দয়া’র নামে খাদ্যসামগ্রী বিতরণ নয়—রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় এই জনগণের স্থান নিশ্চিত করতে হবে।
রাষ্ট্রের প্রশ্নে নতুন সংলাপ চাই—পুরাতন মুখ, পুরাতন দল নয়
বাংলাদেশের রাজনীতি এখন পুরাতনদের হাতে জিম্মি—তারা সবাই কোনো না কোনোভাবে এই লুটের কাঠামোর লাভভোগী। তারা যদি এই কাঠামো বদলাতে পারত, এত বছরেও পারত। তারা পারে না, কারণ তারা চায় না। কাজেই নতুন রাষ্ট্রচেতনা গড়তে হলে নতুন নেতৃত্ব চাই—যে নেতৃত্ব দলগত নয়, শ্রেণিগত; যে নেতৃত্ব ধানমণ্ডি থেকে নয়, পথঘাট থেকে উঠে এসেছে।
এবার নতুন বাংলাদেশ গড়তে হলে দরকার—
• লজ্জাহীন সত্য বলার মত সাংবাদিকতা
• বয়ানের আড়ালে না লুকিয়ে সরাসরি বাস্তব প্রশ্ন তোলার মতন বুদ্ধিজীবী
• এক্সেলশিট নয়, হৃদয়ে রাষ্ট্রচিন্তা করার মত অর্থনীতিবিদ
• ‘শত্রু নয় প্রতিবেশী’ ভিত্তিক স্বাধীন পররাষ্ট্রনীতি
• এবং সবশেষে, এক অভূতপূর্ব জনআন্দোলনের মধ্য দিয়ে গড়ে ওঠা একটি ন্যায়ভিত্তিক গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র।
শেষ কথাঃ এই রাষ্ট্র ‘টোকাই’দের ফিরিয়ে দেবে কি না, সেটাই এখন ইতিহাসের পরীক্ষা
আমরা যাদের টোকাই বলি, তাদের কাছে আজ ইতিহাসের পাসওয়ার্ড রয়েছে। তারা যদি আর একবার উঠে দাঁড়ায়—এইবার শুধু রাজপথে নয়, কাঠামোর ভিতরেও প্রবেশ করে—তবে এই রাষ্ট্র কেবল বদলাবে না, নতুন রাষ্ট্র হবে।
এই লেখায় আমি সেই তীব্র সত্যটি তুলে ধরলাম। এখন আপনারা বলুন—এই জনতার ঘাম আর রক্তের দাম কী হবে?
দরকার দেশের প্রতিটি নাগরিকের সমঅধিকার প্রতিষ্ঠা ও নিরাপত্তার নিশ্চয়তা। শুধুমাত্র প্রশাসন নয়, আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীকে অবশ্যই জনগণের পাশে দাঁড়াতে হবে, তাদের দাসত্ব ত্যাগ করে নাগরিকদের সেবা দিতে হবে। আর রাজনীতির ময়দান থেকে সকল প্রকার দুর্নীতি, স্বার্থপরতা ও দলীয় ষড়যন্ত্র মুছে ফেলা ছাড়া এই কাজ অসম্ভব।
আমাদের মুক্তিযুদ্ধের গর্বিত ইতিহাস, সংগ্রামের স্মৃতি এবং গণতন্ত্রের অটুট ভিত্তি ফিরিয়ে আনা ছাড়া ভবিষ্যতের প্রজন্মের জন্য দেশকে নিরাপদ করা সম্ভব নয়। এ পথে সবাইকে মিলেমিশে কাজ করতে হবে—চাই সেটি রাজনীতিবিদ হোক, প্রশাসক হোক, সেনাবাহিনী হোক বা সাধারণ মানুষই হোক।
এখন আমাদের মূল লক্ষ্য হওয়া উচিত—সৎ ও দৃঢ় নেতৃত্বের তলে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা করা, সকলের অধিকার রক্ষা নিশ্চিত করা, প্রশাসনের জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠা করা, এবং স্বাধীন ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে সুশাসন স্থাপন করা।
যখন এসব আদর্শের ভিত্তি দৃঢ় হবে, তখন টোকাই জনগণের সংগ্রাম সত্যিকার অর্থে সফল হবে, সেই সংগ্রাম দেশের ভবিষ্যতকে আলোকিত করবে, আর দীর্ঘদিন অবহেলিত এই দেশের নাগরিকরা তাদের অধিকার ফিরে পাবে।
লেখক, সাবেক পরিচালক, ফাইজার, সুইডেন
মত দ্বিমত
কয়লার কোন অংশ পরিষ্কার করবেন আর ডায়মন্ডের কোন অংশে বাদ দিবেন?
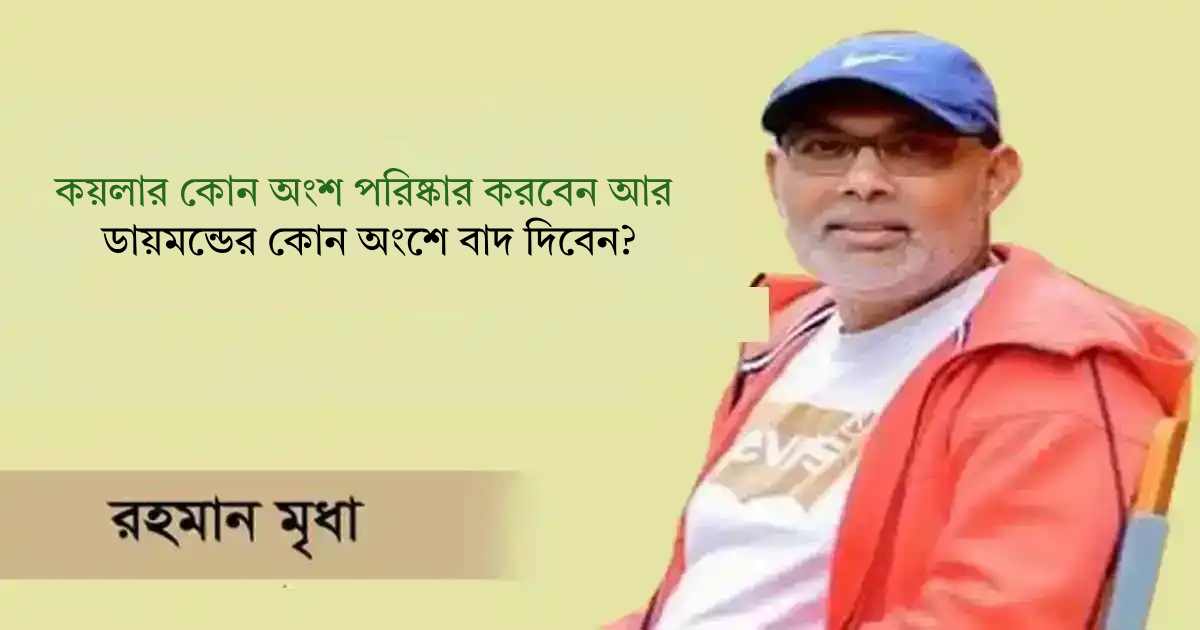
বাংলাদেশে গণমাধ্যমকে রাষ্ট্রের ‘চতুর্থ স্তম্ভ’ হিসেবে অভিহিত করা হলেও, আজ তা যেন একরকম দৃশ্যমান বিভ্রান্তির কারখানায় রূপ নিয়েছে। পাঠকের চোখ যখন জিজ্ঞাসু হয়— ‘সত্য ঠিক কোথায়?’—তখন বোঝা যায় যে এই স্তম্ভটি নিজেকে জিইয়ে রাখার নামে নিজের ভিতরেই ফাটল ধরাচ্ছে। সংবাদপত্রের চকচকে প্রিন্ট কিংবা স্টুডিওর আলোয় ঝলমলে টকশোগুলোর আড়ালে যে অদৃশ্য নাটাই রয়েছে, তা চালায় এক সুপরিকল্পিত ক্ষমতার চক্র। রাজনীতি, বাজার আর তথ্যানিয়ন্ত্রণে পারদর্শী অভিজাত শ্রেণি—এই ত্রিমুখী ছায়া একত্রে পড়েছে রিপোর্টিংয়ের ভাষায়, সংবাদ বাছাইয়ের নিয়মে, আর সম্পাদকীয় নীতির অভ্যন্তরে।
এই অবস্থায় ‘কয়লার কোন অংশ পরিষ্কার করবেন আর ডায়মন্ডের কোন অংশে বাদ দিবেন?’—এই বাক্যটি শুধুই রূপক নয়, বরং আমাদের সামনে দাঁড় করায় এক গভীর নৈতিক প্রশ্ন। তথ্য যদি আর জনগণের অধিকার না থাকে, বরং ‘ব্যবস্থার মালিকানা’ হয়ে ওঠে, তবে হীরার আলোও হয়ে যায় ক্ষমতার ঝলকানি, আর কয়লার ভিতর চাপা পড়ে যায় সেই ঘষে ওঠা সম্ভাব্য সত্য—যার উদ্ভাস ছিল একসময় সংবাদমাধ্যমের বিবেক।
বিশ্বজুড়ে বিভিন্ন সমীক্ষা আজ দেখাচ্ছে, বাংলাদেশের জনগণ ক্রমাগত আস্থা হারাচ্ছে সংবাদমাধ্যমের ওপর থেকে। Reuters Institute-এর ২০২৪ সালের ডিজিটাল নিউজ রিপোর্ট অনুযায়ী, মাত্র ৩২ শতাংশ পাঠক বিশ্বাস করেন যে সংবাদমাধ্যম সত্য তুলে ধরে, যেখানে ৬৪ শতাংশ মনে করেন তারা প্রায়শই বিভ্রান্তিকর বা উদ্দেশ্যপ্রণোদিত তথ্যের মুখোমুখি হন—বিশেষত টিভি টকশো ও অনলাইন নিউজ পোর্টালের মাধ্যমে। এই আস্থাহীনতা একদিকে সেন্সেশনালিজমের জোয়ার, আরেকদিকে অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার বিলুপ্তি—এই দুইয়ের যুগপৎ চাপে তৈরি হয়েছে।
সংবাদ পরিবেশনের নামে এখন অধিকাংশ মাধ্যম যেন ‘বুম-জার্নালিজম’ নামক চমক-নির্ভর খেলায় মত্ত। রিপোর্টার আর জবাবদিহির মুখোমুখি নয়, বরং কনটেন্ট ক্রিয়েটর আর মনোযোগ-কাড়ার প্রতিযোগী হয়ে উঠেছে। যে সাংবাদিকতা এক সময়ের শোষিত মানুষের কণ্ঠ ছিল, তা আজ যেন একটি করপোরেট ব্র্যান্ডিং প্ল্যাটফর্ম, যার মূল গ্রাহক পলিটিক্যাল কর্পোরেশন।
রাষ্ট্রীয় আইন ও বিধিনিষেধের জালে এই চতুর্থ স্তম্ভটিকে বন্দি করা হয়েছে—একটি নিঃশব্দ, নিয়ন্ত্রিত স্বাধীনতার আড়ালে। ডিজিটাল সিকিউরিটি অ্যাক্ট (২০১৮), ব্রডকাস্ট বিল, কিংবা সাম্প্রতিক সাইবার নিরাপত্তা আইন—এই সব কিছু যেন সাংবাদিকতার গলায় বেঁধে দেওয়া একেকটি অদৃশ্য শিকল। ২০২৩ সালে মাত্র এক বছরে ১২১ জন সাংবাদিককে রাষ্ট্রবিরোধী কিংবা তথ্যপ্রযুক্তি আইনে অভিযুক্ত করা হয়েছে—এই তথ্য দিয়েছে ‘আর্টিকেল ১৯’। এটি কোনো বিচ্ছিন্ন পরিসংখ্যান নয়, বরং এক বিস্তৃত নিঃশব্দীকরণের প্রতিচ্ছবি।
আজ সংবাদ কক্ষের নীতিগত সিদ্ধান্ত আর কেবল সাংবাদিকের বিবেক বা পেশাদারিত্ব দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় না। বরং তা নির্ধারিত হয় রাজনৈতিক যোগাযোগ, কর্পোরেট মালিকানার স্বার্থ আর বিজ্ঞাপনদাতার মুখরক্ষার প্রয়োজনীয়তা দ্বারা। বড় দৈনিকগুলোর অনেক সম্পাদকই স্বীকার করেন, যে কোনো সংবেদনশীল রিপোর্ট প্রকাশের আগে ‘উপরে জানানো’ বাধ্যতামূলক এক আনুষ্ঠানিকতা হয়ে উঠেছে।
এই বাস্তবতায় সত্য ক্রমশ রূপ নিচ্ছে এক নির্মিত দৃশ্যপটের—যেখানে চকচকে প্রতিবেদনে আছে নির্ঝঞ্ঝাট নির্বাচন, নিখুঁত উন্নয়ন, ইউনিয়ন পর্যায়ের ভোটারদের উৎসাহ; অথচ গায়েবি মামলা, বিরোধী দলের গ্রেপ্তার, কিংবা রাষ্ট্রযন্ত্রের নির্লিপ্ততা তলিয়ে যায় একটি শিল্পিত ক্যামেরা ফ্রেমের বাইরে। প্রশ্ন থেকে যায়—এটি কি বাস্তবতার প্রতিবিম্ব, না কি একটি মনস্তাত্ত্বিক ইন্দ্রজাল?
তবুও অন্ধকারে কিছু আলো জ্বলে। মূলধারার বাইরে কিছু সাহসী কণ্ঠ রয়েছে যারা—নির্ভীকভাবে রিপোর্ট করছে গুম, নির্যাতন, অর্থ পাচার কিংবা ভূমিদস্যুতার মতো ইস্যুতে।
এই মুহূর্তে শুধু সাংবাদিক না, পাঠকেরও দায়িত্ব রয়েছে। তথ্য যাচাই করা, উভয় পক্ষের বক্তব্য শোনা, ফ্যাক্টচেকিং-এর কৌশল আয়ত্ত করা—এগুলো এখন নাগরিক দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত। কারণ গণতন্ত্রের ভিত্তি যদি হয় প্রশ্ন করার অধিকার, তবে সেই প্রশ্নের উৎস হতে হবে সচেতন ও দ্বিধাহীন বিবেকে।
আজ আমাদের দাঁড়াতে হবে প্রশ্নের মুখোমুখি— ‘কয়লার কোন অংশ পরিষ্কার করবেন?’—অর্থাৎ কোন কাঠামোর অভ্যন্তরে চাপা পড়া সত্যটিকে পুনরুদ্ধার করবেন? আর ‘ডায়মন্ডের কোন অংশে বাদ দিবেন?’—অর্থাৎ কোন রাজনৈতিক নান্দনিকতা ও মিডিয়া-নির্মিত ঝলকানিকে উন্মোচন করবেন, যেখানে সত্য নেই, আছে কেবল প্রচারণার শূন্যতা?
বাংলাদেশের রাজনৈতিক বাস্তবতা আজ আর নীতির চর্চার জায়গা নয়। এটি হয়ে উঠেছে এক নাট্যধর্মী সংঘর্ষের মঞ্চ—যেখানে ক্ষমতা ও প্রতিপক্ষ একে অপরকে ঠেলছে ধ্বংসের দিকে, আর মাঝখানে থেমে গেছে জনগণের নিঃশ্বাস। ঢাকার রাজপথে যখন আন্দোলনের নামে তালাবদ্ধ হয় নগর ভবন, তখন গরিব মানুষের পানির সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়, ময়লার পাহাড়ে ঢেকে যায় শহর, আর নিরব বাতিতে অন্ধকার হয়ে পড়ে গলির মাথা।
সম্প্রতি ইশরাক হোসেনের নেতৃত্বে ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের ভবন তালাবদ্ধ করার ঘটনাটি যেন এই নাট্যকলার সর্বশেষ দৃশ্য। একদিকে প্রতীকী প্রতিবাদ, অন্যদিকে জনসেবা ৩০–৪০ শতাংশ কমে যাওয়ার মতো বাস্তব ক্ষতি। স্থানীয় সরকার উপদেষ্টার খোলা ক্ষোভ—একটা প্রত্যাশাহীন রাষ্ট্রের হতাশ কণ্ঠ। আন্দোলনের নাটক ঢাকা দিচ্ছে লন্ডনের ঐতিহাসিক বৈঠকের বার্তা, যেখানে ড. ইউনূস ও তারেক রহমানের ঐকমত্য ছিল এক সম্ভাবনার ইঙ্গিত—আজ তা ঢেকে গেছে ঢাকার নাট্যগুরুত্বে।
এই রাজনীতিতে ক্ষমতাসীনদের অপব্যবস্থা যেমন ভয়াবহ, তেমনি বিরোধীদের আত্মঘাতী সিদ্ধান্তও কম দায়ী নয়। নির্বাচনে অংশ না নিয়ে গণতন্ত্র ফেরানোর দাবি, কিংবা স্থানীয় সরকারে থেকে প্রতীকী আন্দোলনের নামে জনগণের দুর্ভোগ বাড়ানো—এসব পদক্ষেপ রাজনৈতিক পরিপক্বতা নয়, বরং আত্মপ্রতারণার এক নতুন ভাষ্য।
গণমাধ্যম, যার কাজ এসব অসংগতি তুলে ধরা, সে নিজেই আজ অনেক ক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে রাজনৈতিক প্রপাগান্ডার বাহক। একদিকে রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রিত সংবাদপত্র সরকারপ্রেমের মহড়ায়, অন্যদিকে কিছু অনলাইন পোর্টাল ব্যক্তিগত এজেন্ডা বাস্তবায়নের নেপথ্যচালক।
সেই সূত্রেই আবার ফিরে আসি—‘কয়লার কোন অংশ পরিষ্কার করবেন?’—এ প্রশ্নটি কেবল সংবাদপত্রের নয়, বরং গোটা রাজনৈতিক কাঠামোর বিবেকের প্রশ্ন।
আর ‘ডায়মন্ডের কোন অংশ বাদ দিবেন?’—এটি কেবল শ্লোগান ও প্রচারণার নয়, বরং সেই জনগণের নিঃশব্দ কান্নার প্রতিধ্বনি, যাদের নামেই চলে রাজনীতি, কিন্তু যাদের জীবনই থেকে যায় অন্ধকারে।
যে দেশে নেতৃত্বের চাইতে নাটক, সত্যের চাইতে প্রচারণা, আর সংগঠনের চাইতে কৌশল বেশি মূল্য পায়—সেই দেশে গণতন্ত্র কেবল হীরার মতো চকচকে ভ্রান্তি হয়ে থাকে। আর সংবাদমাধ্যম হয়ে পড়ে শুধুই এক নকল আয়না—যার মুখে সত্য নেই, আছে কেবল প্রতিচ্ছবির অপসংস্কৃতি।
তাই, ফিরে আসি সেই প্রশ্নে—‘কয়লার কোন অংশ পরিষ্কার করবেন?’ এটা শুধু মিডিয়ার প্রশ্ন নয়, রাজনৈতিক কাঠামোরও প্রশ্ন। আর ‘ডায়মন্ডের কোন অংশ বাদ দিবেন?’—এটি শুধুই শ্লোগানের বাহারে মিশে যাওয়া জনগণের বেদনার অন্তঃস্বর।
কিন্তু কথা তো এখানে থামে না। আমরা সারাক্ষণ ‘জনগণ’ বলে মুখে ফেনা তুলে ফেলি, কিন্তু একবার থেমে, চোখ বন্ধ করে কি জিজ্ঞেস করি— ‘এই জনগণ আসলে কী চায়?’
আরো গভীরে গিয়ে, আমি কি নিজেকে কখনও জিজ্ঞেস করেছি— ‘আমি কী চাই?’ আমি কি চাই সত্য? নাকি এক চমকপ্রদ গল্প, যেখানে জবাবদিহির বদলে থাকে অভিনয়? আমি কি চাই পরিবর্তন, না চাই এক ধরনের জৌলুসপূর্ণ স্থবিরতা?
একটি রাষ্ট্রে যদি নেতৃত্বের চেয়ে কৌশল বেশি গুরুত্ব পায়, যদি সত্যের চেয়ে প্রচারণা বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়, যদি সাংগঠনিক দৃঢ়তার বদলে নাটক চলে— তবে সেখানে গণতন্ত্র থাকে না, থাকে কেবল এক ভয়ানক দৃশ্যপট— যার মাঝে আমরা সবাই হাঁটছি, হয়তো ভাবছি— ‘সম্ভবত আমরা ঠিক আছি।’ কিন্তু… আসলে কি?
রহমান মৃধা, সাবেক পরিচালক, ফাইজার, সুইডেন। Rahman.Mridha@gmail.com
মত দ্বিমত
ভালোবাসার বদলে যাওয়া রূপ: একটি ট্রেক, একটি হৃদয়, আর এই সময়ের প্রেম
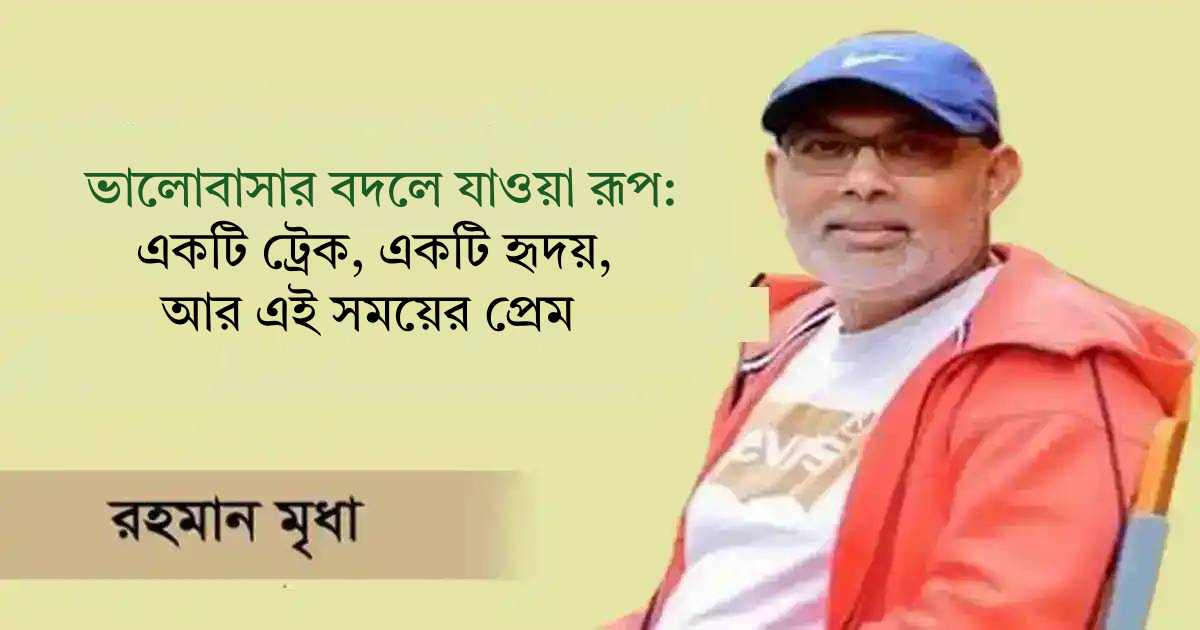
‘তুমি নেই—তবু আছো।’ এই বাক্যটি কেবল একটি স্মৃতির নয়, এটি একটি সময়ের প্রতিচ্ছবি। একাকীত্বে জন্ম নেওয়া প্রেম, স্মার্টফোনে গড়ে ওঠা সম্পর্ক, আর মেঘের ভিতর দিয়ে হাঁটা কোনো এক গভীর টান—সব মিলেই যেন আমাদের বর্তমান ভালোবাসার মানচিত্র।
আজকের দিনে প্রেম কি আর চিঠিতে লেখা থাকে? এক সময়কার অপেক্ষা, হেঁটে দেখা করতে যাওয়া কিংবা গোপনে চোখাচোখি—এসব যেন রূপকথার গল্প হয়ে গেছে। এখন প্রেম জন্ম নেয় ইনবক্সে, টিকে থাকে রিয়েকশনে, এবং শেষ হয় ‘সিন’ হয়ে থাকার মধ্য দিয়ে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক শিক্ষার্থী বলেছিলেন, ‘ক্লাসে দেখা হয় কম, কিন্তু ইনবক্সে কথা হয় বেশি। ভালোবাসা এখন একধরনের নীরব চ্যাট হিস্টোরি।’
এটা কি খারাপ? একদিক থেকে না। প্রেম যেমন সময়ের সন্তান, তেমনি মানুষের মনের দরজা খোলারও নতুন উপায়। তবে সম্পর্ক হয়ে উঠছে কিছুটা দ্রুতগামী, অস্থায়ী এবং অনিশ্চিত।
এই সময়ে প্রেম অনেকটাই যেন একটি পাবলিক ইভেন্ট।
ফেসবুকে ‘রিলেশনশিপ স্ট্যাটাস’ না বদলালে সম্পর্কটাই সন্দেহের মুখে পড়ে। একসঙ্গে ছবি না দিলে প্রশ্ন উঠে— ‘তোমরা কি এখনো একসাথে?’ আর ইনবক্সে মেসেজ ‘দেখা গেছে’ কিন্তু উত্তর নেই—তখন জন্ম নেয় এক অদৃশ্য দূরত্ব।
ভালোবাসা এখন যেন অনুভবের জায়গা থেকে সরে এসে পরিণত হয়েছে এক ধরনের সামাজিক অভিনয়ে। কে কার সঙ্গে, কোথায় ঘুরতে গেল, কে কাকে কী উপহার দিল—এসবের চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে কে কিভাবে ‘শো’ করছে তার ভালোবাসা।
সোশ্যাল মিডিয়ার এই বাহ্যিক চাপ যেন প্রেমকে ভেতর থেকে নয়, বরং বাইরে থেকে প্রমাণ করার একটা বাধ্যবাধকতা তৈরি করেছে। প্রেমের গভীরতা নয়, এখন যেন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে—প্রেমটা কে কতটা ‘দেখাতে’ পারছে
সময়ের এক বড় পরিবর্তন এসেছে নারীর অবস্থান নিয়ে। প্রেম এখন আর ‘ছেলেটাই সিদ্ধান্ত নেবে’ এমন নয়। একজন তরুণী কর্পোরেট কর্মী বলেছিলেন, ‘ভালোবাসি, তবে নিজের ভবিষ্যৎ আগে দেখি। আমি আর নিজের জীবন কারও আবেগে সমর্পণ করতে চাই না।’ এমন আত্মবিশ্বাসী অবস্থান প্রশংসার দাবি রাখে, তবে পুরুষদের অনেকে এখনো পুরোনো কাঠামোয় আটকে আছে। ফলে সম্পর্কের সমতা এবং বোঝাপড়ায় নতুন চ্যালেঞ্জ দেখা দিচ্ছে।
বর্তমানে প্রেম অনেকটাই ‘কমফোর্ট জোন’-নির্ভর হয়ে উঠেছে। মানসিক চাপ, অস্থিরতা বা দ্বন্দ্ব এলেই ভেঙে যায় সম্পর্ক। মনোরোগ বিশেষজ্ঞ ডা. শামসুল হক বলেন, ‘মানুষ এখন সম্পর্ক চায়, কিন্তু আত্মত্যাগ চায় না। যেখানে সামান্য অসুবিধা এলেই সরে যায়, সেখানে প্রেমের গভীরতা দুর্লভ।’ তবুও এমন মানুষ আছে যারা প্রেমকে লড়াইয়ের মতো করে ধরে রাখে। যারা অপেক্ষা করে, যারা বোঝে—ভালোবাসা মানে শুধু ভালো লাগা নয়, বরং জীবনকে ভাগ করে নেওয়ার প্রস্তুতি।
আমার এক প্রিয় বান্ধবী, যার জীবনদর্শন আর প্রকৃতিপ্রেম আমাকে বহুবার নাড়া দিয়েছে, একবার নিজের ভ্রমণের অভিজ্ঞতা আমার সঙ্গে শেয়ার করেছিল। জীবনের এক সন্ধিক্ষণে, যখন সে প্রেমের মানে খুঁজছিল নিজের ভেতরেই, তখন সে একা বেরিয়ে পড়েছিল নেপালের পথে—অন্নপূর্ণা পর্বতমালার দিকে। তার সেই ভ্রমণের গল্প—তার চোখে দেখা প্রকৃতি, তার হৃদয়ে গাঁথা অনুভূতি—আমার মধ্যে এমন এক প্রভাব ফেলেছিল, যা এক সময় কলমে ধরা দেওয়ার দাবি রাখে। সেই অভিজ্ঞতাকেই আমি তুলে ধরছি এই লেখায়—আমার নয়, তার আত্মসন্ধানী যাত্রার গল্প; তবে এই গল্পের শব্দ ও ছায়া আমি নিজের মতো করে বুনেছি।
পৃথিবীর দক্ষিণ এশীয় উচ্চভূমিতে, হিমালয়ের কোলঘেঁষা এক ভূখণ্ডে সে যাত্রা করেছিল। পোখরা, মানাং, আর থোরাং লা পাস—এই তিনটি নাম হয়তো অনেকের কাছে নিছক ভ্রমণগন্তব্য, কিন্তু তার কাছে ছিল আত্মার রূপান্তরযাত্রার তিনটি অধ্যায়। তার বর্ণনায় প্রকৃতি কেবল দৃশ্য নয়, এক শিক্ষক; আর পথচলা শুধুই পদচারণা নয়—এক ধ্যানমগ্ন আত্মসমীক্ষা।
শুরু হয়েছিল পোখরা থেকে। শান্ত ফেওয়া লেকের ধারে বসে সে যেন আবিষ্কার করেছিল—প্রকৃতির নিঃশব্দতা অনেক সময় প্রেমের ভাষা হয়ে ওঠে। সেখান থেকেই শুরু এক অজানা টানের দিকে, এক অন্তর্জাগতিক অভিযাত্রা।
উচ্চতাজনিত অসুস্থতা, হিমশীতল বাতাস, আর শরীরের ক্লান্তি—সব মিলিয়ে মনে হচ্ছিল যেন এক গভীর একাকীত্বের মধ্যে সে হাঁটছে। তবুও, ছোট্ট একটি তিব্বতীয় মন্দিরে বসে তার মনে হয়েছিল: “যাকে ভালোবাসি, সে হয়তো দূরে—তবুও তার উপস্থিতি আমার নিঃশ্বাসে মিশে আছে। ঠিক এই বাতাসের মতো।”
১৭,৭৬৯ ফুট উচ্চতায় পৌঁছানো—যেখানে শরীর বারবার থেমে যেতে চায়, কিন্তু মন বলে—“আরো এক ধাপ।” তার ভাষায়, এটা ছিল ঠিক প্রেমের মতো—যেখানে সব কষ্ট পেরিয়ে, এক মুহূর্ত আসে আত্মিক তৃপ্তির; চোখে জল, ঠোঁটে হাসি, আর এক নির্ভার অনুভব: ‘সে পাশে নেই, তবুও যেন অনুভব করি—সে আমার মধ্যে রয়েছে, আমার পথচলায়।’
ভালোবাসা কি হারিয়ে গেছে? না। ভালোবাসা এখনো আছে—ফেসবুক পোস্টে, হোয়াটসঅ্যাপের অপেক্ষায়, কিংবা পাহাড়ের চূড়ায় নিঃশ্বাস নিতে নিতে। শুধু আমরা বুঝতে পারছি না তার নতুন রূপ। আমরা এখনো বলি, ‘তুমি আমার মনে সারাক্ষণ।’ কিন্তু সেটা হয়তো বলা হয় না সরাসরি—লিখে রাখি কোথাও, চুপচাপ মনে রাখি, অথবা গোপনে এক পাহাড়ি ট্রেকের পথে তাকে স্মরণ করি।
‘তুমি নেই—তবু আছো। কোনো ছবিতে নয়, কোনো শব্দে নয়, এমনকি কোনো চিঠির পাতায়ও না। তুমি আছো আমার নিঃশ্বাসে, আমার সকাল আর রাতের মাঝখানে…’
এই প্রেমের অনুভব একা কারো নয়, এটা আমাদের সময়ের অভ্যন্তরীণ গল্প। এক সময়, এক মানুষ, এক ভালোবাসা—আর এক জীবনের রূপান্তর।
রহমান মৃধা, সাবেক পরিচালক, ফাইজার, সুইডেন। Rahman.Mridha@gmail.com