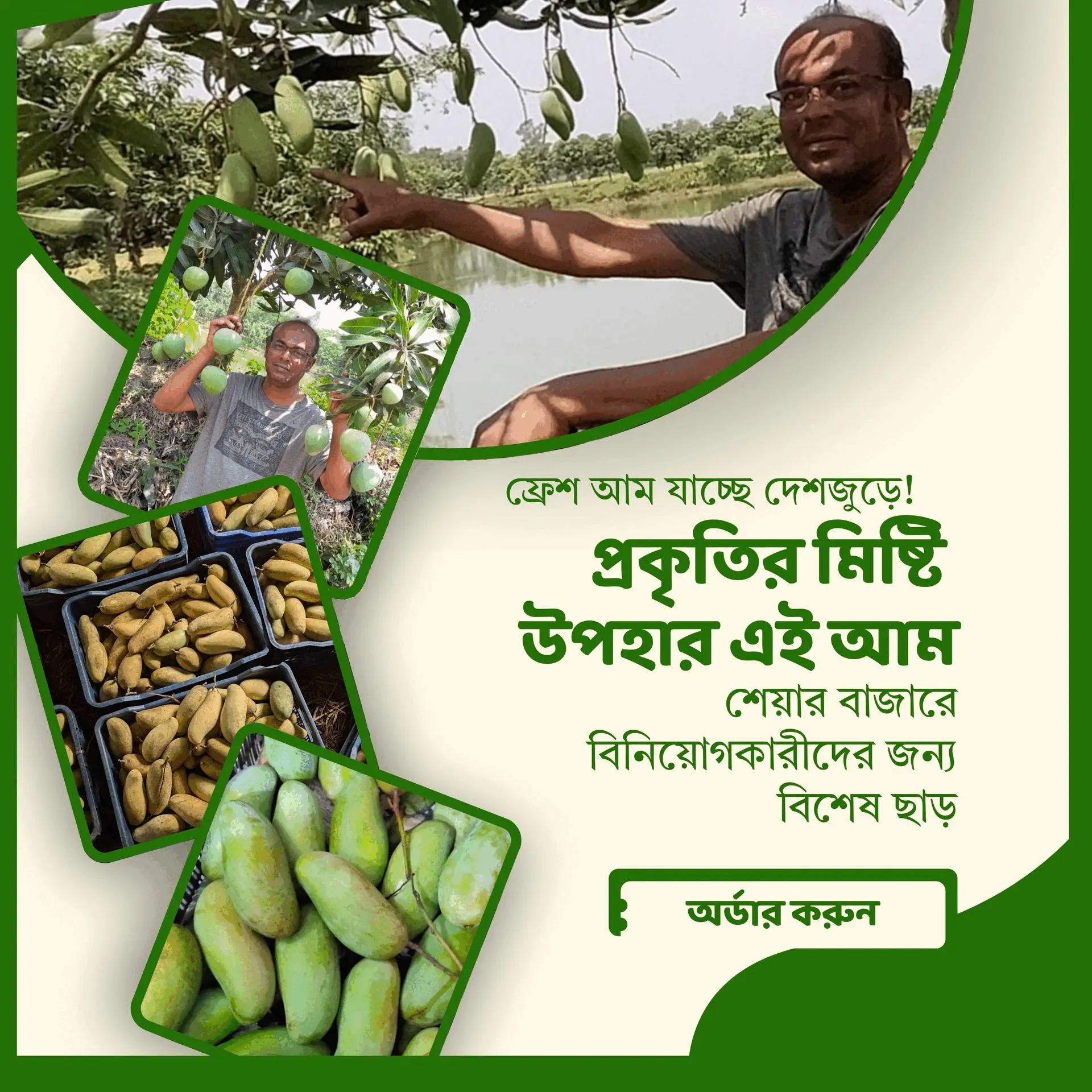মত দ্বিমত
বিশেষায়িত শিক্ষক প্রশিক্ষণ বিশ্ববিদ্যালয়: সময়ের দাবি ও জাতির ভবিষ্যতের প্রয়োজন
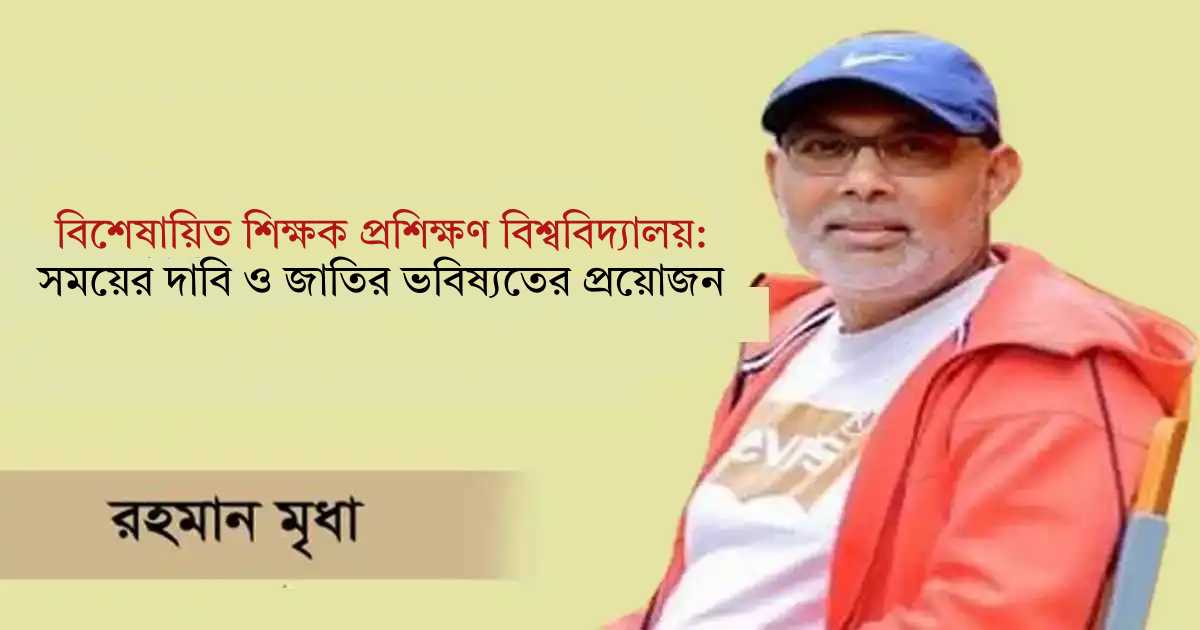
শিক্ষা শুধু তথ্য গ্রহণের প্রক্রিয়া নয়, বরং মানুষ গড়ার সবচেয়ে শক্তিশালী উপায়। একটি জাতি তার ভবিষ্যৎ যেমন নির্ধারণ করে তার অর্থনীতি ও রাজনীতির মাধ্যমে, ঠিক তেমনি — এমনকি তারও আগে — শিক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমে। কিন্তু এই ব্যবস্থার সফলতা নির্ভর করে যাঁদের হাতে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালিত হয়, সেই শিক্ষকদের ওপর। আর সুশিক্ষার কারিগর হতে হলে শিক্ষককে শুধু পাঠদানে দক্ষ হলেই চলে না, তাঁর দরকার গভীর মনোবিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান, নৈতিকতা ও নেতৃত্বের জ্ঞান। এই দক্ষতা অর্জনের জন্য প্রয়োজন বিশেষায়িত শিক্ষক প্রশিক্ষণ বিশ্ববিদ্যালয় – একটি পূর্ণাঙ্গ প্রতিষ্ঠান, যেখানে শিক্ষক গঠনের সব স্তর কাঠামোবদ্ধ ও গবেষণাভিত্তিক হবে।
কেন বিশেষায়িত প্রশিক্ষণ বিশ্ববিদ্যালয় দরকার?
আজকের বিশ্ব চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের মুখোমুখি। প্রযুক্তির ছোঁয়ায় প্রতিদিন বদলে যাচ্ছে সমাজ ও শিক্ষার ধরন। শিক্ষার্থীরা এখন কেবল পাঠ্যবই নয়, বরং ইউটিউব, গুগল, সোশ্যাল মিডিয়া থেকে প্রতিনিয়ত তথ্য নিচ্ছে। এই বাস্তবতায় একজন শিক্ষককে হতে হয় শুধু বই পড়ানো ব্যক্তি নয়, বরং একজন নেতা, কোচ, গাইড এবং জীবনদর্শনের নির্মাতা। এই রূপান্তরের জন্য প্রয়োজন এমন একটি প্রশিক্ষণ প্ল্যাটফর্ম, যা শিক্ষককে পরিপূর্ণভাবে প্রস্তুত করবে।
একটি কাঠামোবদ্ধ শিক্ষা প্রক্রিয়ার চার স্তর: একটি রূপক ধারণা
আমরা যদি শিক্ষাকে একটি গাছ রোপণের প্রক্রিয়ার সঙ্গে তুলনা করি, তাহলে বুঝতে পারি:
১. বীজ বপন (প্রাথমিক শিক্ষা)
২. চারা রোপণ (মাধ্যমিক শিক্ষা)
৩. গাছ লাগানো (কলেজ পর্যায়)
৪. ফল ফলানো (বিশ্ববিদ্যালয় স্তর)
এই পুরো প্রক্রিয়া সফলভাবে পরিচালনার জন্য দরকার একজন “প্রক্রিয়ার পরিচালক” বা “শিক্ষা নীতিনির্ধারক”, যিনি জানবেন কী ধরনের শিক্ষক কোথায় প্রয়োজন, কীভাবে নিয়োগ ও মূল্যায়ন করতে হবে, এবং কীভাবে মাইন্ডসেট গঠন করতে হবে।
স্তরভিত্তিক বিশ্লেষণ: শিক্ষক গঠনের ঘাটতি ও করণীয়
১. প্রাথমিক স্তর: মূল চরিত্র গঠনের সময়
এই স্তরে শিশুরা অনুকরণ ও অনুসরণের মাধ্যমে শেখে। এখানকার শিক্ষকের প্রধান কাজ শিশুর আচরণ পর্যবেক্ষণ, উৎসাহ দেওয়া এবং তাদের ক্রিয়েটিভিটি গড়ে তোলা। এজন্য শিক্ষককে জানতে হবে মনোবিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান, আধুনিক প্রযুক্তি, এমনকি পরিবেশ ও নৈতিকতা।
বাস্তবতা:
• অধিকাংশ শিক্ষক এই স্তরের উপযোগী প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত নন।
• শিক্ষক নিয়োগে গুণগত যাচাই অনেক ক্ষেত্রেই অনুপস্থিত।
• মনিটরিং ও ফিডব্যাক ব্যবস্থায় দুর্বলতা রয়েছে।
প্রস্তাব:
• বাধ্যতামূলক মানসিক স্বাস্থ্য ও শিশু বিকাশ বিষয়ক প্রশিক্ষণ
• গেম-ভিত্তিক ও লার্নিং-বাই-ডুইং মডেল ব্যবহার
• নির্ধারিত মূল্যায়ন চক্রে শিক্ষক প্রশিক্ষণ আপডেট
২. মাধ্যমিক স্তর: পরিচয় ও পথ নির্ধারণের সময়
কৈশোরে একজন শিক্ষার্থীর মানসিক ও শারীরিক পরিবর্তন হয় নাটকীয়ভাবে। এই সময়ে শিক্ষককে হতে হয় গাইড, অভিভাবক ও বন্ধু। শুধু পাঠ্যবিষয়ের শিক্ষকতা নয়, বরং জীবনের নীতিনির্ধারক হয়ে উঠেন শিক্ষক।
বাস্তবতা:
• অধিকাংশ শিক্ষক এই মানসিক স্তরের প্রয়োজনীয়তা বোঝেন না।
• শিক্ষার্থীদের ডিজিটাল আসক্তি, অবসাদ ও মনোযোগহীনতা বেড়েছে।
• প্রশিক্ষণের অভাবে শিক্ষকগণ এই চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে পারছেন না।
প্রস্তাব:
• ডিজিটাল লিটারেসি ও কাউন্সেলিং প্রশিক্ষণ বাধ্যতামূলক
• ভার্চুয়াল ম্যানেজমেন্ট এবং ক্লাসরুম সাইকোলজি অন্তর্ভুক্তি
• শিক্ষার্থীর মানসিক স্বাস্থ্য পর্যবেক্ষণে সিস্টেম তৈরি
৩. কলেজ স্তর: জীবনের গতি নির্ধারণের সময়
এই সময় একজন শিক্ষার্থী নিজের ভবিষ্যৎ পেশা, আদর্শ ও জীবনদর্শন নির্ধারণ করে। ভালো গাইডেন্সের অভাবে শিক্ষার্থী হারিয়ে যেতে পারে।
বাস্তবতা:
• শিক্ষকদের সঙ্গে শিক্ষার্থীর বোঝাপড়া অনেক সময় দূরত্বপূর্ণ।
• পারিবারিক, রাজনৈতিক বা সামাজিক চাপ শিক্ষার্থীদের বিভ্রান্ত করে।
• রেগুলার ফিডব্যাক এবং সহানুভূতিশীল যোগাযোগের ঘাটতি রয়েছে।
প্রস্তাব:
• রিলেশনশিপ ব্যাসেড লার্নিং মডেল চালু করা।
• শিক্ষক-শিক্ষার্থী বোঝাপড়ার জন্য মাসিক কাউন্সেলিং সেশন।
• দায়িত্ব-কেন্দ্রিক শিক্ষা কৌশল বাস্তবায়ন।
৪. বিশ্ববিদ্যালয় স্তর: জীবনের চূড়ান্ত প্রস্তুতি
এটাই হলো শিক্ষার প্যাকেজিং পর্ব। এখান থেকে শিক্ষার্থী পেশাগত জগতে প্রবেশ করে। তারা শুধু একজন কর্মচারী নয়, বরং একজন দায়িত্বশীল নাগরিক হয়ে উঠবে কিনা, তা নির্ভর করে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার উপর।
বাস্তবতা:
• অনেক ক্ষেত্রেই শিক্ষকের ভূমিকা সীমাবদ্ধ সিলেবাসে।
• শিক্ষার্থীরা ‘পারফর্মেন্স’ শেখে না, শেখে শুধু ‘পরীক্ষা পাশ’।
• সিভিক দায়িত্ববোধ, ক্রিটিক্যাল থিংকিং বা আত্মউন্নয়ন শেখানো হয় না।
প্রস্তাব:
• শিক্ষকের জন্য লাইফ স্কিল ও লিডারশিপ প্রশিক্ষণ
• ইন্ডাস্ট্রি-একাডেমিয়া পার্টনারশিপ
• শিক্ষার্থীদের দায়িত্বশীল নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার জন্য বিশেষ কোর্স
বিশেষায়িত শিক্ষক প্রশিক্ষণ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রয়োজনীয় বৈশিষ্ট্য
১. জাতীয় পর্যায়ের মানদণ্ডে শিক্ষক প্রশিক্ষণ কাঠামো
২. প্রত্যেক স্তরের জন্য আলাদা ট্র্যাক ও স্পেশালাইজেশন
৩. শিক্ষাদান ছাড়াও রিসার্চ, ডেভেলপমেন্ট ও মনিটরিং সেল
৪. ই-লার্নিং এবং ভার্চুয়াল ক্লাসরুম পরিচালনায় দক্ষতা
৫. জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে শিক্ষক এক্সচেঞ্জ প্রোগ্রাম
৬. শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে সমন্বিত নিয়ন্ত্রণ ও মূল্যায়ন ব্যবস্থা
দুর্নীতিমুক্ত শিক্ষা ব্যবস্থার দাবি
শিক্ষা ব্যবস্থায় কোনো প্রকার দুর্নীতি একেবারেই গ্রহণযোগ্য নয়। শিক্ষক নিয়োগ, প্রশিক্ষণ, পদোন্নতি কিংবা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালনার প্রতিটি স্তরে যদি স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত না করা যায়, তাহলে কোনো শিক্ষাব্যবস্থাই সফল হতে পারে না। দুর্নীতিগ্রস্ত একজন শিক্ষক মানেই ভবিষ্যৎ প্রজন্মের নৈতিক অধঃপতনের দায়। কাজেই এই প্রস্তাবিত বিশেষায়িত শিক্ষক প্রশিক্ষণ বিশ্ববিদ্যালয়কে হতে হবে সম্পূর্ণ দুর্নীতিমুক্ত, স্বচ্ছ এবং নৈতিকতা-ভিত্তিক একটি মডেল প্রতিষ্ঠান—যেখানে মূল্যায়ন হবে দক্ষতার ভিত্তিতে, নিয়োগ হবে যোগ্যতার ভিত্তিতে, এবং পরিচালনা হবে সততার ভিত্তিতে। এটাই হতে হবে শিক্ষার প্রথম শর্ত।
অব্যবহৃত জনসম্পদের ব্যর্থতা
আজ যখন গোটা বিশ্ব দক্ষ জনশক্তির খোঁজে হন্যে হয়ে ফিরছে, তখন বাংলাদেশ, যা বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ যুব জনগোষ্ঠীর দেশ, তার বিশাল ম্যানপাওয়ারকে কাজে লাগাতে ব্যর্থ হচ্ছে — শুধু সুপরিকল্পিত শিক্ষা ও দক্ষতা উন্নয়ন অবকাঠামোর অভাবে। এই ব্যর্থতা শুধু অর্থনৈতিক নয়, এটি একটি কৌশলগত ও জাতীয় ব্যর্থতা। সুশিক্ষিত, প্রশিক্ষিত ও নেতৃত্ব-সক্ষম নাগরিক তৈরি না করতে পারলে, এই জনশক্তি একসময় বোঝায় পরিণত হতে পারে। কাজেই এই সংকট থেকে উত্তরণের একমাত্র উপায় হলো—একটি শক্তিশালী, দক্ষতানির্ভর ও দৃষ্টিভঙ্গিমূলক শিক্ষা কাঠামো গড়ে তোলা, যার কেন্দ্রে থাকবে বিশেষায়িত শিক্ষক প্রশিক্ষণ।
শিক্ষকের অভিজ্ঞতা: প্রশিক্ষণ ছাড়া পাঠদানের বাস্তব সংকট
মফস্বলের এক মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেন মাজেদা বেগম। বিষয় ইংরেজি, কিন্তু কোনো ধরনের প্রফেশনাল শিক্ষক প্রশিক্ষণ বা ক্লাসরুম ম্যানেজমেন্ট নিয়ে তাঁর কোনো শিক্ষাই নেই। তিনি নিজেই বলেন, “আমার বিষয়ভিত্তিক জ্ঞান থাকলেও কীভাবে পড়াতে হবে, ছাত্রদের মনোযোগ ধরে রাখতে হবে, কীভাবে ক্লাসে জটিল বিষয় সহজভাবে উপস্থাপন করতে হবে—এসব শেখার কোনো সুযোগ পাইনি।” ফলাফল দাঁড়িয়েছে, ক্লাসে গণ্ডগোল বাড়ছে, ছাত্ররা বিষয় বুঝছে না, আগ্রহ হারাচ্ছে। এটা কেবল মাজেদা বেগমের গল্প নয়, দেশের হাজারো শিক্ষকের গল্প। শিক্ষার শিকড় যখন দুর্বল থাকে, তখন ফল আসলেও তা হয় অপুষ্ট। বিশেষায়িত শিক্ষক প্রশিক্ষণ না থাকলে আমরা এমন অপুষ্ট ফলেই সন্তুষ্ট থাকতে বাধ্য হব।
ঠিক এই বাস্তবতায় দাঁড়িয়ে, বাংলাদেশের একটি গ্রামের স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসায় পাঠদান করছেন সুইডেনপ্রবাসী অধ্যাপক ড. মান্নান মৃধা (KTH, বায়োমেডিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং)। তাঁর নিজ জেলা মাগুরার নহাটা গ্রামে তিনি নিয়মিত ফিরে আসেন, ছাত্র-শিক্ষকদের সঙ্গে কথা বলেন—“কী শিক্ষা, কেন শিক্ষা, কীভাবে শিক্ষা”—এই তিনটি প্রশ্নের জীবনঘনিষ্ঠ উত্তর খোঁজার জন্য। কীভাবে শিক্ষায় ‘মজা’ ঢুকিয়ে শেখাকে আনন্দময় করা যায়—তা তিনি নিজ হাতে দেখিয়ে দেন। মান্নান মৃধার এই কাজ নিছক প্রবাসী উদ্যোগ নয়; বরং এটি সুইডেন ও ফিনল্যান্ডের বিশেষায়িত শিক্ষাব্যবস্থার বাস্তব প্রয়োগ, যেখানে শিক্ষকতা শুধু পেশা নয়, সমাজ গঠনের দায়িত্ব।
ফিনল্যান্ডে শিক্ষক হতে হলে মাস্টার্স ডিগ্রির পাশাপাশি কাঠামোবদ্ধ প্রশিক্ষণ বাধ্যতামূলক। শেখাতে জানার পাশাপাশি জানতে হয় ছাত্রদের মনস্তত্ত্ব, শেখানোর কৌশল, এবং শিক্ষাকে জীবনঘনিষ্ঠ করে তোলার উপায়। ফিনল্যান্ড ও সুইডেনে শিক্ষকরা কেবল শ্রেণিকক্ষে পাঠদান করেন না, তাঁরা গবেষক ও নীতিনির্ধারকদের অংশীদার। সমাজে তাঁদের সম্মান রাষ্ট্রদূতের সমান। পরীক্ষার সংখ্যা সেখানে কম, কিন্তু শেখা গভীর। এই শিক্ষাব্যবস্থার মূল দর্শন হলো—“শিক্ষক গড়াই শিক্ষার প্রথম কাজ।” একজন শিক্ষককে হতে হয় নেতৃত্বদানে সক্ষম, মূল্যবোধসম্পন্ন এবং চিন্তার দিশারি। এই নীতিগত বিনির্মাণেই দেশগুলো এমন একটি মানবিক ও দক্ষ নাগরিক তৈরির প্ল্যাটফর্ম গড়ে তুলতে পেরেছে—যেখানে পরীক্ষায় নয়, মানুষ তৈরিতে জোর দেওয়া হয়। বাংলাদেশ যদি শিক্ষার মানে মৌলিক পরিবর্তন আনতে চায়, তাহলে এই মডেল শুধু অনুকরণ নয়, বরং উদ্দীপনা হয়ে উঠতে পারে।
জাতি গঠনের কারিগর যদি হয় শিক্ষক, তবে শিক্ষকের গড়ন হবে জাতিগঠনের প্রথম কাজ। আজ প্রয়োজন সেই প্রতিষ্ঠান, যা শিক্ষককে গড়ে তুলবে নতুন যুগের উপযোগী করে — চিন্তা, দক্ষতা এবং মূল্যবোধের সমন্বয়ে। এ জন্য বিশেষায়িত শিক্ষক প্রশিক্ষণ বিশ্ববিদ্যালয় শুধু প্রয়োজন নয়, বরং এখন এটি জাতীয় অগ্রাধিকারের বিষয় হওয়া উচিত। কারণ, সুশিক্ষা ছাড়া মনুষ্যত্ব গড়ে ওঠে না — আর সুশিক্ষার কারিগর তৈরি না হলে উন্নয়নের ভিত্তিই দুর্বল থেকে যাবে।
রহমান মৃধা, গবেষক ও লেখক
(সাবেক পরিচালক, ফাইজার সুইডেন)
Rahman.Mridha@gmail.com

মত দ্বিমত
বাংলাদেশের রাজনীতিতে অনুশোচনার অভাব ও নতুন জাগরণের ডাক
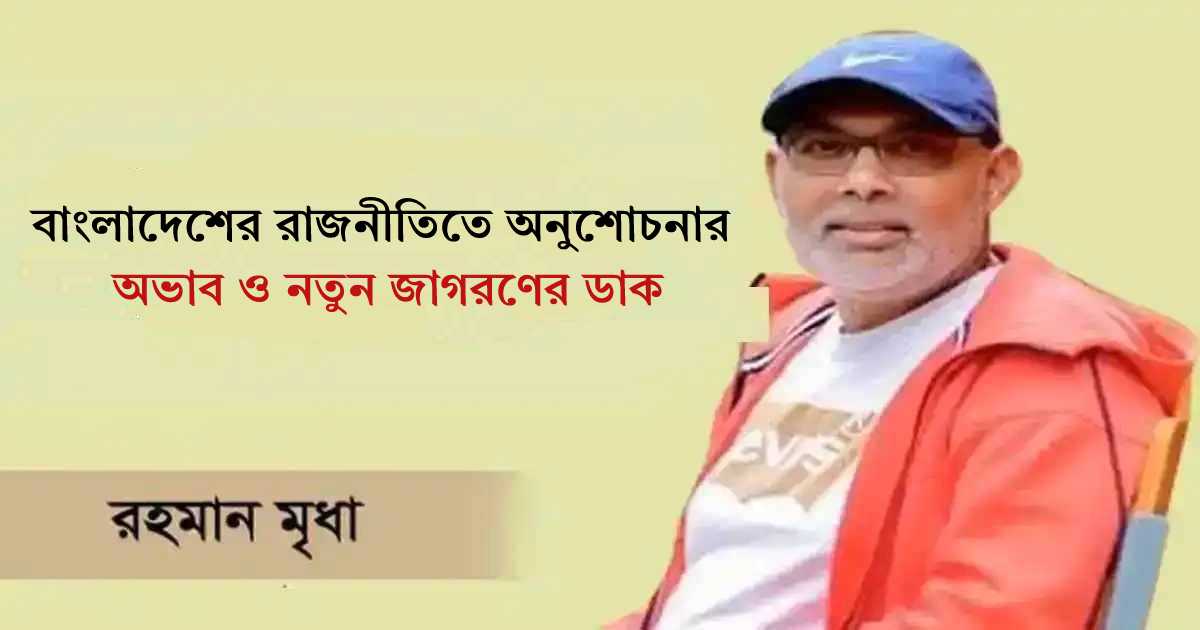
আমরা কম বেশি ভুল করি, করি না? কিন্তু আমাদের অনুসচনা হয় না কেন? বাংলাদেশ এবং বাঙালি সহ আরো কিছু মানুষের বসবাস এই দেশটিতে। যেভাবেই হোক দেশটা দীর্ঘ ৯ মাসেই সেই ৭১-এ স্বাধীন হয়ে গেলো। শেখ মুজিব দেশে ফিরলেন, নিজ দায়িত্বে প্রেসিডেন্ট হলেন যদিও চারদিকের চামচারা নানা ধরনের রাজনৈতিক সুবিধা নিতে নির্লজ্জের মতো কেউ কিছু বলেনি। সম্ভবত বিনা সফতেই নিজ দায়িত্বে প্রেসিডেন্ট হলেন এবং পরে আবু সাঈদ চৌধুরীকে প্রেসিডেন্ট ঘোষণা করে নিজে প্রধানমন্ত্রী হলেন। তারপর কোন ফাঁকে জাতির পিতায় ভূষিত হলেন এবং বঙ্গবন্ধু হলেন। শেষ পর্যায়ে একদলীয় শাসন চালু করে রাষ্ট্রকে ব্যক্তিকেন্দ্রিক পথে নিয়ে গেলেন।
এরপর এলো জিয়াউর রহমানের উত্থান। মুক্তিযোদ্ধা সেনা অফিসার হিসেবে ক্ষমতায় এসে তিনি রাষ্ট্রকে নতুনভাবে গড়তে চাইলেন। তাঁর উদ্যোগে বিএনপি প্রতিষ্ঠিত হয়, বহুদলীয় রাজনীতি ফিরে আসে। কিন্তু ক্ষমতার খেলায় তাঁর শাসনও স্বচ্ছতা ও ন্যায়বিচারের প্রশ্নে বিতর্কিত রয়ে যায়।
তারপর এলো হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদ। তিনি সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে ক্ষমতা দখল করে দীর্ঘদিন শাসন করেন। তাঁর সময়ে প্রশাসনিক অবকাঠামোর কিছু সংস্কার হলেও রাজনৈতিক সংস্কৃতির অবনতি ঘটে। দুর্নীতি, দলীয়করণ এবং গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলোর দুর্বলতা সেই সময়ে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পায়। এরশাদের শাসন আমাদের শেখায়—সামরিক শাসন কখনোই জনগণের প্রতিনিধিত্বশীল রাষ্ট্র গড়তে পারে না।
পরে এলো খালেদা জিয়া ও শেখ হাসিনার পালাবদলের দীর্ঘ ইতিহাস। দুই দলের ক্ষমতার দ্বন্দ্ব, দুর্নীতি, দলীয় স্বার্থসিদ্ধি ও প্রতিহিংসার রাজনীতিতে দেশ বারবার আঘাত পেয়েছে। এক সময় গণতন্ত্র কেবল ভোটের সংখ্যায় সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েছে, মানুষের অধিকার, ন্যায়বিচার ও সমতার প্রশ্ন পিছিয়ে গেছে।
এখানে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হলো—রাষ্ট্রের সশস্ত্র বাহিনীর ভূমিকা কী হওয়া উচিত? ইতিহাসে আমরা দেখেছি সেনাবাহিনী বারবার রাষ্ট্রক্ষমতায় হস্তক্ষেপ করেছে। অথচ একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে তাদের মূল দায়িত্ব হলো জাতীয় নিরাপত্তা রক্ষা, রাজনৈতিক ক্ষমতার ভারসাম্য ভাঙা নয়। ভবিষ্যতের জন্য শিক্ষা হলো—সশস্ত্র বাহিনীকে নিরপেক্ষ ও সাংবিধানিক কাঠামোর ভেতরে রাখতে হবে, যাতে তারা গণতন্ত্রকে রক্ষা করে, হুমকি না হয়।
এরপর এলো ড. ইউনূস নেতৃত্বাধীন অন্তবর্তীকালীন সরকার। তাঁদের দুটি উল্লেখযোগ্য সাফল্য হলো—প্রথমত, দেশটিতে গৃহযুদ্ধের সম্ভাবনা থাকলেও সেটি ঘটেনি। দ্বিতীয়ত, লুটপাট সত্ত্বেও দেশ দেউলিয়া হয়ে যায়নি। তবে প্রশাসনিক সংস্কার, সুশাসন প্রতিষ্ঠা ও রাজনৈতিক সংস্কৃতির রূপান্তরে তারা কার্যকর হতে পারেনি। এখন দেখার পালা তারা একটি সত্যিকারের সুষ্ঠু নির্বাচন আয়োজন করতে সক্ষম হন কিনা।
সবশেষে নতুন প্রজন্মের কথা আসছে। ২০২৪ সালে তারা দেশের মৌলিক অধিকার ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হয়েছিল। কিন্তু প্রশ্ন থেকে যায়—তারা কি সেই অধিকার ধরে রাখতে পারবে? তাদের নৈতিক মূল্যবোধ কি অতীতের নেতাদের থেকে ভিন্ন কিছু হবে? যদি না হয়, তবে আমরা আবারও একই অনুশোচনার চক্রে ঘুরপাক খেতে থাকব।
বাংলাদেশ রাষ্ট্রের ইতিহাসে নেতৃত্ব সংকট, গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার ব্যর্থতা এবং ক্ষমতাকেন্দ্রিক রাজনীতির পুনরাবৃত্তি আমাদের জাতীয় জীবনে আজ গভীর অনুশোচনার জন্ম দিয়েছে। শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্ব থেকে শুরু করে জিয়াউর রহমান, এরশাদ, খালেদা জিয়া এবং শেখ হাসিনার সময়কাল পর্যন্ত আমরা প্রত্যক্ষ করেছি—রাষ্ট্রের কাঠামো সংস্কারের পরিবর্তে ব্যক্তিকেন্দ্রিক ক্ষমতার চর্চা। যার ফলে প্রশাসন দুর্বল হয়েছে, সশস্ত্র বাহিনীকে কখনো রাজনৈতিকভাবে ব্যবহার করা হয়েছে, আবার কখনো তারা পর্দার আড়ালে নীতিনির্ধারণী প্রভাব বিস্তার করেছে।
রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে দীর্ঘদিন ধরে অবকাঠামোগত দুর্বলতা রয়ে গেছে। প্রশাসন রাজনৈতিক আনুগত্যের বন্দী হয়ে পড়েছে, যেখানে দক্ষতা, জবাবদিহিতা এবং স্বচ্ছতা অবহেলিত। একইভাবে, সশস্ত্র বাহিনীর ভূমিকা কী হওয়া উচিত এবং রাষ্ট্র পরিচালনায় তাদের প্রভাব কোথায় সীমিত থাকবে—সেই প্রশ্নের কোনো সুস্পষ্ট উত্তর আমরা পাইনি। ফলে রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা ও ক্ষমতার দ্বন্দ্ব বারবার জাতিকে গভীর সংকটে ফেলেছে।
অতএব, এখন দায়িত্ব নতুন প্রজন্মের। কিন্তু এ দায়িত্ব পালন সহজ নয়। কারণ বাস্তবতা হলো—আজকের তরুণদের একটি বড় অংশ বেকার। তাদের হাতে নেই পর্যাপ্ত ক্ষমতা, নেই দক্ষতা, নেই কর্মসংস্থানের নিশ্চয়তা। ফলে তারা সারাদিন রাজনৈতিক নেতাদের আশেপাশে ঘুরে বেড়ায়, কখনো ক্ষমতাসীনদের ছত্রছায়ায় দুর্নীতি ও লুটপাটে অংশ নেয়, আবার কখনো রাজনৈতিক হানাহানির বলি হয়। তাদের বেকারত্ব দূরীকরণে কোনো কার্যকর পরিকল্পনা নেই, কারণ দুর্নীতিবাজ সরকার টিকে থাকার স্বার্থে এই তরুণ সমাজকে ব্যবহার করছে নিজেদের ক্ষমতার খেলায়—ফলে দেশের বারোটা বাজছে।
আমি ভেবেছিলাম, অন্তবর্তী সরকারের নেতৃত্বে ড. ইউনূস অন্তত একটি জাতীয় কর্মসংস্থান পরিকল্পনা তৈরি করবেন, একটি সঠিক রোডম্যাপ দেখাবেন-যাতে তরুণ প্রজন্ম দক্ষতায়, সততায় এবং সৃজনশীলতায় জাতিকে এগিয়ে নিতে পারে। কিন্তু তিনি সেই কাজটিও করতে পারেননি।
বাংলাদেশের রাজনীতির দীর্ঘ ইতিহাস আমাদের এখন একটাই শিক্ষা দেয়—অনুশোচনা ছাড়া আমাদের পরিবর্তন হবে না। শেখ মুজিব থেকে জিয়া, এরশাদ থেকে খালেদা-হাসিনা পর্যন্ত প্রতিটি যুগে ভুল ছিল, অন্যায় ছিল। কিন্তু কোথাও প্রকৃত অনুশোচনা দেখা যায়নি। সেই কারণেই একই ভুল বারবার পুনরাবৃত্তি হয়েছে, এখনো হচ্ছে।
আমাদের সামনে একমাত্র করণীয় হলো-একটি জাতীয় পরিকল্পনা প্রণয়ন, যেখানে শিক্ষাকে কর্মসংস্থানের সঙ্গে যুক্ত করা হবে, তরুণদের জন্য প্রযুক্তি ও শিল্পভিত্তিক দক্ষতা উন্নয়নের সুযোগ তৈরি করা হবে, এবং নৈতিক ভিত্তির ওপর দাঁড় করিয়ে রাষ্ট্রকে পুনর্গঠনের কাজ শুরু করা হবে।
নতুন প্রজন্ম যদি সেই সঠিক দিকনির্দেশনা পায়, তবে তারা শুধু নিজেদের নয়, জাতির ভবিষ্যৎও আলোকিত করতে পারবে। অন্যথায়, আমরা বারবার একই প্রশ্নেই ফিরে যাব—এতো কিছুর পরেও আমরা আমাদের অনুশোচনা করি না কেন?
অতীত থেকে শিক্ষা নিয়ে, অনুশোচনার সংস্কৃতি গড়ে তুলে, আমরা যদি একটি নৈতিক ও সুশাসনভিত্তিক রাষ্ট্র গড়তে পারি, তবে জাতির ভবিষ্যৎ আলোকিত হবে। কিন্তু যদি তা না হয়, তবে আমরা শুধু প্রশ্ন করেই যাব—এতো কিছুর পরেও দেশের প্রায় ১৬ কোটি মানুষের জীবনমান উন্নয়নের মিথ্যা প্রতিশ্রুতি বারবার দেওয়া হয়েছে এবং হচ্ছে, কিন্তু কই—তাদের ভাগ্যের কোনো পরিবর্তন তো হয়নি, হচ্ছে না! তারপরও আমাদের কোনো অনুশোচনা নেই, কিন্তু কেন?
রহমান মৃধা
গবেষক ও লেখক
(সাবেক পরিচালক, ফাইজার, সুইডেন)
Rahman.Mridha@gmail.com
মত দ্বিমত
স্বাধীনতার হুমকির মুখে গণমাধ্যম
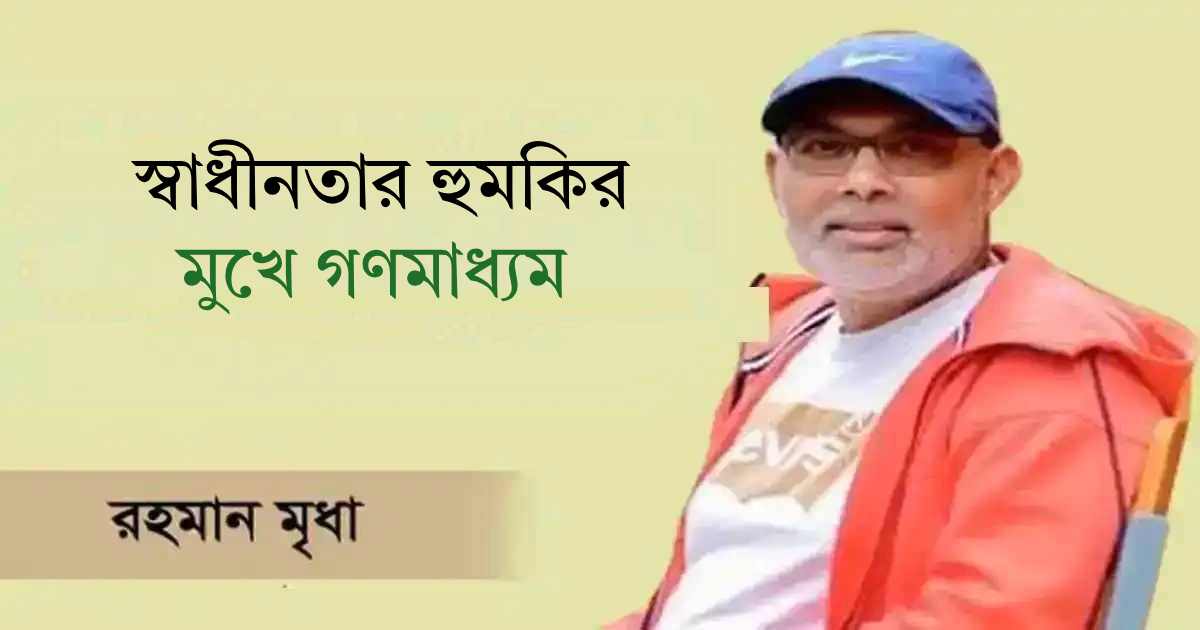
বিশ্বব্যাপী গণমাধ্যম স্বাধীনতার ওপর যখন প্রবল চাপ, তখন বাংলাদেশে পরিস্থিতি প্রায় মৃত্যুর দ্বারপ্রান্তে। স্বাধীন সাংবাদিকতার মেরুদণ্ড ভেঙে দেওয়া হয়েছে রাজনৈতিক আনুগত্য, ভীতি ও তোষামোদে। বাংলাদেশের সাংবাদিকরা আজ সত্য প্রকাশ করতে ভুলে গেছেন—বরং সরকারের প্রশংসা করাই হয়ে গেছে প্রধান কাজ। শেখ হাসিনা ক্ষমতায় থাকাকালীন, সাংবাদিকদের একটি অংশ প্রকাশ্যে বলতেন—‘সমালোচনা নয়, প্রশংসা করতেই এসেছি।’ এই মানসিকতা গণতন্ত্রের জন্য শুধু ক্ষতিকর নয়, এটি রাষ্ট্রের মৌলিক স্বচ্ছতাকেও ধ্বংস করেছে।
আজও সেই একই চক্র সাংবাদিকতা করছে—যারা সরকারের সমালোচনা করতে ভয় পায়, কারণ তারা জানে, টেন্ডার, বিজ্ঞাপন কিংবা পৃষ্ঠপোষকতা বন্ধ হয়ে যাবে যদি চাটুকারিতার বাইরে পা বাড়ানো হয়। প্রশ্ন হলো—বাংলাদেশে যদি কেউ ‘সুইডেনের আদর্শ’ বলে একটি মডেল প্রস্তাব করে, সেটি কি এই মানসিকতার মধ্যে কার্যকর হতে পারবে?
বাংলাদেশের বাস্তবতা হলো—
সংবাদমাধ্যমের মালিকানা: অধিকাংশ বড় মিডিয়া প্রতিষ্ঠানের মালিক রাজনৈতিক বা ব্যবসায়িক স্বার্থে জড়িত।
সম্পাদকীয় স্বাধীনতার অভাব: সম্পাদকরা অনেক ক্ষেত্রে নিজেরা সেন্সরশিপ প্রয়োগ করেন, যাতে ক্ষমতাসীনদের বিরাগভাজন না হতে হয়।
রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ ও আইনি অস্ত্র: ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনসহ নানা ধারা সাংবাদিকদের ভয়ভীতি প্রদর্শনের জন্য ব্যবহৃত হয়।
পাঠকের আস্থা কমে যাওয়া: মানুষ জানে, সংবাদপত্র অনেক সময়ই ক্ষমতাবানদের হাতের কণ্ঠস্বর, জনগণের নয়।
এই পরিস্থিতিতে বাংলাদেশের গণতন্ত্র ও রাষ্ট্র কাঠামো যদি সত্যিই পুনর্গঠিত করতে হয়, তাহলে শুধু আইন নয়—মানসিকতার পরিবর্তন অপরিহার্য। আর এজন্য প্রয়োজন সুইডেনের মতো শক্তিশালী ও স্বাধীন পাবলিক সার্ভিস মিডিয়া মডেল।
সুইডেনের উদাহরণ: গণতন্ত্রের রক্ষাকবচ
সুইডেনে পাবলিক সার্ভিস সম্প্রচার প্রতিষ্ঠান—সুইডিশ টেলিভিশন (SVT), সুইডিশ রেডিও (SR) এবং শিক্ষামূলক রেডিও (UR)—আইন দ্বারা সুরক্ষিত, রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ থেকে মুক্ত এবং সরাসরি জনগণের কাছে জবাবদিহিমূলক। এ প্রতিষ্ঠানগুলো পরিচালিত হয় Radio and Television Act (2010:696) অনুযায়ী।
মূল বৈশিষ্ট্য:
আইনের সুরক্ষা: কোনো সরকারি কর্তৃপক্ষ সম্প্রচারের কনটেন্টে হস্তক্ষেপ করতে পারবে না—এটি আইনে স্পষ্টভাবে বলা আছে।
আর্থিক স্বাধীনতা: ২০১৯ সাল থেকে কর-ভিত্তিক পাবলিক সার্ভিস ফি চালু হয়েছে, যা Förvaltningsstiftelsen för SR, SVT och UR নামের একটি স্বাধীন ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে পরিচালিত হয়।
নিরপেক্ষতা ও বৈচিত্র্য: সংখ্যালঘু ভাষা, প্রতিবন্ধীদের জন্য কনটেন্ট, শিশু-কিশোরদের জন্য শিক্ষা ও সংস্কৃতি ভিত্তিক অনুষ্ঠান ইত্যাদি তাদের কাজের অংশ।
জনগণের জবাবদিহি ব্যবস্থা:
১. অভিযোগ দাখিল: যে কেউ সুইডিশ প্রেস ও ব্রডকাস্টিং অথরিটি (MPRT)-তে অভিযোগ করতে পারে।
২. সরাসরি মতামত প্রদান: SVT, SR, UR-এর ওয়েবসাইটে অভিযোগ ও প্রতিক্রিয়া জানানোর সুযোগ রয়েছে।
৩. বার্ষিক প্রতিবেদন: কর্মদক্ষতা ও দায়িত্বপালনের অগ্রগতি সংসদে প্রকাশ ও জনগণের জন্য উন্মুক্ত করা হয়।
৪. সংসদীয় শুনানি: খোলামেলা আলোচনায় জনগণের মতামত গুরুত্ব পায়, কিন্তু কনটেন্টে রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ হয় না।
বাংলাদেশের জন্য শিক্ষা
যদি বাংলাদেশে সুইডেনের মতো একটি মডেল গড়ে তোলা যায়, তবে—
•সাংবাদিকরা সরকারের ভয় ছাড়াই কাজ করতে পারবেন।
•জনগণের আস্থা ফিরবে।
•গুজব, প্রোপাগান্ডা ও বাণিজ্যিক চাপ কমে যাবে।
•সংখ্যালঘু ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর কণ্ঠস্বর শোনা যাবে।
কিন্তু এই মডেল কার্যকর করতে হলে শুধু আইন নকল করলেই চলবে না—প্রথমে সাংবাদিকতা থেকে চামচামি ও আত্মসমর্পণ দূর করতে হবে। গণমাধ্যমকে জনগণের জন্য, জনগণের হাতে ফিরিয়ে দিতে হবে।
বাস্তবতার কঠিন মুখোমুখি
একটি সুন্দর উদাহরণ দেখানো সহজ, কিন্তু বাস্তবে তা প্রয়োগের জন্য দরকার একটি শক্ত ভিত্তি। সুইডেনের বর্তমান গণতান্ত্রিক কাঠামো গড়ে উঠেছে—
•মজবুত অর্থনীতি
•উচ্চমানের শিক্ষা ব্যবস্থা
•সামাজিক নিরাপত্তা নেটওয়ার্ক
•সীমিত জনসংখ্যা ও কার্যকর প্রশাসনিক কাঠামো
•উচ্চ নৈতিক মূল্যবোধ (Moral Values)
এবং—সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ—রাজকীয় প্রথা ভেঙে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় রূপান্তরের দীর্ঘ রাজনৈতিক যাত্রা।
বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে এর মানে দাঁড়ায়—দুর্নীতি, অনিয়ম, পারিবারিক একচ্ছত্র শাসন, বিচারহীনতার সংস্কৃতি এবং ক্ষমতার অপব্যবহারের বিরুদ্ধে লড়াই ছাড়া সুইডেনের মডেল শুধু কাগজে থাকবে, বাস্তবে নয়। তাই গণমাধ্যম সংস্কারের পাশাপাশি গোটা রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার ইনার ইঞ্জিনিয়ারিং—অর্থাৎ জনগণের মধ্যে নৈতিকতা, জবাবদিহি ও সচেতনতার সংস্কার—শুরু করতে হবে।
স্বচ্ছ গণতন্ত্র কেবল আইনের মাধ্যমে নয়, বরং জনগণের মানসিকতা ও অংশগ্রহণের মাধ্যমেই প্রতিষ্ঠিত হয়-এই সাহসী কথাটি আমি বলতে পারলাম শুধু এই জন্যই, আমি দীর্ঘ চল্লিশ বছর ধরে সুইডেনে বেস্ট প্র্যাকটিস করছি এসবের ওপরে।
রহমান মৃধা, সাবেক পরিচালক, ফাইজার, সুইডেন। Rahman.Mridha@gmail.com
মত দ্বিমত
চরকায় তেল ঢালুন, ভণ্ডদের বাজার শূন্য করুন
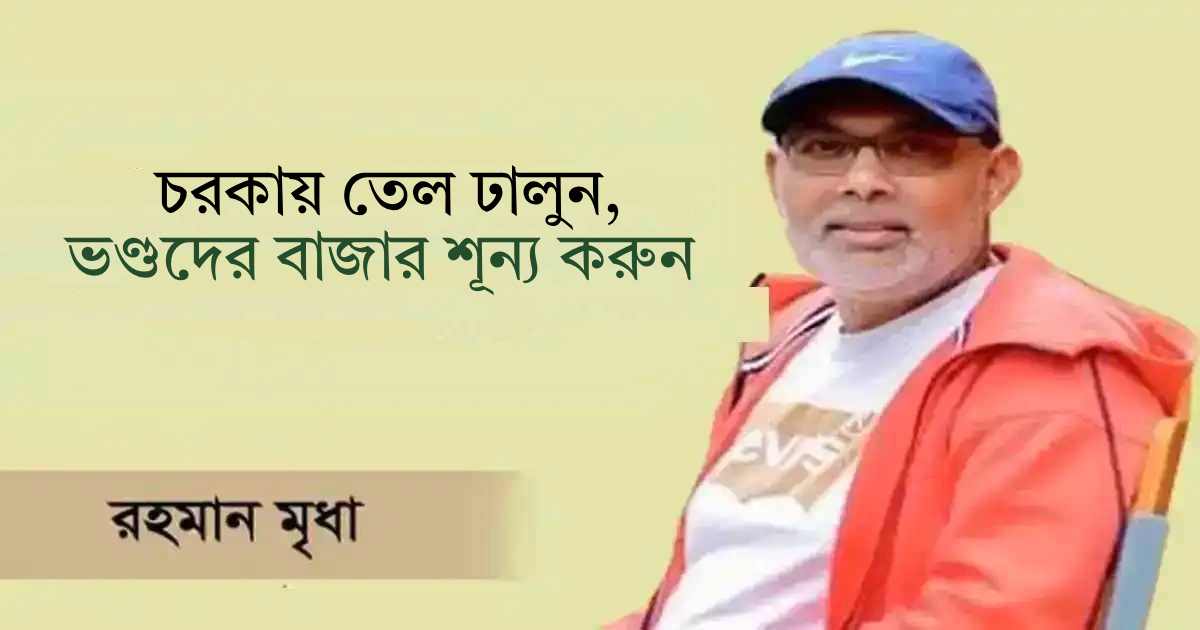
সবাই আমরা সোনার বাংলাকে ভালোবাসি—এই কথা শুনলে গর্ব হয়। কিন্তু প্রশ্ন হলো—আমরা কি সত্যিই সেই ভালোবাসার মর্ম বুঝি? ভালোবাসা তো শুধু মুখের বুলি নয়; সেটি অনুভব করতে হয়, কাজে প্রকাশ করতে হয়। ভালোবাসার প্রকৃত অর্থ হলো দেশের উন্নতি, মানুষের কল্যাণ, ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা, আর সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতা। কিন্তু আজকের বাস্তবতায় আমরা কি এসবের জন্য কিছু করছি? নাকি ভালোবাসার নাম করে দেশকে ভাগাভাগি করছি, বিদ্বেষ ছড়াচ্ছি, আর ব্যক্তিগত স্বার্থের পেছনে ছুটছি?
আমরা দেশকে ভালোবাসি বলি, কিন্তু নিজের জীবনযাপন, আচরণ, সিদ্ধান্ত—সবকিছু দিয়ে কি সেই ভালোবাসাকে সম্মান দিচ্ছি? নাকি দেশকে শুধু একটা ভৌগোলিক ঠিকানা ভাবছি, যেখানে টাকা রোজগার হয়, সুবিধা পাওয়া যায়, আর অন্যায়ের প্রতি চুপ থাকা যায়?
ভালোবাসা মানে শুধু আবেগ নয়—এটি দায়িত্ব। দায়িত্ব নিজের দেশকে ভালোবাসতে, তার উন্নয়নে কাজ করতে, অবিচার ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে দাঁড়াতে। আজ আমাদের অভাব নেই ভালোবাসার; আমাদের অভাব ভালোবাসার প্রমাণের।
তাহলে দেখা যাক, কোন কোন কুকর্ম সোনার বাংলাকে ভালোবাসার সাথে কোনোভাবেই মিলতে পারে না—
দুর্নীতি: জনগণের ঘামঝরা টাকায় হাত চালানো, দায়িত্বের দরজা বন্ধ করে ব্যক্তিগত ভান্ডার ভরাট করা।
সন্ত্রাসবাদ: ভয় আর আতঙ্কের ছায়া ফেলে জনজীবনকে জিম্মি করা।
চাঁদাবাজি: শ্রমজীবী মানুষের রক্ত চুষে নেওয়া।
কাজে ফাঁকি: কর্তব্য ফেলে দায়িত্বের কফিনে শেষ পেরেক ঠুকে দেওয়া।
গুজব ছড়ানো: মিথ্যার আগুন জ্বালিয়ে ঘৃণার বাতাস বইয়ে দেওয়া।
মিথ্যাচার: সত্যকে হত্যা করে অবিশ্বাসের রাজত্ব কায়েম করা।
গরিবের হক চুরি: অভাবীর অন্ন কেড়ে নিয়ে তৃপ্তির হাসি হাসা।
স্বার্থপরতা: দেশের স্বার্থকে জলাঞ্জলি দিয়ে ব্যক্তিগত এজেন্ডার পূজা করা।
বিভাজন সৃষ্টিকারী রাজনীতি: মানুষকে মানুষ থেকে বিচ্ছিন্ন করে ভ্রাতৃত্বকে বিষিয়ে দেওয়া।
অযোগ্য নেতৃত্ব: উন্নয়নকে অবরুদ্ধ করে দেশের স্বপ্নকে শ্বাসরুদ্ধ করা।
এখন প্রশ্ন—যে রাজনীতিবিদ বুকে হাত দিয়ে গর্জে বলে “আমি সোনার বাংলাদেশকে ভালোবাসি”, অথচ তার কর্মকাণ্ড এই কুকর্মের তালিকায় পাওয়া যায়—তার ভালোবাসা কি সত্যি? নাকি সুপরিকল্পিত প্রতারণা?
দেশপ্রেম কোনো অনুষ্ঠানমুখী প্রদর্শনী নয়—না জাতীয় সঙ্গীতের সুরে দাঁড়িয়ে থাকা, না শহীদ মিনারে খালি পায়ে যাওয়া, না স্মৃতিসৌধে ফুল দিয়ে ছবি তোলা। আসল দেশপ্রেম শুরু হয় পরিবার থেকে, দায়িত্ব থেকে, বিবেক থেকে। আপনি যদি ঘরের মানুষকে মর্যাদা দেন, অন্যের অধিকারকে শ্রদ্ধা করেন, সততা দিয়ে জীবিকা অর্জন করেন—তাহলেই দেশের হৃদস্পন্দনে ভালোবাসা ঢেলে দিচ্ছেন। নিজের চর্কায় তেল দিলে গোটা দেশের চাকা সচল থাকে—আর তাতেই বেঁচে ওঠে সোনার বাংলার স্বপ্ন। কিন্তু সেই স্বপ্ন জাগাতে হলে প্রথমে আমাদের মুক্ত করতে হবে দেশকে সেই সুবর্ণ ডাকাতদের হাত থেকে—যারা ক্ষমতায় উঠে জনগণের কাঁধে পা দিয়েছে, কিন্তু সেই কাঁধের হাড় ভেঙে দিয়েছে। আজ যারা দেশকে “মা” বলে ডাকে, তারাই মায়ের গলার হার, কানের দুল, এমনকি খোঁপার ফুলও চুরি করে নেয়।
তাদের দেশপ্রেমের মাপ হয় বিদেশি ব্যাংকে ডলারের অঙ্ক দিয়ে, আর জনগণের ভালোবাসা মাপে আগেই ভরা ভোটের বাক্স দিয়ে। তারা ভাবে দলীয় পতাকা উঁচিয়ে রাখলেই দায়িত্ব শেষ—কিন্তু দেশপ্রেম মানে নীরব আত্মত্যাগ, সততা ও দায়বদ্ধতা।
যেদিন আমরা সবাই মিলে নিজেদের চর্কায় তেল ঢালতে শুরু করব, সেদিন “দেশপ্রেমের ব্যবসায়ীরা” বুঝতে পারবে—বাজারে তাদের কোনো ক্রেতাই নেই। আর সেদিন সোনার বাংলার স্বপ্ন শুধু বাঁচবেই না—সে স্বপ্ন দাঁড়াবে এই ভণ্ড দেশপ্রেমিকদের কবরের উপর, হেসে বলবে—এবার তোমাদের বিদায়।
রহমান মৃধা, সাবেক পরিচালক, ফাইজার সুইডেন। Rahman.Mridha@gmail.com
মত দ্বিমত
পরাজিত সশস্ত্র বাহিনীর হাতে কিভাবে বাংলাদেশ সুরক্ষিত থাকতে পারে?
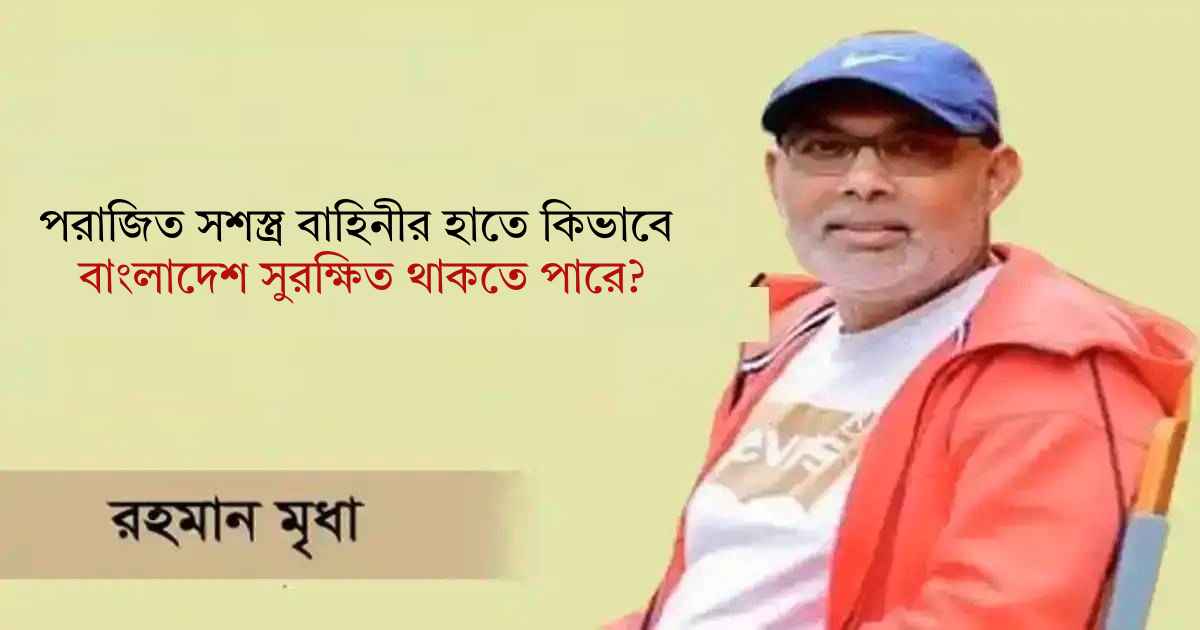
৫ আগস্ট ২০২৪ বাংলাদেশের ইতিহাসে এক নাটকীয় ও অভূতপূর্ব দিন। সেদিন দীর্ঘদিনের স্বৈরশাসক শেখ হাসিনা হঠাৎ করে দেশ ত্যাগ করেন এবং নিরাপদে ভারতে পৌঁছান। আরও বিস্ময়কর হলো, এই সেফ এক্সিট নিশ্চিত করে সেনাবাহিনী-যা দেশের সংবিধান বা প্রচলিত আইন কোথাও অনুমোদিত নয়। একজন ক্ষমতাচ্যুত ও জনগণের রোষানলে পতিত শাসককে সামরিক বাহিনী পালাতে সাহায্য করেছে-এটি শুধু নৈতিক অবক্ষয়ের নজির নয়, বরং রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্বের ওপর সরাসরি আঘাত।
১৯৭১ সালে পাকিস্তান পরাজিত হওয়ার পর তাদের সৈন্যরা পাকিস্তানের সেনাবাহিনীতে আর ফেরেনি। বিশ্বজুড়ে এটি স্বাভাবিক প্রক্রিয়া—যারা দেশের স্বাধীনতা ও জনগণের আস্থা হারায়, তারা সামরিক বাহিনীর অংশ থাকতে পারে না। কিন্তু বাংলাদেশে উল্টো চিত্র: ৫ আগস্ট ২০২৪-এর পরও সেই একই সেনা কর্মকর্তা ও সদস্যরা দিব্যি পদে বহাল, বেতন তুলছে এবং দেশের অবনতির নীরব দর্শক হয়ে আছে।
৫ আগস্ট শেখ হাসিনা পালিয়ে যান, সেনাবাহিনীর সহায়তায় সেফ এক্সিট পান। রাজধানী ও প্রধান শহরে জনতার স্বস্তি ও ক্ষোভ মিশ্র প্রতিক্রিয়া—স্বস্তি কারণ স্বৈরশাসকের পতন, ক্ষোভ কারণ তিনি বিচার বা জবাবদিহি ছাড়াই পালিয়ে গেলেন। ৬ আগস্ট দেশের বিভিন্ন স্থানে জনগণ উচ্ছ্বাস প্রকাশের পাশাপাশি স্বচ্ছ তদন্ত ও বিচার দাবি জানায়। কিন্তু সামরিক বাহিনী নীরব থাকে, প্রশাসন ভেঙে পড়ে, ক্ষমতার শূন্যতা তৈরি হয়। ৭ থেকে ১০ আগস্ট আইন-শৃঙ্খলার অবনতি শুরু হয়। বিভিন্ন জায়গায় লুটপাট, সহিংসতা ও প্রতিশোধমূলক হামলার ঘটনা ঘটে। সেনাবাহিনী তৎপর না হয়ে বরং দূর থেকে পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করে—যা জনগণের মধ্যে সন্দেহ আরও বাড়িয়ে তোলে। ১১ আগস্ট অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের আলোচনা শুরু হয়, কিন্তু প্রশাসন ও নিরাপত্তা কাঠামো এখনও মূলত পুরোনো শাসকের অনুগতদের হাতে। জনগণ উপলব্ধি করে—এ পরিবর্তন কেবল মুখোশ; রাষ্ট্রযন্ত্র এখনো শিকড়ে পরিবর্তিত হয়নি। ১২ আগস্ট এবং পরবর্তী সময়ে আন্দোলনের নতুন ঢেউ ওঠে, দাবি ওঠে—পরাজিত সেনা ও প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হোক। কিন্তু ক্ষমতাধর মহল নানা অজুহাতে তা বিলম্বিত করে।
যে সেনাবাহিনী জনগণের অধিকার রক্ষা করতে ব্যর্থ হয়েছে, স্বৈরশাসককে পালাতে সহায়তা করেছে, এবং পরাজয়ের পরও পদে বহাল আছে—তাদের হাতে দেশের নিরাপত্তা রাখা কতটা যৌক্তিক? যদি রাষ্ট্র তার পরাজিত ও অবিশ্বস্ত রক্ষকদের সরাতে না পারে, তবে সার্বভৌমত্ব, ন্যায়বিচার ও গণতন্ত্র কি সত্যিই প্রতিষ্ঠা পাবে? এটাই এখন বাংলাদেশের সামনে সবচেয়ে বড় রাজনৈতিক ও নৈতিক সংকট।
বাংলাদেশ ৫ আগস্ট ২০২৪-এ গণঅভ্যুত্থানের মাধ্যমে স্বৈরশাসককে সরালেও, রাষ্ট্রপ্রধানের পদে রয়ে গেলেন সেই স্বৈরাচারেরই পছন্দের ও নিয়োগপ্রাপ্ত ব্যক্তি। একজন রাষ্ট্রপতি, যিনি জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত নন, বরং ক্ষমতাসীন গোষ্ঠীর স্বার্থে বসানো—তিনি এখনও দেশের সর্বোচ্চ সাংবিধানিক পদে বহাল। এটি শুধু রাজনৈতিক ব্যর্থতা নয়, বরং গণতান্ত্রিক নীতির প্রতি চরম অবমাননা।
প্রশ্ন উঠছে—অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গত এক বছরে আসলে কী করেছে? সংস্কারের নামে নানা ঘোষণা এসেছে, কিন্তু বাস্তবে প্রশাসনিক কাঠামোতে বড় কোনো পরিবর্তন হয়নি; দুর্নীতি ও পক্ষপাতিত্ব আগের মতোই বিদ্যমান। সেনা ও নিরাপত্তা বাহিনী এখনও পুরোনো শাসকের অনুগত কর্মকর্তাদের দখলে। বিচার ব্যবস্থা জনআস্থা পুনরুদ্ধার করতে ব্যর্থ হয়েছে; রাজনৈতিক অপরাধের বিচার প্রায় স্থবির। ফলে সংস্কারের বদলে জনগণ দেখেছে—প্রতারণা, সময়ক্ষেপণ এবং ক্ষমতা আঁকড়ে ধরা।
বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক পুনর্গঠনের সবচেয়ে বড় পদক্ষেপ হওয়া উচিত একটি অবাধ, সুষ্ঠু ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচন। কিন্তু আজও প্রশ্ন রয়ে গেছে—নির্বাচন কবে হবে, তা কোনও সুনির্দিষ্ট তারিখে ঘোষণা করা হয়নি। নির্বাচন পরিচালনার নিয়ম-কানুন কে ঠিক করবে, তা নিয়ে স্বচ্ছ প্রক্রিয়া নেই। বিরোধী দল ও নাগরিক সমাজকে আলোচনার টেবিলে আনার প্রকৃত উদ্যোগ দেখা যায়নি। ফলে জনগণ আশঙ্কা করছে—নির্বাচন আবারও ক্ষমতাসীন গোষ্ঠীর হাতে সাজানো নাটকে পরিণত হবে।
৫ আগস্ট ২০২৪-এর পর আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি কিছুদিনের জন্য ভেঙে পড়ে। পরে সামরিক বাহিনী ও পুলিশ আংশিক নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করলেও রাজনৈতিক সহিংসতা এখনও চলছে; প্রতিশোধমূলক হামলা থামেনি। গ্রামীণ এলাকায় অপরাধ ও সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড বেড়েছে। সাংবাদিক ও মানবাধিকার কর্মীরা হয়রানি, হুমকি ও হামলার মুখে কাজ করছেন। বাংলাদেশ কার্যত একটি অসুরক্ষিত অস্থিরতার জোনে পরিণত হয়েছে।
অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান হিসেবে ড. মুহাম্মদ ইউনূস শুরুতে জনগণের মধ্যে আশা জাগালেও, বাস্তবে তাঁর ভূমিকা এখন প্রশ্নবিদ্ধ। ৩-জিরো ধারণা (দারিদ্র্য শূন্য, বেকারত্ব শূন্য, কার্বন নিঃসরণ শূন্য) নিয়ে তিনি ব্যস্ত থেকেছেন, অথচ দেশের রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা ও নিরাপত্তা সংকটে কার্যকর সমাধান আনতে পারেননি। ক্ষমতার কেন্দ্রে থাকা সত্ত্বেও তিনি রাষ্ট্রপতি, সেনাবাহিনী ও নিরাপত্তা ব্যবস্থার কাঠামোগত সংস্কার এড়িয়ে গেছেন। ফলে অনেকেই বলছেন- ড. ইউনূস ৩-জিরো নিয়ে ভাবতে গিয়ে নিজেকে রাজনৈতিক শূন্যে পরিণত করেছেন।
বাংলাদেশ আজ একটি অস্থির সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে। আমরা দেখেছি ক্ষমতার অপব্যবহার, সংস্কারের নামে প্রতারণা, এবং নেতৃত্বের ব্যর্থতা। কিন্তু ইতিহাস বারবার প্রমাণ করেছে-যে জাতি স্বাধীনতার জন্য রক্ত দিতে পারে, সে জাতি নিজেদের ভাগ্যেরও নির্মাতা হতে পারে। ৫ আগস্ট ২০২৪ কেবল একটি তারিখ নয়; এটি ছিল জনগণের শক্তির এক বিস্ফোরণ। সেই শক্তি আজও মরে যায়নি—শুধু সংগঠিত হওয়া এবং সঠিক দিক নির্দেশনার অপেক্ষায় আছে। আজ প্রয়োজন গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য অটল জনচাপ, সত্যিকারের যোগ্য নেতৃত্ব বেছে নেওয়ার সাহস, এবং রাষ্ট্রের প্রতিটি স্তরে জবাবদিহি প্রতিষ্ঠা। অতীতের ভুল আমাদের শিক্ষা দিয়েছে; এখন সেটিকে পরিবর্তনের পাথেয় করতে হবে। যদি আমরা প্রত্যেকে নিজের অবস্থান থেকে ন্যায়, স্বচ্ছতা ও সততার পক্ষে দাঁড়াই—তাহলেই বাংলাদেশ আবার নতুন ভোরের মুখ দেখবে। কারণ, অন্ধকার যতই গভীর হোক, ভোর ঠিক আসবেই।
রহমান মৃধা
গবেষক ও লেখক
(সাবেক পরিচালক, ফাইজার, সুইডেন)
Rahman.Mridha@gmail.com
মত দ্বিমত
৩৩ বছর বয়সে রাষ্ট্রদূত নিয়োগ নিয়ে বিতর্ক, হাসিনার পালিয়ে যাওয়াও নজিরবিহীন

হাসিনার পালিয়ে যাওয়াও নজিরবিহীন! যেমন নজিরবিহীন ছাত্রদের ২৭ বছর বয়সে উপদেষ্টা হওয়া। অথচ পৃথিবীর বহু দেশে ৩৫ বছরের আগেই মানুষ রাষ্ট্রপ্রধান হয়েছে। আলেকজান্ডার তো অর্ধেক পৃথিবী জয় করে ৩৩ বছর বয়সেই পৃথিবী ছেড়ে গেছে।
বাংলাদেশে ২৫ বছর বয়সে শীর্ষ জাতীয় দৈনিকের পেশাদার সম্পাদক নিয়োগ হয়েছিল—যার অধীনে মতিউর রহমানের মতো লোকও কাজ করেছেন। আর এখানে নাকি ৩৩ বছর বয়সে রাষ্ট্রদূত হওয়া যাবে না! কারণ যদুর বাপ কদু ৫৮ বছর বয়সে রাষ্ট্রদূত হয়েছিল—তাই নাকি সবারও বুড়ো বয়সেই দায়িত্ব নিতে হবে! যোগ্যতা নয়, বয়সই হবে মাপকাঠি!
যার কথা বলছেন, তিনি যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দপ্তরের ফরেন সার্ভিস ইনস্টিটিউটে (এফএসআই) দক্ষিণ এশিয়া অঞ্চলে নিয়োগপ্রাপ্ত নবনিযুক্ত মার্কিন কূটনীতিকদের জন্য লেকচারার হিসেবে বক্তৃতা প্রদান করেন। পৃথিবীর টপ সব পাবলিকেশন এবং জার্নালে তার বই ও আর্টিকেল প্রকাশিত হয়েছে। জটিল বিশ্ব রাজনীতির অন্যতম পাক্কা খেলোয়াড় একটি দেশের পার্লামেন্টের অ্যাডভাইজার এবং পার্লামেন্টারি ডিপ্লোম্যাট হিসেবে কাজ করেছেন | তাকে কিন্তু পৃথিবীর শীর্ষ সব মিডিয়া ইন্দো-প্যাসিফিক আর সাউথ এশিয়ান পলিটিক্স নিয়ে ইন্টারভিউ করে। তিনি ইউরো-এশিয়ার একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে ইন্দো-প্যাসিফিক স্টাডিজের চেয়ারম্যান, সহযোগী অধ্যাপকও হয়ে গেছেন। অথচ আপনি ৬০ পেরিয়েছেন, তবু আপনাকে কেউ ডাকে না।
তো জ্বালাটা আসলে এই—‘আমি পারিনি, তাই শালার পুত তোকে-ও হতে দেব না!’ এই তো আসল কথা!
লেখক: কামরান সিদ্দিকী, গণমাধ্যমকর্মী।