মত দ্বিমত
যোগ্যতা বনাম ক্ষমতা: তন্ত্রের আয়নায় মানুষের মুক্তি-সংকট
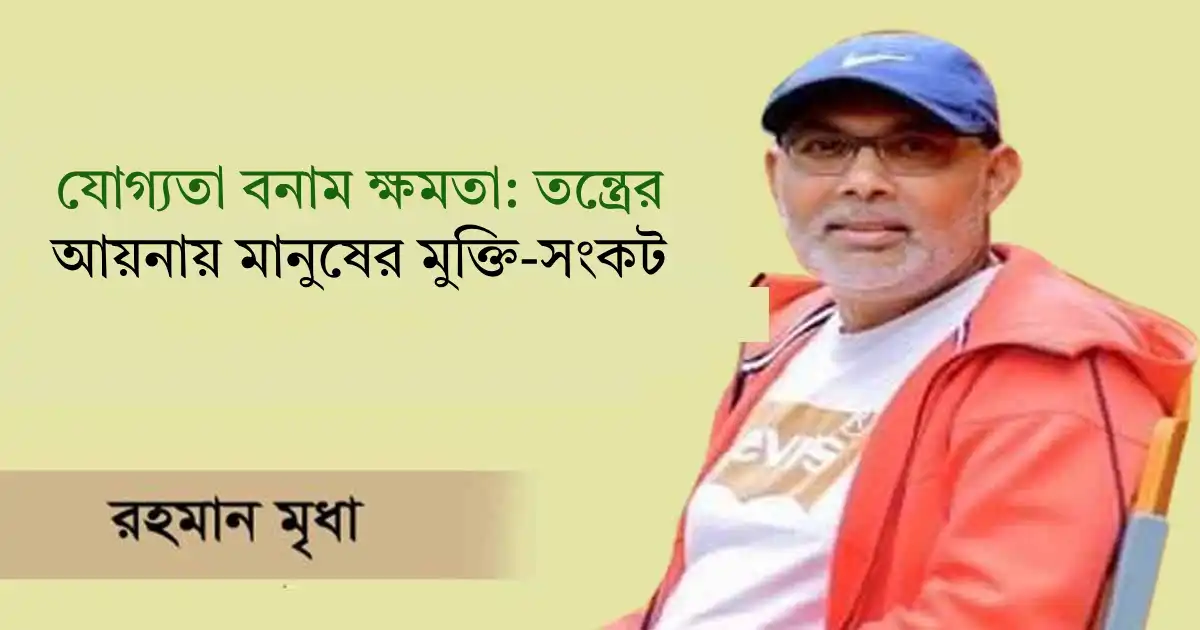
ভূমিকা: প্রশ্নের শিকড়ে ফিরে যাওয়া যোগ্য ব্যক্তি কখন অযোগ্য হয়ে পড়ে?
এই প্রশ্নে লুকিয়ে আছে হাজার বছরের রাজনীতি, রাষ্ট্রচিন্তা এবং সমাজব্যবস্থার মূল সংকট। কেউ জন্মসূত্রে রাজা, কেউ নির্বাচনে বিজয়ী, কেউ ধর্মীয় নেতারূপে, কেউ সৈনিক থেকে শাসক। কিন্তু প্রায়শই দেখা যায়—ক্ষমতা তাদের পরিবর্তন করে, কিংবা সিস্টেমই তাদের বিকৃত করে দেয়।
যোগ্যতা তখন শুধু একটি শুরুর দাবি হয়ে থাকে—বাস্তব শাসনে তা হয় বিকৃত, পরিত্যক্ত কিংবা বিক্রিত। এই বিশ্লেষণে আমরা ফিরে যাব রাজতন্ত্র, পরিবারতন্ত্র, প্রজাতন্ত্র, একনায়কতন্ত্র, ধর্মতন্ত্রের ইতিহাসে। দেখব—কে কিভাবে ‘যোগ্য’ হয়েছিলেন, এবং কেন কালের প্রবাহে ‘অযোগ্য’ হয়ে উঠলেন।
শেষত, আমরা দাঁড়াব বর্তমান বাস্তবতায়—যেখানে একমাত্র প্রশ্ন হবে, মানুষের মুক্তির জন্য কোন তন্ত্র সবচেয়ে প্রয়োজনীয়?
তন্ত্র মানে কী?
তন্ত্র মানে শাসনের কাঠামো। এই কাঠামোই ঠিক করে, কে শাসক হবে, কীভাবে ক্ষমতা অর্জন হবে, জনগণের সঙ্গে সম্পর্ক কেমন হবে, আর দায়বদ্ধতার ধরণ কেমন হবে।
সাধারণভাবে পাঁচটি তন্ত্র চিহ্নিত করা যায়:
১. রাজতন্ত্র (Monarchy)
২. পরিবারতন্ত্র / বংশতন্ত্র (Dynastic politics)
৩. প্রজাতন্ত্র / গণতন্ত্র (Republic/Democracy)
৪. একনায়কতন্ত্র / সামরিক শাসন (Autocracy/Military rule)
৫. ধর্মতন্ত্র (Theocracy)
আমরা দেখব—এই পাঁচটি তন্ত্রেই ‘যোগ্য’ মানুষ শাসনে আসেন, কিন্তু সময়ের সাথে কেউ অযোগ্য হয়ে পড়েন। প্রশ্ন হলো—কেন?
যোগ্যতার সংজ্ঞা: আমাদের অবস্থান
আমরা যেই যোগ্যতার কথা বলছি, তা চার স্তরের উপর প্রতিষ্ঠিত:
১. নৈতিকতা: ব্যক্তির নীতিবোধ, মানবিকতা, স্বচ্ছতা
২. দক্ষতা ও শিক্ষা: রাষ্ট্রচিন্তা, অর্থনীতি, ইতিহাস, বিজ্ঞান-প্রযুক্তি, সাংস্কৃতিক জ্ঞান
৩. কর্মদক্ষতা: বাস্তব সিদ্ধান্ত গ্রহণের যোগ্যতা, প্রশাসনিক সক্ষমতা
৪. জনসম্পৃক্ততা: মানুষের কণ্ঠস্বর শোনা, বেকারত্ব দূরীকরণ, দুর্নীতির বিরুদ্ধে অবস্থান, সামাজিক দায়বদ্ধতা।
এই চারটি উপাদান মিলেই গঠিত হয় প্রকৃত যোগ্যতা। এই যোগ্যতা ছাড়া কেউ নেতা হতে পারেন না—আর যদি হনও, তারা ক্ষমতার ভার বহন করতে পারেন না।
রাজতন্ত্র ও পরিবারতন্ত্রের আয়নায় যোগ্যতা ও অযোগ্যতার বিবর্তন
রাজতন্ত্র— জন্মগত শ্রেষ্ঠত্ব না ঐতিহাসিক জড়তা?
রাজতন্ত্রের ভিত্তি দাঁড়িয়ে আছে এক অদ্ভুত দাবির ওপর—“একজন মানুষ, কেবলমাত্র একটি নির্দিষ্ট বংশে জন্মেছে বলেই, সে অন্য সবার চেয়ে অধিক যোগ্য।” এটি আদিতে ঈশ্বরদত্ত বা ঐশ্বরিক অনুমতির দাবির সঙ্গে যুক্ত ছিল।
ইতিহাসের কয়েকটি দৃষ্টান্ত:
• ফারাও (মিশর): নিজেকে ঈশ্বরের প্রতিনিধি দাবি করতেন।
• চীনের রাজবংশ: “Mandate of Heaven”-এর ধারক ছিলেন।
• ইংল্যান্ডের রাজতন্ত্র: রাজা/রানী ছিলেন রাষ্ট্রপ্রধান এবং চার্চের প্রধান।
• ভারতীয় উপমহাদেশে: মুঘল ও অন্যান্য রাজাদের শাসন ছিল জন্মভিত্তিক উত্তরাধিকার নির্ভর।
কেন তারা যোগ্য ছিলেন (বা মনে করা হতো):
•উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত, কূটনৈতিক, সংস্কৃতিতে পারদর্শী
•সেনাপতি ও প্রশাসক হিসেবে প্রস্তুত করা হতো ছোটবেলা থেকে
কেন তারা অযোগ্য হয়ে উঠতেন:
• জন্ম-যোগ্যতা কোনও বাস্তব দক্ষতা বা মূল্যবোধ নিশ্চিত করে না
• অধিকাংশ উত্তরসূরি শাসকেরা অহংকারী, অলস বা নির্মম হয়ে ওঠেন
• জনগণের সঙ্গে সম্পর্ক দুর্বল হয়ে পড়ে
• নেতৃত্ব হয় এক বদ্ধবৃত্ত—কোনো বিকল্প বা সংশোধন নেই
রাজতন্ত্র একসময় শৃঙ্খলা এনেছিল, কিন্তু সময়ের ব্যবধানে এটি মানুষের মধ্যে বৈষম্য, ক্ষমতার অপব্যবহার ও অযোগ্যতার চক্র তৈরি করে। জন্মই নেতৃত্বের মাপকাঠি হতে পারে না—এটি চরম অন্যায় এবং অমানবিক।
পরিবারতন্ত্র — গণতন্ত্রের মুখোশে বংশানুক্রমিক আধিপত্য
পরিবারতন্ত্র হলো গণতন্ত্রের বিকৃত রূপ—যেখানে শাসক নির্বাচিত হলেও, ক্ষমতা এক পরিবারের মধ্যেই ঘুরপাক খায়। এটি আধুনিক কালে রাজতন্ত্রের উত্তরাধিকার।
বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান, ফিলিপাইন, উত্তর কোরিয়া, শ্রীলংকা—সবখানেই এই প্রবণতা লক্ষণীয়:
• শেখ পরিবার বনাম জিয়া পরিবার (বাংলাদেশ)
• গান্ধী পরিবার (ভারত)
• ভুট্টো পরিবার (পাকিস্তান)
• কিম বংশ (উ. কোরিয়া)
যোগ্যতা বলে দাবি করা হয়:
• ‘ঐতিহ্য’, ‘অভিজ্ঞতা’, ‘পরিচিতি’, এবং ‘জনসম্পৃক্ততা’
আসলে ঘটে যা:
• পরিবারতন্ত্র রাজনীতিকে একটি ব্যক্তিগত ব্যবসায় পরিণত করে
• দুর্নীতি, আত্মীয়করণ (nepotism), এবং লুটপাট বেড়ে যায়
• যুবসমাজ বা নতুন নেতৃত্ব উঠে আসার সুযোগ পায় না
• দলগত শৃঙ্খলার চেয়ে পারিবারিক আনুগত্য বড় হয়ে দাঁড়ায়
জনগণের ক্ষতি কোথায়:
• একই চক্রের মধ্যে সমস্যার সমাধান অসম্ভব
• উন্নয়ন ও নীতিনির্ধারণ হয় ক্ষমতা রক্ষার কৌশলে, জনগণের কল্যাণে নয়
পরিবারতন্ত্রের মধ্যে জন্ম ও সম্পর্কের যোগ্যতাকে অগ্রাধিকার দেয়া হয়, যা গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের সঙ্গে সরাসরি সাংঘর্ষিক। একে গণতন্ত্রের নামে একটি ব্যক্তিমালিকানাধীন রাষ্ট্রব্যবস্থা বলা চলে।
সংক্ষিপ্ত অন্তর্বর্তী সংলাপ:
রাজতন্ত্র একসময় শৃঙ্খলা এনেছিল
পরিবারতন্ত্র আধুনিক রাজতন্ত্রে রূপান্তরিত হয়েছে
কিন্তু উভয় তন্ত্রেই
যোগ্যতা = বংশ,
যোগ্যতা ≠ শিক্ষা, দক্ষতা, মূল্যবোধ, জনসম্পৃক্ততা।
আধুনিক তন্ত্রে যোগ্যতার মৃত্যুকাহিনি
গণতন্ত্র—সংখ্যার রাজনীতিতে গুণমানের পতন
গণতন্ত্র একসময় মানুষের স্বপ্ন ছিল। স্বাধীন মত প্রকাশ, জন-ইচ্ছার প্রতিফলন, এবং প্রতিনিয়ত পরিবর্তনের সুযোগ—এসব ছিল এই ব্যবস্থার প্রাতিষ্ঠানিক প্রতিশ্রুতি। কিন্তু ধীরে ধীরে গণতন্ত্র সংখ্যার খেলায় পরিণত হয়, যেখানে “কতজন বলছে” সেটাই ঠিক, “কে কী বলছে” তা নয়।
এই ব্যবস্থায় যোগ্যতা মূল্য পায় তখনই, যখন তা জনপ্রিয় হয়। একসময় নেতৃত্ব পেতে হলে লাগত দূরদর্শিতা, নৈতিকতা ও সেবার ইতিহাস, আজ তা মুছে গেছে নির্বাচনী কৌশল, গণমাধ্যমের প্রভাব এবং অর্থবলের ছায়ায়। আর এই ছায়ার মধ্যেই হারিয়ে যায় প্রকৃত যোগ্যরা—যারা কথা বলেন মানুষের অধিকারের পক্ষে, উন্নয়নের স্থায়ী রূপরেখা নিয়ে।
এইভাবে গণতন্ত্র পরিণত হয় ‘ভোট-সর্বস্ব ব্যবস্থায়’, যেখানে সত্য নয়, আবেগ বিক্রি হয়—যেখানে যোগ্যতা নয়, পরিচিতি আর প্রতিশ্রুতি জিতে যায়। জনগণ বিভ্রান্ত হয় মিডিয়ার নাটকে, রাজনৈতিক ধর্মীয় উস্কানিতে, আর সেখানে দাঁড়িয়ে এক সময়কার যোগ্য ব্যক্তিটিও জনসমর্থনহীন হয়ে পড়ে, হয়ে যায় ‘অযোগ্য’।
একনায়কতন্ত্র—শৃঙ্খলার নামে চিন্তার হত্যাকাণ্ড
একনায়কতন্ত্র আসে সংকটকে পুঁজি করে—“দেশে বিশৃঙ্খলা চলছে”, “বিচারব্যবস্থা দুর্বল”, “রাজনীতি দুষ্টু খেলোয়াড়ে ভরা”—এইসব যুক্তি দিয়ে যখন ক্ষমতা তুলে দেওয়া হয় একজন বা এক গোষ্ঠীর হাতে, তখনই শুরু হয় এক ভিন্ন খেলাধুলা।
প্রথমে মনে হয়, কেউ একজন দৃঢ় হাতে হাল ধরেছে। উন্নয়ন হয়, শৃঙ্খলা ফিরে আসে, ঘুষ-দুর্নীতি কমে যায়। কিন্তু ধীরে ধীরে দেখা যায়—যে কথা বলছে না, সে-ই টিকে আছে। আর যে প্রশ্ন তোলে, সে ‘অবিশ্বস্ত’, ‘রাষ্ট্রদ্রোহী’, ‘বিদেশি এজেন্ট’। এইখানেই যোগ্য ব্যক্তি পরিণত হয় অযোগ্যতে। কারণ একনায়কের প্রয়োজন চাটুকার, চিন্তাশীল নয়। রাষ্ট্র তখন চালায় ‘একজনের অভিমত’, দেশের কণ্ঠ হয়ে ওঠে ‘একটা মঞ্চ’—আর সেখানে হাজার চিন্তাশীল মানুষের মধ্যে একজনও টিকে না।
বহু যোগ্য শিক্ষাবিদ, অর্থনীতিবিদ, বিজ্ঞানী বা কর্মী—যারা স্বাধীনভাবে চিন্তা করে—তারা এই ব্যবস্থায় হয় নির্বাসিত, নয় নিঃশব্দ।
ধর্মতন্ত্র—নৈতিকতার নামে জ্ঞানের নিধন
ধর্ম, মূলত মানুষের ভিতরকার মূল্যবোধ গঠনের জন্য। কিন্তু রাষ্ট্র যখন ধর্ম দিয়ে পরিচালিত হয়, তখন ধর্ম হয় শাসনের হাতিয়ার। নৈতিকতার জায়গায় আসে ভয়, আত্মোপলব্ধির জায়গায় আসে বিধান। ধর্মতন্ত্রে যোগ্যতা নির্ধারিত হয় ঈশ্বরের নামে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কয়েকজন মানুষের ব্যাখ্যার মাধ্যমে। তারা ধর্মের যে অংশকে চায়, সেটুকু তুলে ধরে; বাকি ইতিহাস, বৈজ্ঞানিক জ্ঞান, সমাজতত্ত্ব—সব হয় ‘নিষিদ্ধ’ জ্ঞান। এখানে যোগ্যতা মানে হয় ‘ধর্মীয় ব্যাখ্যা জানা’, কিন্তু তার সঙ্গে বাস্তব রাষ্ট্র পরিচালনার জ্ঞান, অর্থনীতি বা প্রযুক্তির জ্ঞান—তা অপ্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে। তাই একজন ধর্মীয় নেতা রাষ্ট্রনায়ক হতে পারেন, অথচ তিনি সমাজের জটিল বাস্তবতা বুঝেন না। যারা বোঝেন, তারা ‘অবিশ্বাসী’ বা ‘ভ্রান্ত’। এই অবস্থায় একসময় যোগ্য ব্যক্তি—যিনি মানুষের মুক্তি, শিক্ষা, সমতা ও আধুনিকতা নিয়ে কাজ করেন—তাকে রাষ্ট্রশত্রু হিসেবে চিহ্নিত করা হয়।
সম্মিলিত উপলব্ধি:
তিনটি আধুনিক তন্ত্র—গণতন্ত্র, একনায়কতন্ত্র, ধর্মতন্ত্র—প্রথমদিকে মানুষকে আশ্বাস দিয়েছিল পরিবর্তনের, মুক্তির, ন্যায়ের। কিন্তু সময়ের সাথে তারা সকলেই যোগ্যতার পরিবর্তে বেছে নিয়েছে তাদের স্বার্থ রক্ষাকারীদের।
• গণতন্ত্রে যোগ্যতা হারায় সংখ্যার ভারে,
• একনায়কতন্ত্রে হারায় মতপ্রকাশের বন্ধনে,
• ধর্মতন্ত্রে হারায় জ্ঞান ও মানবিকতার অবদমনে।
এই বাস্তবতায় প্রশ্ন উঠে—তাহলে আমরা কোন পথে যাব? আমরা কোন যোগ্যতা চাই? এবং সে উত্তর খুঁজতেই প্রয়োজন পরবর্তী পদক্ষেপ, যেখানে প্রস্তাব করা হবে এক নতুন রাষ্ট্রব্যবস্থার রূপরেখা—যেখানে মানুষ, নীতি ও দক্ষতা হবে কেন্দ্রবিন্দু।
তাহলে কেমন তন্ত্র চাই মানুষকে মানুষের মতো বাঁচাতে?
মানুষমুখী রাষ্ট্রব্যবস্থা — এক ‘নৈতিক দক্ষগণতন্ত্র’-এর নকশা
কেন সব তন্ত্র ব্যর্থ হলো মানুষের কাছে?
রাজতন্ত্র বলল, “আমার জন্মই আমার যোগ্যতা”—মানুষ হারালো মর্যাদা
পরিবারতন্ত্র বলল, “আমার বংশই আমার অধিকার”—মানুষ হারালো সম্ভাবনা
গণতন্ত্র বলল, “সংখ্যাই সত্য”—মানুষ হারালো বিচার
*একনায়ক বলল, “আমি আইন”—মানুষ হারালো কণ্ঠ
*ধর্মতন্ত্র বলল, “ভয়েই শান্তি”—মানুষ হারালো স্বাধীনতা
এতগুলো তন্ত্র থাকতেও যদি মানুষ হয় গৃহহীন, বেকার, অপমানিত, নিপীড়িত—তবে প্রশ্ন জাগে, রাষ্ট্র কার জন্য? তন্ত্র কার জন্য?
বিকল্প কী? — এক নতুন প্রস্তাবনা: নৈতিক দক্ষগণতন্ত্র (Moral Meritocracy-based Democracy)
আমরা একটি এমন তন্ত্র কল্পনা করি— যেখানে নেতৃত্ব নির্ধারিত হবে নৈতিকতা, দক্ষতা, জনদায়িত্ব, এবং সাধারণ মানুষের সঙ্গে বাস্তব সংযোগ-এর ভিত্তিতে। এই তন্ত্রের চারটি স্তম্ভ হবে:
১. নৈতিকতা:
• রাষ্ট্রনায়ক হতে হলে তার জীবনচরিত, সম্পদের উৎস, ও নীতিনৈতিকতা জনসমক্ষে স্বচ্ছভাবে উন্মুক্ত হতে হবে
• দুর্নীতিমুক্ত ও জনহিতকর কাজের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে
২. দক্ষতা:
• রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও প্রযুক্তিগত জ্ঞান থাকা আবশ্যক
• নেতৃত্বে আসার আগে পাবলিক সার্ভিস, নীতিনির্ধারণ, বা সমন্বয় কাজে অভিজ্ঞতা থাকা চাই
৩. গণপ্রতিনিধিত্ব:
• নিরপেক্ষ প্ল্যাটফর্ম ও নির্বাচনী ব্যবস্থার মাধ্যমে প্রার্থীদের যাচাই-বাছাই
• স্থানীয় জনগণকে নেতৃত্ব নির্ধারণে সক্রিয় ও শিক্ষিত ভূমিকা নিতে সক্ষম করে তোলা
৪. মানবিকতা:
• রাষ্ট্র হবে লাভের জন্য নয়, মানুষের জন্য
• সুবিধাবঞ্চিত, প্রান্তিক, সংখ্যালঘুদের অগ্রাধিকার ভিত্তিতে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে
বাস্তবায়নের রূপরেখা (Action Framework)
১. শিক্ষাব্যবস্থা সংস্কার:
নৈতিকতা, গণতন্ত্র, অর্থনীতি ও প্রযুক্তিনির্ভর জীবনমুখী পাঠ্যক্রম চালু
২. রাজনৈতিক সংস্কৃতি সংস্কার:
নেতৃত্বের যোগ্যতা নির্ধারণে নির্বাচন কমিশনের পাশে একটি Merit Assessment Council গঠন
৩. মিডিয়া ও তথ্যপুঞ্জের ভূমিকা:
স্বচ্ছতা ও সচেতনতার জন্য তথ্য প্রকাশ বাধ্যতামূলক করা
জনগণকে ভুল তথ্য থেকে রক্ষা করে বাস্তব তথ্যের অধিকার নিশ্চিত করা
৪. প্রবাসী ও তরুণদের অংশগ্রহণ:
বিশ্বব্যাপী দক্ষ জনশক্তিকে রাষ্ট্র গঠনে অন্তর্ভুক্ত করা
নতুন প্রজন্মকে প্রযুক্তি ও মানবিক চিন্তায় শক্তিশালী করা
চূড়ান্ত উপলব্ধি: মানুষই রাষ্ট্রের কেন্দ্রবিন্দু
মানুষ শুধুই ভোটার নয়, মানুষ হলো রাষ্ট্রের অস্তিত্বের কারণ।
অতএব, যে রাষ্ট্র বা তন্ত্র মানুষের যোগ্যতা, মর্যাদা ও জীবনের গুণগত মান উন্নয়নে প্রতিশ্রুত নয়—তা অযোগ্য রাষ্ট্রব্যবস্থা।
উপসংহার:
যেখানে মানুষ বড়, তন্ত্র নয়—সেই রাষ্ট্রই সত্যিকারের মানবিক রাষ্ট্র। রাজা, পিতা, একনায়ক কিংবা ইমাম নয়—আমাদের প্রয়োজন এমন এক রাষ্ট্রনায়ক, যিনি শিক্ষা, মানবতা, দক্ষতা ও জবাবদিহিতার আলোয় পরিচালিত। এবং সে রাষ্ট্রব্যবস্থাকে আমরা নাম দেব —নৈতিক দক্ষগণতন্ত্র। কে সেই সুন্দর কে!
লেখক: রহমান মৃধা, সাবেক পরিচালক, ফাইজার, সুইডেন
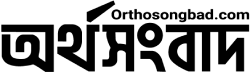
মত দ্বিমত
তরুণ প্রজন্মের চোখে আজকের বাংলাদেশ গুজব, বিভ্রান্তি আর অনিশ্চয়তায় ভরা
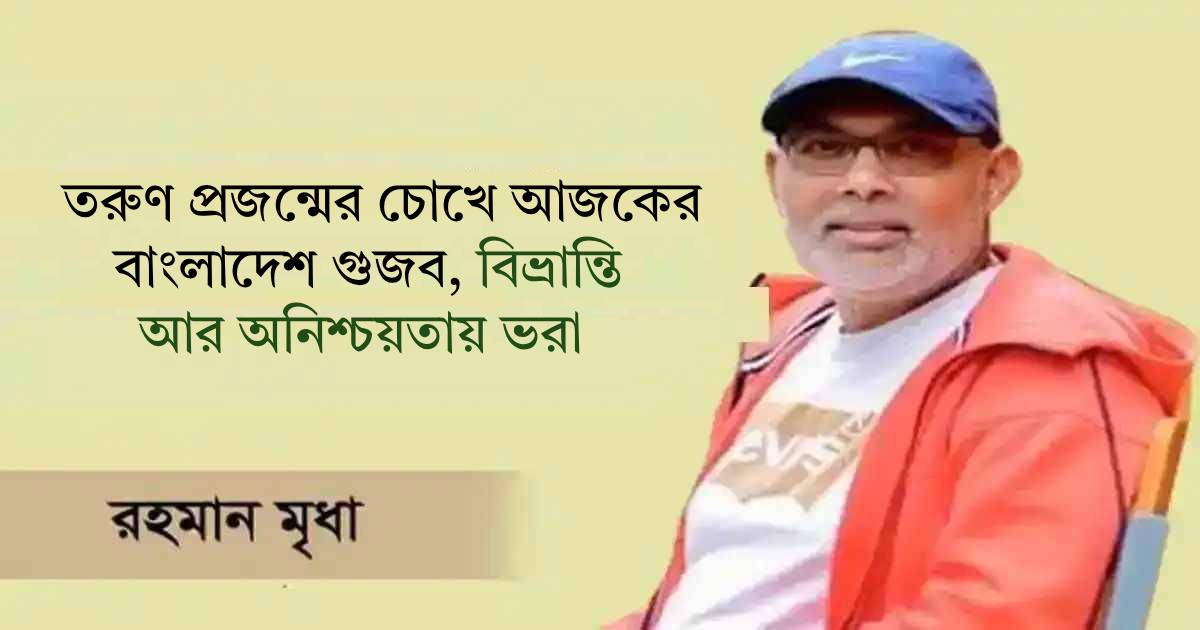
ডাকসু নির্বাচন শেষ না হতেই জাকসু নির্বাচন শুরু হয়েছে। কিন্তু নির্বাচন মানেই এখন আর স্বচ্ছতা কিংবা আস্থার জায়গা নয়, বরং গুজব, পাল্টা গুজব আর দলীয় রাজনীতির ছায়ায় ঢাকা এক নাট্যমঞ্চ। এর মধ্যেই শোনা যাচ্ছে—বিএনপি সহ কয়েকটি দল নির্বাচনে অংশ নিলেও পরে তা প্রত্যাখ্যান করেছে। এদিকে ভোট গণনার কাজ চলছে, কিন্তু চূড়ান্ত ফলাফল কী হবে—সেটি নিয়েই প্রশ্নের শেষ নেই।
প্রশ্ন উঠছে আরও বড় একটি জায়গায়—জামাত কি তাহলে বাংলাদেশের রাষ্ট্র গঠনের স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছে? আবার শোনা যাচ্ছে এমনও গুঞ্জন—স্বয়ং স্বৈরাচারী শেখ হাসিনার নির্দেশে আওয়ামী লীগের সমর্থক শিক্ষার্থীরা নাকি শিবিরের হয়ে নির্বাচনে নেমেছে এবং তাদের জয় নিশ্চিত করেছে। গত ডাকসু নির্বাচনের সময়ও শুনেছি, স্বতন্ত্র প্রার্থী শামীম হোসেন নাকি র’এর এজেন্ট হয়ে প্রার্থী হয়েছিলো।
সব মিলিয়ে এক অদ্ভুত রাজনৈতিক নাটক। কে সত্য বলছে আর কে মিথ্যা, সেটা বোঝা প্রায় অসম্ভব। কারও কাছে তথ্য নেই, কারও কাছে আছে শুধু গল্প। অথচ সত্যিটা চাপা পড়ে আছে—কেউ আসল কথা বলতে চায় না, কিংবা বলার সুযোগ পাচ্ছে না।
এই বাস্তবতা শুধু শিক্ষাঙ্গন নয়, বরং পুরো দেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতির প্রতিচ্ছবি। যে প্রজন্মের এখন বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে ভবিষ্যৎ রাষ্ট্রের নেতৃত্ব গড়ার কথা, তারা আজ গুজব, ষড়যন্ত্র আর অন্ধকার রাজনীতির চক্রে বন্দি। ফলাফল হলো—বিভ্রান্ত তরুণ সমাজ, আস্থাহীন রাজনৈতিক সংস্কৃতি, আর এক প্রশ্নবিদ্ধ বাংলাদেশ।
আমাদের বর্তমান প্রজন্ম তাই একটাই প্রশ্ন তুলতে বাধ্য—what’s going on? কিন্তু সঠিক উত্তর মেলে না।
দেশের কেন্দ্রবিন্দুগুলো হচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয়। এগুলো শুধু শিক্ষার জায়গা নয়, বরং ভবিষ্যৎ রাষ্ট্রনেতা তৈরির কারখানা। অথচ সেই বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানে যদি এতো বিভ্রান্তি, এতো গুজব আর এতো রাজনৈতিক কৌশল ঢুকে পড়ে, তাহলে পুরো বাংলাদেশের অবস্থা কী হবে—এ প্রশ্ন কি আমরা ভেবেছি কখনও?
বর্তমান অন্তর্বর্তীকালীন সরকার যেন জাতিকে আশ্বস্ত করতে চায়—সব ঠিক আছে, সব নিয়ন্ত্রণে আছে। কিন্তু বাস্তবতা ভিন্ন সংকেত দিচ্ছে। অন্যদিকে বিএনপির ডিজিটাল নেতা তারেক রহমান কী ভাবছেন? লন্ডনের নিরাপদ দূরত্ব থেকে তিনি কি দেশে ফেরার ঝুঁকি নেবেন, নাকি “ডিজিটাল নিরাপত্তা”র আড়ালেই থেকে যাবেন? প্রশ্ন উঠছে যখন তাঁর যোগ্যতা নিয়ে, তখনই আলোচনায় আসছে তাঁর অতীত—অপরাধীর প্রত্যাবর্তন ও রাজনৈতিক সংস্কৃতির গভীর সংকট।
একজন দণ্ডপ্রাপ্ত রাজনীতিবিদ দেশে ফিরছেন—এ খবরেই রাজনৈতিক অঙ্গনে উত্তেজনা ছড়িয়েছে। দুর্নীতি, অবৈধ সম্পদ অর্জন এবং নানা অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডের অভিযোগে তাঁর বিরুদ্ধে আদালতের রায় রয়েছে। তবুও তিনি একটি বৃহৎ রাজনৈতিক দলের নেতৃত্বে আসীন, আর তাঁর সমর্থকরা বর্ণাঢ্য সংবর্ধনার প্রস্তুতিতে ব্যস্ত।
মূল সমস্যা নিহিত আছে নেতৃত্বের যোগ্যতা ও নৈতিক ভিত্তির প্রশ্নে। যাঁর নেই কোনো প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা, নেই স্বাভাবিক পেশা বা বৈধ আয়ের উৎস, তিনি কীভাবে একটি জাতীয় দলের নেতৃত্বের দাবিদার হতে পারেন? তাঁর একমাত্র পরিচয়—তিনি মুক্তিযোদ্ধা ও রাষ্ট্রপতির সন্তান এবং সাবেক প্রধানমন্ত্রীর ছেলে। অর্থাৎ নেতৃত্বের ভিত্তি তাঁর ব্যক্তিগত অবদান নয়, বরং উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত পরিচয়।
এই চিত্র শুধু একজনকে ঘিরে নয়; বরং এটি আমাদের রাজনৈতিক সংস্কৃতির অন্তর্নিহিত সংকটকে উন্মোচিত করে। দল ও নেতার প্রতি অন্ধ আনুগত্য, ব্যক্তিত্বপূজা এবং বংশকেন্দ্রিক রাজনীতির কারণে অপরাধপ্রবণতা বারবার আড়াল হয়ে যায়। সমর্থকরা অপরাধের সত্যকে উপেক্ষা করে, বরং রাজনৈতিক আবেগে তা “নায়কোচিত প্রত্যাবর্তন” বলে আখ্যা দেয়।
কিন্তু একটি দেশের গণতন্ত্র টিকে থাকে যোগ্যতা, সততা ও জবাবদিহিতার ওপর। যদি অপরাধপ্রবণ ব্যক্তি কেবল পারিবারিক পরিচয়ের কারণে নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত হন, তবে তা রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলোর দুর্বলতাকেই প্রতিফলিত করে। যতই জাঁকজমকপূর্ণ সংবর্ধনা দেওয়া হোক না কেন, এটি আসলে আমাদের রাজনৈতিক ও নৈতিক মানদণ্ডের অবক্ষয়ের প্রতিচ্ছবি।
অতএব, এ মুহূর্তে জাতির সামনে সবচেয়ে বড় প্রশ্ন—আমরা কী ধরনের নেতৃত্ব চাই? অপরাধীকে বরণ করা নাকি যোগ্য ও সৎ নেতৃত্বকে প্রতিষ্ঠা করা? দেশের দীর্ঘমেয়াদী ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে এই প্রশ্নের সঠিক উত্তরের ওপর।
আরেকটি অদ্ভুত প্রশ্ন উঠে আসে—যদি আওয়ামী লীগ শিবিরকে সমর্থন করে, তবে কি বিএনপির যুবদলকে ছাত্রলীগ সমর্থন করবে? নাকি উল্টো, তারা একদিন আবার জামায়াতের সঙ্গে গোপন জোট গড়ে তুলবে? আমাদের রাজনীতির ইতিহাস বলছে—অসম্ভব কিছুই নেই।
তাহলে আসল চিত্র কী? উত্তর নেই। শুধু প্রশ্ন, শুধু গুজব, শুধু অবিশ্বাস। শত প্রশ্নে দেশ ভরে গেছে, অথচ একটিরও সঠিক উত্তর মেলে না। কারণ দেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতি দীর্ঘদিন ধরে মিথ্যার চর্চায় অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে। সত্যকে আড়াল করে মিথ্যাকে জাহির করাই এখন যেন প্রাত্যহিক রুটিন।
এই অবস্থায় সাধারণ মানুষ, বিশেষ করে তরুণ প্রজন্ম, ভীষণ হতাশ। তারা রাজনীতিকে আর ভবিষ্যতের ভরসা মনে করে না। তাদের চোখে রাজনীতি মানে দুর্নীতি, সুবিধা আর ক্ষমতার খেলা।
আমার দৃঢ় বিশ্বাস, এখন যদি দেশের রাজনীতিবিদদের জবাবদিহিতার আওতায় আনা না যায়, তবে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম পুরোপুরি রাজনীতি থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে। হয়তো সময় এসেছে সকল দুর্নীতিবাজ রাজনীতিবিদদের ধরে ধরে জেলে ঢোকানোর—একটি পরিশুদ্ধ রাজনৈতিক সংস্কৃতি গড়ে তোলার জন্য। আমরা অতিষ্ঠ হয়ে গেছি। আর নয়—এবার যথেষ্ট হয়েছে।
বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর থেকে বারবার এক করুণ সত্য সামনে এসেছে—রাজনৈতিকভাবে এই জাতি একের পর এক পরাজয়ের গল্প শুনে চলেছে। মুক্তির স্বপ্ন ছিল যে স্বাধীনতায়, সেই স্বপ্নকে কলুষিত করেছে দুর্নীতি, মিথ্যা প্রতিশ্রুতি আর অযোগ্য নেতৃত্ব। যারা দীর্ঘদিন ক্ষমতায় থেকেও মানুষের আস্থা ফিরিয়ে আনতে ব্যর্থ হয়েছে, তাদের হাতে আর কোনোদিন এই দেশকে নিরাপদ রাখা সম্ভব নয়।
প্রকৃতপক্ষে, এই দুর্নীতিগ্রস্ত রাজনীতিবিদদের মানসিক চিকিৎসার আওতায় আনা উচিত—কারণ তারা সত্যকে ভুলে গিয়ে মিথ্যাকে এতটাই চর্চা করেছে যে, আজ বাস্তবতা ও ভ্রান্তির ফারাকও তারা চিনতে পারে না। এদের হাতে দেশকে চালনা করা মানে ভবিষ্যৎকে অন্ধকারে ঠেলে দেওয়া।
তাহলে সামনে পথ কী?
দেশকে এগিয়ে নিতে হলে একমাত্র ভরসা সাধারণ জনগণ। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়—এই জনগণই বারবার অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছে। এখন প্রয়োজন তাদের ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টা, প্রয়োজন একটি নৈতিক বিপ্লব। আমাদের সময়ের দাবি হচ্ছে—সৎ, সাহসী এবং দায়িত্বশীল মানুষের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর। কেবল তারাই পারবে ভাঙা আস্থা মেরামত করতে, দেশকে সত্যিকার অর্থে গণতন্ত্র ও উন্নয়নের পথে এগিয়ে নিতে।
আজ বাংলাদেশ দাঁড়িয়ে আছে এক নতুন রাজনৈতিক কল্পনার দোরগোড়ায়। যদি আমরা সাহস করে মিথ্যার রাজনীতি থেকে বেরিয়ে আসতে পারি, যদি আমরা দুর্নীতির শৃঙ্খল ছিন্ন করতে পারি, তবে এই দেশ আবারও স্বপ্ন দেখবে—একটি স্বাধীন, ন্যায়ভিত্তিক, সমৃদ্ধ বাংলাদেশের।
আমার দৃঢ় বিশ্বাস—এখনই সময়। আর নয় আপস, আর নয় প্রতারণা। এখন দরকার সত্য, ঐক্য, আর নতুন নেতৃত্বের পথে অগ্রযাত্রা।
রহমান মৃধা, সাবেক পরিচালক, ফাইজার, সুইডেন। Rahman.Mridha@gmail.com
মত দ্বিমত
কেন শিবিরের বিরুদ্ধে এত প্রপাগান্ডা?
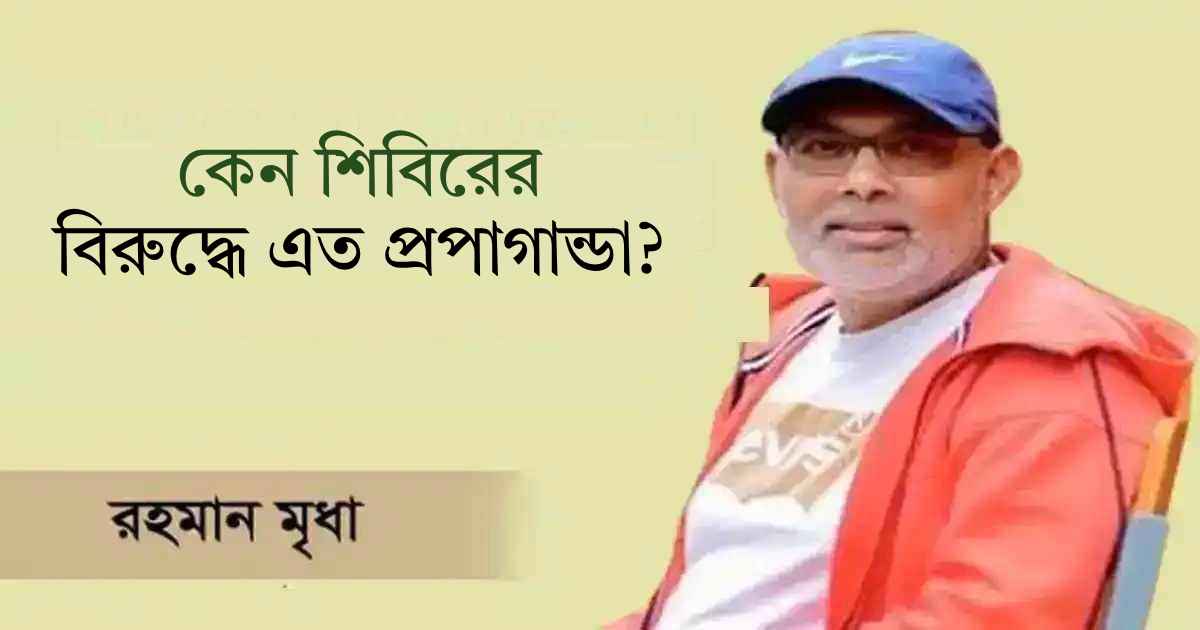
আমি চল্লিশ বছরেরও বেশি সময় ইউরোপে বসবাস করছি। এই দীর্ঘ সময়ে কখনো শুনিনি শিবির কোনো ভালো কাজ করেছে। বরং সবসময় শুনেছি তারা নৃশংস—মানুষের পায়ের রগ কেটে দেয়, নারীদের ধর্ষণ করে, সন্ত্রাসী বানায় ইত্যাদি। কিন্তু আমি দেশের বাইরে থাকলেও, বাংলাদেশের খবর–ঘটনায় সবসময় সচেতন থাকি। আন্দাজে বা গুজবের ওপর নির্ভর করি না। যাচাই–বাছাই ছাড়া কিছু লিখতেও চাই না। কারণ আমি জানি, ভ্রান্ত তথ্যের ভিত্তিতে লিখলে তা শুধু ভুল বার্তাই ছড়ায়।
ডাকসু নির্বাচনের সময় বেশ কিছু ঘটনা আমি লক্ষ্য করেছি। দেখলাম একজন শিক্ষার্থী ভিসিকে টেবিলে আঘাত করে হুমকি দিচ্ছে। একদল বহিরাগত গুণ্ডা ভাড়া করে বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢুকানো হয়েছে। আবার অন্য একটি পক্ষ ক্যাম্পাসের বাইরে দাঁড়িয়ে স্লোগান দিচ্ছে— শিবিরের চৌদ্দগুষ্টি উদ্ধার কর।
এমন সময়েই আমার মনে প্রশ্ন জাগল— যে সংগঠনকে নিয়ে এত নেতিবাচক প্রচারণা, তাদের সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা কীভাবে সম্পর্ক রাখছে? অবাক হয়ে দেখলাম, অনেক ছাত্রী শিবিরের নেতাকর্মীদের কাছে এসে ‘ভাইয়া’ বলে সম্বোধন করছে, সেলফি তুলছে। অথচ অন্য ছেলেরা ভদ্রভাবে কথা বললেও মেয়েরা তাড়াহুড়ো করে সরে যাচ্ছে। বিষয়টি আমাকে সত্যিই বিস্মিত করল।
আমি ভাবলাম— এখানে নিশ্চয়ই কোনো ভিন্ন সত্য লুকিয়ে আছে। রহস্য উদঘাটন করার আগেই সহধর্মিণীর সঙ্গে বিষয়টি আলোচনা করলাম। তিনি সুইডিশ। আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, “আচ্ছা বলো তো, কী কারণে একজন নারী কোনো পুরুষকে দেখে অস্বস্তি বোধ করে?”
তিনি বললেন, নারীদের মধ্যে বিশেষ এক ধরনের ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় কাজ করে। এই অনুভূতি তাদেরকে বুঝতে সাহায্য করে কে ভদ্র, কে কপট, কার সঙ্গে নিরাপদ। ভদ্রতা, নম্রতা, স্বাভাবিক ব্যবহার—এসব মেয়েরা খুব দ্রুত বুঝতে পারে।
আমি আবার তাঁকে কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, “তুমি আমাকে কীভাবে পছন্দ করলে?” তিনি হেসে উত্তর দিলেন, “তুমি তোমার আচরণ দিয়ে আমাকে পছন্দ করতে বাধ্য করেছিলে।”
সেখান থেকেই বুঝলাম—নারীরা আস্থার জায়গা থেকে সিদ্ধান্ত নেয়। ভয় বা বাহ্যিক ভদ্রতার আড়ালে লুকানো চরিত্র তারা টের পায়।
আমি আগে কখনো শিবির কী, তা ভালোভাবে জানতাম না। শুধু নেতিবাচক প্রচারণার ফলেই তাদের চিনি। কিন্তু লেখালেখির সুবাদে খোঁজখবর নিতে গিয়ে দেখলাম, ইসলামের মৌলিক কিছু অধিকার যেমন—শিক্ষার অধিকার, নারীর মর্যাদা, দুর্নীতির বিরুদ্ধে অবস্থান—এসব বিষয় তারা তাদের আদর্শের অংশ হিসেবে ধরে রেখেছে।
বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবিরের গঠনতন্ত্রে নারী শিক্ষার ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া আছে। তাদের ছাত্রীসংগঠন নারীদের মধ্যে নৈতিক শিক্ষা, আত্মমর্যাদা ও সামাজিক কাজের প্রচারে যুক্ত। যদিও রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের চাপে এই তথ্যগুলো প্রায়ই আড়ালে থাকে, কিন্তু যারা ভেতর থেকে চেনে তারা ভিন্ন অভিজ্ঞতার কথা বলে।
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মেয়েরা নিশ্চয়ই অজ্ঞ নন, তারা বোঝেন কোথায় নিরাপদ। অথচ প্রচারণায় শিবিরকে সবসময় অমানবিক ও হিংস্র হিসেবে দেখানো হয়। ডাকসু নির্বাচনের সময় আমি যদি নিজ চোখে দৃশ্যগুলো না দেখতাম, তাহলে হয়তো আমিও ধরে নিতাম—শিবির সত্যিই একটি সন্ত্রাসী সংগঠন।
তাহলে প্রশ্ন জাগে—সত্যকে এত ভয় পায় কেন? বিশেষ করে আওয়ামী লীগ ও বিএনপি নামের দুই বড় দল কেন শিবিরকে নির্মূল করার জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করে? নিশ্চয়ই এখানে অন্য কোনো রাজনৈতিক হিসাব আছে।
গতবছর আমি আমার ছোটবেলার বিদ্যালয়ের সভাপতি নির্বাচনে বিএনপির নেতাকর্মীদের দুর্নীতি দেখেছি। পরে ২০০৪ সালের গণঅভ্যুত্থানের পর থেকে দেখছি, যখন কেউ ভয়ে প্রতিবাদ করতে সাহস করে না, তখনই বুঝতে পেরেছি—আওয়ামী লীগের মতো বিএনপিরও পতন নিশ্চিত।
আমি সরাসরি তারেক রহমান ও তার দলের কিছু শীর্ষ নেতার সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলাম। বলেছিলাম, “আমরা সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে দেশকে দ্বিতীয়বার মুক্ত করেছি। এখনো যদি সন্ত্রাসীরাই দেশ দখল করে, তবে আগের সন্ত্রাসীদের অপরাধ কোথায় ভিন্ন?” কিন্তু কোনো লাভ হয়নি।
অত্যন্ত দুঃখের বিষয়, বঙ্গবন্ধুর মতো জিয়াউর রহমানের সঙ্গেও আমার ছোটবেলায় মেলামেশার সুযোগ হয়েছিল। তাই হয়তো মনে অজান্তেই তাঁদের প্রতি এক ধরনের শ্রদ্ধা জন্মেছিল। কিন্তু তাঁদের পরিবার ও উত্তরসূরিদের কর্মকাণ্ডে সেই শ্রদ্ধা মুছে গেছে।
দেশটা কারো বাপের নয়। আমি শুধু আমার দেশের মানুষের কথাই ভাবি। তাদের বিপদে–আপদে পাশে থাকার চেষ্টা করি। চাই—সবাই ভালো থাকুক। চাই—নতুন প্রজন্মকে বিশ্বাস করা হোক এবং দেশ পরিচালনার দায়িত্ব তাদের হাতে দেওয়া হোক।
আওয়ামী লীগ, বিএনপির মতো শিবিরও একটা নাম। শুধু নাম দিয়ে কাজ হয় না, সে প্রমাণ আমরা পেয়েছি। তবে মিথ্যাচার বা প্রপাগান্ডা না ছড়িয়ে বরং কাজের মাধ্যমে বিচার হওয়া উচিত। আজকের বাংলাদেশে দুর্নীতি ছেড়ে সত পথে চললে, সত্য কথা বললে শিবিরের মতো অন্যরাও আপনাকে অনুসরণ করবে।
পরনিন্দা, পরচর্চা ছেড়ে নিজের উন্নতির দিকে মন দিন। অন্তত আখেরাতের টিকিটটা সাথে নিতে পারবেন।
উপদেশ দেওয়ার প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু যেমন রেমিট্যান্স পাঠাতে কেউ আমাকে বলে না, তবু আমি পাঠাই—তেমনি উপদেশ দিতেও কেউ বলেনা, তবুও দিই—ক্ষতি কী?
রহমান মৃধা, সাবেক পরিচালক, ফাইজার, সুইডেন। Rahman.Mridha@gmail.com
মত দ্বিমত
ডাকসু নির্বাচন গণতন্ত্রের পথে কী আশা, বাধা ও সম্ভাবনার বার্তা দিল?
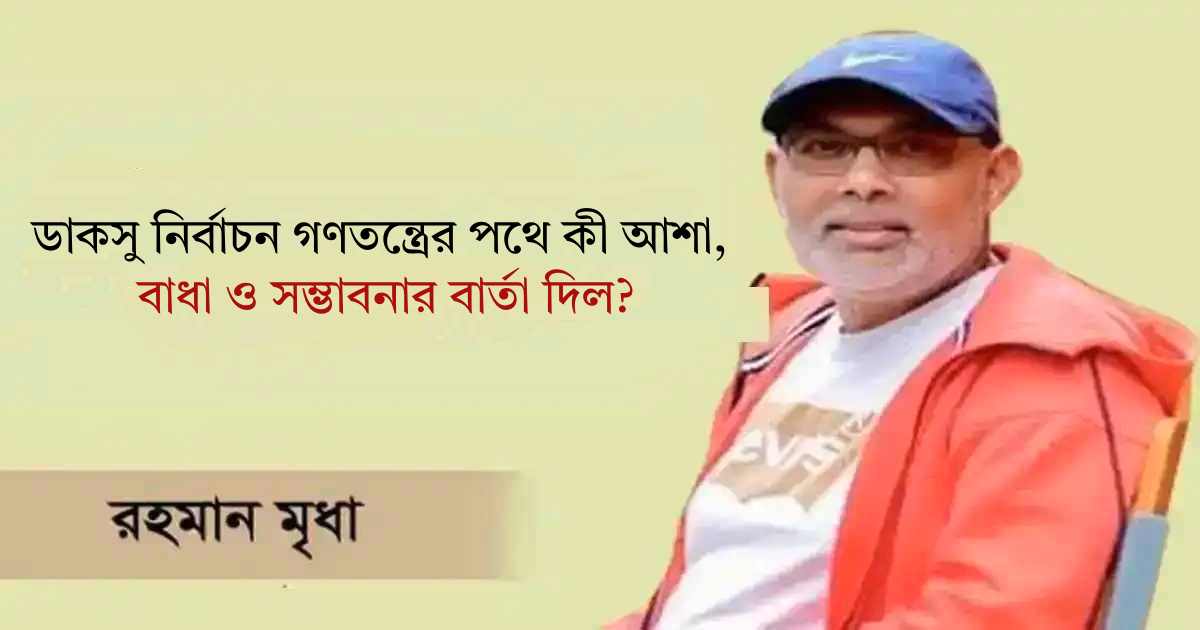
গণতন্ত্রের অনুশীলনকে যদি সঠিকভাবে মূল্যায়ন করতে হয়, তবে তার সূচনা হওয়া উচিত শিক্ষাঙ্গন থেকে। বিশেষ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, যাকে দেশের রাজনৈতিক ইতিহাসের কেন্দ্রবিন্দু বলা হয়, সেখানে ছাত্রসংগঠনের স্বাধীন নির্বাচন গণতান্ত্রিক চর্চার প্রথম পরীক্ষাগার। এবারের ডাকসু নির্বাচন অনেকেই মনে করেছিলেন একটি নতুন সূচনা হতে পারবে। কিন্তু বাস্তবতা বলছে, এখানেও বাধা এসেছে।
আমি খতিয়ে দেখেছি—কিছু শিক্ষার্থীকে তাদের নিজ এলাকার ক্ষমতাসীন বা প্রভাবশালী রাজনৈতিক দলের নেতাকর্মীরা ফোন করে চাপ দিতে চেষ্টা করেছেন। কেউ হয়তো সেটিকে উপেক্ষা করেছে, কেউ আবার ভয় পেয়েছে। প্রশ্ন হলো, এভাবেই কি আমরা গণতন্ত্রকে এগিয়ে নিতে চাই?
তবুও একটি বিষয় স্পষ্ট হয়েছে। বারবার দমন-পীড়নের পরও কেন শিবিরের মতো একটি সংগঠন শিক্ষার্থীদের মাঝে এখনো আকর্ষণ সৃষ্টি করে? গত ৫৪ বছরের অভিজ্ঞতা থেকে এটিই শেখার বিষয়—দমন কখনোই কোনো আদর্শকে মুছে ফেলতে পারে না। বরং দমন যত বেশি, তার প্রতিক্রিয়া সমাজে তত গভীরভাবে থেকে যায়। এখান থেকে রাষ্ট্র ও সমাজের জন্য কয়েকটি শিক্ষণীয় দিক রয়েছে। গণতন্ত্রে সমান সুযোগ মানে হলো শিক্ষার্থীরা বুঝে গেছে, কারো কণ্ঠ রুদ্ধ করা মানেই তাকে রাজনৈতিকভাবে দুর্বল করা নয়। বলপ্রয়োগ করে কাউকে হারানো যায় না, বরং যুক্তি ও আলোচনার মাধ্যমে প্রমাণ করতে হয় কোন পথ সঠিক। আর বিশ্ববিদ্যালয়ে যদি গণতান্ত্রিক অনুশীলন ব্যাহত হয়, তাহলে জাতীয় নির্বাচনে সুষ্ঠু পরিবেশ আশা করা বৃথা।
এখন প্রশ্ন আসে—ভালো আর মন্দের পার্থক্য কীভাবে নির্ধারণ করবো? ভালো হলো যেখানে স্বচ্ছতা, অংশগ্রহণ ও আলোচনার সুযোগ থাকে। আর মন্দ হলো যেখানে চাপ, প্রভাব, অর্থ আর ভয়ভীতি প্রাধান্য পায়। একটি সমাজ ও রাষ্ট্রের অগ্রগতির জন্য অপরিহার্য হলো, ভালোকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়া এবং মন্দকে রাজনৈতিক অঙ্গন থেকে সরিয়ে দেওয়া।
ডাকসু নির্বাচন গতকাল সম্পন্ন হয়েছে এবং আজ ফলাফল প্রকাশিত হয়েছে। এর ফলাফল এবং অভিজ্ঞতা থেকেই জাতির জন্য শিক্ষণীয় বিষয় হবে আসন্ন জাতীয় নির্বাচন। যদি ডাকসু নির্বাচন সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠিত হয়, তাহলে নির্বাচন কমিশনের প্রতি আস্থা বাড়বে এবং জাতীয় নির্বাচন সম্পর্কেও জনগণের মনে নতুন করে আশা জাগবে। কিন্তু এখানে মৌলিক প্রশ্ন উঠতে বাধ্য—আমরা যাকে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া বলছি, বাস্তবে কি সেটি সত্য? যদি সত্য হয়, তাহলে কেন একটি প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাঙ্গনের নির্বাচন সম্পন্ন করতে এত বিশাল প্রশাসনিক বাহিনী মোতায়েন করতে হয়? কেন নিরাপত্তা বাহিনীর উপস্থিতি ছাড়া আমরা শান্তিপূর্ণ পরিবেশ নিশ্চিত করতে পারি না?
আমরা যদি দেশের সর্বোচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি ডাকসু নির্বাচনও সম্মিলিত প্রচেষ্টায় সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়ন করতে না পারি, তাহলে ১৮ কোটি মানুষের জন্য যে গণতন্ত্রের চর্চার স্বপ্ন দেখাচ্ছি, সেটি কতটা বাস্তবসম্মত? অন্যদিকে, সন্ত্রাস, চাঁদাবাজি, হত্যা, লুটপাট, হামলার মতো অপ্রিয় সত্যগুলোকে সুন্দর ইংরেজি শব্দে “মব অ্যাকশন” বলে চালিয়ে দিলে বাস্তবতা কি পাল্টে যায়? যদি রাজনৈতিক এজেন্ডা বাস্তবায়নের পথ হয় ভয় দেখানো আর শক্তি প্রদর্শন, তবে সহজ, সঠিক এবং সরল পথে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা আদৌ কি সম্ভব?
এই প্রশ্নগুলো আমাদের নৈতিক চেতনার দ্বার খুলে দিক। এটিই হবে জনগণের শেখার সুযোগ—“লিসন অ্যান্ড লার্ন”। কারণ রাজনীতি করা আর রাজনীতি করতে চাওয়া দুটি আলাদা জিনিস; আবার দুর্নীতিবাজ রাজনীতিবিদ হয়ে রাজনীতি করাও একেবারেই ভিন্ন জিনিস। এই ভিন্ন জিনিসগুলো রাষ্ট্র থেকে একে একে দূর করতে হবে—এখনই।
অনেকে প্রশ্ন করতে পারেন—এত বড় দুর্নীতি এত অল্প সময়ে কীভাবে রোধ করা সম্ভব? আমি বলবো, অসম্ভব নয়। টুইন টাওয়ার ধ্বংস মুহূর্তেই ঘটেছিল। শেখ হাসিনার পতনও ঘটেছে হঠাৎ করেই। প্রাকৃতিক দুর্যোগ কিংবা মৃত্যু কখনোই পূর্বঘোষণা দিয়ে আসে না। তাহলে নির্বাচন ব্যবস্থার শুদ্ধিকরণ কি অসম্ভব? না, মোটেও নয়। যখন দুর্নীতি করা সম্ভব হয়েছে, তখন তা বন্ধ করাও সম্ভব—প্রয়োজন কেবল দৃঢ় সংকল্প আর সঠিক সিদ্ধান্ত।
আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতাও আমাদের শেখায়। ভারত বারবার ছাত্ররাজনীতিকে গণতন্ত্রের প্রস্তুতিমূলক অনুশীলন হিসেবে ব্যবহার করেছে। দক্ষিণ কোরিয়া ও তাইওয়ানের মতো দেশে ছাত্রআন্দোলন গণতান্ত্রিক রূপান্তরের প্রধান চালিকাশক্তি হয়েছে। এমনকি পশ্চিমা বিশ্বেও বিশ্ববিদ্যালয়গুলো প্রায়শই গণতন্ত্র ও সংস্কারের সূতিকাগার। বাংলাদেশের ডাকসু নির্বাচনও সেই ধারাবাহিকতার অংশ হতে পারে, যদি এটি সুষ্ঠু হয়।
সবশেষে একটি আহ্বান—গণতন্ত্র হোক কেবল মুখের বুলি নয়, জীবনের বাস্তব অনুশীলন। প্রশ্ন হতে পারে, বাংলাদেশ স্বাধীনতা অর্জনের পর বাস্তব অনুশীলনগুলো কী কখনও গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় হয়েছে? তাহলে আছে কী কোনো অনুসারী, যাদের পথ অনুসরণ করব? বাংলাদেশে নেই, কিন্তু আমাদের পূর্বপুরুষদের মাঝে আছে।
তাই আমি বলবো: চালাও সে পথে যে পথে তোমার প্রিয়জন গেছে চলি।
রহমান মৃধা
গবেষক ও লেখক
সাবেক পরিচালক, ফাইজার, সুইডেন
Rahman.Mridha@gmail.com
মত দ্বিমত
দুর্নীতিবাজ রাজনীতির অবসান: এক জাতীয় অঙ্গীকার
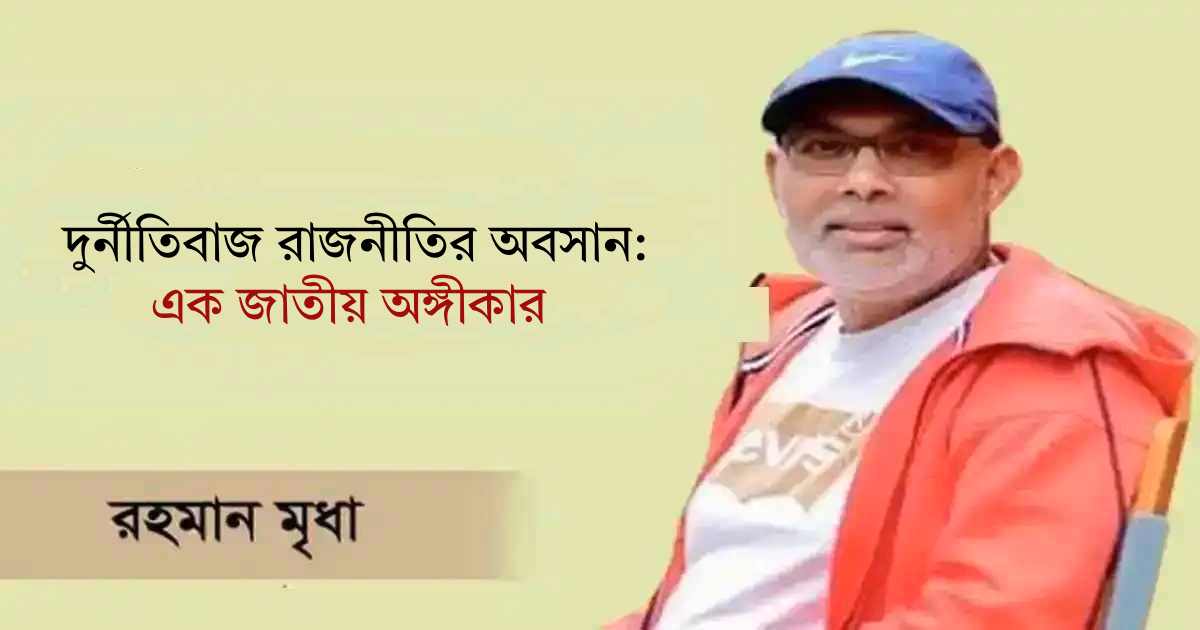
রাজনীতিবিদরা যদি রাজনীতি করে দেশের উন্নয়নে কোনো অবদান রাখতে না পারে, তবে তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া জরুরি। দরকার হলে জেলহাজতে পাঠাতে হবে, যাতে ভবিষ্যতে কেউ এ ধরনের অপকর্মে যুক্ত হওয়ার সাহস না পায়।
চুরি, ছিনতাই, মাদক ব্যবসা, সন্ত্রাস, অবৈধ অর্থ পাচার আর দুর্নীতি—এই অপরাধগুলোতে তারা সক্রিয়ভাবে জড়িত থেকেছে। প্রশ্ন হচ্ছে, গত ৫৪ বছরে তারা দেশের জন্য কী কোনো ভালো কাজ করেছে? যদি না করে থাকে, তবে কেন তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে না?
আপনি হাতে গুনে একজন সৎ রাজনীতিবিদের নাম বলতে পারবেন কি, যার নামে কোনো দুর্নীতির অভিযোগ নেই? যদি না পারেন, তবে বুঝতেই হবে যে গোটা রাজনৈতিক ব্যবস্থাই দুর্নীতিগ্রস্ত।
তাহলে প্রশ্ন দাঁড়ায়—অন্তর্বর্তীকালীন সরকার কী ধরনের সংস্কার করছে? গত এক বছরে তাদের বিরুদ্ধেও দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছে। দেশের মানুষের উন্নয়নের পরিবর্তে তুলনামূলকভাবে এসব অভিযোগই আলোচনায় এসেছে, যা একটি ভয়াবহ আশঙ্কার বিষয়।
এরপরও কি জাতি হিসেবে আমাদের কোনো দায়বদ্ধতা নেই? নিশ্চয়ই আছে। এই পরিস্থিতিকে এভাবে চলতে দেওয়া যায় না।
আমি আমার অবস্থান তুলে ধরলাম। যদি আপনি আমার কথার সঙ্গে দ্বিমত করেন, অনুগ্রহ করে যুক্তিসঙ্গত কারণ দেখিয়ে তা উপস্থাপন করুন। আমি আন্তরিকভাবে ক্ষমা চাইতে প্রস্তুত। কিন্তু যদি আমার বক্তব্যই সত্য প্রমাণিত হয়, তবে আসুন—আমরা একসাথে রুখে দাঁড়াই এবং দুর্নীতিবাজ রাজনীতির অপশক্তিকে বিদায় করি।
কারণ এরা দেশের শত্রু, এদের বাংলাদেশের মাটিতে থাকার কোনো অধিকার নেই। সংস্কার মানে একটাই—দুর্নীতিবাজ রাজনীতি দেশ থেকে চিরতরে বিদায় করা।
আমাদের করণীয়
• গণমাধ্যম ও সামাজিক মাধ্যমে দুর্নীতির প্রকৃত চিত্র তুলে ধরা।
• নাগরিকদের বোঝানো—দুর্নীতিবাজ রাজনীতিবিদ মানেই দেশের শত্রু।
• বিশেষ দুর্নীতি দমন ট্রাইব্যুনাল গঠন করে দ্রুত বিচার।
• অবৈধ সম্পদ বাজেয়াপ্ত করে রাষ্ট্রের কোষাগারে ফেরত আনা।
• দুর্নীতিবাজদের আজীবন রাজনীতি থেকে নিষিদ্ধ করা এবং তাদের পরিবারের বেআইনি সম্পদ বাজেয়াপ্ত করা।
• দুর্নীতিবাজ প্রার্থীদের নির্বাচনে অযোগ্য ঘোষণা।
• রাজনৈতিক দলে গণতন্ত্র ও স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা।
• তরুণ প্রজন্মকে দুর্নীতিবিরোধী আন্দোলনে যুক্ত করা।
• শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে সততা ও নৈতিকতা শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা।
• দুর্নীতিবাজদের সামাজিকভাবে বর্জন—তাদের বিয়ে, সমাবেশ, সমাজে কোনো সম্মান না দেওয়া।
• নিরপেক্ষভাবে দুর্নীতিবাজদের বিচারের আওতায় আনা।
• “দুর্নীতিমুক্ত বাংলাদেশ” ঘোষণা করে বাস্তবায়ন রোডম্যাপ তৈরি।
• বিদেশে পাচার করা অর্থ ফিরিয়ে আনা।
• দুর্নীতিবাজদের বৈদেশিক সম্পদের তথ্য প্রকাশ।
• সততা, স্বচ্ছতা ও ন্যায়বিচারকে জাতীয় সংস্কৃতিতে রূপান্তর।
• প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে “সততার উত্তরাধিকার” গড়ে তোলা।
• দুর্নীতিবিরোধী সব শক্তিকে ঐক্যবদ্ধ করা।
• প্রমাণ সংগ্রহ করে জনগণের সামনে প্রকাশ করা।
• আন্দোলনের মাধ্যমে জনচাপ সৃষ্টি করে সরকারকে বাধ্য করা।
• বিকল্প সৎ নেতৃত্বকে গড়ে তোলা।
• জাতীয় চার্টার বা ঘোষণা প্রকাশ করা—যেখানে থাকবে দুর্নীতির বিরুদ্ধে জাতির অবস্থান ও ভবিষ্যতের অঙ্গীকার।
জাতীয় অঙ্গীকার
• দুর্নীতির বিরুদ্ধে আপসহীন লড়াই চালাবো।
• সততা, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি প্রতিষ্ঠা করবো।
• দুর্নীতিবাজদের শুধু বিচার নয়, রাজনীতি থেকে চিরতরে বহিষ্কার করবো।
• জনগণ মিলে তাদের সামাজিকভাবে বর্জন করবো, যাতে আর কখনো কেউ দুর্নীতির সাহস না করে।
• ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে একটি ন্যায়ভিত্তিক রাষ্ট্র উপহার দেবো।
সারকথা: দুর্নীতিবাজ রাজনীতিকে বিদায় না দিলে, জাতির মুক্তি নেই। তাই আসুন, আমরা একসাথে রুখে দাঁড়াই।
রহমান মৃধা
গবেষক ও লেখক
সাবেক পরিচালক, ফাইজার, সুইডেন
Rahman.Mridha@gmail.com
মত দ্বিমত
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বনাম কেমব্রিজ: শিক্ষার মানের এক সঙ্কট এবং সম্ভাবনা
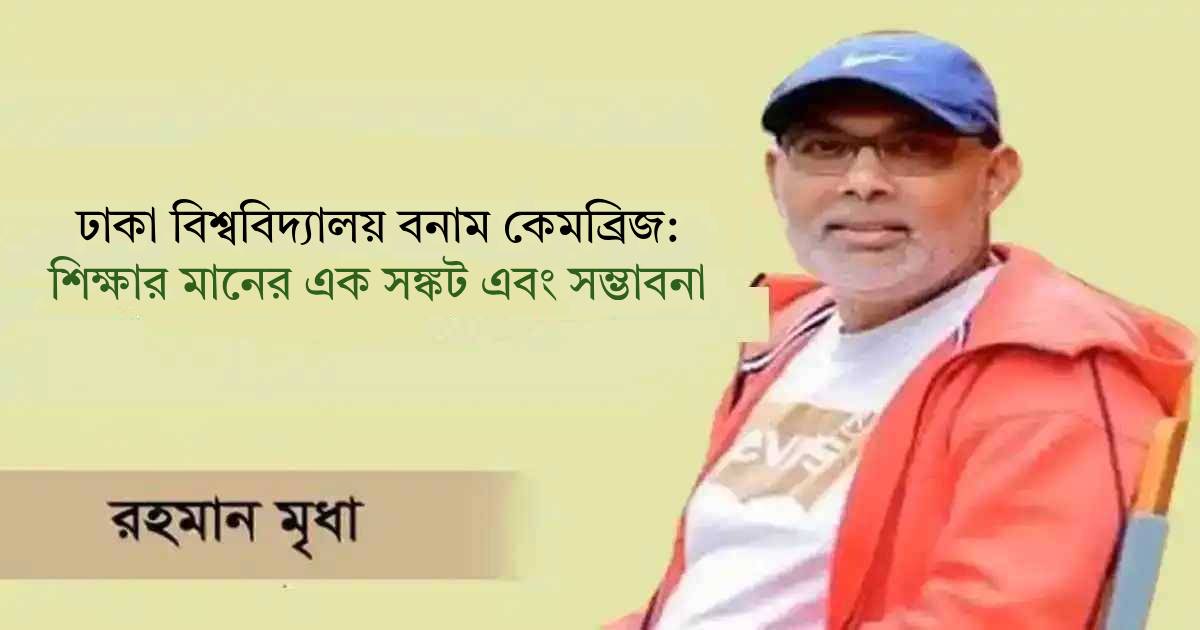
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশের উচ্চশিক্ষার প্রধান প্রতিষ্ঠান। এর স্থাপত্য, ইতিহাস এবং সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটের কারণে এটি বিশেষ মর্যাদা পেয়েছে। তবে বাস্তবতা দেখায় যে, শিক্ষার মান, প্রশাসনিক কার্যক্রম এবং রাজনৈতিক প্রভাবের কারণে বিশ্ববিদ্যালয় আজ নানা চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল লক্ষ্য শিক্ষার্থীর জ্ঞান, নৈতিকতা এবং চিন্তাশীলতার বিকাশ, কিন্তু কিছু বাস্তব সমস্যা এই লক্ষ্যকে প্রভাবিত করছে। অনেক শিক্ষার্থী রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড এবং অন্যান্য কারণে নিয়মিত ক্লাসে উপস্থিত হয় না। কিছু বিভাগে অভিজ্ঞ শিক্ষকের অভাব এবং অপ্রশিক্ষিত শিক্ষক থাকায় শিক্ষার মানে ভিন্নতা দেখা যায়। কেন্দ্রীয় লাইব্রেরিতে প্রচুর বই আছে, তবে অনেক বই ব্যবহারযোগ্য নয় বা রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে শিক্ষার্থীর গবেষণার কাজে আসে না। বিশ্ববিদ্যালয় প্রায়শই রাজনৈতিক ছাত্রসংগঠনের প্রভাবের মুখোমুখি হয়। রাজনৈতিক সংঘর্ষ, দ্বন্দ্ব এবং প্রভাব শিক্ষার্থীর নিরাপত্তা ও ক্যাম্পাসের শান্তিকে প্রভাবিত করতে পারে। অবস্থান সংসদ ভবনের কাছাকাছি হওয়ায় রাজনৈতিক প্রভাব আরও প্রকট। কিছু ক্ষেত্রে, প্রশাসনিক দুর্বলতা ও অব্যবস্থাপনার কারণে শিক্ষার্থীরা অসুবিধায় পড়ে।
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রাবাস বা হলগুলোতে শিক্ষার্থীরা নানা ধরনের সাংস্কৃতিক, সামাজিক এবং রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করে। তবে, কিছু অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা ঘটে, এবং কিছু শিক্ষার্থী ক্লাসে না এসে বাইরে সময় কাটাতে পছন্দ করে। রাজনৈতিক ছাত্রসংগঠনের প্রভাব থাকায় কিছু শিক্ষার্থী ক্ষমতাসীন দলের সমর্থন না থাকলে বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হতে পারে। শিক্ষার মান নিয়ে কথাবার্তা কম হয়, এবং শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের নৈতিকতার বিষয়ও প্রায়শই আলোচনার বাইরে থাকে।
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান অবস্থার পেছনে রাজনৈতিক প্রভাব, প্রশাসনিক দুর্বলতা, শিক্ষার মানের অবনতি এবং শিক্ষাব্যবস্থায় দুর্নীতি অন্যতম কারণ। প্রতিষ্ঠার সময় বিশ্ববিদ্যালয়কে উচ্চমানের শিক্ষা ও গবেষণার ক্ষেত্রে অগ্রগতি করার জন্য পরিকল্পনা করা হয়েছিল। তবে বর্তমান সময়ে বাস্তবতা অনেক ক্ষেত্রেই প্রত্যাশার সাথে মিলছে না। বিশ্ববিদ্যালয়কে শিক্ষার মান, গবেষণার অগ্রগতি, প্রশাসনিক কার্যক্রম এবং শিক্ষার্থীদের নৈতিকতার ভিত্তিতে মূল্যায়ন করা উচিত। এই মূল্যায়ন বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন, শিক্ষাবিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং স্বাধীন মূল্যায়ন সংস্থার মাধ্যমে নিয়মিতভাবে, যেমন প্রতি পাঁচ বছরে একবার, অনুষ্ঠিত হওয়া উচিত।
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এখনও সম্ভাবনাময়। তবে রাজনৈতিক প্রভাব, প্রশাসনিক দুর্বলতা এবং শিক্ষার পরিবেশে বিঘ্ন থাকায় এটি তার পূর্ণ সম্ভাবনা অর্জন করতে পারছে না। শিক্ষার্থী, শিক্ষক, প্রশাসন এবং নীতি নির্ধারকদের যৌথ প্রচেষ্টা বিশ্ববিদ্যালয়কে একটি উচ্চমানের শিক্ষার প্রতিষ্ঠান হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে পারে। সঠিক পদক্ষেপ, স্বচ্ছতা এবং সংস্কারই সেই পথে দিশা দেখাবে।
ওক্সফোর্ড বা কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় বিশ্বের প্রাচীন ও মর্যাদাপূর্ণ উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে অন্যতম। আমি জীবনের কোনো এক সময় কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়েছি, তাই এর শিক্ষার মান, কলেজ ব্যবস্থা এবং গবেষণার সুযোগ সম্পর্কে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা আছে। প্রতিষ্ঠার থেকে আজ পর্যন্ত এটি শিক্ষার মান, গবেষণার গুণগত মান এবং প্রশাসনিক স্বচ্ছতার ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক মানদণ্ড হিসেবে পরিচিত। এখানে শিক্ষার্থীর নৈতিক ও মানসিক বিকাশকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেওয়া হয়। শিক্ষার্থীরা নিয়মিত ক্লাসে অংশগ্রহণ করে, এবং পাঠ্যক্রমের সঙ্গে গবেষণার সুযোগ সমন্বিত। শিক্ষকগণ অত্যন্ত দক্ষ, প্রশিক্ষিত এবং শিক্ষাদানে নিবেদিত, যা শিক্ষার মানকে ধারাবাহিকভাবে উচ্চ রাখে। কেমব্রিজে রাজনৈতিক প্রভাব সীমিত; প্রশাসনিক ব্যবস্থা স্বচ্ছ এবং নিরপেক্ষ, ফলে শিক্ষার্থীর নিরাপত্তা, ক্যাম্পাসের শান্তি এবং শিক্ষার পরিবেশে বিঘ্ন ঘটে না।
লাইব্রেরি এবং গবেষণা সুবিধা অত্যন্ত সমৃদ্ধ। বই ও রিসোর্সের সংখ্যা প্রচুর, আধুনিক ডিজিটাল রিসোর্স সহজলভ্য, এবং রক্ষণাবেক্ষণ যথাযথভাবে করা হয়। শিক্ষার্থীরা গবেষণার জন্য প্রয়োজনীয় সব সুযোগ ও তথ্য পায়। ক্লাস এবং গবেষণার মধ্যে সমন্বয় অত্যন্ত সুচারু, ফলে শিক্ষার্থীর জ্ঞান ও চিন্তাশীলতা সর্বোচ্চ মাত্রায় বিকাশ লাভ করে। শিক্ষার্থী ও শিক্ষক উভয়ই শিক্ষার প্রতি নিবেদিত, এবং নৈতিকতার মানও দৃঢ়।
কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থীর সার্বিক উন্নয়নের ওপর গুরুত্ব দেয়। কেবল পাঠ্যক্রম নয়, সাংস্কৃতিক, সামাজিক এবং শিক্ষণীয় কর্মকাণ্ডও শিক্ষার্থীর জীবনের অংশ। প্রশাসনিক ও শিক্ষাগত ব্যবস্থাপনা একে একটি স্থিতিশীল এবং ফলপ্রসূ শিক্ষা পরিবেশ হিসেবে গড়ে তোলে। আন্তর্জাতিক মানের গবেষণা, বিশ্বখ্যাত শিক্ষক এবং সুশৃঙ্খল প্রশাসন প্রতিষ্ঠানটিকে বিশ্বজুড়ে শিক্ষার্থীর কাছে অত্যন্ত মর্যাদাপূর্ণ করে তুলেছে।
বিশ্ববিদ্যালয়টি তার ইতিহাসের প্রতিটি স্তরে শিক্ষার মান, গবেষণার সুযোগ এবং শিক্ষার্থীর নৈতিক বিকাশকে অগ্রাধিকার দিয়ে এসেছে। শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি, মনোযোগ এবং কার্যকলাপের মান নিয়মিতভাবে পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন করা হয়। প্রশাসনিক স্বচ্ছতা এবং শিক্ষক-শিক্ষার্থী সম্পর্কের স্বচ্ছতা শিক্ষার মানকে বজায় রাখতে সাহায্য করে। ফলে, কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় একটি আদর্শ শিক্ষার পরিবেশ হিসেবে বিশ্ব মানচিত্রে পরিচিত।
দুটি বিশ্ববিদ্যালয়, দুটো চিত্র—ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়। একটির অভ্যন্তরীণ অবস্থা রাজনৈতিক প্রভাব, প্রশাসনিক দুর্বলতা, শিক্ষার মানের অনিয়ম এবং দুর্নীতিতে ভরা; অন্যটি স্থিতিশীল, স্বচ্ছ প্রশাসন ও উচ্চমানের শিক্ষায় নিবেদিত। এ থেকে আমাদের জাতি হিসেবে বড় প্রশ্ন জাগে—আমরা কীভাবে দেশের দুর্নীতি ছাড়া প্রতিযোগিতার বাজারে টিকে থাকব? বিদেশের সঙ্গে যখন প্রতিযোগিতা অব্যাহত, আমাদের শিক্ষার মান, নৈতিকতা, প্রশাসনিক স্বচ্ছতা এবং দুর্নীতিহীন পরিবেশ যদি এমন অবস্থায় থাকে, তাহলে আমাদের শিক্ষার্থী ও প্রজন্ম কিভাবে আন্তর্জাতিক মানের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে পারবে?
সমস্যার মূল কারণ স্পষ্ট: রাজনৈতিক প্রভাব, প্রশাসনিক দুর্বলতা, শিক্ষার প্রতি উদাসীনতা, নৈতিকতার অভাব এবং দেশের মধ্যে সিস্টেমিক দুর্নীতি। শিক্ষার প্রতিষ্ঠানগুলোতে যদি এই উপাদানগুলো নিয়ন্ত্রণে না থাকে, তবে জাতির ভবিষ্যৎ ও প্রতিযোগিতামূলক সক্ষমতা দুটোই ক্ষতিগ্রস্ত হয়।
করনীয় স্পষ্ট: প্রথমে শিক্ষার মান নিশ্চিত করতে হবে। শিক্ষকের যোগ্যতা, পাঠ্যক্রমের গুণমান এবং গবেষণার সুযোগ উন্নত করতে হবে। প্রশাসনিক স্বচ্ছতা আনার জন্য নিয়মিত মূল্যায়ন ও তদারকি প্রয়োজন। রাজনৈতিক প্রভাব কমাতে স্বাধীন, নিরপেক্ষ প্রশাসন প্রতিষ্ঠা করতে হবে। শিক্ষার্থীর নৈতিকতা ও মনোযোগ বৃদ্ধির জন্য পড়াশোনা এবং গবেষণাকে অনুপ্রেরণামূলক পরিবেশে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। দুর্নীতিহীন পরিবেশ প্রতিষ্ঠা এবং সংস্কারমুখী নীতি কার্যকর করা অপরিহার্য।
যদি এসব পদক্ষেপ নেওয়া যায়, তবে আমরা একটি সংস্কারমূলক পথ ধরে জাতি হিসেবে আন্তর্জাতিক মানের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে পারব। প্রতিযোগিতার বাজারে টিকে থাকার জন্য শিক্ষা, নৈতিকতা, প্রশাসনিক স্বচ্ছতা এবং দুর্নীতিহীন পরিবেশ—এই চারটি উপাদানই আমাদের ভবিষ্যতের মূল চাবিকাঠি।
রহমান মৃধা, সাবেক পরিচালক, ফাইজার, সুইডেন। Rahman.Mridha@gmail.com




























