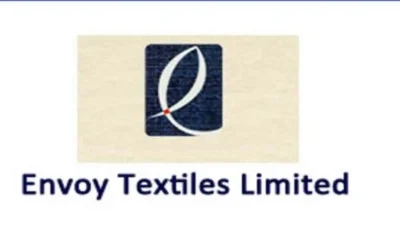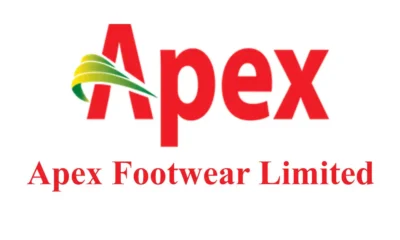মত দ্বিমত
ইলন মাস্ক: প্রযুক্তির দুনিয়ায় বিপ্লবের এক অপ্রতিরোধ্য যাত্রা
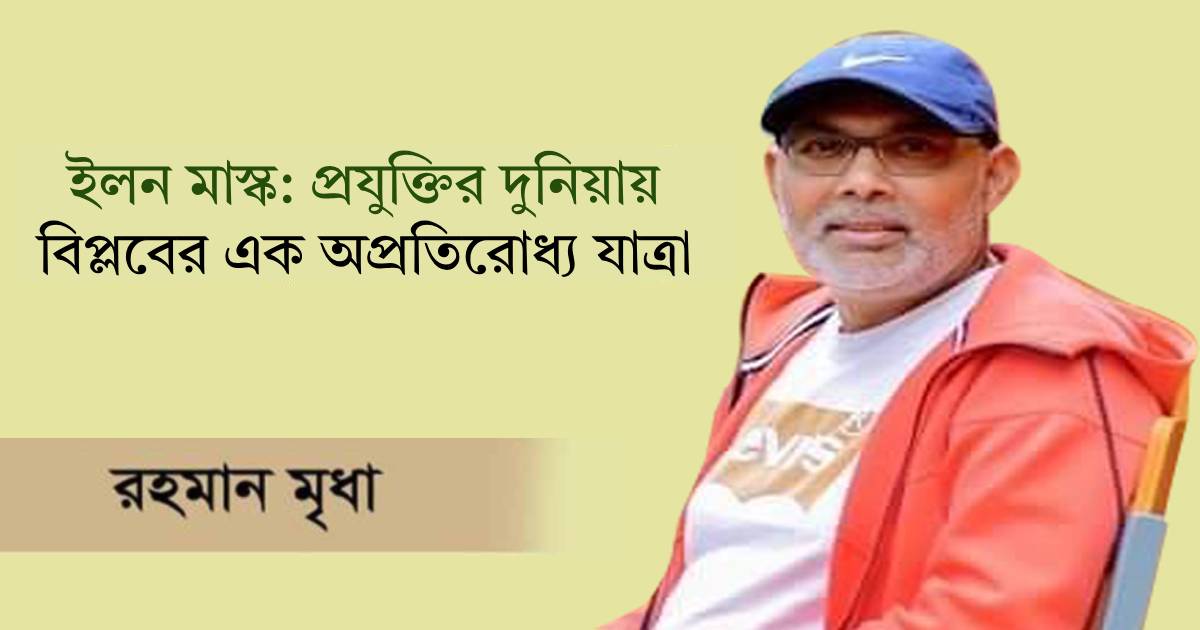
ইলন মাস্ক, সেই নামটি যা বিশ্বের প্রান্তে প্রান্তে ছড়িয়ে পড়েছে, তার অবদান প্রযুক্তির প্রতিটি দিকেই স্পষ্ট। সাধারণ মানুষ তাকে শুধু টেসলা, স্পেসএক্স, সোলারসিটি কিংবা হাইপারলুপ এর মতো বিপ্লবী উদ্ভাবনী প্রকল্পের উদ্যোক্তা হিসেবে জানে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তিনি শুধুমাত্র একজন উদ্ভাবক নন, বরং একটি অসীম সাহসী ব্যবসায়ী এবং ভবিষ্যৎবিদ।
ইলন মাস্কের জীবনে চড়াই-উতরাই ছিলো। এলন মস্কের জন্ম দক্ষিণ আফ্রিকায় ১৯৭১ সালে, এবং সেই শিশুকাল থেকে শুরু হয় তাঁর আগ্রহের যাত্রা। ছোটবেলা থেকেই তিনি প্রযুক্তির প্রতি গভীর আগ্রহ তৈরি করেন, আর এই আগ্রহই একদিন তাকে পৃথিবীর সবচেয়ে বড় প্রযুক্তি সংস্থাগুলোর প্রধান কর্ণধারে পরিণত করে। পেপাল, টেসলা এবং স্পেসএক্স প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে তাঁর নয়া ব্যবসায়িক সম্রাজ্যের সূচনা হয়।
তবে তার জীবন সহজ ছিল না। টেসলা এর উত্থান থেকে শুরু করে, স্পেসএক্স এর অস্থির যাত্রা এবং সর্বশেষ হাইপারলুপ এর মতো অসম্ভব পরিকল্পনা, প্রতিটি পদক্ষেপে ছিলো অগণিত চ্যালেঞ্জ, বিতর্ক এবং তার উপরে উচ্চাকাঙ্ক্ষী অঙ্গীকার। অনেকেই মনে করেছিলেন, তাঁর প্রকল্পগুলো শুধুমাত্র আর্থিক সংকট এবং অস্থিরতার দিকে এগিয়ে যাবে, কিন্তু ইলন মাস্কের দৃঢ় সংকল্প এবং ভবিষ্যৎমুখী ভাবনা তাকে সর্বত্র সফলতার চূড়ায় পৌঁছে দেয়।
পৃথিবী বদলে দেওয়ার যাত্রা
বিশ্বে তাঁর শিরোনামে যেসব প্রতিষ্ঠানগুলো জনপ্রিয়তা পেয়েছে, সেগুলোর মধ্যে অন্যতম টেসলা। টেসলা একসময় শুধুমাত্র একটি স্বপ্ন ছিলো, যা অনেকের কাছে অসম্ভব মনে হয়েছিলো। কিন্তু মাস্ক তার ব্যক্তিগত জীবনের চ্যালেঞ্জ ও ভাঙাচোড়া সম্পর্ক সত্ত্বেও, নিজস্ব প্রযুক্তির ওপর বিশ্বাস রেখে সেই অসম্ভবকেও সম্ভব করেছেন। প্রযুক্তিগত দিক থেকে, টেসলা এর বৈদ্যুতিক গাড়ি, শক্তি সংরক্ষণ এবং পরিবেশবান্ধব যন্ত্রপাতি বিপ্লব সৃষ্টি করেছে।
আরেকটি দৃষ্টান্ত স্থাপনকারী প্রকল্প হলো স্পেসএক্স, যার লক্ষ্য ছিল মহাকাশে বাণিজ্যিকভাবে প্রবেশের জন্য একটি নতুন পথ সৃষ্টি করা। মাস্ক স্পেসএক্সের মাধ্যমে পৃথিবী থেকে বাইরের মহাকাশে মানুষের যাত্রা শুরু করতে চেয়েছিলেন এবং সেখানেও তাঁর আগ্রহ সফল হয়েছে।
ব্যক্তিগত জীবন ও একাধিক বিবাহ
তবে, প্রযুক্তির জগতের পাশাপাশি ইলন মাস্কের ব্যক্তিগত জীবনও বিভিন্ন দিক থেকে আলোচিত। ট্যালুলাহ রেইলি, জাস্টিন মাস্ক, এবং গ্রিমস এর মতো ব্যক্তিত্বের সঙ্গে তার একাধিক সম্পর্ক এবং বিবাহ, তাঁর জীবনকে আরো জটিল করে তুলেছিলো। এসব সম্পর্কের পাশাপাশি, তার সন্তানদের প্রতিও তিনি গভীরভাবে মনোযোগী ছিলেন, তবে অনেকেই তাঁর জীবনযাত্রা এবং ব্যক্তিগত সম্পর্কগুলো নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে। তাছাড়া, রোলিং স্টোন এর এক সাক্ষাৎকারে তিনি নিজেই জানিয়েছেন, তিনি ব্যস্ততার কারণে নিজের সন্তানদের সঙ্গ যথেষ্ট সময় দিতে পারেননি এবং এই বিষয়টি তার কাছে ‘রিগ্রেট’ ছিলো।
রাজনৈতিক অন্তর্দ্বন্দ্ব এবং ট্রাম্প প্রশাসন
এদিকে, ইলন মাস্কের রাজনৈতিক অবস্থানও গত এক দশক ধরে অনেক পরিবর্তিত হয়েছে। একসময় তিনি বিল গেটস এবং বারাক ওবামা এর প্রতি সমর্থন জানিয়েছিলেন, কিন্তু বর্তমানে তিনি নিজের অবস্থান অনেকটাই মধ্যপন্থী হিসাবে তুলে ধরেন। ট্রাম্প প্রশাসনের সময় তার কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত এবং মন্তব্য শিরোনাম হয়েছে। সেখান থেকে, তিনি খুবই বিতর্কিত পরিসরে পড়েছিলেন, কারণ তিনি ট্রাম্পের বেশ কিছু সিদ্ধান্তের সমর্থক ছিলেন। তবে, একসময় তিনি এই প্রশাসন থেকে সরে গিয়ে, নিজের ব্যক্তিগত কর্মকাণ্ড এবং ব্যবসায়িক দিক আরও শক্তভাবে পুনর্নির্মাণে মনোনিবেশ করেছেন।
ব্যবসায়িক দিক থেকে নতুন সিদ্ধান্ত
বর্তমানে, ইলন মাস্কের সিদ্ধান্ত ছিলো ট্রাম্প প্রশাসন থেকে সরে গিয়ে, তার নিজস্ব ব্যবসায়িক দুনিয়ায় ফিরে যাওয়া। সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম ‘X’ এর ওপর তার কাজের মাধ্যমে তিনি বিশ্বজুড়ে যোগাযোগের নতুন এক দিগন্ত খুলে দিতে চান, যেখানে তার লক্ষ্য প্রযুক্তি, যোগাযোগ এবং সামাজিক সংস্কৃতি নিয়ে নতুন দৃষ্টিভঙ্গি সৃষ্টি করা। তবে, ইলন মাস্কের মতো একজন বিশাল ব্যক্তিত্বের জন্য নতুন সিদ্ধান্ত সবসময়ই বিস্ময়ের সৃষ্টি করে। টেসলা, স্পেসএক্স, বোরিং কোম্পানি-এর মতো বিপ্লবী উদ্যোগের পাশাপাশি, তাঁর চিন্তাধারা ভবিষ্যতের প্রতি আশাবাদী। অর্থনৈতিক দিক থেকে তিনি বিপুল লাভের দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন, তবে তার রাজনৈতিক অবস্থান এবং ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে চলমান বিতর্ক তাকে সবার চোখে আরও আলাদা করে তোলে।
সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রভাব: এক নতুন দিগন্তে ইলন মাস্ক
ইলন মাস্ক, যিনি প্রযুক্তির বিশ্বে সবচেয়ে প্রভাবশালী ব্যক্তিত্বদের মধ্যে একজন, তিনি ভবিষ্যতের দিকে আরও একধাপ এগিয়ে চলেছেন। তবে, শুধু প্রযুক্তির উদ্ভাবনই নয়, সামাজিক এবং রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও তার অবদান ও প্রভাব লক্ষণীয়। ইলন মাস্কের কাজের উদ্দেশ্য শুধু পৃথিবী পরিবর্তন নয়, বরং সমাজের মানসিকতাও পরিবর্তন করা। তিনি বিশ্বাস করেন যে, বিশ্বায়ন এবং উন্নত প্রযুক্তি পৃথিবীকে সমৃদ্ধ করবে এবং কেবল নির্দিষ্ট কিছু মানুষের জন্য নয়, বরং সবার জন্য সুফল বয়ে আনবে।
অর্থনৈতিক শক্তি: ভবিষ্যতে কি অপেক্ষা করছে?
মাস্কের ব্যবসায়িক দিক থেকে, তার প্রতিষ্ঠানগুলোর আর্থিক অবস্থা অত্যন্ত শক্তিশালী, এবং তার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা সেগুলোর মধ্যে নতুন উচ্চতায় পৌঁছানোর ব্যাপারে। টেসলা এখন একটি গুরুত্বপূর্ণ কোম্পানি, যেটি বিদ্যুৎচালিত গাড়ির বাজারে একাধিক বিপ্লব ঘটিয়েছে। শুধু গাড়ি নয়, তাদের শক্তি সংরক্ষণ প্রযুক্তি, সোলার প্যানেল, এবং নতুন নকশার ব্যাটারি প্রযুক্তি কোম্পানিকে অর্থনৈতিক দিক থেকে আরও শক্তিশালী করেছে।
তবে, স্পেসএক্স-এর প্রভাব অনেক বিস্তৃত। মহাকাশের বাজারে সাশ্রয়ী ও উন্নত প্রযুক্তি এনে স্পেসএক্স মানুষকে মহাকাশে প্রেরণের জন্য প্রস্তুত করেছে। এলন মাস্কের লক্ষ্য, শুধু পৃথিবী বা রোবোটিক প্রযুক্তির মাধ্যমেই মানুষের জীবন উন্নত করা নয়, বরং মঙ্গলগ্রহের উপনিবেশ স্থাপন করা। এটি একটি দুরূহ পরিকল্পনা হলেও মাস্ক তার অসীম বিশ্বাসের সাথে এগিয়ে যাচ্ছেন। তিনি বিশ্বাস করেন, মঙ্গলগ্রহের জন্য উপনিবেশ স্থাপন একমাত্র উপায় হতে পারে যদি পৃথিবী কখনো বিপদে পড়ে বা মানবজাতি একটি নতুন স্থান খুঁজে পায়।
সামাজিক যোগাযোগ ও ডিজিটাল বিপ্লব
একটি গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্ত আসে যখন মাস্ক ট্রাম্প প্রশাসন থেকে সরে গিয়ে তার নিজের ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম এবং সম্প্রচার ব্যবসার দিকে মনোযোগ দেন। তার এক্স (X) সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মটি সামাজিক যোগাযোগের দুনিয়াতে নতুন অধ্যায় রচনা করার জন্য প্রস্তুত। এখানে গণতন্ত্র এবং বিশ্বের নেতাদের প্রতি সংলাপের মাধ্যমে সমাজের প্রভাব পরিবর্তন করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। তার একমাত্র উদ্দেশ্য হলো সোশ্যাল মিডিয়ায় সঠিক তথ্য প্রবাহ, যাতে বিভ্রান্তি এবং মিথ্যা তথ্য রোধ করা যায়।
তিনি মনে করেন, ডিজিটাল স্পেসে তাকে চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে হবে। তবে এক্স তার নিজস্ব সামাজিক সংলাপকে পরবর্তী স্তরে নিয়ে যেতে সক্ষম হবে, বিশেষত যখন তার মতো একটি ব্যক্তিত্ব সামগ্রিকভাবে নতুন প্রযুক্তি এবং রাজনৈতিক চিন্তাভাবনাকে প্রভাবিত করে।
ব্যক্তিগত জীবন: কোনো পরিবর্তন আসছে?
এদিকে, ইলন মাস্কের ব্যক্তিগত জীবনও অতীতে ছিল বিতর্কিত এবং চ্যালেঞ্জপূর্ণ। একাধিক বিবাহ এবং সন্তানের মধ্যে তার সম্পর্ক অনেকাংশেই আলোচিত। তবে, তার বর্তমান জীবনে, গ্রিমসের সাথে তার সম্পর্কটিকে তিনি প্রযুক্তি, সামাজিক যোগাযোগ এবং শিল্পের একটি মেলবন্ধন হিসেবে দেখতে শুরু করেছেন। তার সন্তানদের প্রতি গভীর সম্পর্ক, যেখানে তিনি অনেক সময় কাজে মগ্ন থাকলেও তার সন্তানদের পাশে দাঁড়াতে চেষ্টা করেন। তবে, তার নিজস্ব জীবনের অবিচ্ছিন্ন চাপ তাকে কখনো কখনো বিশেষ মুহূর্তগুলো উপভোগ করতে বাধা দেয়।
রিগ্রেট এবং নতুন শিখন
ইলন মাস্ক নিজেই বিশ্ববিদ্যালয়ের আকাশছোঁয়া জীবন থেকেও বলতে দ্বিধা করেন যে, কিছু বিষয়, যেমন অতিরিক্ত কাজের চাপ বা পরিবারে তার উপস্থিতির অভাব, তিনি অতীতে রিগ্রেট করেন। তবে, তিনি একে একটি শিক্ষণীয় বিষয় হিসেবে দেখেন এবং মনে করেন, ‘সবকিছু একসাথে থাকা সম্ভব নয়, তবে পরবর্তী সময়ে অন্যদের পাশে থাকতে পারা যাবে’।
রাজনৈতিক ভূমিকা: বিশ্বকে একত্রিত করা
এদিকে, রাজনীতি এবং বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক অবস্থান নিয়ে মাস্কের চিন্তাধারা খুবই মৌলিক এবং ব্যক্তিগত। তার মতো একজন প্রযুক্তিবিদ ও ব্যবসায়ী, বিশ্বের সরকারগুলোর মধ্যে প্রযুক্তি ভিত্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রতি একেবারেই আগ্রহী। বিশ্ব অর্থনীতির উন্নতি এবং বিশ্বব্যাপী সমস্যাগুলোর সমাধান সম্ভব করতে তিনি বিশ্বাস করেন, গ্লোবাল প্রযুক্তির একীভূত সহযোগিতা এবং সামাজিক ন্যায়বিচার প্রয়োজন।
মাস্ক জানেন যে, তার পদক্ষেপ শুধু প্রযুক্তিগত উদ্ভাবন নয়, বরং রাজনৈতিক, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক প্রভাবের ক্ষেত্রেও হতে হবে। তিনি চান, বিশ্বকে একীভূত করা, যেখানে সবার কাছে সুযোগ থাকবে।
শেষ কথা: অতীতের শিক্ষা, বর্তমানের সংগ্রাম এবং ভবিষ্যতের রূপকল্প
ইলন মাস্কের জীবনে যতই প্রতিকূলতা বা সমালোচনা আসুক না কেন, তিনি একটি নতুন পৃথিবী গড়ার পরিকল্পনা নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছেন। তার উদ্দেশ্য শুধু ব্যবসা নয়, বরং বিশ্বের ভবিষ্যৎ। উন্নত প্রযুক্তি, কর্মসংস্থান, গ্রহের সুরক্ষা এবং বৈষম্য দূরীকরণ—এগুলোই তার চূড়ান্ত লক্ষ্য।
তবে, পৃথিবীর পরিবর্তন এত সহজ নয়। মাস্কের পথে চ্যালেঞ্জ থাকবে, অনেকটা ট্রাম্প প্রশাসন থেকে সরে গিয়ে নতুন দিশা খোঁজা যেমন ছিলো, তেমনি প্রতিটি পদক্ষেপ নতুন উত্তরণের কথা বলে। শেষমেশ, ইলন মাস্ক আজ যেভাবে ভবিষ্যতের রূপান্তরের জন্য কাজ করছেন, তাতে একদিন তিনি হয়তো একটি নতুন যুগের সূচনা করবেন, যা প্রযুক্তি, সমাজ এবং অর্থনীতির দিক থেকে ইতিহাসে চিরকাল স্মরণীয় হয়ে থাকবে।
পরিশেষে, ইলন মাস্কের যাত্রা অবিরাম, দৃঢ়বিশ্বাসী এবং অপ্রতিরোধ্য- এটি প্রযুক্তির ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায়, যা কেবল ভবিষ্যতের জন্য নয়, বর্তমানে পৃথিবীকে নতুন দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে দেখার সুযোগ সৃষ্টি করছে।
লেখক: রহমান মৃধা, সাবেক পরিচালক, ফাইজার, সুইডেন
অর্থসংবাদে প্রকাশিত কোনো সংবাদ বা কনটেন্ট কপিরাইট আইনে পূর্বানুমতি ছাড়া ব্যবহার করা যাবে না।

মত দ্বিমত
লুণ্ঠন আর লাশের ভাণ্ডারে পরিণত বাংলাদেশ: রাজনীতি নয়, মাফিয়া সিন্ডিকেটের দখলদারি
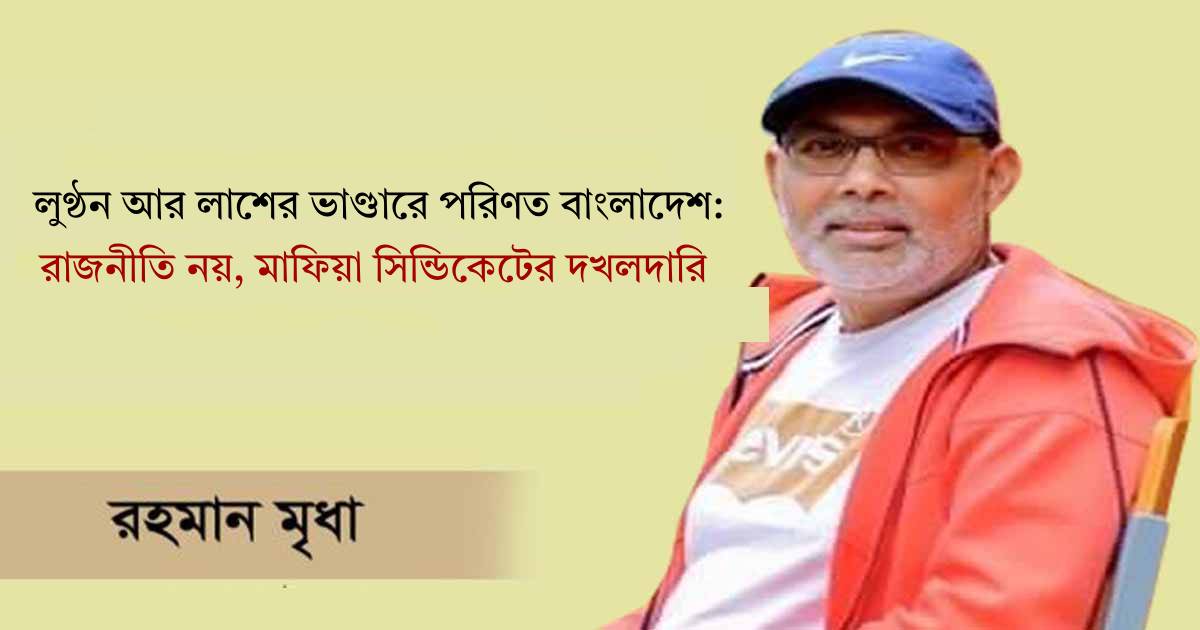
দেশটা আজ আর রাষ্ট্র নয়-এটা এখন ভাইয়ে ভাইয়ে ভাগ করা এক কর্পোরেট পাঁয়তারা, যেখানে নামমাত্র ভিন্ন দুই দল আসলে এক লুণ্ঠনবাজ চক্রের দুই শাখা মাত্র।
বিএনপি এখন মুখে গণতন্ত্রের বুলি আওড়ায়, আর হাতে নেয় আওয়ামী দস্যুদের ফেলে যাওয়া সম্পদের দখল। পালিয়ে যাওয়া আওয়ামী নেতারা কাঁধে চোরাই সম্পত্তির ব্যাগ আর পেছনে সেনা প্রটোকল নিয়ে দেশ ছাড়ছে, আর বিএনপি সেই দখলদারির লেজ লুটিয়ে দেশটাকে নিজের করে নিচ্ছে—এই নোংরা নাটক আর কতকাল চলবে?
সেনাবাহিনীর এক নির্লজ্জ অংশ এখন এই লুণ্ঠনের সহযাত্রী। তারা অস্ত্র দিয়ে নয়, নীরব সহযোগিতায় দিচ্ছে ‘সেফ একজিট’, যেন জাতিকে বিক্রি করে দেওয়া একটি লুকানো প্যাকেজ ডিল। যেই আওয়ামী লীগ এক দশক ধরে জনগণকে গিলে খেয়েছে, সেই দলের দালালরা আজ বিদেশে ঘর তোলে—আর বিএনপি দেশীয় লুটপাটে নেমে পড়ে। এ যেন ‘চোর বদল, চুরি নয়’!
এদিকে, ড. ইউনূস হয়ে উঠেছেন সেই অদ্ভুত প্রতীক, যিনি পর্দার আড়ালে থেকে আন্তর্জাতিক মহলকে সান্ত্বনা দেন—“বাংলাদেশে সংস্কার চলছে!”
সংস্কার? নাকি ব্যর্থতার মেকআপ? তিনি কি বুঝেন না, এই সংস্কারের নামেই হচ্ছে আরেক দফা জনগণকে ধোঁকা দেওয়ার আয়োজন?
এই মুহূর্তে দেশটা কোথায় দাঁড়িয়ে?
• প্রশাসন বিক্রি হয়ে গেছে দলীয় কর্মীদের কাছে।
• বিচারব্যবস্থা নিরপেক্ষ নয়, ভয়পেয়ে চুপ।
• নিরাপত্তা বাহিনী দুইদলের পালাক্রমে ব্যবহৃত হচ্ছে সন্ত্রাসীদের পেটোয়া বাহিনী হিসেবে।
• সাংবাদিকতা হয় দালালি, না হয় নিপীড়নের শিকার।
• বিশ্ববিদ্যালয়গুলো জ্ঞানের চর্চা নয়—দলের দালাল তৈরির কারখানা।
• আর রেমিট্যান্স যোদ্ধারা? তারা এখনো ডলার পাঠাচ্ছে সেই দেশকে, যাকে শাসন করছে চোর আর মাফিয়ারা।
এইবার আমাদের সহ্য করার সীমা পেরিয়ে গেছে।
করোনার মতো বিশ্বব্যাপী মহামারির সময় যেভাবে সবাই এক হয়েছিল, এখন সময় এসেছে সেই ঐক্যের থেকেও বড় এক যুদ্ধে নামার—এইবার লক্ষ্য দুর্নীতির মূলোৎপাটন।
দুর্নীতি আর দলবাজি এখন ভাইরাসের চেয়েও ভয়ংকর।
এটা শুধুমাত্র অর্থ চুরি করে না—এটা ভবিষ্যৎ খায়, স্বপ্ন নষ্ট করে, আত্মসম্মান ছিঁড়ে ফেলে।
একটি প্রস্তাবিত সংগ্রামী চেতনা: “রাষ্ট্র পুনর্গঠনের যুদ্ধ”
১. এই আন্দোলনের কোনো দল থাকবে না—থাকবে কেবল জনগণ বনাম চোর।
২. নেতৃত্ব আসবে প্রবাসীদের কাছ থেকে—যারা দলবাজির ঊর্ধ্বে, এবং এই দেশটাকে ভালোবেসেই বাঁচিয়ে রেখেছে।
3. সাংবাদিক, লেখক, শিল্পী, কৃষক, শ্রমিক—সবাইকে একাট্টা হতে হবে এক কণ্ঠে: “চোরের দেশ চাই না, আমাদের দেশ ফেরত চাই!”
4. আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে জানাতে হবে—এবার আর নির্বাচন নয়, নির্মূল চাই!
এইবার, কোনো নরম কথা নয়। এইবার, ঘৃণার ঘৃণিত রাজনীতিকে শেষ করে দিতে হবে।
এই যুদ্ধ গণতন্ত্র ফিরিয়ে আনার নয়—এটা গণতন্ত্রকে নতুন করে গড়ার যুদ্ধ।
যারা এই রাষ্ট্রকে পঁচিয়ে তুলেছে, তাদের আর শুধরে দেওয়ার সুযোগ নেই।
তাদের বিচার করতে হবে—জনগণের কাঠগড়ায়, ইতিহাসের আদালতে।
এইবার—জাগতে হবে, দাঁড়াতে হবে, প্রতিরোধ গড়তে হবে।
না হলে আগামী প্রজন্ম আমাদের ক্ষমা করবে না।
আমাদের বিপ্লবের নীলনকশা (Manifesto of National Moral Uprising)।
• অপ্রিয় সত্য থাকে
• করণীয় এবং বর্জনীয় স্পষ্টভাবে চিহ্নিত হয়
• একটি ধারাবাহিক জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক কর্মপন্থা উপস্থাপিত হয়
• প্রবাসীদের, তরুণদের, এবং সচেতন নাগরিকদের জাগ্রত করে তোলা যায়
জাতীয় নৈতিক জাগরণের রোডম্যাপ
(Remittance Fighters’ Manifesto for Moral Revolution)
প্রথম অধ্যায়: বাস্তবতা ও বোধোদয়
• দেশ এখন লুণ্ঠনের রাষ্ট্রে পরিণত: রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ নয়—দুই পক্ষই এখন মাফিয়া সিন্ডিকেট
• সেনাবাহিনীর এক অংশ, প্রশাসন, আদালত, পুলিশ—সবই দখল ও দুর্নীতির অংশীদার
• রেমিট্যান্স যোদ্ধারা দেশের অর্থনীতি বাঁচালেও, তাদের কোনো স্বীকৃতি নেই
• আন্তর্জাতিক দৃষ্টিতে বাংলাদেশের গণতন্ত্র এখন প্রশ্নবিদ্ধ ও ভণ্ডামীতে পূর্ণ
দ্বিতীয় অধ্যায়: লক্ষ্যে অবিচলতা
আমাদের চূড়ান্ত দাবি:
১. দুর্নীতিমুক্ত গণতান্ত্রিক প্রশাসন পুনর্গঠন
২. রাজনৈতিক দলগুলোর অর্থনৈতিক ও প্রশাসনিক দখলদারিত্বের অবসান
৩. প্রবাসীদের ভোটাধিকার ও নেতৃত্বে বাস্তব ক্ষমতায়ন
৪. একটি সত্যিকারের জনগণের সংবিধান পুনর্গঠন প্রক্রিয়া
৫. আন্তর্জাতিক স্বচ্ছ তদন্ত—দুই দল, সেনাবাহিনী, এবং সরকারি কর্মচারীদের বিরুদ্ধে
তৃতীয় অধ্যায়: করণীয় ও সংগ্রামের রূপরেখা
১. দেশে ও বিদেশে সমান্তরাল সচেতনতামূলক আন্দোলন:
• সোশ্যাল মিডিয়ায় সংঘবদ্ধ ক্যাম্পেইন (truth bombs, exposé series)
• প্রবাসী সম্মেলন ও রেমিট্যান্স প্ল্যাটফর্ম গঠন
• স্বাধীন সাংবাদিক ও লেখকদের মাধ্যমে তথ্য প্রকাশ
২. জাতীয়ভাবে নিরপেক্ষ সংগঠন গঠন:
• “জাতীয় নৈতিক আন্দোলন পরিষদ”—দলনিরপেক্ষ, প্রবাসীবান্ধব সংগঠন
• স্থানীয় পর্যায়ে দুর্নীতিবিরোধী গণজাগরণ কমিটি
৩. আন্তর্জাতিক লবিং ও চিঠি প্রেরণ:
• UN, EU, Human Rights Watch, Transparency International-এর কাছে গণচিঠি
• বিভিন্ন দেশের সংসদ সদস্যদের কাছে প্রবাসীদের সরাসরি চিঠি
• মিডিয়াতে লেটার-টু-এডিটর প্রচার
চতুর্থ অধ্যায়: বর্জনীয় বিষয়সমূহ
• ভোট ছাড়া নির্বাচনকে স্বীকৃতি দেওয়া
• রাজনৈতিক দলের মুখপাত্র বা দালালদের বিশ্বাস করা
• নিরবতা—কারণ, নিরবতা মানে অপরাধে অংশগ্রহণ
পঞ্চম অধ্যায়: আত্মপ্রতিরোধ ও আত্মমর্যাদার বিপ্লব
• কোনো রাজনৈতিক চক্রের অধীনে নয়—নিজেদের নেতৃত্বে নিজেদের দেশ গড়ার সময় এখন
• এই আন্দোলন হবে যুদ্ধ নয়, বিবেকের সংঘাত
• এই যুদ্ধ হবে অস্ত্র নয়, তথ্য, নৈতিকতা, জনসমর্থনের বিপ্লব
শেষ ঘোষণা:
“এইবার থামাতে হবে। এইবার নামতে হবে।
এইবার, বিপ্লব না হলে দেশ থাকবে না।”
রেমিট্যান্স যোদ্ধার রায়:
দুর্নীতিমুক্ত গণতন্ত্র আগে, তারপরই নির্বাচন।”
রহমান মৃধা, গবেষক ও লেখক
(সাবেক পরিচালক, ফাইজার, সুইডেন)
Rahman.Mridha@gmail.com
অর্থসংবাদে প্রকাশিত কোনো সংবাদ বা কনটেন্ট কপিরাইট আইনে পূর্বানুমতি ছাড়া ব্যবহার করা যাবে না।
মত দ্বিমত
বাংলাদেশ আর আমি- এ যেন এক অভিন্ন সত্তা
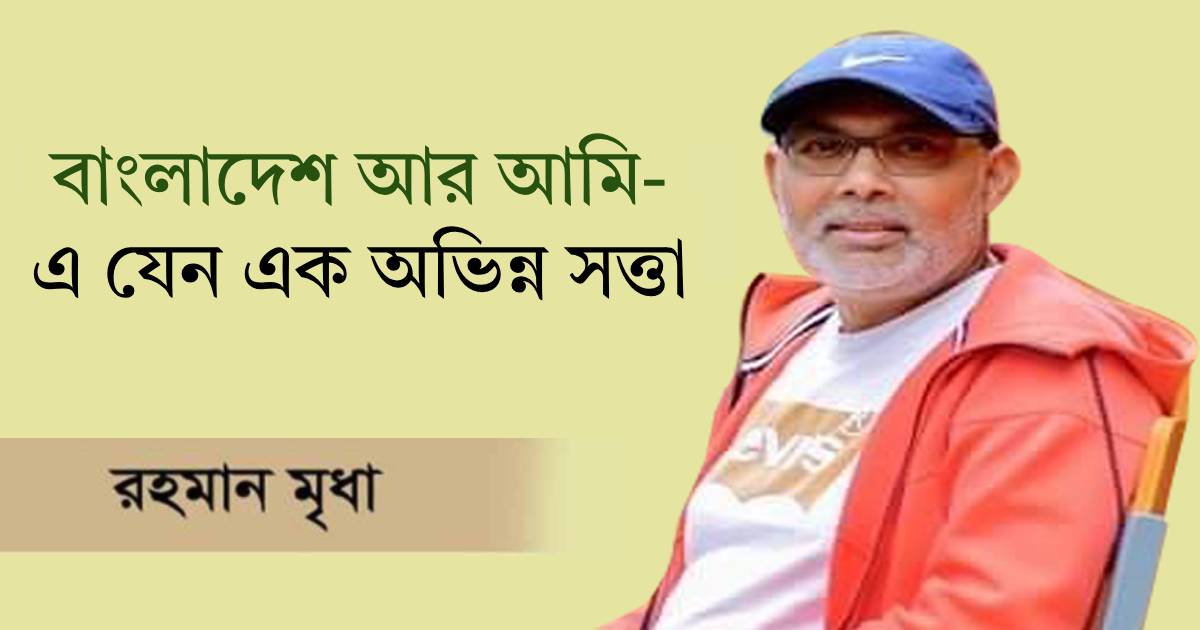
বাংলাদেশ আর আমি– এ যেন এক অভিন্ন সত্তা। চাইলে দেশটিকে ছেড়ে থাকতে পারি না, আবার তার মিথ্যা, শোষণ আর দুর্নীতির রাজনীতির কারণে কাছে যেতেও পারি না। ভালোবাসার বাঁধনে আবদ্ধ বলে পেছন ফিরে তাকাই, কিন্তু দেশের রক্তচোষা রাজনীতিবিদদের কুকর্ম আর মিথ্যাচার আমাকে আটকে রাখে।
আমি বিশ্বাস করি—আল্লাহ্র আলোকিত পথে হাঁটাই মুক্তির একমাত্র উপায়। সেই পথেই চলি, যেখানে সত্য আছে, যেখানে প্রিয় মানুষদের আদর্শিক ছায়া পড়ে। কিন্তু, দুঃখের বিষয়, যাদের হাতে দেশ ছিল—তারাই দেশকে পদদলিত করেছে, পথভ্রষ্ট করেছে, মানুষের স্বপ্ন ভেঙে চুরমার করেছে।
তাই আজ দূর থেকে দেশের জন্য কাজ করি। দেশের মানুষকে ভালোবেসে, তাদের চোখের জল দেখে আজ আমি কলম তুলে নিই, বুকের ভেতর জমা ক্ষোভ ছড়িয়ে দিই প্রতিটি শব্দে। কারণ দেশের জন্য কিছু করতে হলে, মুখে বুলি না ঝাড়লেও চলে, কাজে প্রমাণ দিতে হয়।
কিন্তু, হায়! যখনই দেখি কেউ সাহস করে দেশের হাল ধরতে চায়, নতুন করে গড়তে চায় স্বপ্নের বাংলাদেশ—ঠিক তখনই সেই পুরনো গলাবাজ, সেই চেনা মুখগুলো গলা ফাটিয়ে চিৎকার শুরু করে: ‘নির্বাচন চাই! ভোট চাই!’
তাদের প্রশ্ন করি—কোথায় ছিল এই ভোটের অধিকার, যখন তোমরা ক্ষমতায় ছিলে?
১. শেখ মুজিবুর রহমান নির্বাচনের বাইরে ক্ষমতায় ছিলেন প্রায় ১.৫ বছর।
২. জিয়াউর রহমান ছিলেন ৪.৫ বছর, সেনাশাসনের মুখোশে।
৩. হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ ছিলেন পুরো ১০ বছর—সরাসরি সামরিক শাসক!
৪. ২০০৬ সালে খালেদা জিয়া ক্ষমতা ছাড়ার সময়ও নির্বাচনের নামে নাটক চলেছে।
৫. আর শেখ হাসিনা—২০০৯ থেকে ২০২৪ পর্যন্ত, একের পর এক পাতানো নির্বাচন, রাষ্ট্রীয় দমন-পীড়ন আর ভুয়া উন্নয়নের গল্পে জনগণকে ধোঁকা দিয়েছেন।
তাহলে প্রশ্ন জাগে—এই সময়গুলোতে কোথায় ছিল জনগণের প্রকৃত অধিকার? আপনারা ক্ষমতায় গিয়েছেন, বারবার গিয়েছেন—কিন্তু কী দিয়েছেন জাতিকে? শিক্ষিত বেকারত্ব, পাটকলের গেট বন্ধ, চিকিৎসাহীন মৃত্যু, দুর্নীতির পাহাড়, আর দেশ ছেড়ে চলে যাওয়ার হাহাকার! নিজেরা ফকির থেকে কোটি টাকার মালিক হয়েছেন, আর দেশের মানুষ আজও ভাতের জন্য দাঁড়ায় রাস্তায় লাইনে!
এখন যখন বাংলাদেশ তার সত্যিকারের অভিভাবককে পেয়েছে, তখনই শুরু হয়েছে কণ্ঠরোধের ষড়যন্ত্র—‘নির্বাচন চাই, নির্বাচন চাই!’ এই আওয়াজ এখন যেন শুধুই বিরক্তিকর প্যাঁচপ্যাঁচানি।
ভাইরে, বিপ্লব কখনও ব্যালট চায় না। ইতিহাসের প্রতিটি মৌলিক পরিবর্তন এসেছে বিপ্লবী শক্তির হাত ধরে, জনগণের ভরসা আর নেতৃত্বের আস্থায়। বিপ্লব মানেই স্বতঃসিদ্ধ বৈধতা। আমেরিকার স্বাধীনতা আন্দোলন, ফরাসি বিপ্লব, রাশিয়ার অক্টোবর বিপ্লব—সবই ছিল রাজনীতির প্রচলিত নিয়ম ভেঙে নতুন পথ রচনা করার গল্প।
আজ বাংলাদেশের মানুষ আর ভোটের জন্য গলা ফাটায় না—তারা চায় একজন আদর্শবান, ন্যায়পরায়ণ শাসক। একজন মানুষ, যে লুটপাট করবে না, ক্ষমতাকে দান হিসেবে নয়—দায়িত্ব হিসেবে নেবে। যে কৃষকের ঘাম বুঝবে, ছাত্রের চোখে স্বপ্ন দেখবে, বৃদ্ধের মুখে শান্তির হাসি আনবে।
আর যারা দিনভর রাস্তায় নেমে নির্বাচন, নির্বাচন বলে গলা ফাটায়—তাদের বলি, যে নিজের সংসার চালাতে পারে না, সে দেশ চালাবে কীভাবে? রাজনীতি আজ ব্যবসা নয়, চাকরি নয়—এটা সেবা। আর যদি সেবা না পারেন, সোজা কাজ করুন, ঘাম ঝরান, পরিবারকে খাওয়ান, দেশের জন্য সৎভাবে আয় করুন।
আমি বিদেশে থেকেও দেশের জন্য কাজ করি। আপনি দেশে থেকে পারবেন না কেন? দেশপ্রেম মানে ব্যানার নয়, ব্যালট নয়—দেশপ্রেম মানে নিজের যোগ্যতাকে দেশের কল্যাণে উৎসর্গ করা।
আজ আমাদের প্রয়োজন সৎ নেতৃত্ব, আদর্শিক কাঠামো আর জাতীয় ঐক্য। ভোট নয়, দল নয়, ক্ষমতা নয়—আমরা চাই বাংলাদেশ গড়ে উঠুক নতুন ন্যায়ের ভিতের ওপর।
তাই বলছি— নোভোটিং এট দিস মোমেন্ট! বিপ্লবী সরকারের জন্য ভোট লাগে না! কারণ, সত্যিকারের বিপ্লব কখনও ব্যালটে আসে না—সে আসে মানুষের মঙ্গল আর ইতিহাসের অনিবার্যতার হাত ধরে!
লেখক: রহমান মৃধা, সাবেক পরিচালক, ফাইজার, সুইডেন
অর্থসংবাদে প্রকাশিত কোনো সংবাদ বা কনটেন্ট কপিরাইট আইনে পূর্বানুমতি ছাড়া ব্যবহার করা যাবে না।
মত দ্বিমত
দুর্নীতির দুষ্টচক্রে আজ সমাজ বিভক্ত
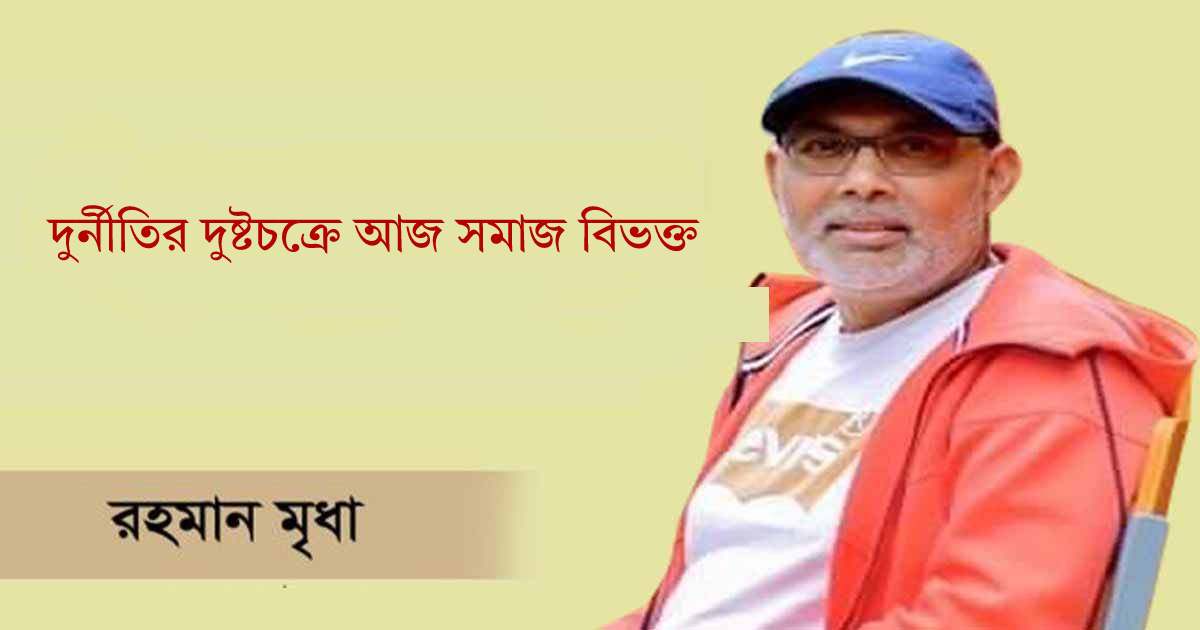
রতনে রতন চেনে-এই প্রবাদটি আমাদের বর্তমান রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার নির্মম প্রতিফলন। ক্ষমতার অধিকারীরা নিজেদের স্বার্থে সিদ্ধান্ত বদলাতে পারে, কিন্তু যেখানে রাষ্ট্রীয় দুর্নীতি, পরিবারতন্ত্র এবং দলীয় সন্ত্রাস শাসনব্যবস্থার ভিত্তি হয়ে ওঠে, সেখানে পরিবর্তনের কোনো সুযোগ থাকে না। বাংলাদেশের বর্তমান শাসকগোষ্ঠী এমন এক দানবীয় ক্ষমতার বলয়ে আবদ্ধ, যেখানে জনগণের অধিকার, স্বাধীনতা ও নিরাপত্তা দলীয় স্বার্থের কাছে তুচ্ছ হয়ে গেছে। শাসকের আশীর্বাদপুষ্ট সন্ত্রাসী বাহিনী, দুর্নীতিবাজ রাজনৈতিক কর্মী ও প্রশাসনের দুর্নীতিগ্রস্ত অংশ সমাজের প্রতিটি স্তরে অন্যায়কে প্রতিষ্ঠিত করেছে।
ক্ষমতার লোভে অন্ধ এই স্বৈরতান্ত্রিক গোষ্ঠী দলীয় পরিচয়ে অপরাধীদের রক্ষা করছে, তাদের হাতে তুলে দিচ্ছে রাষ্ট্রীয় সম্পদ আর জনগণের রক্ত-ঘাম ঝরানো উপার্জন। ২০২৪ সালের রাজনৈতিক বিপ্লবের পর দেশের অপরাধীরা আরও নির্লজ্জভাবে প্রকাশ্যে আসছে—যারা একসময় ছায়ার আড়ালে ছিল, তারা এখন দলের আনুগত্যের পুরস্কার হিসেবে চাঁদাবাজি, দখলবাজি আর ভয়ংকর সন্ত্রাসের লাইসেন্স পাচ্ছে। একদিকে ক্ষমতাধরদের ভোগবিলাস বাড়ছে, অন্যদিকে সাধারণ মানুষ নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের দাম নিয়ে হাহাকার করছে। রাষ্ট্রের প্রতিটি প্রতিষ্ঠান আজ দলীয় স্বার্থ রক্ষার যন্ত্রে পরিণত হয়েছে, যেখানে ন্যায়বিচার, গণতন্ত্র ও জনগণের অধিকার একরকম বিলুপ্ত।
বিশ্বের দিকে তাকালে দেখি, ডোনাল্ড ট্রাম্প, এলন মাস্কের মতো ব্যক্তিত্বরা সম্পদের পাহাড় গড়ার পাশাপাশি নতুন নতুন চিন্তাধারা দিয়ে নেতৃত্ব দিচ্ছেন। তারা নিজের অবস্থান আরও শক্তিশালী করতে উদ্ভাবন, প্রযুক্তি ও ব্যবসায় মনোযোগ দিচ্ছেন, বিশ্বকে নতুন দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে এগিয়ে নিচ্ছেন। অথচ আমাদের দেশে রাজনীতি মানেই ক্ষমতা আঁকড়ে ধরে রাখা, দলীয় দুর্নীতিকে প্রশ্রয় দেওয়া এবং জনগণের সম্পদ লুটপাট করা। যখন আধুনিক বিশ্ব নতুন বিপ্লবের পথে হাঁটছে, তখন আমরা এক গোষ্ঠীর শোষণের যাঁতাকলে নিষ্পেষিত হচ্ছি।
পরিবর্তনের পথে সবচেয়ে বড় বাধা হচ্ছে পুরনো চিন্তাভাবনা, দলীয় লেজুড়বৃত্তি ও স্বৈরতান্ত্রিক মানসিকতা। পুরো বিশ্ব যখন ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে, তখন আমরা দলীয় স্বার্থের বলি হয়ে ধ্বংসের দিকে এগোচ্ছি। শাসকগোষ্ঠীর মূল লক্ষ্য জনগণের কল্যাণ নয়, বরং ক্ষমতাকে চিরস্থায়ী করা।
বাংলাদেশের বর্তমান বাস্তবতা আরও ভয়ংকর। এখানে সুস্পষ্ট পরিকল্পনা বা দূরদর্শী নেতৃত্ব নেই, আছে শুধু ক্ষমতার লড়াই। শাসকেরা জনগণকে মিথ্যা আশ্বাসের ফাঁদে ফেলে, ঠিক যেমন হামিলনের বাঁশিওয়ালা গ্রামবাসীদের ভুল পথে চালিত করেছিল। জনগণের সামনে কোনো বাস্তবসম্মত লক্ষ্য নেই, শুধু চোখ ধাঁধানো প্রতিশ্রুতি আর শাসকদের চাটুকারিতায় গড়া এক বিভ্রান্তিকর ভবিষ্যৎ। ক্ষমতার এই দানবীয় প্রতিযোগিতায় রাষ্ট্রের সম্পদ লুটপাট হচ্ছে, দুর্নীতি আরও গভীরে প্রোথিত হচ্ছে, আর সাধারণ মানুষ নিঃস্ব হয়ে পড়ছে।
এই বাস্তবতা কি আমাদের ভবিষ্যতকে অন্ধকারে ঠেলে দেবে? নাকি আমরা সাহসী হয়ে সত্যিকারের পরিবর্তনের পথে হাঁটব?
বারবার রক্ত দিয়ে স্বৈরশাসকের পতন ঘটানোর চেয়ে, আমাদের পুরো শাসনব্যবস্থার কাঠামোই বদলাতে হবে, যেন কোনো স্বৈরাচারী বা পরিবারতান্ত্রিক সরকার আর জন্ম নিতে না পারে। আমাদের দায়িত্ব শুধু ভোট দেওয়া নয়, বরং রাষ্ট্রের প্রতিটি স্তরে সচেতনভাবে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা। সমাজের প্রতিটি মানুষকে তাদের অধিকার, স্বাধীনতা ও ন্যায়বিচারের জন্য রুখে দাঁড়াতে হবে। দুর্নীতিবাজ শাসক ও তাদের সন্ত্রাসীদের রুখতে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন ছাড়া আর কোনো বিকল্প নেই।
যদি আমরা আজও চুপ করে থাকি, তবে আগামী প্রজন্মের জন্য আমরা এক নিঃস্ব, পরাধীন ও ধ্বংসপ্রাপ্ত রাষ্ট্র রেখে যাব। তাই সময় এখনই—দুর্নীতির বিরুদ্ধে জেগে ওঠার, অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর এবং একটি সত্যিকারের গণতান্ত্রিক, ন্যায়ভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠার!
একটি সৃজনশীল, উন্নত এবং সমৃদ্ধ সমাজ গঠনের মূল ভিত্তি হলো— শিক্ষার উন্নতি, গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের চর্চা, অর্থনৈতিক সমতা প্রতিষ্ঠা এবং সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতা। এই উপাদানগুলোই একটি দেশকে উন্নয়নের পথে এগিয়ে নিয়ে যায়। কিন্তু দুঃখজনকভাবে, আমাদের বাস্তবতা একেবারেই ভিন্ন। এখানে শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য হারিয়ে গেছে; শিক্ষাব্যবস্থা হয়ে উঠেছে ক্ষমতাসীনদের হাতের পুতুল, যেখানে জ্ঞানার্জনের চেয়ে বেশি গুরুত্ব পাচ্ছে দুর্নীতি, দলীয়করণ ও ব্যক্তিস্বার্থ।
একটি সমাজ তখনই টিকে থাকে যখন তার জনগণ শুধুমাত্র বেঁচে থাকার তাগিদে দৌড়ায় না, বরং নিজেদের অধিকারের জন্য সংগ্রাম করে এবং ভবিষ্যতের জন্য একটি সুষ্ঠু রাষ্ট্র গড়ে তুলতে সচেষ্ট হয়। কিন্তু আমাদের সমাজের প্রতিটি স্তরে এখন এমন একটি বাস্তবতা তৈরি হয়েছে, যেখানে মানুষের চেতনা ভোঁতা হয়ে গেছে। তারা রাষ্ট্রীয় অবিচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করা দূরে থাক, বরং নিজেদের অধিকার নিয়েই বিভ্রান্ত।
বিশ্বের এক প্রান্তে যখন ধর্মীয় মূল্যবোধ, যেমন রমজান মাস, মানুষকে আত্মশুদ্ধি ও নৈতিকতার শিক্ষা দেয়, তখন সেই একই সমাজের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষা বোর্ড দুর্নীতির আখড়ায় পরিণত হলে তা নিছক ব্যক্তিগত ব্যর্থতা নয়— বরং রাষ্ট্রীয় কাঠামোর ভয়ানক দুর্বলতার প্রমাণ। এটি প্রমাণ করে যে, দুর্নীতি এখন শুধুমাত্র ব্যক্তির চরিত্র নষ্ট করছে না, বরং পুরো রাষ্ট্রযন্ত্রকে এক সাংবিধানিক অস্থিতিশীলতার দিকে ঠেলে দিয়েছে।
এই পরিস্থিতিতে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হলো— এভাবে আর কতদিন চলতে থাকবে? যদি সত্যিই আমাদের সমাজকে সুষ্ঠু, ন্যায্য এবং উন্নত ভবিষ্যতের দিকে পরিচালিত করতে হয়, তাহলে এই দুর্নীতিগ্রস্ত কাঠামো ভেঙে ফেলা ছাড়া কোনো বিকল্প নেই।
একটি বিপরীত চিত্র স্পষ্ট হয়ে উঠছে: বাংলাদেশে দুর্নীতি, সন্ত্রাসী কার্যক্রম ও পারিবারিক শাসন ব্যবস্থা রাষ্ট্র পরিচালনার মূল হাতিয়ারে পরিণত হয়েছে। জনগণ এমন এক শাসকশ্রেণীর হাতে বন্দি, যারা কোনো পরিবর্তন চায় না— তাদের একমাত্র লক্ষ্য হলো নিজেদের ক্ষমতা ও পারিবারিক স্বার্থ টিকিয়ে রাখা।
এটি অনেকটা হামিলনের গ্রামবাসীদের মতো, যারা প্রথমে বুঝতেই পারেনি যে তারা ভুল পথে চলছে। বাংলাদেশের জনগণও যদি নিজেদের অধিকার, স্বাধীনতা এবং ন্যায়ের ব্যাপারে সচেতন না হয়, তবে তারা চিরকাল শাসকের পথ অনুসরণ করতেই থাকবে, নিজেদের ভবিষ্যতকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দেবে।
আজকের বাংলাদেশ ভয়াবহ এক রাজনৈতিক বাস্তবতার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছে। রাষ্ট্রীয় দুর্নীতি, পরিবারতন্ত্র এবং সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড এখন দেশের প্রতিটি স্তরে গভীরভাবে প্রবেশ করেছে। এটি এমন একটি কাঠামো, যেখানে জনগণ নিজেদের অধিকার ভুলে গিয়ে শাসকদের প্রতি অন্ধ আনুগত্য প্রদর্শন করছে। কিন্তু এই আনুগত্য কোনো উন্নয়ন বা কল্যাণ বয়ে আনবে না— বরং এটি হামিলনের বাঁশিওয়ালার গল্পের মতো জনগণের জীবনকে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাবে।
এই সন্ত্রাসী শক্তি, দুর্নীতি এবং অযোগ্য নেতৃত্ব দেশের সম্ভাবনাকে ধ্বংস করছে। দেশের উন্নয়ন সম্ভব নয়, যতদিন না আমরা এই কাঠামোকে ভেঙে নতুন ব্যবস্থা গড়তে পারি। জনগণের উচিত অন্ধ আনুগত্যের পথ ছেড়ে সচেতন ও শিক্ষিত হয়ে নতুন দিগন্তের দিকে এগিয়ে যাওয়া। অন্যথায়, দেশের ভবিষ্যৎ অন্ধকারের অতলে তলিয়ে যাবে।
একটি কার্যকর, ন্যায়সংগত ও আধুনিক রাষ্ট্রব্যবস্থা গড়ে তোলার একমাত্র উপায় হলো পুরোনো, দুর্নীতিগ্রস্ত কাঠামোর পরিবর্তে নতুন কাঠামো তৈরি করা।
এই কাঠামোর ভিত্তি হবে—
শিক্ষায় স্বচ্ছতা ও দক্ষতা। প্রশাসনে জবাবদিহিতা। বিচারব্যবস্থায় নিরপেক্ষতা। অর্থনীতিতে সমতা ও ন্যায়বিচার।
কিন্তু বর্তমান বাস্তবতায়, রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ প্রতিটি খাতই দলীয়করণ ও দুর্নীতির শিকার, যার ফলে কাঠামোগত সংস্কার ছাড়া কোনো উন্নয়ন সম্ভব নয়।
বিশেষ করে শিক্ষাব্যবস্থা আজ দলীয়করণ, দুর্নীতি ও প্রশাসনিক অব্যবস্থাপনার জালে বন্দি। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রাথমিক শিক্ষাপর্যন্ত সর্বত্র দুর্নীতি ও ক্ষমতার অপব্যবহার দৃষ্টিগোচর হয়—
প্রশাসনিক পদে দলীয় নিয়োগ: বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ও প্রশাসনিক পদগুলোতে রাজনৈতিক আনুগত্যকে প্রাধান্য দিয়ে নিয়োগ দেওয়া হয়, ফলে যোগ্যদের জায়গা সংকুচিত হয়ে যায়।
🔴 ভর্তি ও নিয়োগ বাণিজ্য: অর্থের বিনিময়ে ছাত্র ভর্তি ও শিক্ষক নিয়োগ করা হয়, ফলে প্রকৃত মেধাবীরা বঞ্চিত হয় এবং শিক্ষার মান ধ্বংস হয়ে যায়।
🔴 ক্যাম্পাসে দলীয় সন্ত্রাস: ক্ষমতাসীন দলের ছাত্র সংগঠন ক্যাম্পাসে ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করেছে— হলে সিট বাণিজ্য, সাধারণ শিক্ষার্থীদের উপর হামলা, এবং ভিন্নমত দমন এখন স্বাভাবিক বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে।
🔴 পরীক্ষায় অনিয়ম ও সেশনজট: প্রশ্নফাঁস, প্রভাবশালীদের হস্তক্ষেপ এবং প্রশাসনিক দুর্নীতির কারণে প্রকৃত মূল্যায়ন অসম্ভব হয়ে উঠেছে।
🔴 শিক্ষাকে ব্যবসায় পরিণত করা: উচ্চশিক্ষার ব্যয়বৃদ্ধি, সরকারি প্রতিষ্ঠানে ঘুষ সংস্কৃতি এবং কোচিং বাণিজ্যের কারণে সাধারণ মানুষের জন্য শিক্ষার সুযোগ সীমিত হয়ে পড়েছে।
যে শিক্ষাব্যবস্থায় রন্ধ্রে রন্ধ্রে দুর্নীতি ঢুকে গেছে, সেখান থেকে পাস করা শিক্ষার্থীরা ভবিষ্যতে রাষ্ট্রের দায়িত্বে গেলে কীভাবে দুর্নীতিমুক্ত থাকবে?
আজকের শিক্ষার্থী যখন ঘুষ দিয়ে চাকরি নেয়, তখন সে ভবিষ্যতে সৎ থাকার কথা ভাববেই বা কেন? ফলে, এই চক্র বন্ধ না হলে দুর্নীতি কেবল আরও শক্তিশালী হয়ে টিকে থাকবে।
এই ভয়ংকর বাস্তবতা থেকে মুক্তি পেতে হলে আমাদের রুখে দাঁড়াতে হবে।
শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে দলীয় হস্তক্ষেপ বন্ধ করতে হবে। দুর্নীতিবাজ প্রশাসকদের অপসারণ করতে হবে। স্বাধীন ও নিরপেক্ষ বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন নিশ্চিত করতে হবে। শিক্ষার মানোন্নয়ন নিশ্চিত করতে হবে, যাতে যোগ্যতা ও মেধা ফিরে আসে।
এখন সময় এসেছে দেশের জনগণের জেগে ওঠার। যদি আমরা পরিবর্তন না আনি, তাহলে শাসকগোষ্ঠীর লুটপাট অব্যাহত থাকবে এবং আমাদের ভবিষ্যৎ চিরতরে ধ্বংস হয়ে যাবে।
সত্যিকার পরিবর্তনের জন্য— সংগ্রাম শুরু হোক আজই!
বাংলাদেশের বর্তমান রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক অবস্থা চরম দুর্নীতি, সন্ত্রাস ও পরিবারতন্ত্রের বেড়াজালে বন্দি। এই অবস্থা থেকে বেরিয়ে আসতে হলে একটি নতুন কাঠামো গড়ে তুলতে হবে, যেখানে সুশাসন, ন্যায়বিচার এবং প্রগতিশীল সমাজের ভিত্তি স্থাপন করা হবে। এটি শুধু রাজনৈতিক পরিবর্তনের প্রশ্ন নয়, বরং গোটা রাষ্ট্রব্যবস্থার আমূল সংস্কার ছাড়া উন্নয়ন সম্ভব নয়।
একটি কার্যকর রাষ্ট্রের প্রথম শর্ত হলো দক্ষ, স্বচ্ছ ও রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত প্রশাসন। বর্তমান প্রশাসন দলীয় আনুগত্যের ভিত্তিতে পরিচালিত হয়, যেখানে মেধা ও দক্ষতার কোনো মূল্য নেই। এটি পরিবর্তন করতে হলে—
রাজনৈতিক হস্তক্ষেপহীন প্রশাসন: প্রশাসনের সকল নিয়োগ ও পদোন্নতি শুধুমাত্র মেধা ও যোগ্যতার ভিত্তিতে দিতে হবে, যাতে রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলো প্রকৃত দক্ষ লোক দ্বারা পরিচালিত হয়।
ডিজিটাল প্রশাসন: সরকারি কার্যক্রমে ব্লকচেইন ও এআই প্রযুক্তি সংযুক্ত করতে হবে, যাতে দুর্নীতির সুযোগ কমে এবং স্বচ্ছতা নিশ্চিত হয়।
নাগরিক সেবার সহজলভ্যতা: প্রশাসনিক হয়রানি বন্ধে অনলাইন পোর্টাল, একক হেল্পডেস্ক এবং ডিজিটাল সেবা সম্প্রসারণ করতে হবে, যাতে জনগণ দ্রুত ও কার্যকর সেবা পায়।
বর্তমান বিচারব্যবস্থা রাজনৈতিক প্রভাব ও দুর্নীতির শিকার। বিচারব্যবস্থার স্বাধীনতা ছাড়া ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়। এজন্য—
স্বাধীন বিচার বিভাগ: বিচারব্যবস্থাকে রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক হস্তক্ষেপমুক্ত করতে হবে এবং আদালতকে পূর্ণ স্বাধীনতা দিতে হবে।
দ্রুত ও ডিজিটাল বিচার: মামলা নিষ্পত্তির দীর্ঘসূত্রিতা দূর করতে অনলাইন কোর্ট ও ই-জুডিশিয়ারি ব্যবস্থা চালু করতে হবে, যাতে বিচার সহজ ও দ্রুত হয়।
আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সংস্কার: পুলিশ ও অন্যান্য বাহিনীগুলোকে রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত করে তাদেরকে জনগণের সেবায় আরও কার্যকর করতে হবে।
দুর্নীতি ও অর্থনৈতিক বৈষম্যের কারণে দেশের সম্পদ কিছু গোষ্ঠীর হাতে কেন্দ্রীভূত হচ্ছে। অর্থনীতিকে পুনর্গঠনের জন্য—
ব্যাংক ও শেয়ারবাজারের জবাবদিহিতা: ব্যাংক লুট ও শেয়ারবাজার কেলেঙ্কারির বিরুদ্ধে কঠোর আইন প্রণয়ন ও প্রয়োগ নিশ্চিত করতে হবে।
ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের জন্য সহায়তা: নতুন ব্যবসা ও স্টার্টআপগুলোকে স্বল্পসুদে ঋণ এবং কর সুবিধা দিতে হবে, যাতে অর্থনীতি উৎপাদনমুখী হয়।
অর্থপাচার রোধ: কালো টাকা বৈধ করার সুযোগ বন্ধ করতে হবে এবং বিদেশে অর্থপাচার কঠোরভাবে দমন করতে হবে।
বাংলাদেশে এখনো শ্রেণিভেদ, বৈষম্য ও ক্ষমতার অপব্যবহার প্রকট। একটি সমান সুযোগের সমাজ গড়তে হলে—
সমান অধিকার ও সুযোগ: শিক্ষা, চাকরি ও অন্যান্য ক্ষেত্রে শ্রেণিভিত্তিক বৈষম্য দূর করতে হবে।
দুর্নীতিগ্রস্তদের সামাজিক বর্জন: দুর্নীতিবাজ ব্যক্তিদের সমাজে গ্রহণযোগ্যতা কমাতে হবে এবং তাদেরকে সামাজিকভাবে প্রত্যাখ্যান করতে হবে।
জনসচেতনতা বৃদ্ধি: জনগণকে তাদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন করা এবং রাষ্ট্রের অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী করে তুলতে হবে।
বিশ্ব এখন চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের যুগে, কিন্তু বাংলাদেশ এখনো দুর্নীতিগ্রস্ত ও সেকেলে প্রশাসনিক কাঠামোর মধ্যে আটকে আছে। এর পরিবর্তন আনতে হলে—
ডিজিটাল প্রশাসন ও বিচার ব্যবস্থা: ব্লকচেইন ও এআই প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে সরকারি কার্যক্রম স্বচ্ছ ও দক্ষ করতে হবে।
ডিজিটাল অর্থনীতি: সকল লেনদেন স্বচ্ছ করতে হবে এবং ফিনটেক ও ক্যাশলেস অর্থনীতির সম্প্রসারণ করতে হবে, যাতে কালো টাকার লেনদেন কমে।
প্রযুক্তিনির্ভর সামাজিক ও স্বাস্থ্যসেবা: টেলিমেডিসিন, অনলাইন শিক্ষা এবং ডিজিটাল কল্যাণমূলক কার্যক্রম সহজলভ্য করতে হবে।
বাংলাদেশের বর্তমান পরিস্থিতি অনেকটা হামিলনের গ্রামবাসীদের মতো—যেখানে জনগণ অন্ধভাবে নেতৃত্বের পেছনে ছুটছে, কিন্তু তারা বুঝতে পারছে না যে এই পথ তাদের ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাচ্ছে।
এই পরিস্থিতি থেকে মুক্তির একমাত্র পথ হলো কাঠামো ভেঙে একটি নতুন সুশাসন, ন্যায়বিচার ও গণতন্ত্রভিত্তিক রাষ্ট্র গড়ে তোলা। এজন্য—
শিক্ষাব্যবস্থা সংস্কার করতে হবে, যাতে মেধা ও নৈতিকতা অগ্রাধিকার পায়। প্রশাসনকে দুর্নীতি ও দলীয়করণমুক্ত করতে হবে, যাতে যোগ্য ও দক্ষ নেতৃত্ব তৈরি হয়। অর্থনৈতিক নীতিগুলোকে দুর্নীতিমুক্ত করে জনগণের জন্য সমৃদ্ধির সুযোগ তৈরি করতে হবে।
এটি শুধু রাজনৈতিক পরিবর্তন নয়, বরং পুরো শিক্ষাব্যবস্থায়, সামাজিক মনোভাব এবং প্রশাসনিক কাঠামোয় আমূল পরিবর্তন আনতে হবে।
আমাদের অন্ধ আনুগত্য ও রাজনৈতিক সন্ত্রাসের বেড়াজাল থেকে মুক্তি পেতে হবে। কাঠামো ভেঙে নতুন ব্যবস্থা তৈরি করতে হবে। দুর্নীতি ও পরিবারতন্ত্রকে চিরতরে উৎখাত করতে হবে। সুশাসন, গণতন্ত্র ও সমাজের উন্নয়ন ছাড়া বাংলাদেশের মুক্তি সম্ভব নয়।
এখনই নতুন কাঠামো গড়ার সময়! সুশাসন, ন্যায়বিচার ও জনগণের ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করতে হলে আমাদের ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করতে হবে। বাংলাদেশকে প্রকৃত অর্থে একটি সুষ্ঠু, স্বচ্ছ ও স্বাধীন দেশ হিসেবে গড়ে তুলতে হলে এখনই এই পরিবর্তন আনতে হবে!
রহমান মৃধা, গবেষক ও লেখক
(সাবেক পরিচালক, ফাইজার, সুইডেন)
Rahman.Mridha@gmail.com
অর্থসংবাদে প্রকাশিত কোনো সংবাদ বা কনটেন্ট কপিরাইট আইনে পূর্বানুমতি ছাড়া ব্যবহার করা যাবে না।
মত দ্বিমত
পেশাগত দায় ও নৈতিকতা: লেখকের কৈফিয়ত ও সম্পাদকের দুঃখ প্রকাশ

ছোটবেলায় পাঠ্যপুস্তকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাটিকা ‘খ্যাতির বিড়ম্বনা’ পড়ে বেশ মজা পেয়েছিলাম। তখন মনের অজান্তে এক গভীর বোধও জন্ম নিয়েছিল যে খ্যাতি কখনো আশীর্বাদ, আবার কখনো অভিশাপও হতে পারে। সাম্প্রতিক ঘটনায় জীবনের এই পড়ন্তবেলায় সেই নাটিকাটির কথা আবার মনে পড়ে গেল। আমি অনুভব করছি যে, যারা নিয়মিত আমার লেখাগুলো পড়েন, ভাবেন, মূল্যায়ন করেন; তাঁদের কারো কারো নজরে আসা সাম্প্রতিক দু’টো ঘটনা আমাকে পীড়া দিচ্ছে। পাঠকদের কাছে একটি আন্তরিক কৈফিয়ত না জানিয়ে যেন আর কোনোভাবেই স্বস্তি পাচ্ছি না। তাই নিজেকে ভারমুক্ত করতে আজকের এই লেখার অবতারণা।
অনাকাঙ্খিত ঘটনা দু’টোর জন্য একটি আত্মজিজ্ঞাসার দায়ভার অনুভব করছি, যে দায় শুধুই পেশাগত নয়; নৈতিক এবং মানবিকও বটে। সংগত কারণে এই লেখাটিতে ঘটে যাওয়া অনাঙ্খিত ঘটনা দু’টোর ব্যাখ্যা, সেগুলোর জন্য কিছু অনুশোচনা, আর নিজের ব্যর্থতার জন্য দুঃখ প্রকাশ করছি।
দীর্ঘ এক দশকেরও বেশি সময় পত্রপত্রিকায় লেখালেখি করা থেকে দূরে থাকার পর, গণঅভ্যুত্থান-পরবর্তী এক নতুন গণতান্ত্রিক সম্ভাবনার আবহে আবারও কলম হাতে নিয়েছি। পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে মনে হয়েছিল সমাজ, রাষ্ট্র ও মানবিক মূল্যবোধের পক্ষে কিছু বলার, কিছু লেখার দায় এড়ানো উচিত নয়। সৌভাগ্যক্রমে কয়েকটি জাতীয় পত্রপত্রিকা আমার লেখা সাদরে গ্রহণ করেছে এবং আমাকে তাদের নিয়মিত লেখক হিসেবে পুনরায় জায়গা দিয়েছে। কিন্তু লেখালেখির জগতে এই প্রত্যাবর্তনের আনন্দের মাঝে সম্প্রতি দু’টি বিব্রতকর ঘটনা ঘটে গেছে। দুইটি জাতীয় দৈনিকে অসাবধনতাবশত আমার নামে অন্যের লেখা প্রকাশিত হয়েছে। যদিও উভয় ক্ষেত্রেই তা ছিল অনিচ্ছাকৃত ভুল এবং পত্রিকা কর্তৃপক্ষও বিষয়টি তাৎক্ষণিকভাবে স্বীকার করে দুঃখ প্রকাশ করেছেন ও পরবর্তী সংখ্যায় সংশোধনী প্রকাশ করেছে। তথাপি পেশাগত নৈতিকতার জায়গা থেকে ঘটনাগুলো আমাকে গভীর অস্বস্তিতে ফেলেছে।
পেশাগত জগতে বিশ্বাসযোগ্যতা কোনো তাৎক্ষণিক বা বাহ্যিক কৃতিত্ব নয়; এটি গড়ে ওঠে দীর্ঘ সময় ধরে শ্রম, আত্মবিশ্বাস ও নৈতিক দায়বোধের সম্মিলিত প্রয়াসের মাধ্যমে। বিশ্বাসযোগ্যতা, দায়িত্বশীলতা ও সুনাম অর্জনের পথে যেমন অধ্যবসায় ও সততা অপরিহার্য, তেমনি এক মুহূর্তের অসতর্কতা, ভুল সিদ্ধান্ত বা যথার্থ যোগাযোগের ঘাটতিতেও সেই বিশ্বাস বিনষ্ট হতে পারে। প্রাচীন গ্রিক দার্শনিক প্লেটো তাঁর ‘রিপাবলিক’ গ্রন্থে ন্যায়বিচার, দায়িত্ববোধ ও জ্ঞানভিত্তিক নেতৃত্বকে আদর্শ রাষ্ট্রের মূলভিত্তি হিসেবে যে গুরুত্ব দিয়েছিলেন, ঠিক তেমনি পেশাগত পরিসরেও নৈতিকতা ও দায়িত্বশীলতা কোনো অতিরিক্ত আনুষঙ্গিক নয়, বরং এটি পেশাগত চেতনা, আস্থা ও আন্তরিকতা রক্ষার অবিচ্ছেদ্য উপাদান। ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান—উভয়ের জন্যই এটি একটি নীতিগত স্তম্ভ। অতএব ভবিষ্যতে যেন এ ধরনের অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতি পুনরায় না ঘটে এবং পেশাগত সতর্কতার পাশাপাশি সততা, স্বচ্ছতা ও দায়বদ্ধতা অক্ষুণ্ণ থাকে, সে লক্ষ্যে কিছু বিষয়কে এখানে খোলামেলা ও স্পষ্টভাবে তুলে ধরা এবং নির্মোহভাবে আলোচনার প্রয়োজন অনুভব করছি।
রাষ্ট্রীয় কিংবা পেশাগত পরিসরে আমি কোনো খ্যাতিমান ব্যক্তি নই। আমি একজন সাধারণ মানুষ, জীবন পাঠশালার একজন সক্রিয় জীবনব্যাপী শিক্ষার্থী ও ঝঞ্জাবিক্ষুব্ধ চলার পথের এক অনুসন্ধিৎসু পথিক, সেই অর্থে আমৃত্যু শিক্ষানবিশ। তবে শিক্ষানবিশ হলেও, আমি পেশাগত পরিসরে যুক্ত এবং সেই কারণে এই ঘটনা দু’টো সম্পর্কে কৈফিয়ত প্রদান পেশাগত পরিচয় থেকেই আমার ওপর ন্যূনতম একটি নৈতিক দায় মনে করছি। আত্মগ্লানি লুকোতে সততার প্রশ্নে আপস করা আমার কাছে আত্মপরিচয়ের সঙ্গেই বিশ্বাসঘাতকতা। তাই কেউ যদি বলেন, ‘এটা তো খুবই সামান্য একটি ভুল’, পেশাজীবি হিসেবে আমি তা সহজে মেনে নিতে পারি না। কারণ এই ‘সামান্য’ ভুলই একজন পেশাজীবীর এবং তাঁর প্রতিষ্ঠানের ভাবমূর্তি ও দায়বোধের ভিত কাঁপিয়ে দিতে পারে। আর এই ছোট ছোট ভুলগুলোকে উপেক্ষা করার মধ্য দিয়েই আমরা আমাদের পেশাগত এবং মানবিক মূল্যবোধ, দায়-দায়িত্ব ও নীতি-নৈতিকতা ধ্বংশের রাজপথ তৈরি করি।
ঘটনাগুলো যে অনিচ্ছাকৃতভাবে সংগঠিত হয়েছে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু আমার ও সম্পৃক্ত অপর দুই লেখকের জন্য সেগুলোর অভিঘাত ছিল অনেক গভীর আর অস্বস্তিজনক। বিশেষ করে আমার কাছে মনে হয়েছে, আমি যেন নিজের অজান্তেই অন্য কারো ছায়ায় দাঁড়িয়ে আছি, যেখানে নিজের কণ্ঠস্বরটাই চাপা পড়েছে। অপর দিকে যাঁদের লেখা আমার নামে ছাপা হয়েছে জানার পর তাঁদের মনের অবস্থাটাও যে খুব একটা ভাল ছিল না, সেটা সহজেই অনুমেয়। এই অভিজ্ঞতা এক ধরনের অস্তিত্বগত অস্বস্তি তৈরি করেছে, যা শুধুই ব্যক্তিগত নয়; বরং বুদ্ধিবৃত্তিক ও নৈতিক সংকটেরও ইঙ্গিতবাহী। এই জায়গায় এসে রবীন্দ্রনাথের সেই বিড়ম্বিত উচ্চারণের প্রতিধ্বনি যেন শুনি, যেখানে খ্যাতি কোনো আরাধ্য নয়, বরং হয়ে ওঠে এক বোঝা যা বহনের দায়ে মানুষ ক্লান্ত, জর্জরিত, এমনকি নিজেকেই হারিয়ে ফেলে। যদিও আমার ক্ষেত্রে বিষয়টি খ্যাতির নয়; বরং এক বিভ্রান্তিকর প্রতিচ্ছবির, যা আমার চিহ্ন না রেখেই আমার হয়ে কথা বলছে। এই বিড়ম্বনা, এই অপার বেদনার ভিতর থেকেই এই ব্যাখ্যা দেওয়ার প্রয়োজন অনুভব করেছি; নিজেকে স্পষ্ট ও সৎভাবে উপস্থিত করার জন্য, এবং নিজের দায় নিজেই গ্রহণ করার দায়বদ্ধতা থেকে।
প্রথম ঘটনাটি ঘটে এক সুহৃদের আন্তরিক অনুরোধের সূত্রে। তিনি তাঁর একটি লেখা আমাকে পাঠিয়ে বলেন, একটি নির্দিষ্ট জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় তা প্রকাশে আমি যেন তাঁকে সহায়তা করি। আমি লেখাটি সংশ্লিষ্ট পত্রিকার সম্মানিত সম্পাদকের কাছে পাঠাই এবং সচেতনভাবে তাঁর ইমেইল ঠিকানাও সংযুক্ত করি, যেন তিনি সরাসরি লেখকের সঙ্গেই যোগাযোগ করতে পারেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে, মনে হয় তিনি আমার ইমেইল মনোযোগ দিয়ে পড়ার সুযোগ পাননি এবং ভেবেছিলেন যে ইমেইলে সংযুক্ত লেখাটি আমারই। যেমন ভাবা তেমন কাজ। ফলাফল হিসেবে যে সাপ্তাহে কর্মব্যস্ততায় আমি কোনো লেখা পাঠাতে পারিনি, সে সাপ্তাহে ওই লেখাটি তিনি আমার নামে প্রকাশ করেছেন এবং তিনি সেই প্রকাশিত লেখার অনলাইন ভার্সানের লিংকও আমাকে পাঠান।
লিংকে গিয়ে লেখাটির শিরোনাম পড়েই আমি চমকে উঠি। এই তো সেই মুহূর্ত, যখন পেশাগত সংকল্প আর মানবিক বিব্রতবোধ একসঙ্গে ধাক্কা দেয়। মনে পড়ল দার্শনিক ইমানুয়েল কান্টের সেই নীতিবাক্য: ‘নীতির মানদণ্ড হওয়া উচিত এমন আচরণ, যা তুমি চাও সবাই অনুসরণ করুক’। আমি কি এমন আচরণ অনুমোদন করি? না। কাজেই আমি লজ্জা ও বিব্রতবোধ থেকে সঙ্গে সঙ্গে সম্পাদককে আগে প্রেরিত ইমেইলটি ফরওয়ার্ড করি এবং অনুরোধ জানাই যেন অনলাইন সংস্করণে সংশোধন আনা হয় ও প্রকৃত লেখকের কাছে দুঃখ প্রকাশ করা হয়। পত্রিকা কর্তৃপক্ষ প্রশংসনীয় দ্রুততায় অনলাইনে সংশোধনী আনে এবং আমার সেই সুহৃদ তাতে এতটাই খুশি হন যে, তিনি আমাকে ‘পুরস্কৃত’ করতে চান! কিন্তু ততক্ষণে আমি এমন এক আত্মগ্লানিতে আচ্ছন্ন, এমন সংকোচে ডুবেছিলাম যে, তাঁর সঙ্গে স্বাভাবিকভাবে কথাও বলতে পারছিলাম না। এ যেন এমন এক লজ্জা, যা শুধু আত্মপ্রবঞ্চনার ভয় থেকে নয়, বরং নিজের নৈতিক অবস্থান থেকে কারো প্রশ্নের মুখে পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থেকে জন্ম নেয়।
দ্বিতীয় ঘটনাটি ঘটে রমজানের শেষ সপ্তাহে, যখন আত্মসংশ্লেষ ও আত্মনিয়ন্ত্রণের ভাবনাই মনোজগতকে আচ্ছন্ন করে রাখে। লেখালেখি থেকে তখন কিছুটা মনোযোগ সরে গিয়েছিল, ফলে সেই সাপ্তাহে কাউকেই কোনো লেখা পাঠানো হয়নি। এমন সময় ফেসবুকে অনুজপ্রতীম সতীর্থের একটি অসাধারণ পোস্ট নজরে আসে যেটা পড়ে চিন্তায়, ভাষায় ও সংবেদনায় মন ছুঁয়ে যায়। সেটি হুবহু কপি করে, যথাযথভাবে লেখকের নাম উল্লেখ করে, আমি আমার টাইমলাইনে শেয়ার করি এই ভেবে যে, এটাকে আরও বেশি মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া উচিত। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে, আমার ফেসবুক টাইমলাইনের সেই শেয়ারকৃত লেখাটিই আমার পরিচিত আরেক সম্পাদক সাহেব, সম্ভবত অসাবধানতাবশত লেখার নিচে লেখকের নাম তাঁর নজর এড়িয়ে গিয়েছে, আমার নামেই তাঁর দৈনিকে ছেপে দেন। এক অতিউৎসাহী পাঠক সেই পত্রিকার ই-পেপারের লিংক আমাকে পাঠালে লেখাটির শিরোনাম দেখে আমি বিব্রত হয়ে পড়ি। সাথে সাথে সম্পাদক সাহেবকে বিষয়টি অবহিত করি, তিনি দুঃখ প্রকাশ করেন এবং পরবর্তী সংখ্যায় এ বিষয়ে একটি সংশোধনী ছাপেন।
এখানে প্রশ্ন শুধু তথ্যগত সঠিকতা নয়, প্রশ্ন লেখার প্রকৃত স্বত্ত্বধিকার বা মালিকানা, এবং পেশাগত ও নৈতিক দায়বদ্ধতার পাশাপাশি চিন্তার উৎসকে যথাযথ সম্মান জানানো। হান্না আরেন্ড যে ‘নির্বাক নৈতিকতা’র বিরুদ্ধে সরব হতে বলেছিলেন, এই ঘটনা যেন তারই এক বাস্তব পাঠ। জ্ঞান বা চিন্তা যতই মূল্যবান হোক না কেন, তা যখন প্রকৃত লেখককে বাদ দিয়ে অন্যের নামে ছাপা হয়, তখন তা কেবল একজন লেখকের প্রতিই অবিচার নয়, বরং সেটা পাঠকের প্রতিও একপ্রকার বঞ্চনা। সেই বোধ থেকেই আমি সম্পাদক সাহেবের সঙ্গে যোগাযোগ করি, কোনো অভিযোগ করার জন্য নয়, বরং একটি নৈতিক অবস্থান থেকে বিষয়টাকে তুলে ধরার জন্য। এ কথা নিঃসন্দেহে সত্য যে, দু’টি ঘটনাই নিছক ভুল; কোনো অমঙ্গলজনক অভিপ্রায় থেকে ঘটেনি। তবু ইতিহাস আমাদের শেখায়, ভুলের দায় এড়িয়ে যাওয়া যেমন দৃষ্টিকটু, তেমনি ভুল থেকে শিক্ষালাভ না করাও একটি গুরুতর ব্যর্থতা। সেই বিবেচনায়, এই অনভিপ্রেত অভিজ্ঞতা থেকে কয়েকটি মূল্যবান শিক্ষা গ্রহণ করাকে আমি আমার পেশাগত ও নৈতিক দায়িত্ব বলে মনে করি।
প্রথমত, পত্রিকা কর্তৃপক্ষের উচিত লেখকের সঙ্গে নিবিড় যোগাযোগ স্থাপন ও সেটা রক্ষা করা। কোন নির্বাচিত লেখা চূড়ান্তভাবে প্রকাশের আগে লেখককে অবহিত করলে, যেকোনো বিভ্রান্তি বা সম্পাদনাগত মানবিক ও পেশাগত ভুল সংশোধনের একটি সুযোগ তৈরি হয়। লেখক-সম্পাদক সম্পর্ক কেবল কাগুজে যোগাযোগে সীমাবদ্ধ থাকলে ভুল বেড়ে যায়, আর তার দায় বর্তায় উভয় পক্ষের ওপরেই। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার আলোকে বলা যায়, আমাদের দেশের ছাপা গণমাধ্যমগুলোর পেশাদারিত্বকে আরো শানিত ও দায়িত্বশীল করা উচিত বলে মনে করছি। লেখকের লেখা পেলে তার জন্য প্রাপ্তি স্বীকার ও ছাপা আগে জানানো যে কোন লেখাটি কোন সংখ্যায় যাচ্ছে। তাতে নি:সন্দেহে এ ধরনের ভুল হওয়ার সম্ভাবনা কমে যাবে।
দ্বিতীয়ত, আমার নিজের পক্ষ থেকেও আরও স্পষ্টভাবে সম্পাদকের সাথে যোগাযোগ স্থাপনের চেষ্টা করা জরুরি ও সেখানে দু’পক্ষেরই আরো দায়িত্বশীল হওয়া দরকার। ভবিষ্যতে যখন অন্যের লেখা কোনো ছাপার গণমাধ্যমে প্রকাশের জন্য সুপারিশ করব, তখন আমাকে দ্ব্যর্থহীনভাবে জানাতে হবে যে, সেটি আমার নিজের লেখা নয়, যাতে করে সে লেখাটি প্রকাশের ক্ষেত্রে যেন কোনো সম্পাদনাগত, ব্যবস্থাপনাগত বা প্রশাসনিক ভুলের সুযোগ না থাকে। একইভাবে মনে রাখতে হবে যে, ফেসবুকে কোনো লেখা শেয়ার করার সময় শুধু লেখকের নাম উল্লেখ করলেই দায়িত্ব শেষ হয় না। যেহেতু লেখা আমার নয়, সেহেতু সেটাকে উদ্ধৃতির মাঝে রাখা উচিত। অপরদিকে যেকোনো পুনঃপ্রকাশ বা ভিন্ন পরিপ্রেক্ষিত থেকে ব্যাখ্যার সম্ভাব্য ঝুঁকির বিষয়েও আমাকে সতর্ক থাকতে হবে।
আসলে আমাদের দৈনন্দিন পেশাগত ও সামাজিক আচরণে সতর্কতার অভাব, দ্রুততা ও অনুমানভিত্তিক সিদ্ধান্তের যে প্রবণতা রয়েছে, এই দুটি ঘটনাই তার প্রতিফলন। সোফোক্লিস তাঁর ট্র্যাজেডিতে বলেন, ‘জ্ঞান থাকলেই ভুল হয় না, কিন্তু ভুল থেকেই জ্ঞান জন্ম নিতে পারে’—আমি এই ঘটনা দু’টো থেকে সেই শিক্ষাটিই গ্রহণ করতে চাই।
পরিশেষে স্পষ্ট করে বলতে চাই, এটি কোনো খ্যাতির বিড়ম্বনা নয়, বরং ব্যক্তি ও পেশার প্রতি আমার দায়িত্ববোধ থেকে জন্ম নেওয়া এক বিব্রতকর অভিজ্ঞতা। ভুলগুলো নিঃসন্দেহে অনিচ্ছাকৃত, কিন্তু সে কারণেই তা এড়ানো যেত যদি ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান উভয়পক্ষই পেশাগতভাবে আরো সতর্ক, সংবেদনশীল ও দায়বদ্ধ হতো। পেশাগত জগতে কখনো কখনো আমাদের আত্মপরিচয়ের বাইরে গিয়ে নতুন চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে হয়। এ অভিজ্ঞতা আমার জন্য তেমনই এক পাঠ, যা আমাকে আরও মননশীল, সংবেদনশীল ও দায়িত্বশীল হতে অনুপ্রাণিত ও সর্তক করবে। আমি বিশ্বাস করি, ভুল শুধরে নেওয়ার মধ্যে দুর্বলতা নয়, বরং তা সততা ও শক্তির প্রকাশ। প্রিয় পাঠক এবং পত্রিকা কর্তৃপক্ষ; আপনারা আমার লেখার সঙ্গী, আমার সংলাপ, বয়ান ও আলোচনার শ্রোতা, চিন্তাভাবনা ও চেতনার অংশীদার, আর তাই এই অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতিতে আপনাদের সবার আন্তরিক সহানুভূতিও আমার প্রাপ্য। আপনাদের সহৃদয় বিবেচনাবোধ ও ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে এই অনাঙ্খিত ভুলগুলোকে দেখার বিনীত অনুরোধ রইলো।
ড. মাহরুফ চৌধুরী, ভিজিটিং ফ্যাকাল্টি, ইউনিভার্সিটি অব রোহ্যাম্পটন, যুক্তরাজ্য। mahruf@ymail.com
অর্থসংবাদে প্রকাশিত কোনো সংবাদ বা কনটেন্ট কপিরাইট আইনে পূর্বানুমতি ছাড়া ব্যবহার করা যাবে না।
মত দ্বিমত
অন্তরের গহীনে পহেলা বৈশাখ: ছোটবেলার স্মৃতি থেকে নতুন অধ্যায়ের সূচনা
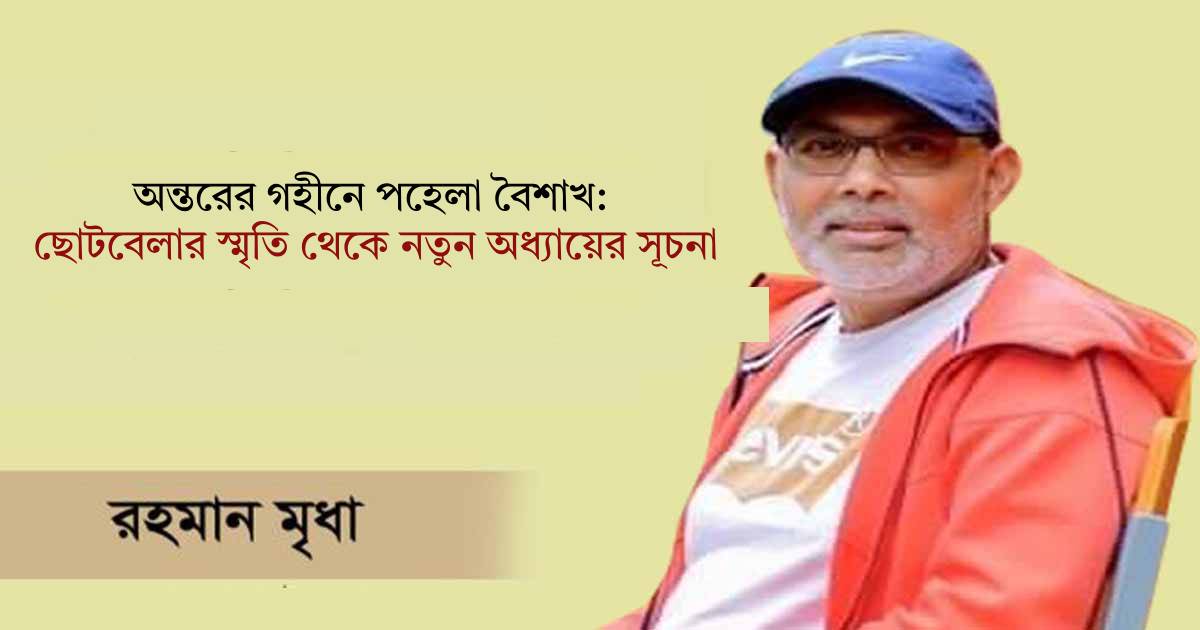
দেশ এবং ভাষা, একে অপরের সাথে গভীরভাবে গাঁথা, যেন দুই প্রাচীন রেশমি সুতো এক সুতায় বাঁধা। বাংলা ভাষা, এই মাটি, এই জনগণের অভ্যন্তরীণ আত্মা—এগুলো সবই একযোগে জড়িয়ে থাকে, যেখানে একে অপরের মধ্যে কোনো বিভেদ নেই। এই দেশের মানুষ, যে ভাষায় কথা বলে, যে সংস্কৃতির মধ্যে বেড়ে ওঠে, সেই ভাষা ও সংস্কৃতি তার অস্তিত্বের অঙ্গ। এবং পহেলা বৈশাখ, এই বাঙালি নববর্ষ, ঠিক তেমনই একটি দিন—যে দিনটি শুধুমাত্র একটি নতুন বছরের সূচনা নয়, বরং একটি নতুন অধ্যায়ের যাত্রা, যেখানে আমরা সবাই একযোগে একটি নতুন সূর্যের দিকে এগিয়ে যাই।
এদিনের অমলিন আনন্দে ইলিশ মাছের সাথে পান্তাভাত, পাশে মরিচ, পেঁয়াজ আর নুনের স্বাদ—এই খাবারের মধ্যে রয়েছে এক অমোঘ সম্পর্ক। স্নিগ্ধতার এক স্বরূপ, যা কেবল বাংলার মাটিতেই সম্ভব। চিরকালীন এই ঐতিহ্য, যেখানে বছরের শুরুতে হালখাতা আর মিষ্টির আদান-প্রদান, এক নিঃশব্দ চুক্তি—একটি নতুন বছরে ব্যবসা, সম্পর্ক, জীবন—সব কিছুই নতুন করে শুরু হতে থাকে।
এবারের পহেলা বৈশাখে, পুরনো বছরের সেই সমস্ত অশুভ প্রতিচ্ছবি, ধান্দাবাজি, চাঁদাবাজি—সবকিছু দূর হয়ে যাবে। নববর্ষের এই দিনটি যেন এক নতুন দিগন্তের সূচনা, যেখানে আমরা শুধুমাত্র নতুন কিছু পাওয়ার স্বপ্ন দেখি না, বরং সেই পুরনো দিনের অশান্তি ও কষ্ট থেকে মুক্তির জন্য, একটি সুন্দর, সজীব এবং পবিত্র জীবনের দিকে অগ্রসর হতে চাই।
প্রকৃতি ও সংস্কৃতি, একে অপরের পরিপূরক। বাংলা নববর্ষ, পহেলা বৈশাখ, এই দিনটি শুধুমাত্র আমাদের ক্যালেন্ডারের একটি নতুন পৃষ্ঠা নয়, বরং এটি আমাদের চারপাশের প্রকৃতির এক অনবদ্য রূপ। বৈশাখের প্রথম দিনে আকাশের কোণে মেঘের গম্ভীরতা, যেন সে জানাচ্ছে নতুন বছর আসছে, নতুন আশা, নতুন উল্লাস। ঝড়ো হাওয়ার মধ্যে বৈশাখী বৃষ্টি এসে প্রকৃতির গা ভিজিয়ে দেয়, যেমন আমাদের হৃদয়ের গভীরে বয়ে আনে এক নতুন আনন্দের তরঙ্গ। বাতাসে ছড়িয়ে পড়ে মিষ্টি গন্ধ—কলমি শাক, পাটুলি ফুল, পলাশের রঙে মোড়া নববর্ষের ফুল। এই দিনটি যেন প্রকৃতির নিজস্ব এক শ্রদ্ধাঞ্জলি, যে ফুলগুলো শোভা পায় আমাদের ছোট-বড়, শহর-বাংলাদেশের প্রতিটি কোণায়।
গ্রামের পলিতে কিংবা শহরের কোন পার্কে, পহেলা বৈশাখের এই প্রাকৃতিক সৌন্দর্য যেন বাড়িয়ে দেয় আনন্দের অনুভূতি। পুরনো বাংলার গ্রামের প্রান্তরে পাকা ফসলের সুবাস, সেই প্রাচীন ঝিলগুলোর শান্ত জল, খালি মাঠে এক অপূর্ব প্রাকৃতিক দৃশ্য—এগুলি শুধু চোখে নয়, আমাদের মনে প্রতিধ্বনিত হয়, যেন পহেলা বৈশাখের প্রতিটি মুহূর্ত প্রকৃতি নিজ হাতে আমাদের জন্য সাজিয়ে রেখেছে।
এই দিনটি শুধুমাত্র সাংস্কৃতিক উদযাপন নয়, এটি প্রকৃতির সঙ্গে আমাদের সম্পর্কেরও একটি বিশেষ রূপ, যা আমাদের শিকড়ের দিকে ফিরিয়ে নিয়ে যায়। সারা দেশের মানুষের আনন্দে মেতে ওঠা, গ্রামীণ পরিবেশে গুচ্ছগুচ্ছ পটল, কাঁচা কলা, কচুরিপানা—এই সব প্রকৃতির উপাদান, একে অপরকে সহযোগিতা করে নতুন বছরের দারুণ সূচনা করতে। বৈশাখী বাতাস, মাটির গন্ধ এবং নতুন জীবনের এক সতেজ শ্বাস—এই উপাদানগুলো একত্রিত হয়ে পহেলা বৈশাখের উদযাপনকে শুধু একটি দিন নয়, বরং এটি যেন একটি নয়া দিগন্তের সূচনা, যেখানে প্রকৃতি এবং সংস্কৃতি হাতে হাত রেখে একত্রে উদযাপন করে।
পহেলা বৈশাখের দিনটি যেন এক সুন্দর গল্প, যার প্রতিটি দৃশ্য জীবনের এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা। ভোর বেলা, যখন প্রথম সূর্য ওঠে, রাস্তায় রাস্তায় মানুষের পদচারণা শুরু হয়। শহরের বাজারে, ফুলের দোকানে ভিড় জমে যায়—প্রতিটি দোকানে সাজানো থাকে নানা রঙের ফুল। গোলাপের লাল, গাঁদার হলুদ, শাপলার সাদা, আর পলাশের তীব্র কমলা রঙের ফুলের গুচ্ছ, যেন প্রকৃতির নিজস্ব শুভেচ্ছা। সেখানে একেকটি ছোট গল্প প্রতিধ্বনিত হয়, এক বিক্রেতা তার দোকানে সাজানো ফুলগুলো তুলে তুলে বিক্রি করছে, আর এক বৃদ্ধা আনন্দের সাথে একটি ছোট পুতুলের ফুল কেনে, যেন পুরনো দিনের রঙিন স্মৃতি ফিরে পাচ্ছে।
গ্রামের সরু পথে, হালকা রোদে, লাল-সাদা শাড়ি পরা মেয়েরা চমক দিয়ে হেঁটে যায়, তাদের গায়ে ফুলের মালা, হাতে সজাগ চুড়ি, মুখে হাসি—পহেলা বৈশাখের আনন্দের প্রতীক। ছোট ছেলে-মেয়ে, তারা ঝরে পড়া পাতা ও ফুলের সঙ্গে খেলছে, মুখে মিষ্টি খাবারের খুশি হাসি, যেন পুরো গ্রামটি এক নতুন রঙে রাঙানো। পথে, গ্রামের পুকুরে নৌকায় চড়ে মাঝির গান শুনতে পাওয়া যায়, সেই গান যা বাঙালি ঐতিহ্যের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ, একটি দৃশ্য যা শুধু বাঙালির কাছে নয়, সারা বিশ্বে নস্টালজিয়া তৈরি করে।
আর শহরের বড় পার্ক, রমনা বটতলায়, যেখানে হাজার হাজার মানুষের ভিড়। উজ্জ্বল রঙের পাঞ্জাবি ও শাড়ি পরিহিত মানুষ একসঙ্গে দাঁড়িয়ে সুর মেলাচ্ছে, সবাই যেন একসাথে গাইছে—“এসো হে বৈশাখ এসো এসো…”। এ যেন এক উত্সব, এক সমবেত সঙ্গীত, যেখানে সবার হৃদয় এক সঙ্গে মিলছে। বটগাছের নিচে, পুরনো দারুণ ঐতিহ্যের গুনগুন, আর চিরন্তন প্রাকৃতিক সুরের মাঝে, পহেলা বৈশাখকে অভ্যর্থনা জানাতে সবাই মিলিত।
এটি একটি মুহূর্ত, যেখানে অতীত ও বর্তমান একসাথে মিশে যায়, যেখানে প্রতিটি সুর, প্রতিটি ফুল, প্রতিটি হাসি এক নতুন কাহিনী রচনা করে—পহেলা বৈশাখের দিনটি, যা আমাদের জীবনে সেই সোনালী দিনগুলোর কথা মনে করিয়ে দেয়, যখন আমরা একে অপরকে আরও ভালোভাবে জানতাম, ভালোবাসতাম।
পৃথিবীর নানা প্রান্তে নতুন বছর উদযাপন হয়, তবে বাংলা নববর্ষের প্রতি যে অনন্য ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা, তা পৃথিবীর অন্যান্য অঞ্চলের থেকে একেবারেই আলাদা। যেমন, ইংরেজি নববর্ষ ১ জানুয়ারিতে আসে, এবং পশ্চিমা দেশগুলোতে এটি এক আড়ম্বরপূর্ণ পার্টির মাধ্যমে পালিত হয়। রাতের বেলা, আতশবাজি, মিউজিক এবং জাঁকজমকপূর্ণ অনুষ্ঠানে মেতে ওঠে মানুষ। তবে বাংলা নববর্ষের উৎসবটি শুধুমাত্র একটি রাতের অনুষ্ঠান নয়, এটি একটি পুরো দিনের, পুরো সমাজের একটি অনন্য ঐতিহ্য। এখানে দিন শুরু হয় প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের সঙ্গে, যেখানে সূর্যোদয়ের সাথে এক অনাবিল শান্তির পরিবেশ সৃষ্টি হয়।
ভারতেও নানা অঞ্চলে নববর্ষ উদযাপন করা হয়, যেমন বাংলা নববর্ষ, পাঞ্জাবের বৈশাখি, এবং গুজরাটের উত্তরায়ণ। যদিও এগুলোর মধ্যে সাদৃশ্য রয়েছে—ফসল কাটার সময়, কৃষকের জীবনের শুরু—তবে প্রতিটি অঞ্চলের নববর্ষের রীতি, সংস্কৃতি এবং আচার-অনুষ্ঠান আলাদা। বাংলাদেশের পহেলা বৈশাখ, বিশেষ করে বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে, মিষ্টি গন্ধে ভরা গাছে গাছে রঙিন ফুল আর পরিবেশের মধ্যে অন্যরকম এক অনুভূতি তৈরি হয়, যা আর কোথাও পাওয়া যায় না।
বিশ্বের বিভিন্ন দেশের নববর্ষ উদযাপন হয় ভিন্নভাবে। যেমন চীনা নববর্ষে থাকে লাল রঙের উত্সব, যা পৃথিবীজুড়ে প্রাচীন ঐতিহ্যের অংশ হিসেবে পরিচিত, যেখানে বিশেষ খাবার, সাংস্কৃতিক নৃত্য ও ড্রাগন র্যালি থাকে। আর জাপানি নববর্ষে, বরফাচ্ছন্ন পর্বতমালা এবং সাদা প্রাকৃতিক দৃশ্যে পালিত হয় উৎসব, যেখানে পরিবারের সঙ্গে সময় কাটানোর গুরুত্ব দেওয়া হয়। তবে এসব সবার মধ্যে একটি সাধারণ মিল রয়েছে—নতুন বছরের সূচনায় পুরনো সব পেছনে ফেলে এগিয়ে যাওয়ার ইচ্ছা ও আশা।
বাংলাদেশে পহেলা বৈশাখ উদযাপনের অনন্য বৈশিষ্ট্য হলো এর মানুষের মাঝে একাত্মতা তৈরি করা। এখানে বিভিন্ন ধর্ম, বর্ণ, সম্প্রদায়ের মানুষ একত্রিত হয়ে নৃত্য, সঙ্গীত এবং ঐতিহ্যবাহী খাবারের মাধ্যমে দিনটি উদযাপন করে, যা বাংলাদেশের এক অসাধারণ বৈশিষ্ট্য। এই দিনটি শুধু একটি কালেন্ডারীয় পরিবর্তন নয়, বরং আমাদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য এবং শিকড়ের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন। এটা যেন মানুষের মনের মধ্যে এক নতুন প্রেরণা দেয়, যেখানে সবাই মিলে সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং রাজনৈতিক বিরোধ ভুলে এক হয়ে জীবন উদযাপন করে।
বিশ্বের অন্যান্য দেশে, যেমন সুইডেন, নেদারল্যান্ডস কিংবা স্পেনে, নববর্ষ উদযাপন হয় অঙ্গীকার, আশাবাদ এবং বন্ধুত্বের ভিত্তিতে। তবে পহেলা বৈশাখের বৈশিষ্ট্য হলো, এর মধ্যে যে উন্মুক্ততা, ঐক্য ও সামাজিক যোগাযোগ রয়েছে, তা যেন এক নতুন দৃষ্টিভঙ্গি সৃষ্টি করে, যেখানে জাতিগত ঐতিহ্যকে সম্মান জানিয়ে, সবাই একসঙ্গে উদযাপন করে।
বাংলাদেশের পহেলা বৈশাখের উদযাপন, তাই শুধু একটি জাতির নববর্ষ উদযাপন নয়, এটি একটি বৈশ্বিক উত্সবের অংশ, যা আমাদের সংস্কৃতির গুরুত্ব, শান্তি ও ঐক্য প্রতিষ্ঠা করতে সহায়তা করে। এটি একটি দৃঢ় আহ্বান—বিশ্বের প্রতি যে, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি এবং মানুষের শিকড়কে সম্মান জানিয়ে, আমরা যেন নিজেদের বিশ্বাসে অটুট থেকে, সবধরনের বিভেদ ও বৈষম্য ভুলে মানবতা, ভালোবাসা ও একাত্মতায় বিশ্বাস রাখি।
পহেলা বৈশাখের দিনটি যেন এক অমূল্য স্মৃতি, যা হৃদয়ে চিরকাল রয়ে যায়। ছোটবেলায়, আমার গ্রামের পথে পহেলা বৈশাখের আনন্দ ছিল এক অপূর্ব দৃশ্য। দুপুর বেলা, পান্তা-ইলিশ আর পেঁয়াজ, চিঁড়া-দইয়ের এক অপূর্ব পর্বে বসে, আমার সঙ্গীরা একে অপরকে জানাতো বছরের শুভেচ্ছা। তবে সবচেয়ে স্মরণীয় ছিল, পহেলা বৈশাখের দিনটিতে রমনার বটতলায় যাওয়া। একসঙ্গে গানের তালে তালে নাচ, গল্প বলা—যেখানে শুধু ঐতিহ্যই নয়, সেখানে ছিল একাত্মতা, ভালোবাসা আর বিশ্বাসের শক্তি। আমি যেন তখন উপলব্ধি করতাম, পহেলা বৈশাখ শুধু একটি নতুন বছরের সূচনা নয়, বরং একটি নতুন জীবনের সূচনা, যেখানে আশা ও সম্ভাবনার আলো জ্বলতে থাকে।
তখনকার সেই দিনগুলোর কথা মনে পড়লে, মনে হয়—আজও যদি সেই ঐতিহ্যকে অটুট রাখতে পারতাম, যদি সেদিনের মতোই আমরা সবাই এক হয়ে নতুন বছরের শুরুটা উদ্যাপন করতে পারতাম, তবে হয়তো আমাদের সমাজের সবার মধ্যে সত্যিকার অর্থে ঐক্য এবং শান্তি প্রতিষ্ঠা হত। এই স্মৃতিগুলো যেন এখনো মনকে উজ্জীবিত করে—যতই সময় এগিয়ে যাক, পহেলা বৈশাখের সেই স্নিগ্ধ রোদ, সেই পান্তা-ইলিশ, সেই গানের সুর—সব কিছু মনে হয়, কখনো মুছে যাবে না, বরং প্রতিটি পহেলা বৈশাখের সঙ্গে নতুন করে জীবন্ত হয়ে উঠবে।
পহেলা বৈশাখ (১৪ এপ্রিল) সারা বিশ্বের বাঙালিদের জন্য এটি শুধু একটি দিন নয়, এটি আমাদের জীবনের এক নতুন যাত্রা, যেখানে আশা, ভালবাসা, পরিবর্তন ও ভবিষ্যতের প্রতি আস্থা থাকুক। এখানে ধর্ম, জাতি কিংবা বিশ্বাসের কোনো ব্যাপার নেই—এটা শুধু জাতিগত পরিচয়ের উদযাপন।
আমরা যেন ভুলে না যাই, আমাদের সংস্কৃতি এবং বিশ্বাসকে সম্মান করতে হবে এবং কোনো কিছুই আমাদের জাতিগত পরিচয়ের সাথে সাংঘর্ষিক হতে পারে না। তাই আসুন, আমরা যেন বিশ্বে এক শক্তিশালী, উদার জাতি হয়ে উঠি। দূর হোক কুসংস্কার, জয় হোক মানবতার, গড়ে উঠুক বাঙালির ঐতিহ্য এবং সংস্কৃতি।
এবারের পহেলা বৈশাখ হতে পারে ভবিষ্যৎ নির্মাণের চাবিকাঠি, যা সবার জন্য ভালোবাসা, শান্তি এবং সমৃদ্ধি বয়ে আনবে। সবাইকে বাংলা নববর্ষের প্রাণঢালা শুভেচ্ছা এবং ভালোবাসা।
রহমান মৃধা, গবেষক ও লেখক
(সাবেক পরিচালক, ফাইজার, সুইডেন)
Rahman.Mridha@gmail.com