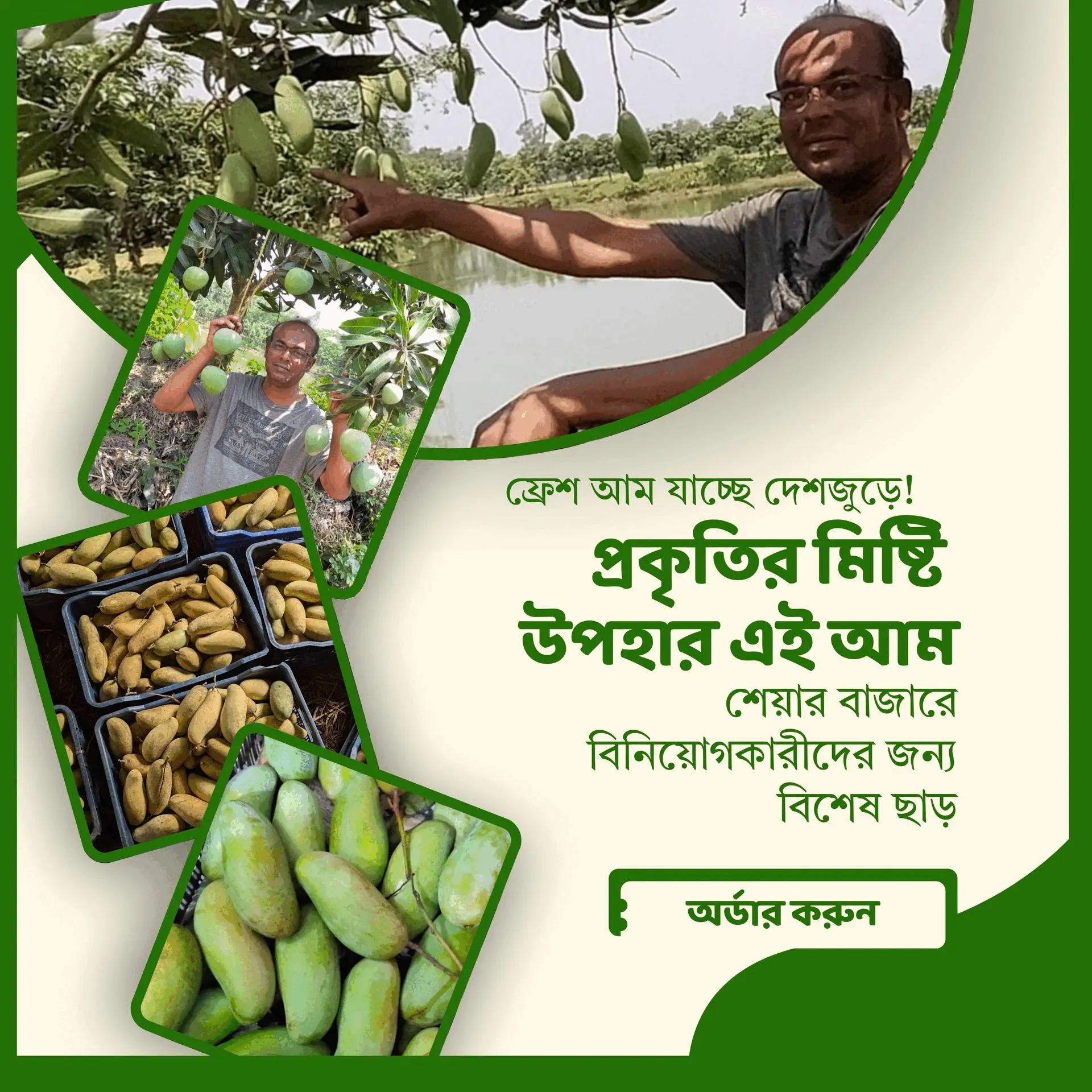অর্থনীতি
জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের চেয়ারম্যান ও এমসিসিআই প্রতিনিধি দলের আলোচনা সভা

মেট্রপলিট্যান চেম্বার অফ কমার্স এণ্ড ইন্ডাস্ট্রী ঢাকার (এমসিসিআই) সভাপতি কামরান টি. রহমানের নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধি দল জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) চেয়ারম্যানসহ অন্যান্য সদস্যদের সাথে বাজেট প্রস্তাবনা বিষয়ে এনবিআর’র সভা কক্ষে একটি সভায় যোগ দেন।
বুধবার (০৭ ফেব্রুয়ারি) আলোচনা সভার শুরুতে সৌহার্দ্য বিনিময়ের পরে এনবিআর’র চেয়ারম্যান আবু হেনা মো. রহমাতুল মুনিম এমসিসিআই’র সভাপতি কামরান টি. রহমানকে বাজেট প্রস্তাবনা উপস্থাপন করার জন্য অনুরোধ করেন।
এমসিসিআই’র সভাপতি একটি সংক্ষিপ্ত সূচনা বক্তব্য রাখেন এবং বাজেট প্রস্তাবনার কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উল্লেখ করেন। পরবর্তীতে তার সহকর্মী চেম্বারের ট্যারিফ এন্ড ট্যাক্সেশন কমিটির চেয়ারম্যান হাসান মাহমুকে বিস্তারিত আলোচনার জন্যে আহ্বান জানান।
এমসিসিআই’র সভাপতি তার সূচনা বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, এবারের বাজেট অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কোভিড-১৯ মহামারী পরবর্তী অবস্থা; রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধাবস্থা; বিশ্ববাজারে জ্বালানী তেলসহ সকল দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতির কারণে ব্যবসা-বাণিজ্যে অনিশ্চয়তা কাটিয়ে উঠে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরতে সরকারের বিশেষ সহযোগিতা প্রয়োজন। তাছাড়া ২০২৬ সালে বাংলাদেশ উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে পরিগণিত হতে যাচ্ছে। মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত হলে স্বাভাবিকভাবে বাংলাদেশের বাণিজ্য ক্ষেত্রে এবং অন্যান্য কিছু সুবিধা স্বয়ংক্রিয়ভাবে বাতিল হয়ে যাবে। সেই হিসেবে এবারেরবাজেট একটি অন্তর্বর্তীকালীন বাজেট হিসেবেও গণ্য হবে।
তিনি আরো বলেন, আমাদের ধারণা মতে, সামগ্রিক জাতীয় রাজস্বের প্রায় ৪০ শতাংশ বা তার চেয়েও বেশী আসে এমসিআিই’র সদস্য প্রতিষ্ঠানসমূহের কাছ থেকে। দেশের বড় বড় প্রতিষ্ঠান ও শিল্প গ্রুপ যারা প্রতিবছরই সর্বাধিক পরিমাণ জাতীয় রাজস্ব প্রদান করে থাকে, যেমন- বৃটিশ অ্যামেরিকান টোব্যাকো, গ্রামীণফোন, স্কয়ার গ্রুপ, এসিআই গ্রুপ, বেক্সিমকো ও ট্রান্সকম গ্রুপসহ অন্যরাও এমসিসিআই’র সদস্য। সেই হিসেবে এমসিসিআই ও এর সদস্য প্রতিষ্ঠানসমূহ জাতীয় রাজস্ব সংগ্রহে
অগ্রণী ভূমিকা পালন করে আসছে।
এমসিসিআই’র সভাপতি আরো বলেন, এমসিসিআই সবসময়ই একটি উন্নত রাজস্ব ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি চালুকরণে গুরুত্ব আরোপ করে আসছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দক্ষ নেতৃত্বে বাংলাদেশ ‘ডিজিটাল বাংলাদেশ’ থেকে ‘স্মার্ট বাংলাদেশ’ এর দিকে এগিয়ে চলছে এবং সকল ক্ষেত্রেই আমরা উত্তরোত্তর উন্নতি লাভ করছি। অনেক সীমাবদ্ধতার মধ্যেও বর্তমান সকারের দক্ষ নেতৃত্ব এবং বর্তমান এনবিআর চেয়ারম্যানের সামগ্রিক দূরদর্শিতার মাধ্যমে এনবিআর দেশের সামগ্রিক উন্নয়নে বলিষ্ঠ ভূমিকা রেখে চলছে। বর্তমান অর্থ বছরের প্রথম ছয় মাসে কর আহরণের প্রবৃদ্ধি ছিল প্রায় ১৩ দশমিক ৮৯ শতাংশ এবং বর্তমান অর্থ বছরের প্রথম ছয় মাসে রাজস্ব লক্ষ্যমাত্রার প্রায় ৩৮ দশমিক ৫২ শতাংশ কর আহরণ করা হয়েছে।
এমসিসিআই বাজেট প্রস্তাবনার মধ্যে সবসময়ই বাজেট ব্যবস্থাপনা অধিকতর গতিশীল করার দিকে জোর দিয়ে থাকে। এমসিসিআই বিশ্বাস করে যে, বাজেট ব্যবস্থাপনা গতিশীল ও স্বচ্ছ হলে ব্যবসায়ীরা স্বপ্রণোদিত হয়ে রাজস্ব প্রদান করবে। এমসিসিআই তাদের বাজেট প্রস্তাবনায় সামগ্রিক কল্যাণ তথা দেশের কল্যাণ ও ব্যবসায়ীদের কল্যাণ চিন্তা করে থাকে। এতে একদিকে যেমন ব্যবসা-বাণিজ্য সহজ হয়, অন্যদিকে দেশের রাজস্ব আয়েও ঘাটতি হয় না। এমসিসিআই জনগণের বিদ্যমান আয় রক্ষা করে এমন প্রবৃদ্ধি-ভিত্তিক নীতির মধ্যে ভারসাম্য বজায় রেখে বাজেট প্রস্তাবনা দিয়ে থাকে।
এমসিসিআই’র সভাপতি নিন্মলিখিত সুনির্দিষ্ট বিষয়গুলির প্রতি চেয়ারম্যানের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন-
১। তিনি বলেন- বিগত অর্থবছরে কিছু শর্ত সাপেক্ষে প্রায় সকল ক্ষেত্রে কর্পোরেট কর হার ২.৫ শতাংশ পর্যন্ত কমানো হয়েছে। বর্তমান বাস্তবতায়,
হ্রাসকৃত কোম্পানী করহার সুবিধা কেউই ভোগ করতে পারছে না। অর্থ আইন, ২০২৩ অনুযায়ী নগদ লেনদেনের শর্তাবলীর প্রযোজ্যতার কারণে হ্রাসকৃত কর হার সুবিধা নেওয়া সম্ভব হয়ে উঠছে না। বাংলাদেশের অর্থনীতি ৮০ শতাংশের অধিক অনানুষ্ঠানিক অর্থনীতি। এই অনানুষ্ঠানিক ও আনুষ্ঠানিক অর্থনীতির মাধ্যমেই বাংলাদেশের শিল্প ব্যবস্থা ক্রমশ অগ্রসরমান। বাংলাদেশের আর্থসামাজিক অবস্থা বিবেচনায় করহারের ক্ষেত্রে অর্থ আইন, ২০২৩ এর শর্তাবলী বাতিল বিবেচনায় বিষয়টিতে চেয়ারম্যান মহোদয়ের সদয় দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে।
অপর পক্ষে, বাংলাদেশে কার্যকরী করপোরেট কর হার অনেক বেশী। এখানে অননুমোদিত ব্যয় এবং উৎসে কর কর্তন এতো বেশী যে, ব্যবসায়ীরা এই কর্পোরেট করহারের কমানোর সুবিধা ভোগ করতে পারছে না। বাস্তবে এই কর্পোরেট করহার পাবলিক লিমিটেড কোম্পানির ক্ষেত্রে ২০ শতাংশ আর থাকে না, তা ক্ষেত্র বিশেষে ৪০ শতাংশ থেকে ৫০ শতাংশ পর্যন্ত হয়ে যায়। এই বিষয়টিও ভেবে দেখার জন্য চেয়ারম্যানকে অনুরোধ জানিয়েছে।
২। এমসিসিআই’র সভাপতি বলেন- গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার বর্তমানে ‘ডিজিটাল বাংলাদেশ’ থেকে ‘স্মার্ট বাংলাদেশ’ রূপান্তরের দিকে অগ্রসরমান। সরকার সব ক্ষেত্রেই অটোমেশনের দিকে জোড় দিয়ে যাচ্ছে। এরই ধারাবাহিকতায় বর্তমান এনবিআর চেয়ারম্যান মহোদয়ের বলিষ্ঠ নেতৃত্বের মাধ্যমে স্বল্প সময়ের মধ্যেই ‘অনলাইনভিত্তিক আয়কর রিটার্ন যাচাইকরণ’ ব্যবস্থা সত্যিই প্রশংসার দাবীদার। এক্ষেত্রে আয়কর রিটার্ণ জমাদান নথি নং এবং তারিখ অন্তর্ভূক্ত করা গেলে এই ব্যবস্থা আরও ফলপ্রসূ হবে হবে বলে জানিয়েছেন। এছাড়াও ‘অনলাইনভিত্তিক ব্যক্তিগত আয়কর রিটার্ন জমাদান’ পদ্ধতি আরো একটি প্রশংসনীয় উদ্যোগ। তবে, করদাতাগণ সকল ধরনের দলিলাদি অনলাইনের মাধ্যমে সংযুক্তির সুবিধা পেলে এই অনলাইন ভিত্তিক আয়কর রিটার্ন জমাদান পদ্ধতি অনেক জনপ্রিয়তা পাবে বলে এমসিসিআই বিশ্বাস করে।
ভ্যাট ব্যবস্থাপনা সফটওয়্যারের মাধ্যমে বর্তমানে প্রায় সকল কোম্পানীসমূহ মাসিক ভ্যাট রিটার্ন প্রদান করে থাকে। তবে এই ব্যবস্থা পূর্ণাঙ্গভাবে অটোমেশন নয়। ঊ-ওহাড়রপরহম এর মাধ্যমে এই অটোমেশন ব্যবস্থা গতিশীল হবে বলে এমসিসিআই মনে করে। এছাড়াও ব্যবসার সাথে সম্পৃক্ত সকল উপাদানকেই পণ্য বা সেবার উপকরণ হিসেবে বিবেচনা করত আইনের ধারা পরিবর্তন সাপেক্ষে রেয়াত ব্যবস্থার অটোমেশন পূর্ণাঙ্গরূপে গতিশীল হবে বলে এমসিসিআই বিশ্বাস করে। সময়ের চাহিদার প্রতি লক্ষ্য রেখে কর নির্ধারণ ব্যবস্থা, আপীল, ট্রাইবুনাল, বিকল্প বিরোধ নিস্পত্তি (এডিআর) পর্যায়ে প্রচলিত আইনে প্রয়োজনীয় সংশোধনী আনয়নপূর্বক অনলাইনে শুনানী গ্রহণের বিধান প্রবর্তন করা অতীব জরুরী। এছাড়াও করদাতাদের নোটিশ প্রদান, শুনানীতে করদাতাদের হাজিরা পদ্ধতি ইত্যাদির ব্যবস্থাসমূহ ও আইনের সংশোধনীর মাধ্যমে অনলাইনভিত্তিক হওয়া খুবই জরুরী। এই ব্যবস্থার ফলে ব্যবসায়ীদের অর্থ ও সময়ের অপচয়সহ ব্যবসায়িক ব্যয় হ্রাস পাবে। বিষয়টিতে চেয়ারম্যান মহোদয়ের সুনজর প্রার্থনা করেছে।
৩। আয়কর আইন ২০২৩ অনুযায়ী বর্তমানে ২৬৪ ধারা অনুযায়ী ৪৩ টি ক্ষেত্রে আয়কর রিটার্ন জমাদানের প্রমাণপত্র (পিএসআর) দাখিল বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। ব্যাপক সংখ্যক পিএসআর দাখিলের বিধান ব্যবসার সক্ষমতা হ্রাসের পাশাপাশি ব্যবসা সহজীকরণের রাষ্ট্রীয় উদ্যোগকে ব্যাহত করছে। পিএসআর সংগ্রহকারীর পক্ষে হিসাবরক্ষণ ব্যবস্থা জটিল হচ্ছে। কোম্পানীসমূহ এনবিআরের পক্ষে আইনসিদ্ধভাবে কর ব্যবস্থাপনা তদারকি করে থাকে। পক্ষান্তরে, আয়কর আইন বর্হিভূতভাবে, অনেক সময় চঝজ এর তথ্যাবলী ছাড়াও করদাতাদের আয়ের বিবরণ, কর প্রদানের পরিমাণ সংক্রান্ত সংবেদনশীল তথ্যাবলী সংগ্রহ করা যৌক্তিকও নয়। তাছাড়াও রিটার্ন দাখিলের সময়সীমা থাকা সত্বেও হালনাগাদকৃত পিএসআর দাখিলের বিধান সাংঘর্ষিক ও বাস্তবসম্মত নয় বলে পরিলক্ষিত হয়। ফলশ্রুতিতে, এই বিধানের ক্ষেত্রসমূহ বাস্তবসম্মতভাবে বিবেচনাপূর্বক পরিসর সীমিত করার বিষয়ে চেয়ারম্যান মহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।
৪। ০৬ বৎসর এর অধিককাল পর্যন্ত পরিসম্পদ কর বিবেচনা: আয়কর আইন ২০২৩ এর ধারা ২১২(৪) এর দফা (আ) তে ০৬ (ছয়) বৎসরের অধিককাল পর্যন্ত পরিসম্পদ
উক্ত ষষ্ট বৎসরের বিবেচনা করার কথা বলা হয়েছে। বাস্তব অবস্থায় ৬ষ্ট বৎসরের পূর্বোক্ত বছরসমূহের হিসাব অনেকাংশে সংরক্ষণ করা খুবই দূরুহ। ৬ষ্ট বৎসরের অধিককালের কোনরূপ সীমারেখা না রেখে প্রণীত আইন বাংলাদেশের বাস্তব অবস্থার সাথে অসংগতিপূর্ণ। এমসিসিআই পূর্বোক্ত আইনের সাথে সাদৃশ্য রেখে নতুন আয়কর আইন, ২০২৩ এ বিধানটি প্রবর্তন করার জন্য চেয়ারম্যানকে অনুরোধ জানাচ্ছে।
৫। অনুমোদিত ফান্ডসমূহের উপর করারোপ: অর্থ আইন, ২০২৩ অনুযায়ী বেসরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের ভবিষ্য তহবিল, অনুমোদিত বার্ধ্যক্য তহবিল, অনুমোদিত আনুতোষিক তহবিল এবং শ্রমিক কল্যাণ তহবিলের উপর কর আরোপ করা হয়েছে। অন্যদিকে সরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের উক্ত ফান্ডের জন্য কোনরূপ কর আরোপের বিধান নেই। এক্ষেত্রে সরকারি এবং বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে সীমারেখা আইনগতভাবে দৃষ্টিকটু। এমতাবস্থায়, ফান্ডসমূহের কর আরোপ থেকে বিরত থাকতে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য চেয়ারম্যান মহোদয়কে অনুরোধ জানাচ্ছি।
৬। বর্তমান বাস্তবতায় অধিকাংশক্ষেত্রে পণ্যের বিনিময়মূল্যকে সম্পূর্ণরূপে অগ্রাহ্য করে ডাটাবেজ মূল্য বা রেকর্ড মূল্যকে শুল্কায়নের মূল্য হিসেবে বিবেচনা করা হয়ে থাকে। এমতাবস্থায়, আইনের প্রয়োজনীয় সংশোধন এবং আন্তর্জাতিক বাজারের হালনাগাদ তথ্যের ডাটাবেজ জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের মাধ্যমে সাবস্ক্রাইবের মাধ্যমে সম্পূর্ণ অটোমেশন ব্যবস্থার বাস্তবায়ন করতে চেয়ারম্যানের দৃষ্টি আকষর্ণ করেছে।
৭। বর্তমানে দেশের ৪০ লক্ষ জনশক্তি যাদের বয়স ১৫ থেকে ৬০ বৎসর এবং যারা শিক্ষা, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণে অন্তর্ভূক্ত নয় (ঘঊঊঞ)। এই বৃহৎ জনশক্তিকে শ্রমবাজারে নিয়ে আসা খুবই জরুরী। এই বৃহৎ জনশক্তিকে যদি দক্ষ কর্মী হিসেবে গড়ে তোলা যায়, তবে আমাদের জিডিপি (এউচ) এর উপর অবশ্যই ইতিবাচক প্রভাব পড়বে। এরই ধারাবাহিকতায় স্থানীয় শিল্পের বিকাশ খুবই জরুরী। স্থানীয় শিল্প উদ্যোক্তাগণ স্থানীয় পর্যায়ে আন্তর্জাতিক মানের পণ্য উৎপাদনের মাধ্যমে একদিকে বৈদেশিক মুদ্রার সাশ্রয় করছে, অন্যদিকে কর্মস্থান বৃদ্ধির লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। স্থানীয় বাজার সম্প্রসারণের লক্ষ্যে আয়কর হার, মূসক ব্যবস্থাপনা, শিল্প যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রাংশ আমদানীর শুল্ককহার, সম্পূরক শুল্কহার যথাযথভাবে বিবেচনা করে স্থানীয় শিল্প সম্প্রসারণে চেয়ারম্যান সদয় দৃষ্টি দিবেন বলে এমসিসিআই বিশ্বাস করে।
৮। সবশেষে এমসিআিই’র সভাপতি বলেন, ২০২৬ সালে বাংলাদেশ এলডিসি থেকে সম্পূর্ণভাবে বের হয়ে মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত হতে যাচ্ছে। এই বাস্তবতায় আয়কর হার, ভ্যাট হার, সম্পূরক কর, শুল্কহার সহ কাস্টমস ডিউটিসমূহ পূনর্বিণ্যাস করা আবশ্যক। তাছাড়া স্মার্ট বাংলাদেশের নিরিখে সম্পূর্ণ অটোমেশন ব্যবস্থার সুষ্ঠু পরিকল্পনা খুবই জরুরী। এমতাবস্থায় বর্তমান বাজেট প্রস্তাবনা থেকে এর রূপরেখা বা পরিকল্পনা থাকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।
৯। প্রতিনিধি দলের সদস্য বলেন, Thin Capitalization Rule বিবেচনায় মূলধন ও ঋণের সর্বোচ্চ অনুপাত নির্ধারণ করার বিধান প্রবর্তন জরুরী।
১০। প্রতিনিধি দল মনে করেন, ২০২৬ সালে উন্নত আয়ের দেশে পরিপূর্ণ হলে অনেকাংশে রাজস্ব কমে যেতে পারে। সেজন্য পরিপূর্ণভাবে অটোমেশন ব্যবস্থার
সুষ্ঠু পরিকল্পনাসহ একটা কর নীতি আবশ্যক।
১১। প্রতিনিধি দল আরও প্রস্তাব করেছেন, উৎসে কর কর্তন সংক্রান্ত আইনের ধারাসমূহের কিছুটা পরিবর্তন প্রয়োজন।
১২। প্রতিনিধি দল সর্বশেষ ভ্যাট আইনের ক্ষেত্রে ঊ-ওহাড়রপব (Electronic VAT invoice) কেন্দ্রীয় ইউনিট; উপকরণ-উৎপাদ সহগ; রেয়াত ব্যবস্থা সহজীকরণের ধারা সমূহ সহজীকরনের উপর গুরুত্ব আরোপ করার জন্য ও প্রস্তাব করেছে।
এমসিসিআই সার্বিক বাজেট প্রস্তাবনায় আয়কর অধ্যাদেশ বিষয়ে ৪৭টি, মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শূল্ক আইন বিষয়ে ৪৮ টি এবং কাস্টমস্ধসঢ়; আইন বিষয়ে ১২টি প্রস্তাব পেশ করে।
ফলপ্রসূ আলোচনার পর এনবিআরের চেয়ারম্যান সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

অর্থনীতি
ডিজিটাল ব্যাংকের আবেদনপত্র চেয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংক

বাংলাদেশ ব্যাংক দেশীয় প্রথম ডিজিটাল ব্যাংক প্রতিষ্ঠার জন্য আবেদনপত্র আহ্বান করেছে। চলতি বছরের ১–৩০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত আবেদন করা যাবে। আবেদনকারীদের পাঁচ লাখ টাকা ফি জমা দিতে হবে, এবং সব সেবা হবে সম্পূর্ণ ডিজিটাল। মঙ্গলবার (২৬ আগস্ট) এক বিজ্ঞপ্তিতে এসব জানিয়েছে কেন্দ্রীয় ব্যাংক।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, প্রযুক্তিনির্ভর আর্থিক খাতে বৈশ্বিক পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশ ব্যাংক ডিজিটাল ব্যাংকের অনুমোদন দেওয়ার উদ্যোগ নিয়েছে। এর লক্ষ্য হলো আর্থিক খাতের দক্ষতা বাড়ানো, সেবার পরিসর বিস্তৃত করা আর ক্ষুদ্র, কুটির ও মাঝারি উদ্যোক্তাদের (সিএমএসই) অর্থায়নের সুযোগ সহজ করা।
বাংলাদেশ ব্যাংক জানিয়েছে, চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের সুযোগ কাজে লাগিয়ে টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি নিশ্চিত করা এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে ভূমিকা রাখাই এই উদ্যোগের মূল লক্ষ্য। বিশেষ করে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জন্য ঋণপ্রবাহ সহজ করতে ডিজিটাল ব্যাংককে গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার মনে করছে তারা।
আবেদনকারীদের নির্ধারিত প্রস্তাবপত্রের সঙ্গে পাঁচ লাখ টাকা (অফেরতযোগ্য) ফি জমা দিতে হবে। এ টাকা যেকোনো তফসিলি ব্যাংক থেকে ব্যাংক ড্রাফট বা পে-অর্ডারের মাধ্যমে বাংলাদেশ ব্যাংকের অনুকূলে দিতে হবে। শর্ত পূরণ না করলে আবেদন বাতিল হবে।
এ ছাড়া আবেদনপত্র সরাসরি জমা দেওয়ার পাশাপাশি ই-মেইলের মাধ্যমেও সব নথি জমা দিতে হবে। বিস্তারিত নির্দেশনা বাংলাদেশ ব্যাংকের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে।
বাংলাদেশ ব্যাংকের ব্যাংকিং রেগুলেশন ও নীতি বিভাগের (বিআরপিডি) মহাব্যবস্থাপক মো. বায়াজিদ সরকার স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়,বাংলাদেশ ব্যাংক মনে করে, ধারাবাহিক প্রযুক্তিগত উদ্ভাবনের ফলে বৈশ্বিক আর্থিক খাতের চিত্র বদলে গেছে। এই পরিবর্তনের চ্যালেঞ্জ বিবেচনায় নিয়ে আর্থিক পণ্য ও সেবা প্রদানে অধিক কার্যকারিতা আনতে এবং আর্থিক ব্যবস্থার বিস্তৃত পরিসর তৈরি করতে কেন্দ্রীয় ব্যাংক অগ্রাধিকার দিচ্ছে।
এর আগে ২০২৩ সালের ১৪ জুন ডিজিটাল ব্যাংকের নীতিমালা করে বাংলাদেশ ব্যাংক। সেই নীতিমালা অনুযায়ী, ডিজিটাল ব্যাংক প্রতিষ্ঠার জন্য ন্যূনতম পরিশোধিত মূলধন ছিল ১২৫ কোটি টাকা। সম্প্রতি কেন্দ্রীয় ব্যাংক তা বৃদ্ধি করে ৩০০ কোটি টাকা করেছে। প্রচলিত ব্যাংকের লাইসেন্স পেতে প্রয়োজন ৫০০ কোটি টাকা। ১৯৯১ সালের ব্যাংক কোম্পানি আইনের আওতায় ডিজিটাল ব্যাংকের লাইসেন্স দেওয়া হবে। পেমেন্ট সার্ভিস পরিচালিত হবে ২০১৪ সালের বাংলাদেশ পেমেন্ট অ্যান্ড সেটেলমেন্ট সিস্টেম রেগুলেশনের অধীন।
বাংলাদেশ ব্যাংকের নীতিমালা অনুযায়ী, ডিজিটাল ব্যাংক পরিচালনার জন্য প্রধান কার্যালয় থাকবে। সেবা দেওয়ার বেলায় স্থাপনা লাগবে না। অর্থাৎ এই ব্যাংক ওভার দ্য কাউন্টার (ওটিসি) সেবা দেবে না। ডিজিটাল ব্যাংকের নিজস্ব শাখা বা উপশাখা, এটিএম, সিডিএম অথবা সিআরএমও থাকবে না। সব সেবাই হবে অ্যাপনির্ভর, মুঠোফোন বা ডিজিটাল যন্ত্রে।
অর্থনীতি
মানুষের হাতে নগদ অর্থ আবারও বাড়ছে

মানুষের হাতে থাকা নগদ টাকার পরিমাণ আবারও বাড়ছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের সর্বশেষ প্রতিবেদনে দেখা গেছে, চলতি বছরের মে মাসে ব্যাংকের বাইরে নগদ টাকার পরিমাণ ছিল ২ লাখ ৯৩ হাজার ৭৭৮ কোটি টাকা, যা জুনে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২ লাখ ৯৬ হাজার ৪৫১ কোটি টাকা। অর্থাৎ এক মাসে মানুষের হাতে বেড়েছে ২ হাজার ৬৭৩ কোটি টাকা।
এর আগে এপ্রিলে মানুষের হাতে নগদ টাকার পরিমাণ কমলেও মে মাসে তা বেড়েছিল ১৬ হাজার ৪১১ কোটি টাকা।
কেন্দ্রীয় ব্যাংকের তথ্য বলছে, গত বছরের সেপ্টেম্বর থেকে চলতি বছরের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত মানুষের হাতে নগদ টাকার প্রবাহ কমছিল। তবে মার্চে হঠাৎ তা বেড়ে দাঁড়ায় ২ লাখ ৯৬ হাজার ৪৩১ কোটি টাকা। এপ্রিলে আবার কমে দাঁড়ায় ২ লাখ ৭৭ হাজার ৩৬৬ কোটি টাকা। পরের মাস মে থেকে নগদ টাকার পরিমাণ ধারাবাহিকভাবে বাড়ছে।
অর্থনীতিবিদরা বলছেন, উচ্চ মূল্যস্ফীতির কারণে মানুষের খরচ বেড়েছে, এজন্য তারা ব্যাংক থেকে টাকা তুলে হাতে রাখছেন। অন্যদিকে ব্যাংক খাতের অনিয়ম ও আস্থাহীনতাও নগদ টাকার প্রবাহ বৃদ্ধির পেছনে একটি বড় কারণ।
গত বছরের আগস্ট পর্যন্ত মানুষের হাতে নগদ টাকা ক্রমাগত বাড়ছিল। তবে ওই বছরের ৫ আগস্ট ছাত্রজনতার গণঅভ্যুত্থানের মুখে আওয়ামী লীগ সরকারের বিদায়ের পর ব্যাংক খাতে মানুষের আস্থা কিছুটা ফিরতে শুরু করে। এর ধারাবাহিকতায় সেপ্টেম্বরে নগদ টাকার প্রবাহ কমে দাঁড়ায় ২ লাখ ৮৩ হাজার ৫৫৩ কোটি টাকা, অক্টোবরে ২ লাখ ৭৭ হাজার ৮১০ কোটি এবং ডিসেম্বরে ২ লাখ ৭৬ হাজার ৩৭১ কোটি টাকা। চলতি বছরের জানুয়ারিতে আরও কমে দাঁড়ায় ২ লাখ ৭৪ হাজার ২৩০ কোটি এবং ফেব্রুয়ারিতে কমে দাঁড়ায় ২ লাখ ৭১ হাজার ৪৯৫ কোটি টাকা।
তবে গত মার্চে মানুষের হাতে নগদ টাকার পরিমাণ আবার বেড়ে দাঁড়ায় ২ লাখ ৯৬ হাজার ৪৩১ কোটি টাকা। এরপর এপ্রিলে তা কিছুটা কমলেও মে ও জুনে আবার ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতা দেখা গেছে।
এদিকে শুধু নগদ টাকার প্রবাহই নয়, বাজারে মুদ্রা সরবরাহও বেড়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের হিসাব অনুযায়ী, মে মাসে ছাপানো টাকার স্থিতি (রিজার্ভ মানি) ছিল ৩ লাখ ৯৮ হাজার ৮৪৮ কোটি টাকা, যা জুনে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৪ লাখ ১৩ হাজার ১৭৯ কোটি টাকা। অর্থাৎ এক মাসে মুদ্রা সরবরাহ বেড়েছে ১৪ হাজার ৩৩০ কোটি টাকা।
অর্থনীতি
খেলাপি ঋণের ৪৯.৪৩ শতাংশই শিল্প খাতে

ব্যাংক খাতের ক্যানসার হিসেবে পরিচিত খেলাপি ঋণ এখন উৎপাদনমুখী শিল্প খাতে ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের আর্থিক স্থিতিশীলতা প্রতিবেদন-২০২৪ অনুযায়ী, মোট খেলাপি ঋণের প্রায় অর্ধেক (৪৯.৪৩ শতাংশ) এখন তৈরি পোশাক, টেক্সটাইল, চামড়া, জাহাজ নির্মাণসহ বিভিন্ন উৎপাদনমুখী শিল্প খাতে কেন্দ্রীভূত।
প্রতিবেদনে বলা হয়, ২০২৩ সালের ডিসেম্বর শেষে ব্যাংক খাতের বিতরণকৃত ঋণের পরিমাণ ছিল ১৭ লাখ ১১ হাজার ১৩৮ কোটি টাকা। এর মধ্যে খেলাপিতে পরিণত হয়েছিল ৩ লাখ ৪৬ হাজার ৫৪৭ কোটি টাকা, যা মোট বিতরণকৃত ঋণের ২০.২৫ শতাংশ।
এক বছর পর ২০২৪ সালের ডিসেম্বর শেষে উৎপাদনমুখী শিল্প খাতে খেলাপি ঋণের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ১ লাখ ৭১ হাজার ৩০৪ কোটি টাকা। আগের বছর এই খাতে খেলাপি ঋণ ছিল ৭২ হাজার ৬৪১ কোটি টাকা। অর্থাৎ, এক বছরে খেলাপি ঋণ বেড়েছে প্রায় ৯৮ হাজার ৬৬৩ কোটি টাকা।
তৈরি পোশাক ও টেক্সটাইল খাতের সংকট
সবচেয়ে বেশি ঋণ বিতরণ হয়েছে তৈরি পোশাক খাতে। ২০২৪ সালের ডিসেম্বর শেষে এই খাতে বিতরণকৃত ঋণের পরিমাণ ছিল ১ লাখ ৮৮ হাজার ২৭১ কোটি টাকা। এর মধ্যে খেলাপিতে পরিণত হয়েছে ৪৮ হাজার ৬৩৮ কোটি টাকা (১৪.০৪ শতাংশ)। আগের বছর এই খাতে খেলাপি ঋণ ছিল ২২ হাজার ৭০২ কোটি টাকা। এক বছরে খেলাপি ঋণ বেড়েছে ২৫ হাজার ৯৩৬ কোটি টাকা।
অন্যদিকে, টেক্সটাইল খাতে ২০২৪ সালের ডিসেম্বর শেষে বিতরণকৃত ঋণ ছিল ১ লাখ ৪৯ হাজার ১৭১ কোটি টাকা। এর মধ্যে খেলাপিতে পরিণত হয়েছে ৩৬ হাজার ৫২০ কোটি টাকা (১০.৫৪ শতাংশ)। ২০২৩ সালে এ খাতের খেলাপি ঋণ ছিল ১৫ হাজার ৩৩৪ কোটি টাকা। এক বছরে খেলাপি ঋণ বেড়েছে ২১ হাজার ১৮৬ কোটি টাকা।
অন্যান্য শিল্প খাত
চামড়া খাত: ২০২৪ সালের ডিসেম্বর শেষে ঋণ ১৪ হাজার ৮৯৮ কোটি টাকা, খেলাপি ৫ হাজার ৭৭৬ কোটি টাকা। আগের বছর খেলাপি ছিল ২ হাজার ৮১৭ কোটি টাকা।
জাহাজ নির্মাণ খাত: ঋণ ২০ হাজার ৫০৬ কোটি টাকা, খেলাপি ৮ হাজার ৩১ কোটি টাকা। এক বছরে বেড়েছে ৪ হাজার ৪৫৮ কোটি টাকা।
কৃষিভিত্তিক শিল্প খাত: ঋণ ৬৬ হাজার ৯৫৮ কোটি টাকা, খেলাপি ৭ হাজার ৩৫৭ কোটি টাকা।
ব্যবসা-বাণিজ্য খাতেও ঋণখেলাপি
২০২৪ সালের ডিসেম্বর শেষে ব্যবসা ও বাণিজ্য খাতে বিতরণকৃত ঋণের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৩ লাখ ২৩ হাজার ৪৬৭ কোটি টাকা। এর মধ্যে খেলাপি ঋণ দাঁড়িয়েছে ৮৮ হাজার ৩৮৯ কোটি টাকা, যা মোটের ২৫.৫১ শতাংশ।
খাত সংশ্লিষ্টরা বলছেন, শিল্পখাতে ঋণ বিতরণে নিয়মকানুন মানা হয় না। বড় শিল্পপ্রতিষ্ঠান, বিশেষ করে রাজনৈতিকভাবে প্রভাবশালীরা সহজেই ঋণ পায় এবং অনেক ক্ষেত্রে তা ফেরত দেয় না। কেউ কেউ আবার নামে-বেনামে টাকা বিদেশে পাচার করছে। ফলে শিল্পখাতের খেলাপি ঋণ লাগামহীনভাবে বাড়ছে।
অর্থনীতি
সবজির দামে পুড়ছে মানুষ, ডিমের ডজন ১৫৫

বেশ কিছুদিন ধরে সবজির বাজারে ঊর্ধ্বগতির দাম কমার কোনো লক্ষণ নেই। প্রায় সব ধরনের সবজির দাম ৮০ টাকার ঘরে আটকে আছে। তবে করলা, বেগুন ও টমেটোর মতো সবজিগুলোর দাম আরও বেশি। সবজির সঙ্গে সপ্তাহের ব্যবধানে বেড়েছে ডিমের দামও। প্রতি ডজন ডিম বিক্রি হচ্ছে ১৫০ টাকা থেকে ১৫৫ টাকা দরে।
শুক্রবার (২২ আগস্ট) সকালে রাজধানীর বিভিন্ন বাজার ঘুরে সবজির চড়া দামের এমন চিত্র দেখা গেছে।
রাজধানীর শনিরআখরা কাঁচাবাজারে সবজি কিনতে আসা ইকরাম আহমেদ বলেন, আমাদের আয় সীমিত, টানাটানির সংসার। এরমধ্যে কোনো ক্ষেত্রে বেশি খরচ হলে অন্যদিকে টান পড়ে যায়। সবজির মূল্যবৃদ্ধি আসলেই আমাদের কষ্টের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। আগের চেয়ে সবজি কেনা কমিয়ে দিয়েছি। তবে দু-এক কেজি না কিনলে তো রান্না চলবে না। অল্প অল্প করে নিচ্ছি।
শুধু শুধু ইকরাম নন, বাজারে আসা ক্রেতাদের সবাই সবজির চড়া দামে নাকাল। অনেকে দাম বেশি হওয়ায় সবজি কেনা কমিয়ে দিয়েছেন। কেউ আবার সবজি না কিনেই ফিরে যাচ্ছেন খালি হাতে।
বিক্রেতারা বলছেন, টানা বৃষ্টির কারণে এখন সবজির উৎপাদন আর সরবরাহ কম। তাই দাম বেড়েছে।
সবুজ হোসেন নামের একজন বিক্রেতা বলেন, এখন কম উৎপাদনের মৌসুম চলছে। এসময় আবহাওয়ার কারণে জমিতে সবজি চাষ কম হয়, ফলে সরবরাহও কমে যায়। এরমধ্যে অস্বাভাবিক বৃষ্টিতে অনেক এলাকার সবজিক্ষেত তলিয়ে গেছে। এ কারণে বাজারে সবজির দাম বেড়েছে।০
বাজারে এখন আলু, বই কচু ও কাঁচা পেঁপে ছাড়া আর কোনো সবজি ৮০ টাকার কমে মিলছে না। এমনকি গ্রীষ্মের সবজি ঢ্যাঁড়স-পটোলও বিক্রি হচ্ছে ৮০-১০০ টাকায়। এছাড়া বরবটি, বেগুন, উস্তা, চিচিঙ্গা, ঝিঙ্গার, ধুন্দল কাঁকরোলের দাম বাজারভেদে ১০০ থেকে ১২০ টাকা পর্যন্ত বিক্রি হচ্ছে।
বাজারে এখন কাঁচামরিচের দামও অনেক চড়া। প্রতি কেজি বিক্রি হচ্ছে ২০০ থেকে ৩২০ টাকা পর্যন্ত। কয়েকদিন আগেও প্রতি কেজি কাঁচামরিচের দাম ছিল ১৫০ থেকে ১৬০ টাকা। বাজারে এখন প্রতি পিস চালকুমড়া ৭০ টাকা, লাউ ১০০ টাকা, প্রতি কেজি মিষ্টি কুমড়ার ফালি ৪০ টাকা বিক্রি হচ্ছে।
সবজির সঙ্গে সপ্তাহের ব্যবধানে বেড়েছে ডিমের দামও। আগে প্রতি ডজন ডিম ১৪০ টাকায় বিক্রি হলেও এখন বেড়ে হয়েছে ১৫০ থেকে ১৫৫ টাকা। পাড়া-মহল্লার দোকানে প্রতি হালি ডিম বিক্রি হচ্ছে ৫০ থেকে ৫২ টাকা দরে। মাত্র একমাস আগেও প্রতি ডজন ডিমের দাম ছিল ১২০ থেকে ১২৫ টাকা।
ডিমের দাম বেশি কেন—জানতে চাইলে মালিবাগ বাজারের ডিম বিক্রেতা বুলু মিয়া জানান বাজারে অন্যান্য পণ্যের দাম বাড়ায় প্রভাব পড়েছে ডিমের দামেও। সবজির দাম বাড়লেই স্বাভাবিকভাবে ডিমের চাহিদা বেড়ে যায়। এছাড়া বৃষ্টির কারণে ডিমের সরবরাহে বিঘ্ন ঘটে।
বাজারে ব্রয়লার মুরগি প্রতি কেজি ১৭০ থেকে ১৮৫ টাকায় বিক্রি হচ্ছে। যা গত সপ্তাহের চেয়ে কেজিতে ১০ থেকে ২০ টাকা পর্যন্ত বেড়েছে। সোনালি মুরগি বিক্রি হচ্ছে ৩০০ থেকে ৩২০ টাকা কেজি দরে।
কাফি
অর্থনীতি
দুই মাসে বাংলাদেশি পোশাকের ক্রয়াদেশ বেড়েছে ৩২ শতাংশ

যুক্তরাষ্ট্রের নতুন শুল্কনীতির কারণে বাংলাদেশের জন্য নতুন সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। বিদেশি ক্রেতারা ধীরে ধীরে নয়াদিল্লি, ইসলামাবাদ ও বেইজিং থেকে মুখ ফিরিয়ে এখন লাল-সবুজের পতাকার দিকে ঝুঁকছেন। এ ছাড়া বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলের ক্রেতারা অর্ডার নিয়ে ঢাকায় আসছেন, ফলে গত দুই মাসে আগের একই সময়ের তুলনায় ক্রয়াদেশ বেড়েছে প্রায় ৩২ শতাংশ।
বাংলাদেশ গার্মেন্টস ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যান্ড এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশন (বিজিএমইএ), বাংলাদেশ নিটওয়্যার ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যান্ড এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশন (বিকেএমইএ), বাংলাদেশ রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো (ইপিবি) ও সরাসরি পোশাক রপ্তানির সঙ্গে যুক্ত শীর্ষস্থানীয় প্রতিষ্ঠানগুলো জানিয়েছে, দেশের তৈরি পোশাক খাতে নতুন সম্ভাবনা জেগে উঠেছে। চলতি আগস্টের প্রথম সপ্তাহ থেকেই বিশ্ববাজারের ক্রেতাদের মধ্যে বাংলাদেশে নতুন রপ্তানি আদেশ দেওয়ার প্রবল আগ্রহ দেখা যাচ্ছে। এ ধারা অব্যাহত থাকলে সেপ্টেম্বর থেকে তৈরি পোশাকের ক্রয়াদেশ দ্বিগুণ হয়ে যেতে পারে।
পোশাক খাতের সংশ্লিষ্টদের মতে, গত দুই মাসে আগের একই সময়ের তুলনায় ক্রয়াদেশ প্রায় ৩২ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। চলতি অর্থবছরের প্রথম মাসেই মোট রপ্তানি আয়ে ২৫ শতাংশ প্রবৃদ্ধি হয়েছে। ইপিবির তথ্য অনুযায়ী, জুলাই মাসে কেবল পোশাক খাত থেকেই রপ্তানি আয় দাঁড়িয়েছে ৩৯৬ কোটি ডলার, যা দেশের মোট রপ্তানির প্রায় ৮৩ শতাংশ।
ইপিবির ভাইস চেয়ারম্যান আনোয়ার হোসেন জানান, ক্রেতাদের চাহিদা অনুযায়ী রপ্তানি আদেশ গ্রহণ ও সময়মতো শিপমেন্ট সম্পন্ন হলে চলতি অর্থবছরের প্রথম প্রান্তিক (জুলাই-সেপ্টেম্বর) শেষে মোট রপ্তানির প্রবৃদ্ধি ৩০ থেকে ৩৫ শতাংশ কিংবা তারও বেশি হতে পারে। এমন পরিস্থিতি অব্যাহত থাকলে আট মাসের মধ্যেই রপ্তানির লক্ষ্যমাত্রা অতিক্রম করা সম্ভব হবে।
তিনি আরও জানান, শুধু তৈরি পোশাক নয়—চীন ও ভারত থেকে আগে যুক্তরাষ্ট্রে যেসব পণ্য রপ্তানি হতো, সেসবের ক্রেতারাও এখন বাংলাদেশে আসছেন। উদ্যোক্তারা যদি তাদের প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে পারেন, তবে এসব ক্রেতা স্থায়ীভাবেই বাংলাদেশমুখী হতে পারেন। তবে এর জন্য দ্রুত বিদ্যুৎ-জ্বালানি সংকট সমাধান ও বন্দরের সক্ষমতা বাড়ানো জরুরি।
বিকেএমইএ সভাপতি মোহাম্মদ হাতেম জানান, গত ছয়-সাত মাস ধরে চীনের পরিবর্তে অনেক ক্রেতা তাদের আমদানি আদেশ ভারতে স্থানান্তর করছিলেন। কারণ, তারা আগেই অনুমান করেছিলেন যে যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপের বাজারে চীনের রপ্তানিকারকদের কঠিন সময়ের মুখোমুখি হতে হবে। তবে হঠাৎ ভারতের ওপর বাড়তি মার্কিন শুল্ক আরোপ সেই প্রবণতাকে বদলে দিয়েছে। এর সঙ্গে চীনের পোশাক কারখানাগুলোতে শ্রমিক সংকট তৈরি হওয়ায় বাংলাদেশ এ সুযোগ পুরোপুরি কাজে লাগাতে পারবে।
তিনি আশা প্রকাশ করে বলেন, বর্তমান চাহিদা অনুযায়ী সব রপ্তানি আদেশ বাস্তবায়ন করা গেলে চলতি অর্থবছরেই রপ্তানি খাতের প্রবৃদ্ধি ৪০ থেকে ৪৫ শতাংশ ছাড়িয়ে যেতে পারে। তবে শিল্পে বিনিয়োগ ও উৎপাদন প্রবাহ এখনো কিছুটা বাধাগ্রস্ত হচ্ছে, বিশেষ করে ব্যাংকিং খাতের কারণে। তার মতে, ব্যাংকগুলো বর্তমানে পুরোপুরি রিকভারি মোডে আছে, তারা ঋণ আদায়ে মরিয়া। কিন্তু বহু বছরের অনিয়ম ও লুটপাটের সমস্যাগুলো রাতারাতি সমাধান সম্ভব নয়। ঋণের সুদহার বাড়ানো বা ঋণ প্রবাহ কমিয়ে ব্যবসা সম্প্রসারণও সম্ভব নয়। এখনো পরিস্থিতি এমন নয় যে একদিনে সব ঠিক করে ফেলা যাবে। তিনি বলেন, সহনীয় নীতির বিপরীতে গিয়ে যেমন রাজস্ব আয় বাড়ানো যায় না, তেমনি উদ্যোক্তাদের আতঙ্কিত করে ঋণ আদায় করাও সম্ভব নয়।
বিজিএমইএর সাবেক পরিচালক মহিউদ্দিন রুবেল আমার জানান, সাধারণত জুলাই, আগস্ট ও সেপ্টেম্বরে তুলনামূলক কম রপ্তানি হয়ে থাকে; কিন্তু এবার পরিস্থিতি ভিন্ন। রপ্তানি আয় বাড়ছে, একই সঙ্গে আসছে নতুন নতুন ক্রয়াদেশ। আগে যেখানে শুধু বড় ক্রেতারা অর্ডার দিতেন, সেখানে গত এক মাসে যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপের বাজারের জন্য ছোট ছোট ক্রেতারাও অর্ডার দিতে শুরু করেছেন। এতে গত মাসে রপ্তানিতে উল্লেখযোগ্য সাফল্য এসেছে।
তিনি বলেন, যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে পাল্টা শুল্ক কার্যকর হওয়ার পর সেখানকার ক্রেতা প্রতিষ্ঠানগুলোর কাছ থেকে বাংলাদেশ ভালো সাড়া পাচ্ছে। প্রতিযোগী দেশগুলোর তুলনায় চীন ও ভারতের চেয়ে বাংলাদেশ বেশি সুবিধাজনক অবস্থানে থাকায় আমাদের পণ্যের চাহিদা বেড়েছে।
পরামর্শ দিয়ে তিনি বলেন, বাড়তি ক্রয়াদেশ গ্রহণে সতর্ক হতে হবে। কোনো অবস্থাতেই মূল্যছাড়ে পণ্য বিক্রি করা উচিত নয়। কারণ, একবার কম দামে পণ্য বিক্রি করলে পরে ক্রেতারা আর সঠিক দাম দিতে চাইবে না। এতে রপ্তানি আয় বাড়লেও অল্প সময়ের মধ্যেই অনেক প্রতিষ্ঠান উৎপাদন বন্ধ করে দেনার ফাঁদে পড়তে পারে। এ পরিস্থিতি মোকাবিলায় একটি টাস্কফোর্স গঠন করা উচিত সরকারের।