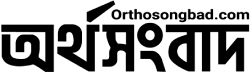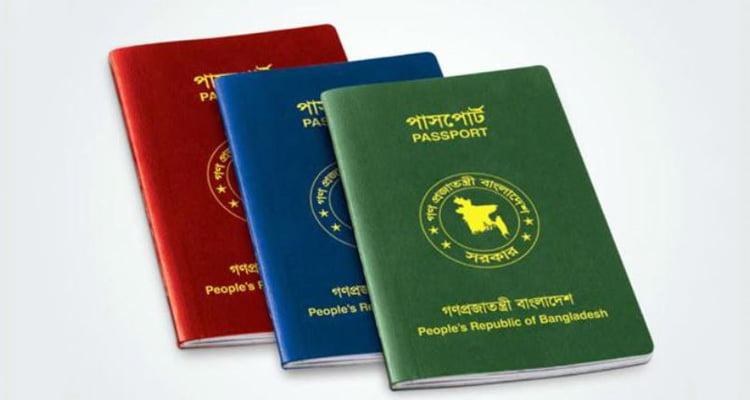বাংলাদেশ বেশি জনসংখ্যার ছোট অর্থনীতির ছোট একটি দেশ। তাই আমাদের মানব সম্পদ ব্যবহারের সুযোগও কম। সেটা দেশে এবং বিদেশেও। আমরা আরো জানি, জনসংখ্যা বাড়ে জ্যামিতিক হারে। রোহিঙ্গাদের মাঝে জন্মহার বেশি।
ফলে, আজকের দশ লাখ রোহিঙ্গা ২০ লাখ, বা কোটি হতে খুব বেশি সময় লাগবে না। বাংলাদেশের সার্বিক অর্থনীতি ও কর্মসংস্থানের ওপর এর যে নেতিবাচক প্রভাব আসন্ন তা নিয়ে কারো দ্বিমত নেই।
প্রধানমন্ত্রী অভিমান করে যেমন বলেছেন, ‘আমরা ১৬ কোটি মানুষকে খাবার দেই। সুতরাং বিপদে পড়ে আমাদের দেশে আসা দুই-পাঁচ-সাত লাখ মানুষকে খাবার দেওয়ার ক্ষমতাও আমাদের আছে।’ কিন্তু শুধু খাবারই তো শেষ কথা না। মানুষের যাবতীয় প্রয়োজন মেটানোই এর সঙ্গে সম্পৃক্ত। আপাতত সাত লাখের হিসেব বেড়ে বহুগুণ হয়ে যাবে।
বাড়তি চাপ পড়বে আমাদের সীমিত অর্থনীতি ও কর্মসংস্থানের ওপর। ইতোমধ্যে তার ইঙ্গিতও দেখা গেছে।
রোহিঙ্গাদের যে বর্তমান প্রজন্ম তারা আজন্ম একটি নির্যাতিত জনগোষ্ঠী। এ নির্যাতনের ইতিহাসের শুরু তাদের জন্মেরও আগে। তাই রোহিঙ্গারা জীবনের প্রয়োজনে সব সুযোগের সদ্ব্যবহার করবে এটাই স্বাভাবিক। সে কারণেই শরণার্থীদের জন্য গ্রহণকারী রাষ্ট্রকে বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হয়।
তাদের জন্য পৃথক শরণার্থী ব্যবস্থার বিকল্প নেই। সীমাবদ্ধতার মধ্যে সরকার বেশ কিছু পদক্ষেপ নিয়েছেও। কিন্তু দশ লাখ ছিন্নমূল মানুষের বিপরীতে যেকোনো ব্যবস্থাপনাই ভেঙে পড়তে পারে। তার মধ্যেও সরকার অত্যন্ত সফলভাবে তাদের নিবন্ধনের কাজটি করতে পেরেছে। কিন্তু নিবন্ধন করেও বাংলাদেশ এর সুফল পাচ্ছে না। কারণ মিয়ানমার এখন বলছে যাদের কাছে মিয়ানমারের পাসপোর্ট বা নাগরিকত্বের সনদ আছে তাদেরই শুধু ফেরত নেওয়া হবে (যদি নেওয়া হয়)।
মিয়ানমারের এ যুক্তি বা শর্ত যে কতটা অযৌক্তিক, বেআইনি ও অবাস্তব তা আগের একটি লেখায় বিস্তারিত বর্ণনা করা হয়েছে। আন্তর্জাতিক বিশ্বও তা জানে। কিন্তু মিয়ানমারের পক্ষ থেকে প্রত্যাবাসনের কোনো নমুনা দেখা যাচ্ছে না।
রোহিঙ্গা নিবন্ধনের আরেকটি উদ্দেশ্য ছিল যাতে তারা এদেশের মূল জনগোষ্ঠীর সঙ্গে মিশে যেতে না পারে। অর্থাৎ, যাতে তারা বাংলাদেশের নাগরিকদের সুযোগ-সুবিধায় ভাগ বসাতে না পারে। একই সঙ্গে শরণার্থী হিসেবে তাদের যে দেশি-বিদেশি আন্তর্জাতিক সুযোগ-সুবিধা রয়েছে তাও যেনো অক্ষুণ্ন থাকে। সেখানে আবার দেশীয় সুবিধাভোগীরা ভাগ বসাতে না পারে। কিন্তু এখন রোহিঙ্গারা শরণার্থী হিসেবে যা পাওয়ার তা পাচ্ছে, সেই সঙ্গে বাংলাদেশের নাগরিকদের সুযোগ-সুবিধার ওপরও ভাগ বসিয়েছে।
বাংলাদেশের পাসপোর্ট ব্যবহার করে বিভিন্ন দেশে কয়েক লাখ রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী এরই মধ্যে চাকরি-ব্যবসা করছে। রোহিঙ্গারা বিদেশে যাক তাতে কোনো সমস্যা নেই। কিন্তু সমস্যা হলো যখন বাংলাদেশের পাসপোর্ট ব্যবহার করে যায় তখন।
কারণ এতে বাংলাদেশি একজন নাগরিকের সুযোগটি সংকুচিত হয়ে যাচ্ছে। এভাবে বিদেশে বাংলাদেশের কয়েক লাখ নাগরিক তাদের কর্মসংস্থানের সুযোগ হারিয়েছে। ভবিষ্যতে এর পরিমাণ আরো বাড়বে। কারণ, বিদেশে কর্মসংস্থানের জন্য কেউ গেলে যদি সুযোগ আসে সে চেষ্টা করে তার পরিবার-পরিজন বা কাছের কাউকে নিতে। রোহিঙ্গারা বিদেশে যাওয়াতে ভবিষ্যতে রোহিঙ্গাদের জন্যই সুযোগ সৃষ্টি হলো, একই সঙ্গে বাংলাদেশের একজন নাগরিক সেই সুযোগ হারালো। ভবিষ্যতের সুযোগও নষ্ট হলো। এ বিষয়টি আপাতত হয়তো দৃশ্যমান না। কিন্তু একটা সময়ে গিয়ে এটি প্রকাশ্য রূপ নেবে।
মালয়েশিয়ায় যেমন প্রচুর তামিল বা দক্ষিণ ভারতীয় আজ বিভিন্ন কাজে জড়িত। বাংলাদেশের কিছু অঞ্চলের লোকজনও যেমন কোনো কোনো দেশে বেশি অবস্থান করছেন-এর মূল কারণ এটাই। সুযোগ সুযোগের সৃষ্টি করে আর বঞ্চনা বঞ্চনারই পথ দেখায়। এটি শুধু বিদেশে কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রেই সত্য নয়, অন্য অনেক ক্ষেত্রেই বাস্তব।
এমনিতেই বিদেশে প্রবাসীদের জন্য কর্মসংস্থানের সুযোগ সীমিত হয়ে আসছে। এমনকি অভিবাসনের সুযোগও অনেক দেশ বন্ধ করে দিয়েছে বা সীমিত আকারে বহাল রেখেছে। মালয়েশিয়ায় আশির দশকে প্রচুর বাংলাদেশি, ভারতীয়, চৈনিকরা গিয়েছে। তারা কাজ করেছে, নাগরিকও হয়েছে। আজ মালয়েশিয়া সেই সুযোগ কমিয়ে দিয়েছে।
মধ্যপ্রাচ্যের অমানবিক কাহিনীতে আমরা উদ্বিগ্ন। সেখানে গিয়ে আমাদের নারী শ্রমিকরা যে অমানবিক ও পাশবিকতার শিকার হন তা গণমাধ্যমে আসছে।
পাশাপাশি বৈধ ও দক্ষ শ্রমিক পাঠানোর ক্ষেত্রে বিদেশি শ্রম বাজারে আমাদের সুনাম নেই। অবৈধভাবে ও বিপথে গিয়ে নানাভাবেই এদেশের শ্রমিকরা জেল-জরিমানার শিকার হন। এটি গ্রহণকারী রাষ্ট্রের জন্য আরো বড় ঝামেলার। সেই সঙ্গে অনেকে সেখানে গিয়ে নানা অপরাধে জড়িয়ে পড়েন। বেঁচে থাকার প্রয়োজনে অনেকে অবৈধ কাজে জড়িয়ে পরে। ফলে, এতে সার্বিকভাবে শ্রম বাজারে আমাদের দুর্নাম হচ্ছে। অনেক জায়গায় আমরা ভালোও করছি। কিন্তু খারাপের আলোচনাটাই বেশি হয়, এটিই স্বাভাবিক।
তারপরও ন্যূনতম যেটুকু সুযোগ আমাদের আছে তার ওপর যদি রোহিঙ্গারা ভাগ বসায় সেটি দুশ্চিন্তারই কথা। কিন্তু তারচেয়েও বেশি ভাবনার বিষয়, রোহিঙ্গারা কীভাবে বাংলাদেশের পাসপোর্ট পায় ও সেই পাসপোর্ট নিয়ে কীভাবেই বা বিদেশে যায়। শেষ প্রশ্নটির জবাব পরিষ্কার। বিদেশে বৈধ-অবৈধ দু'ভাবেই যাওয়া যায়। টেকনাফ থেকে ট্রলারে করেও মালয়েশিয়া যাওয়া যায়। অনেক বাংলাদেশি এভাবে গিয়েছেন ও যাচ্ছেন। বাংলাদেশ থেকে বিদেশে যাওয়ার সব ধরনের অবৈধ পথ আমরা বন্ধ করতে পারিনি। এটি করতে না পারলে আমাদেরই ক্ষতি। যার ক্ষতিকর ফল আমরা এরই মধ্যে পেতেও শুরু করেছি। অনেক রাষ্ট্র বৈধ পথও বন্ধ বা সংকুচিত করে ফেলেছে।
কিন্তু প্রথম ও প্রধান প্রশ্নটি হচ্ছে রোহিঙ্গারা কীভাবে বাংলাদেশি পাসপোর্ট পায়? তারা তো বাংলাদেশের নাগিরক না। তাদের তো বাংলাদেশের নাগরিকত্বের সনদ বা এনআইডি নেই। নেই জন্ম সনদও। বসবাস করার কথা রোহিঙ্গা ক্যাম্পে। তাহলে কীভাবে এটি সম্ভব?
যেখানে এদেশের একজন নাগরিককে পাসপোর্ট পেতে আজও অনেক ঝক্কি পোহাতে হয়। যতোই ‘ডিজিটাল’ এর কথা বলি, দালালের দৌরাত্ম তো কমেনি। পাসপোর্ট অফিস অনেকটাই ডিজিটাল একথা স্বীকার করতে হবে। কিন্তু পুলিশ ভেরিফিকেশনের নামে পয়সা তোলা কমেনি। এদেশে ক’জন পাসপোর্টধারী পাসপোর্ট ভেরিফিকেশনে পুলিশকে পয়সা না দিয়ে পাসপোর্ট পেয়েছেন?
যদি পয়সা না দেন তবে, ‘খুজিয়া পাওয়া যায় নাই’ অথবা অন্য কোনো অবজারভেশন দিয়ে পাঠিয়ে দেবে। ভেরিফিকেশনের নামে হয়রানির প্রতিবেদন বাংলানিউজেও এসেছে বহুবার। কিন্তু অবস্থার পরিবর্তন হয়নি।
পাসপোর্ট ভেরিফিকেশনের মূল উদ্দেশ্যই হলো আবেদনকারী বাংলাদেশের নাগরিক কিনা তা যাচাই করা। সেই সঙ্গে তিনি কোনো অপরাধ কর্মে জড়িত কিনা তাও দেখা। এই যদি কথা হয়, তবে রোহিঙ্গারা বাংলাদেশি পাসপোর্ট পেল কী করে? পুলিশ সেখানে কি ভেরিফিকেশন করলো? এসব প্রশ্নের কোনো জবাব নেই।
আসলে অসাধু একটি দালালচক্র এর সঙ্গে জড়িত আছে। সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে ভেরিফিকেশন কর্মকর্তা, স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, পাসপোর্ট অফিসের কর্মচারী, পুলিশের কতিপয় কর্মকর্তা এবং অন্যান্য দালালদের সঙ্গেও রয়েছে তাদের যোগায়োগ। যেখানে দেশের একজন নাগরিককে পাসপোর্ট পেতে জন্মনিবন্ধন সনদ, জাতীয় পরিচয়পত্রসহ আরো নানা তথ্য প্রদান করতে হয়, সেখানে রোহিঙ্গারা কীভাবে এসব জোগার করে পাসপোর্ট পায় তা এক রহস্যই বটে।
বিতাড়িত হয়ে রোহিঙ্গারা তাদের সঙ্গে নগদ টাকা-পয়সা যা আছে সব নিয়ে এসেছেন। সেই সঙ্গে নিয়ে এসেছেন স্বর্ণালংকার। ফলে, সবকিছুর বিনিময়ে নগদ অর্থ দিয়ে তারা সহজেই বিদেশে পাড়ি জমাতে পারছে। সেজন্য আদম পাচারকারী চক্রের কাছেও রোহিঙ্গারা এখন বড় কাস্টমার।
প্রবাসী কল্যাণমন্ত্রীর তথ্য অনুযায়ী, দুই থেকে আড়াই লাখ রোহিঙ্গা বাংলাদেশের পাসপোর্ট নিয়ে বিদেশে চলে গেছে। এটি সরকারি হিসাব। দুই-আড়াই লাখ বিদেশে কর্মসংস্থানের প্রশ্নে অনেক অঙ্ক। মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর, মধ্যপ্রাচ্য এখন রোহিঙ্গাদের অন্যতম গন্তব্য। ফলে অদূর ভবিষ্যতে রোহিঙ্গারা বিদেশে বাংলাদেশের শ্রম বাজারের দখলদারিত্ব প্রতিষ্ঠা করলে অবাক হওয়ার কিছু নেই।
সরকারি তথ্য মতে, নিবন্ধিত রোহিঙ্গার সংখ্যা এখন ১১ লাখ ১৮ হাজার ৫৭৬। তাদের নাম-ঠিকানা, ছবি ও আঙুলের ছাপসহ সব তথ্য সরকারের কাছে আছে। সমস্যা হচ্ছে, নিবন্ধিত রোহিঙ্গাদের তথ্যভাণ্ডার এখনো পাসপোর্টের মূল সার্ভারের সঙ্গে যুক্ত হয়নি। ফলে, পাসপোর্ট অফিসেরও তেমন কিছু করার নেই। কিন্তু পাসপোর্ট অফিসে আসার আগে মাঠ পর্যায় থেকেই তো রোহিঙ্গাদের পাসপোর্ট নেয়ার চেষ্টা প্রতিহত করা যায়। দুই-চার পাঁচ হাজার থেকে শুরু করে ২০ থেকে ৫০ হাজার টাকায় বাংলাদেশের পাসপোর্ট মেলে। মেলে নাগরিকত্বের সনদও।
সেই সঙ্গে বিদেশে বাংলাদেশি শ্রমিক (আদতে রোহিঙ্গা)। বিষয়টি নিয়ে সংশ্লিষ্টরা একটু ভেবে দেখতে পারেন।